আরোহ পদ্ধতিকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে কিরূপে প্রয়োগ করব?
আমরা ইতোপূর্বে সম্ভাবনাভিত্তিক আরোহ যুক্তি পদ্ধতির সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে অবগত হয়েছি এবং এ পদ্ধতিকে পূর্বের সাথে তুলনা করে মূল্যায়ন করেছি। এখন আমরা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি প্রয়োগ করব।
প্রথম ধাপ
: এখানে আমরা লক্ষ্য করব যে,কতগুলো শৃঙ্খলিত বিষয় এবং জীবন্ত এক অস্তিত্ব হিসাবে মানুষের নির্ভরশীলতা বা প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও সাদৃশ্য বিদ্যমান এবং এর ফলশ্রুতিতে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। আর এ সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে,অন্য কোন বিষয় এর বিকল্প হতে পারে না। কারণ তাহলে মানুষের জীবন বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে ও মানুষের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিম্নে এ ধরনের কিছু বিষয়ের উল্লেখ করব :
পৃথিবী সূর্য থেকে কিছু তাপ গ্রহণ করে যা জীবন নির্বাহের জন্য এবং প্রাণবন্ত অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয়। এ তাপের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে জীবনের যাত্রাপথ বিঘ্নিত হয়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ যদি এ দূরত্ব অধিক হয় জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ পৃথিবীতে পৌঁছবে না। আবার যদি এ দূরত্ব হ্রাস পায়,তবে তাপ বৃদ্ধি পাবে। ফলে পৃথিবীতে জীবন ব্যবস্থা বিপন্ন হবে।
লক্ষ্য করব যে,ভূপৃষ্ঠকে ভূমি এবং পানি ৪ঃ ৫ অনুপাতে দখল করে আছে (বিভিন্ন যৌগরূপে) যা অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে।
এছাড়া নিয়ত অক্সিজেনের রাসায়নিক রূপান্তর সত্ত্বেও মুক্ত বাতাসে এর মোট পরিমাণ অপরির্তিত থেকে যায় যা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং জীবন ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সকল জীবই অক্সিজেনের উপর নির্ভরশীল। যদি বিভিন্ন কারণে অক্সিজেন নিঃশেষ হতে থাকে (র্অথাৎ যদি মূল পরিমাণ কমতে থাকে) তবে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। আরো লক্ষ্য করব যে,মুক্ত অক্সিজেনের পরিমাণ জীবন ধারণের জন্য মানুষের প্রয়োজনের অনুপাতে বিদ্যমান। বাতাস ২১% অক্সিজেন এবং ৭৯% অন্যান্য গ্যাস নিয়ে গঠিত। যদি অক্সিজেনের পরিমাণ তা অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়,তবে পরিবেশ ভস্মীভূত হয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে সার্বক্ষণিক অগ্নিকাণ্ড দেখা দেবে। আবার যদি এর চেয়ে কম হয়,তবে ভূপৃষ্ঠে জীবন ধারণ কষ্টকর হয়ে পড়বে। ফলে মানুষ জ্বালানী কাজে অক্সিজেন এবং আগুন ব্যবহার করতে পারবে না,যা তার জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
প্রকৃতিতে অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং লক্ষ-কোটি বছর ধরে এ পুনরাবৃত্তি হয়েছে,এমন একটি বিষয় হলো প্রয়োজন অনুপাতে অক্সিজেনের পরিমাণ বজায় রাখার প্রক্রিয়া। মানুষ (সাধারণ অর্থে প্রাণী) শ্বাস নেয়ার সময় অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বাতাসে বিদ্যমান অক্সিজেনের মাধ্যমে শ্বসন গ্রক্রিয়া চালায়। রক্তের মাধ্যমে এ অক্সিজেন শরীরের প্রতিটি বিন্দুতে প্রবেশ করে এবং খাদ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের কাজে সহায়তা করে। এ প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি হয় এবং প্রশ্বাসের মাধ্যমে বা কথা বলার ফলে মুখ দিয়ে তা বেরিয়ে যায়। এ পদ্ধতিতে মানুষ এবং পশু সর্বদা এ গ্যাস(CO
)
উৎপন্ন করে,যা উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে।
এ অক্সিজেন পুনরায় শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যবহৃত হয়। প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে এ আদান-প্রদানের ফলে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণের ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ ও সম্ভব হয়।
এ বিনিময় হাজারো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ফলস্বরূপ যা একে অপরের হাতে হাত দিয়ে সম্পাদন করেছে এবং জীবনের চাহিদাসমূহের যোগান দিয়েছে। যদি এ বিনিময় এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না থাকত,তবে জীবন ধারণের উপাদানগুলো (যেমন অক্সিজেন) অল্প অল্প করে কমতে থাকত এবং মানুষের পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ত।
লক্ষ্য করব যে,নাইট্রোজেন একটি ভারী গ্যাস এবং প্রায় জমাটবদ্ধতার কাছাকাছি। নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় বাতাসে অবস্থান করে,যার ফলে হালকা হয় এবং প্রয়োজন মতো ব্যবহারের উপযোগী হয়। লক্ষ্যণীয় যে,যে পরিমাণ অক্সিজেন বাতাসে সর্বদা অবস্থান করে তা নাইট্রোজেনের পরিমাণের সাথে আনুপাতিক সম্পর্ক বজায় রাখে। অর্থাৎ নাইট্রোজেনকে হালকা করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন সর্বদা বিদ্যমান। যদি অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বা নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়,তবে প্রয়োজন অনুসারে হালকা করণের এ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে।
লক্ষ্য করব যে,বাতাস এক নির্দিষ্ট পরিমাণে ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করে। কখনো এ পরিমাণ পৃথিবীর উপাদান ও কণিকাসমূহের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগেও বৃদ্ধি পায় না। এ পরিমাণ মানুষের জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ যদি বিদ্যমান বাতাসের পরিমাণ কম বা বেশি হয়,তবে মানুষের জীবন সমস্যার সম্মুখীন হবে। যদি বাতাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়,তবে মানুষের দেহের উপর চাপও বৃদ্ধি পাবে যাতে করে সে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি হারাবে। আবার যদি বাতাসের পরিমাণ কম হয়,তবে বাতাস আকাশে বিদ্যমান উল্কাসমূহকে বাধা দিতে পারবে না,ফলে ভূপৃষ্ঠে সহজেই উল্কাপাত ও অগ্নিকাণ্ড দেখা দেবে।
লক্ষ্য করব যে,ভূপৃষ্ঠ এক নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন আকর্ষণ করে যেন সমস্ত গ্যাস এতে শোষিত না হয়। যদি ভূপৃষ্ঠ সমস্ত গ্যাস শোষণ করে নিত,তবে জীবনের জন্য কোন গ্যাস অবশিষ্ট থাকত না। ফলে মানুষ,পশু ও বৃক্ষসমূহ জীবন ধারণ করতে পারত না।
লক্ষ্য করব যে,পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব নির্দিষ্ট,যা মানুষ এবং অন্যান্য জীবের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ যদি চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটবর্তী হতো,তবে সাগরসমূহের জোয়ার এমনভাবে বৃদ্ধি পেত যেন পাহাড়সমূহকে উপড়ে ফেলবে।
আমরা প্রাণীর মধ্যে অনেক ধরনের প্রবৃত্তি লক্ষ্য করি। যদিও এ সব প্রবৃত্তির অলৌকিক ভাবার্থ আছে যা বাহ্যত দেখা যায় না। তবে এ সব প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটে তা আমাদের কাছে গোপনীয় নয়,বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সকল প্রবৃত্তিই দর্শনোপযোগী। আর মানুষ তার স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা হাজার হাজার প্রবৃত্তিকে উপলব্ধি ও অনুভব করতে পারে যা তার জীবন যাপন প্রক্রিয়াকে সহজ এবং তাকে রক্ষা করে। আমরা এ সব প্রবৃত্তির অনেকগুলোকেই সঠিকভাবে চিনি না এবং শনাক্তও করতে পারি না। যখন আমরা এ সব প্রবৃত্তিকে প্রকারভেদ ও শ্রেণিবিভক্ত করব তখন আমরা বুঝতে পারব যে,প্রতিটি শ্রেণিই বিশেষ এক শৃঙ্খলার সাথে মানব জীবনকে সাহায্য ও সুরক্ষা বিধান করছে। মানুষের মধ্যে শারীরিক গঠনসমূহ কোটি কোটি অগণিত প্রাকৃতিক ঘটনার উদ্ভব ঘটায় যেগুলোর প্রতিটিই মানুষকে তার জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এখন উদাহরণস্বরূপ যে সকল বাহ্যিক কারণ ও বিষয় প্রাণীর দেখার সাথে সরাসরি জড়িত এবং কোন কিছুর দর্শনানুভূতিতে মানুষকে সহায়তা করে সেগুলোকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্ধারণ করব। চক্ষুলেন্স বস্তুর চিত্র অক্ষিপটে প্রতিফলিত করে। এ অক্ষিপট স্বয়ং ন’
টি স্তরে গঠিত। সবর্শেষ স্তরটি কোটি কোটি স্তম্ভাকৃতি ও কোণাকৃতির কোষের সমন্বয়ে গঠিত যা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। অপরদিকে এ অংশটি চক্ষুলেন্সের সাথে সম্পর্কযুক্ত।‘
কোন বস্তুর দর্শন’
এ পর্যায়ে সংগঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি বস্তু প্রকৃতপক্ষেই বহির্জগতে বিদ্যমান যার উপর দৃষ্টি প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়ে থাকে এবং অপরটি হলো বস্তুর প্রতিচ্ছবি যা উল্টাকারে অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু দর্শন এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়,বরং কেটি কেটি স্নায়ুকোষ অক্ষিপটে প্রতিফলিত উল্টা প্রতিবিম্বকে সোজা (প্রকৃত) করার কাজ সম্পাদন করে এবং একে মানুষের মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। আর এ পর্যায়েই দর্শন সংগঠিত হয় যা মানুষের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির সাথে গভীরভাবে জড়িত।
এমনকি সৌন্দর্য,কমনীয়তা ও সুগন্ধির মতো প্রাকৃতিক বিষয়-বস্তুসমূহের প্রতিটিই স্ব স্ব স্থানে মানুষের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির সাথে জড়িত।
যদি ফুলের পরাগায়ণে কীটপতঙ্গের ভূমিকাকে পর্যবক্ষেণ করি,তবে দেখতে পাব যে,ফুলের সৌন্দর্য,কমনীয়তা ও সুগন্ধ এর একটি বিশেষ কারণ। ফুলের এ উপাদানসমূহই নিজের প্রতি কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে এবং পরাগায়ণের কাজটি সহজীকরণ করে। ফুলের প্রস্ফুটনে পরাগায়ণের জন্য বাতাস যে কার্য সম্পাদন করে এবং কীটপতঙ্গ যে কার্য সম্পাদন করে এ দু’
টি আলাদাভাবে চিহ্নিত হয় না।
প্রজননের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে নারী ও পুরুষের গঠনে (হোক প্রাণী অথবা উদ্ভিদ) এবং পারস্পরিক জীবন ধারণ ও অস্তিত্বের অব্যাহত গতির জন্য প্রকৃতি ও প্রাণীর পারস্পরিক বিনিময়ের সাথে পূর্ণরূপে সমন্বিত।
পবিত্র কোরানে এ ব্যপারে বলা হয়েছে :
و اِن تَعُدُّوا نِعمَةَ اللهِ لا تُحصُوها اِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيم
“
এবং যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে গণনা করিতে চেষ্টা কর,
তাহা হইলে তোমরা আদৌ উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল,
পরম দয়াময়।
”
(নাহল,১৮)
যাহোক,উপরিউক্ত পর্যায়গুলো ছিল প্রথম ধাপের অন্তর্ভুক্ত।
দ্বিতীয় ধাপ
: এ ধাপে আমরা দেখতে পাব যে,প্রকৃতি এবং জীবনের মধ্যে এই যে শতধা পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক তা একটি কল্পনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কল্পনাটি হলো :
‘
এক প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমান,যিনি এ পৃথিবী ও বস্তুসমূহকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং তাঁর এ সৃষ্টির পেছনে একটি উদ্দেশ্য বিদ্যমান।’
অতএব,উল্লিখিত সকল সম্পর্ক এবং বিষয়কে উপরিউক্ত কল্পনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যায়।
তৃতীয় ধাপ
: যদি প্রকৃতই প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তা না থাকে বলে মনে করা হয়,তবে সৃষ্টি ও প্রাণীর জীবনের অগ্রযাত্রা ও সুখ-সমৃদ্ধির পথে এই যে পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক,কোন উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্ভাবনা কতটুকু হতে পারে? এটা পরিষ্কার যে,এর সম্ভাবনা অর্থাৎ এ সকল ঘটনা কোন এক মহাসংঘর্ষের ফল,এমনটি ঘটার সম্ভাবনা খুবই দুর্বল। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে,ভাই ভিন্ন অন্য কারো কর্তৃক চিঠিটি প্রেরিত হলে সকল বিষয় ভাইয়ের সদৃশ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই দুর্বল। কারণ শত শত বৈশিষ্ট্য ও ঘটনার সাদৃশ্য থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। অতএব,কিরূপে এ ধারণা করা যায় যে,আমাদের আবাসস্থল এ পৃথিবীর সকল বিষয় শুধু বস্তু ও বস্তুগত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কোন উদ্দেশ্য ব্যতীতই সংগঠিত হয়েছে? অপরদিকে এ ঘটনাগুলো এমন এক সৃষ্টিকর্তাকে প্রকাশ করে,যিনি প্রজ্ঞাবান এবং যিনি কোন উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন করেন।
চতুর্থ ধাপ
: অতএব,নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় ধাপে বর্ণিত কল্পনাটি প্রাধান্য পায় যে,প্রজ্ঞাবান,চিন্তাশীল ও জ্ঞানী এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বিদ্যমান।
পঞ্চম ধাপ
: প্রাধান্য প্রাপ্ত বিষয়টি এবং দুর্বল সম্ভাবনাময় বিষয়টির মধ্যে তুলনা করব। যত বেশি সংখ্যক সাংঘর্ষিক ঘটনা বা আকস্মিক বিষয়ের ধারণা করা হবে,তৃতীয় ধাপে বর্ণিত ধারণার সঠিকতার সম্ভাবনা তত বেশি দুর্বলতর হতে থাকবে। কারণ এ কল্পনাটি (সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই) তাত্ত্বিক নিয়মের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সাংঘর্ষিক ও আকস্মিক বিষয়সমূহকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে অপারগ।
অতএব,এ ধরনের সম্ভাবনাময়‘
কল্পনা’
একান্তভাবেই নির্ভরশীল হতে পারে না।
এভাবে আমরা এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছব যে,বিদ্যমান এ জগতের জন্য প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব থাকাটা আবশ্যকীয়।
পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে :
سَنُريهِم اَيَاتِنا في الافَاق وَ في اَنفُسِهِم حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُم اَنَّهُ الحَقّ اَوَلَم يَكفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ
“
নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে বিশ্বের প্রান্তে এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যেও আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাইব,
এমনকি তাহাদের জন্য সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে,
ইহা নিশ্চিত সত্য। ইহাই কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে,
তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপর সম্যক পর্যবেক্ষক?
”
(সূরা ফুসসিলাত : ৫৩)
اِنَّ في خَلقِ السَّمَاواتِ و الاَرضِ و اختِلافِ اللّيلِ و النَّهارِ و الفُلكِ الّتي تَجري في البَحرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ و ما اَنزَلَ اللهُ مِن السَّمَاءِ من مَاءٍ فَاَحيَا به الاَرضَ بَعدَ مَوتِهَا و بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ و تَصرِيفِ الرِّياحِ و السَّحَابِ المسخرِ بينَ السَّماءِ و الارضِ لاياتٍ لِقَومٍ يَعقِلونَ
“
নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজন,
রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন এবং নৌযানসমূহ যাহা সমূদ্রে এমন দ্রব্যাদি লইয়া বিচরণ করে যাহা মানবমণ্ডলীর উপকার সাধন করে,
সেই বারিধারা যাহা আল্লাহ্ আকাশ হইতে বর্ষণ করেন,
যদ্বারা তিনি পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন ও উহাতে যাবতীয় জীব-
জন্তুর বিস্তার ঘটান,
বায়ু প্রবাহের পরিবর্তন এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে বিরাজমান বশীভূত ও নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অবশ্যই সেই জাতির জন্য নিদর্শনাবলী আছে,
যাহারা বিচার-
বুদ্ধি খাটায়।
”
(সূরা বাকারা : ১৬৪)
فَارجِعِ البَصَرَ هَل تَرَى مِن فُطُورِ ثُمَّ ارجِعِ البصَرَ()كرَّتَين يَنقَلِب اِلَيكَ البَصَر خَاسئا و هو حَسِير
“
অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবন্ধ কর। তুমি কি কোন ত্রুটি-
বিচ্যুতি দেখিতে পাও?
অতঃপর তুমি পুনঃপুন দৃষ্টি নিবন্ধ কর,(
পরিশেষে তোমার)
দৃষ্টি ব্যর্থ হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।
”
(সূরা মুলক : ৩ ও ৪)
 10%
10%
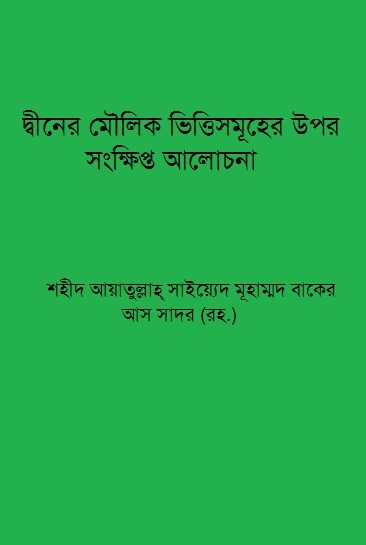 লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুহাম্মদ বাকের সাদর (রহঃ)
লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুহাম্মদ বাকের সাদর (রহঃ)





