আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
সৃষ্টির আদি থেকেই মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আসছে। এমনকি দার্শনিক চিন্তা অথবা যুক্তিতত্ত্বকে অনুধাবনের পূর্বেই সে একক প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। সে স্বীকার করে নিয়েছিল তার সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব। আর তখন থেকেই সে অনুভব করত মহান প্রভুর সাথে তার এক গভীর সম্পর্কের কথা।
প্রভুর প্রতি মানুষের এ বিশ্বাস কোন শ্রেণিবৈষম্যের ফল ছিল না,ছিল না কোন সুবিধাবাদী জালিমের চাতুর্যের ফলও-শোষণের পথকে সুগম করাই যার অভিপ্রায়। তার এ বিশ্বাস না ছিল কোন নিপীড়িত,নিগৃহীত জনপদের জীবনাবসাদের ফলশ্রুতিও যে,এ বিশ্বাস স্থাপন করে তারা কষ্টাক্লিষ্ট জীবন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। কারণ মানুষের এ বিশ্বাস (স্রষ্টায় বিশ্বাস) বিশ্বমানবতার ইতিহাসে এ ধরনের যে কোন বৈষম্য ও সংঘাতের চেয়েও প্রাচীন।
অনুরূপভাবে যুগ যুগ ধরে মানুষের এ লালিত বিশ্বাস কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বস্তুজগৎ ও প্রকৃতিজগতের বৈরিতা থেকে উৎসারিত ভয়-ভীতির ফলও ছিল না। কারণ দ্বীন যদি ভয়-ভীতির ফল হতো,তবে মানবতার দীর্ঘ ইতিহাসে অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ মানুষই-তা যে কোন ধর্মীয় মতাদর্শেরই হোক-সবচেয়ে ভীতু মানুষ হিসাবে পরিগণিত হতো। কিন্তু আমরা জানি যে,যুগ যুগ ধরে যারা ধর্মের আলোকবর্তিকা ধারণ করে সম্মুখপানে এগিয়ে গিয়েছিলেন,তারাই সর্বাপেক্ষা দৃঢ় মনোবল ও মানসিক শক্তির অধিকারী মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিল।
অতএব,মানুষের এ বিশ্বাস তার অন্তরের গভীরে প্রোথিত।
স্রষ্টার প্রতি তার ভালোবাসা,অনুরাগ এবং অবিচলিত বিবেকবোধও আত্মশক্তিরই পরিচায়ক। তার সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে সে মহান প্রভু ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সাথে তার নিজ সম্পর্ককে অনুধাবন করে।পরবর্তীকালে মানুষের মাঝে দার্শনিক মনোবৃত্তির বিকাশ হলে তার পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তুসমূহ থেকে সে সামগ্রিক ধারাণাসমূহ,যেমন অনিবার্যতা,সম্ভাব্যতা ও অসম্ভবত্ব,একত্ব ও বহুত্ব,যৌগিকত্ব ও সরলত্ব,অংশ ও সমগ্র,অগ্রবর্তিতা ও উত্তরবর্তিতা এবং কারণ ও ফলাফল আবিষ্কার করেছিল। এ ধারণাগুলোকে সে তার নিজস্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে এমনভাবে কাজে লাগিয়েছিল যা প্রভুর প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস ও ঈমানের সমর্থক ও সহায়ক হয়েছে। আর এভাবে সে এ ঈমানকে দর্শনের মাধ্যমে বর্ণনা এবং দার্শনিক আলোচনা ও পর্যালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছিল ।
ইতোমধ্যে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ আসল। অতঃপর মানুষ এগুলোকে জ্ঞানার্জন ও পরিচিতি লাভের ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করল। কারণ চিন্তাবিদগণ উপলব্ধি করলেন যে,শুধু সামগ্রিক ধারণাই প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে সত্য,প্রকৃত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিদ্যমান রহস্যসমূহ উদ্ঘাটনের জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং তাঁরা ধারণা করলেন যে,পরীক্ষা-নিরীক্ষা,পর্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানই হলো বিদ্যমান নিয়ম-শৃঙ্খলা ও রহস্য উদ্ঘাটনের প্রকৃত মাধ্যম। এ ইন্দ্রিয়ানুভূতি সামগ্রিকভাবে বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান ও অবগতির পূর্ণতা এবং বিস্তৃতির পথে গুরুত্বপূর্ণ।
এ শ্রেণির চিন্তাবিদগণ এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে,ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো জ্ঞানার্জনের পথে দু’
টি বিশেষ মাধ্যম।
মানুষের জ্ঞান এবং পরিচিতি স্বীয় পথে এগুলোর দিকে হাত বাড়াতে বাধ্য। তদুপরি মানুষ এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রয়োগ করে,তার পরিপার্শ্বে বিদ্যমান সামগ্রিক বিন্যাস ব্যবস্থা,বাস্তবতা ও রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে লাভবান হতে চায়। মানুষের উচিত তার চিন্তালব্ধ ফলাফলকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করা। যেমন গ্রীক চিন্তাবিদ এরিস্টটল ঘরের এক কোণে বসে মুক্তাঙ্গনে বস্তুর গতি এবং গতিশক্তি সম্পর্কে চিন্তা করার পর বিশ্বাস স্থাপন করলেন যে,গতিশীল বস্তু তখনই স্থিরাবস্থায় পৌঁছে যখন গতিশক্তি লীন হয়ে যায়। অপরদিকে গ্যালিলিও,গতিশীল বস্তুকে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং এ পর্যবেক্ষণকে পুনঃপুন অনুধাবন করলেন। অতঃপর গতিশক্তি এবং বস্তুর গতির মধ্যে একটি সম্পর্ক উদ্ভাবন করলেন যে,“
যখন গতিশক্তি কোন বস্তুকে গতিশীল অবস্থায় আনে,ঐ গতিশীল বস্তু স্থিরাবস্থায় আসবে না,যতক্ষণ পর্যন্ত না বিপরীত কোন শক্তি গতিশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং তাকে বাধাগ্রস্ত করে।”
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি গবেষকমণ্ডলীকে এবং মহাবিশ্বের পদার্থসমূহের যাবতীয় বস্তুনিচয়ের (বিদ্যমান) নিয়মগুলো আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে। আর তা দু’
টি পর্যায়ে বা ধাপে অর্জিত হয় :
১। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা,পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রাপ্ত ফলাফল গ্রহণ।
২। বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায় অর্থাৎ প্রাপ্ত ফলাফলগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ ও বিন্যাসকরণ যাতে করে গ্রহণযোগ্য সামগ্রিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।
অতএব,পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি কোন তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথে বুদ্ধিবৃত্তির কাছে অনির্ভরশীল নয়।
কোন প্রকৃতিবিজ্ঞানী বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মহাবিশ্বে বিদ্যমান রহস্যসমূহ থেকে কোন রহস্যের উদ্ঘাটন অথবা প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির সম্পর্ক অবধারণ করতে পারেননি। কারণ প্রথম ধাপে যা অর্জিত হয় তা হলো গভীর পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ। আর দ্বিতীয় ধাপে আকল বা বুদ্ধিবৃত্তি,এ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নিরূপণ করে এবং এর মাধ্যমে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে। এমন কোন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার কথা আমাদের জানা নেই যা দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে। কারণ প্রথম ধাপের বিষয়গুলো হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয় ধাপের বিষয়গুলো হলো প্রামাণ্য ও বিবেচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত যা (এ ধাপে) ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। যেমন নিউটন দু’
টি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান আকর্ষণ বলকে শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে অনুভব করেননি যে,“
এ আকর্ষণ বল ঐ দু‘
টি বস্তুর কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং ঐ বস্তুদ্বয়ের ভরদ্বয়ের গুণফলের সমানুপাতিক।”
বরং যা তিনি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জেনেছেন তা ছিল এই যে,প্রস্তরখণ্ডকে যদি উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়,তবে তা ভূমিতে ফিরে আসে;চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে এবং গ্রহসমূহ সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণনরত। নিউটন তাঁর এ পর্যবেক্ষণগুলোকে পরস্পর বিশ্লেষণ করলেন এবং গবেষণা করলেন। সে সাথে তিনি আকষর্ণকারী বস্তু অভিমুখে গতিশীল আকর্ষিত বস্তুর গতি বৃদ্ধি পাওয়া সংক্রান্ত গ্যালিলিওর সূত্রটি এবং ভূপৃষ্ঠের উপর পতনশীল ও তীর্যক তলসমূহের উপর গড়িয়ে যাওয়া বস্তুসমূহের সুশৃঙ্খল দ্রুতি সংক্রান্ত গ্যালিলিওর তত্ত্বসমূহ এবং গ্রহসমূহের গতি সংক্রান্ত ক্যাপলারের সূত্রসমূহেরও সাহায্য নিলেন। ক্যাপলারের এক সূত্রে বলা হয়েছে যে,‘
সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণনরত প্রতিটি গ্রহের পরিক্রমণ কালের বর্গফল,সূর্য ও উক্ত গ্রহের মধ্যকার দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক’
। অতঃপর নিউটন মহাকর্ষ সূত্র অবিষ্কার ও বর্ণনা করলেন যে,দু’
টি বস্তুকণার মধ্যে বিদ্যমান আকর্ষণ বল উক্ত বস্তুদ্বয়ের ভরদ্বয় এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের গুণফলের সমানুপাতিক।
প্রাকৃতিক বিন্যাস ব্যবস্থার ব্যাপারে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সৃষ্টিকর্তার প্রতি সুস্পষ্টরূপে বিশ্বাস স্থাপন করার ক্ষেত্রে একটি নতুন অবলম্বন হতে পারে। কারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা মহাবিশ্বে যে বিভিন্ন ধরনের সামঞ্জস্য,ঐকতান,নিয়মানুবর্তিতা এবং প্রজ্ঞা ও কৌশলের নিদর্শনাদি আবিষ্কার করেছে তা প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী স্রষ্টার অস্তিত্বকে নির্দেশ করে। তবে প্রকৃতিবিজ্ঞানিগণ প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসাবে এ বিষয়টির গুরুত্ব প্রকাশ করার ব্যাপারে মোটেও ইচ্ছুক ছিলেন না যা এখনও মানব জ্ঞান ও পরিচিতি এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয় ও সমস্যাবলীর প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে একটি দার্শনিক বিষয় বলে গণ্য হচ্ছে। আর খুব শীঘ্রই বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রের বাইরে এমন সব দার্শনিক ও যুক্তিবিদ্যাগত ঝোঁক ও প্রবণতার উদ্ভব হলো যা এ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে (ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি) দার্শনিক ও যৌক্তিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর প্রয়াস চালালো এবং ঘোষণা করল যে,পরিচিতি ও জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ই হলো একমাত্র মাধ্যম। যেখানেই ইন্দ্রিয় অপারগতা প্রকাশ করে সেখানেই মানব পরিচিতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভও অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় ও কোনভাবেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা যার উপর অসম্ভব,তা প্রমাণ করতে মানুষও সম্পূর্ণরূপে অপারগ।
আর এভাবেই ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভুর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করেছে। ইন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক মতবাদের অনুসারীদের মতে খোদা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব নন,তাঁকে দেখাও অসম্ভব এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বকে অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করার এবং তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান লাভের কোন পথই বিদ্যমান নেই। অবশ্য এ ধরনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে অনস্তিত্বশীল প্রমাণ করার জন্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ জ্ঞান ও পরিচিতিকে মাধ্যমরূপে নির্ধারণ শুরু হয়েছে দার্শনিকদের পক্ষ থেকে-সে সকল মনীষীর পক্ষ থেকে নয় যাঁরা ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে এক বিশেষার্থে সফলতায় পৌঁছিয়েছেন। এটা দার্শনিকদেরই কাজ ছিল যাঁরা অভিজ্ঞতালব্ধ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে দর্শন ও অপযুক্তিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।
কিন্তু এ ধারা ও বিশ্বাস পর্যায়ক্রমে স্ববিরোধিতার জালে আটকা পড়েছে। দার্শনিক দিক থেকে এ বিশ্বাস ও ধারা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে,আমরা যে বিশ্বে বাস করি তার অস্তিত্বকেই অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতাকে আংশিক বা পূর্ণভাবে অস্বীকার করে বসেছিল। এ ধারার প্রবক্তারা বলেন,“
ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছাড়া আমাদের অধিকারে কোন অবলম্বন নেই এবং একমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতিই কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে যেভাবে আমরা তা দেখি এবং উপলব্ধি করি ঠিক সেভাবে।”
কিন্তু এ দেখা বা উপলব্ধি করা যথার্থ এবং মৌলিক নয়। কারণ কখনো কখনো কোন কিছুকে উপলব্ধি করি এবং সম্ভবত এর সত্তাকে আমাদের অনুভূতিতে গুরুত্বারোপ করি,কিন্তু লক্ষ্য করতে পারি যে,এর অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার আওতায় পড়ে না। অর্থাৎ তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে অবস্থান করছে। ফলে ইন্দ্রিয়ানুভূতিও ঐগুলোকে প্রমাণের মাধ্যম হতে পারে না। যেমন আমরা আকাশে চাঁদ দেখি এবং আমাদের এ চাঁদ দেখার মাধ্যমে এর অস্তিত্বের প্রতি কেবল গুরুত্বারোপ করতে পারি বৈ কি।
আর ঐ মুহূর্তে একে উপলব্ধিও করতে পারি। কিন্তু সত্যিই কি চাঁদ আকাশে বিদ্যমান? চোখ খোলা এবং এর প্রতি তাকানোর পূর্বেও কি তা বিদ্যমান ছিল?
অতএব,ইন্দ্রিয়ই জ্ঞান লাভের একমাত্র মাধ্যম-এ মতবাদের অনুসারিগণ পরিপূর্ণরূপে কোন কিছুকে প্রমাণ ও গুরুত্বারোপ করতে পারে না।
যেমন যার চোখ টেরা সে বস্তুকে দেখে এবং তার এই দেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করে,কিন্তু ঐ বস্তুর সত্যিকারের অস্তিত্বের (অবস্থানের) প্রতি গুরুত্বারোপ বা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। আর এভাবেই ইন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক মতবাদের অনুসারিগণ অবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে,ইন্দ্রিয় হলো জ্ঞান ও পরিচিতির অন্যতম মাধ্যম। আর তা জ্ঞান ও পরিচিতির মাধ্যম হওয়ার পরিবর্তে এর চূড়ান্ত সীমায় পর্যবসিত হয়েছে। এভাবেই ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ জ্ঞান ও পরিচিতি এমন এক বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে,আমাদের উপলব্ধি ও মনোজগতের বাইরে যার স্বাধীন-স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই।
তাই উক্ত যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিষয়টি‘
ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান’
-এর প্রবক্তারা উল্লেখ করেছেন তা হলো প্রতিটি বাক্য বা উদ্ধৃতিই-যার অন্তর্নিহিত অর্থকে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না ও তার উপর গুরুত্বারোপ সম্ভব হয় না,তবে তা হলো অনর্থক বাক্য-কতগুলো এলোমেলো বর্ণমালার মতোই তা থেকেও কোন অর্থ লাভ করা সম্ভব নয়। আবার যে সকল বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থকে ঐন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করা যায় এবং যার উপর গুরুত্বারোপ করা সম্ভব তা হলো অর্থবোধক বাক্য। সুতরাং যদি ইন্দ্রিয় বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রকৃত অবস্থা অনুসারে অনুধাবন করে ও গুরুত্বারোপ করে,তবে ঐ বাক্য সত্য হবে;আর যদি তার অন্যথা হয় তবে তা হবে মিথ্যা। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয় :‘
বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়’
তবে এ বাক্যটি হলো একটি অর্থবোধক বাক্য এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও সত্য। যদি বলা হয় :‘
শীতকালে বৃষ্টি হয়’
তবে তা একটি অর্থবোধক বাক্য বটে,কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো মিথ্যা। আবার যদি বলা হয় : কদরের রাত্রে এমন কিছু বর্ষিত হয় যা দেখা ও অনুভব করা যায় না,তবে বাক্যটির অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য সত্য বা মিথ্যা হওয়া তো দূরের কথা,বরং এর কোন অর্থই নেই। কারণ ঐন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সত্যতা বা অসত্যতা যাচাই করা যায় না। অনুরূপ যদি কেউ বলে :‘
দাইয কদরের রাত্রে অবতরণ করে’
,তবে সত্যি কথা বলতে কি,এর যেমন কোন অর্থ নেই,তেমনি প্রাগুক্ত বাক্যটিরও অর্থ নেই। এভাবে যদি বলি,‘
খোদা অস্তিত্বশীল’
তবে এটি উপরিউক্ত বাক্যে যে‘
দাইয (অনর্থক শব্দ) অস্তিত্বশীল’
যার কোন অর্থ নেই,তার মতোই। কারণ খোদার অস্তিত্বকে ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় না। এ ধরনের ব্যাখ্যাও যা বাহ্যত যৌক্তিক,স্বয়ং পারস্পরিক বিরোধিতায় নিমজ্জিত। কারণ যে সর্বজনীন উক্তিতে বলা হয়েছে যে,‘
যে সকল বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্য বা মিথ্যারূপে আখ্যায়িত করা যায় না সে সকল বাক্য হলো অর্থহীন’
তা-ও স্বয়ং এ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সত্যতা বা অসত্যতা ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণ করা যায় না। অতএব,ঐ বাক্যটিও অর্থহীন। অর্থাৎ যে যৌক্তিক বাক্যের মাধ্যমে বলা হয়‘
প্রতিটি বাক্যই-যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যায় না-তা অর্থহীন’
,তা-ও ঐ সর্বজনীন উক্তির আওতাভুক্ত। কারণ ঐন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আংশিক এবং সীমাবদ্ধতা ছাড়া সংঘটিত হয় না।
অতএব,এ যুক্তি পারস্পরিক বিরোধিতা সৃষ্টি করে। ফলে এটাকে আর সর্বজনীনতা দেয়া সম্ভব না এবং একটি সর্বজনীন ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গিও এ থেকে প্রতিভাত হয় না। এ যুক্তির ফলে সৃষ্টি সম্পর্কে মহান মনীষিগণ যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তার সবগুলোই একাধারে ভুল পর্যবসিত হয়। কারণ ইন্দ্রিয়‘
সর্বজনীনতা’
কে উপলব্ধি করতে পারে না;শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই যা সীমাবদ্ধ তাকেই প্রমাণ ও উদ্ঘাটন করতে পারে।
সৌভাগ্যবশত বিজ্ঞান তার নিরন্তর ক্রমবিকাশের পথে কখনই এ ধরনের প্রবণতার প্রতি আকর্ষিত হয়নি। বিজ্ঞান সর্বদা এ বিশ্বচরাচরে প্রথমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আবিষ্কার ও গবেষণার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। অতঃপর বিজ্ঞান এ আবিষ্কার প্রক্রিয়াকে ইন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক ও যৌক্তিক প্রবণতাসমূহ যে সকল সংকীর্ণ সীমারেখা আরোপ করেছিল তা থেকে মুক্ত করেছে। এর ফলে বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চ ও বিষয়াদি বিন্যস্তকরণ,সেগুলোকে সর্বজনীন নিয়ম-নীতির অবয়বে স্থাপন এবং এগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কসমূহকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।
তবে বস্তুবাদী দার্শনিক মতবাদসমূহের উপর এ চরমপন্থি ইন্দ্রিয়বাদী প্রবণতাসমূহের দার্শনিক ও যৌক্তিক প্রভাব দিন দিন ক্ষীণ ও ম্লান হয়ে গিয়েছে । আধুনিক বস্তুবাদী দর্শন-দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা হচ্ছে যার প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী-তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও স্পষ্টভাবে এ সকল ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক প্রবণতাসমূহকে প্রত্যাখ্যান করতঃ নিজেকে প্রথম ধাপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক অভিজ্ঞতার সীমা রেখা এবং এমনকি দ্বিতীয় ধাপ অতিক্রম করার অধিকারও প্রদান করে। আর এখানে উল্লেখ্য যে,বিজ্ঞানীরা এ ইন্দ্রিয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক অভিজ্ঞতার আলোকে তার গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড শুরু এবং প্রাগুক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের মাধ্যমে তার ইতি টানেন। কারণ বিজ্ঞানী প্রথম ধাপে অর্জিত ফলাফলগুলোর মধ্যে তুলনা করে একটি সর্বজনীন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও মতবাদ আবিষ্কার করে এবং যে সকল সম্পর্ক এই অর্জিত ফলাফলগুলোর মধ্যে কল্পনা বা ধারণা করা সম্ভব,তা প্রকাশ করে।
এদিক থেকে বস্তুবাদীদের উত্তরসূরি,দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা চরমপন্থী ইন্দ্রিয়বাদী এ ধারার মতে‘
অদৃশ্য ও অলৌকিকতায়’
বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তারা দ্বান্দ্বিক চিন্তার কলেবরে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে একটি সাধারণ মতবাদ ব্যক্ত করে থাকেন।
বস্তুবাদী এবং আধ্যাত্মবাদী (الهيون
) উভয়েই এ ব্যাপারে একমত যে,ইন্দ্রিয়ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সীমানা অতিক্রম করা উচিত এবং জ্ঞান ও পরিচিতির ক্ষেত্রে দু’
টি ধাপ অতিক্রম করাই গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত।
প্রথমধাপ
: ইন্দ্রিয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল সংগ্রহকরণ।
দ্বিতীয়ধাপ
: সংগৃহীত ফলাফলগুলোর তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণ।
বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা,বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই বস্তুবাদী এবং আধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে মতভেদ;অর্থাৎ দ্বিতীয় ধাপে। বস্তুবাদী দর্শন এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে যার মাধ্যমে প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত হয়। অপরপক্ষে,অধ্যাত্মবাদী দর্শন বিশ্বাস করে যে,ঐ সকল (১ম ধাপে) সংগৃহীত তথ্যের বিচার ও বিশ্লেষণ যতক্ষণ পর্যন্ত প্রজ্ঞাবান স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সন্তোষজনক হবে না।
অতএব,প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করার নিমিত্তে নিম্নোল্লিখিত দু’
প্রকারে যুক্তি উপস্থাপন করব। উভয় প্রকার যুক্তির ক্ষেত্রেই প্রথম ধাপে ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ এবং দ্বিতীয় ধাপে বুদ্ধিবৃত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত উপাত্তগুলোকে ব্যবহার করব। অতঃপর এ উপসংহারে পৌঁছব যে,বিদ্যমান এ বিশ্বকে এক প্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন। দু’
প্রকারের যুক্তি হলো :
১. বৈজ্ঞানিক বা আরোহী যুক্তি পদ্ধতি(
Inductive Reasoning)
।
২. দার্শনিক যুক্তি পদ্ধতি(
Philosophical Reasoning)
বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও দলিল বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা তুলে ধরা সমীচীন বলে মনে করছি।
যে সকল যুক্তি ঐন্দ্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভাবনা তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল আরোহ যুক্তি পদ্ধতিকে অনুসরণ করে কোন কিছুকে প্রমাণ করে তাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বলে। অতএব,স্রষ্টার সত্তাকে প্রমাণ করার জন্য আমাদের অনুসৃত পদ্ধতি হলো বৈজ্ঞানিক যুক্তি পদ্ধতি যা সম্ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত।
এজন্য খোদার সত্তাকে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আমরা‘
আরোহ যুক্তি’
রূপে নামকরণ করেছি।
পরবর্তীতে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।
 20%
20%
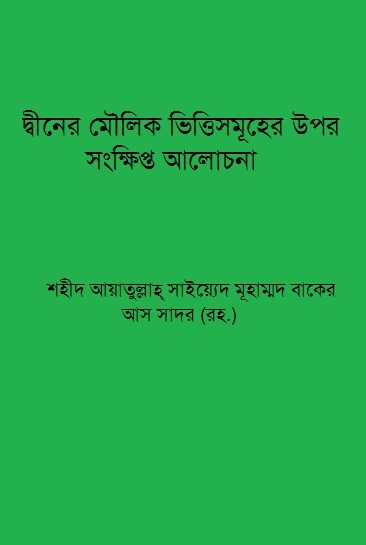 লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুহাম্মদ বাকের সাদর (রহঃ)
লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুহাম্মদ বাকের সাদর (রহঃ)





