নী’
চের মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়িয়েছে তা পরিষ্কার হওয়ার জন্য নী’
চের কিছু কথা দর্শন সম্পর্কিত ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছি। যে সকল গ্রন্থ নী’
চের কথাগুলো বর্ণনা করেছে তার মধ্যে ফুরুগী অন্যদের হতে উত্তমরূপে নী’
চের কথাগুলো উদ্ধৃত করেছেন। তাই ফুরুগী নী’
চের যে কথাগুলো উদ্ধৃত করেছেন আমি তার কিছু অংশ আপনাদের জন্য পড়ব। তিনি নী’
চে সম্পর্কে বলেছেন,“
যখন পৃথিবীর সব দার্শনিক স্বার্থপরতাকে অপছন্দনীয় এবং পরোপকার ও আত্মত্যাগকে পছন্দনীয় মনে করেছেন তখন নী’
চে তার বিপরীতে স্বার্থপরতাকে সত্য ও পছন্দনীয় এবং আত্মত্যাগকে দুর্বলতা ও ত্রুটি মনে করেছেন।”
আমরা পরবর্তীতে‘
আত্মত্যাগ কি দুর্বলতার লক্ষণ’
এ বিষয়ে আলোচনা করবর্।
ডারউইনের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে নী’
চে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামকে দ্বন্দের অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং অন্যরা ডারউইনের যে তত্ত্বকে ভুল মনে করেছেন তাকে তিনি সঠিক বলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন,নিজে বিজয়ী হওয়ার জন্য সব ব্যক্তি ও সত্তাই একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। বিশ্বের সকল শুভাকাঙ্ক্ষীই অধিকাংশের কল্যাণকে দৃষ্টিতে রাখার পক্ষপাতি এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীকে অধিকার লাভের উপযোগী বলে বিশ্বাস করেন। নী’
চের চিন্তার ভিত্তি হলো‘
ব্যক্তির ক্ষমতা তার সৌভাগ্যের হাতিয়ার’
। পূর্ণ সত্তা সেই যার প্রবৃত্তি শক্তিমান ও বিকশিত এবং এ প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণের শক্তিরও সে অধিকারী।
এ পর্যন্ত সবাই বলতেন,যদি এরূপ কাজ কর তা অনৈতিক কর্ম বলে গণ্য হবে। কিন্তু তিনি বলেন,না,বরং যে কাজগুলো তোমার প্রবৃত্তি চায় তা-ই কর এবং নৈতিকতাও এটাই। তোমার প্রবৃত্তি যা বলে তা-ই ভালো কাজ বলে গণ্য।
নী’
চের ভাষায়-“
অনেকেই বলেন,ভালো হতো যদি পৃথিবীতে না আসতাম। সম্ভবত তা-ই। কিন্তু ভালো-মন্দ যা-ই হোক যখন পৃথিবীতে এসেছি অবশ্যই আমাকে এটা ভোগ করতে হবে। যত বেশি ভোগ করব তত উত্তম।”
তিনি বলছেন,“
আমার লক্ষ্য হওয়া উচিত যত বেশি পারা যায় পৃথিবীকে ভোগ করা ও এ থেকে লাভবান হওয়া। যা কিছুই আমার এ লক্ষ্যে পৌছার জন্য সহায়ক হবে তা ভালো এবং নৈতিক।”
মুয়াবিয়াও এ ধরনের চিন্তা করত এবং সব সময় বলত,“
পৃথিবীর নেয়ামতের মধ্যে আমরা নিজেদের ভাসিয়ে দেব।”
অন্য স্থানে নী’
চে বলেছেন,“
এ লক্ষ্যের জন্য যা সহায়ক,যেমন নিষ্ঠুরতা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র,যুদ্ধ,দ্বন্দ্ব-সংঘাত সবই ভালো। আর এর বিরোধী ও প্রতিবন্ধক যা কিছু আছে যদিও তা সততা,ভালোবাসা,অনুগ্রহ,আত্মসংযম হয় তা মন্দ... সব মানুষ,গোত্র ও জাতি সমানাধিকারপ্রাপ্ত- এ কথা বর্জনীয় এবং এ ধরনের বক্তব্য মানব জাতির উন্নয়নের পথে অন্তরায়।”
এ ছাড়াও তিনি বলেছেন,“‘
সকল মানুষের অধিকার সমান’
-এটা ভ্রান্ত চিন্তা। কারণ এর ফলে দুর্বলরা শক্তিশালীদের সারিতে চলে আসে এবং উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়। বরং উচিত দুর্বলদের অধিকারকে পদদলিত হতে দেয়া যাতে করে সবলদের জন্য পথ প্রশস্ত হয়। যখন সবলদের জন্য পথ উন্মোচিত হবে তখন উন্নত মানুষ তৈরি হবে।”
তিনি বলেন,“
মানুষকে অবশ্যই দু’
ভাগে ভাগ করতে হবে। একদল কর্তৃত্বশীল ও ক্ষমতাবান। অন্যদল আনুগত্যপরায়ণ ও দাস। সম্মান ও মর্যাদা কর্তৃত্বশীলদের ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ার। সামাজিক ও নগর কাঠামো উচ্চ শ্রেণীর উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য গঠিত হয়েছে। সুতরাং এটা ঠিক নয় যে,কর্তৃত্বশালীরা অনুগতদের সংরক্ষণ করবে।”
তিনি বলছেন,“
সমাজ শুধু এজন্য যে,শক্তিমানরা যাতে আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছতে পারে এবং এ সমাজে দুর্বলরা তাদের বোঝা বহনকারী।”
সাদীর ভাষায়-
“
ভেড়ার পাল রাখালের জন্য নয়
বরং রাখাল ভেড়ার পালের জন্য।”
“
শক্তিমান ও ক্ষমতাবান প্রভু শ্রেণী হিসেবে বিশেষ পরিচর্যা ও যত্নের অধিকারী যাতে করে উন্নত মানুষ তৈরি হতে পারে এবং মানবতা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে।”
পাশ্চাত্যে মানুষের উন্নত প্রজন্ম সৃষ্টি এবং প্রজাতির সংস্কারের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। আলেক্সিস ক্যারল‘
মানুষ এক অপরিচিত জীব’
গ্রন্থের শেষে এ দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন,প্রজাতিগুলোকে সংস্কার করতে হবে এবং দুর্বল মানবগোষ্ঠীকে প্রজন্ম সৃষ্টির অনুমতি দেয়া যাবে না।
নী’
চের ভাষায়-“
নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে মৌলনীতিটি এতদিন অনুসৃত হয়েছে তা সাধারণের কল্যাণে এবং সংখাগরিষ্ঠ দুর্বল শ্রেণীর পক্ষে,প্রভু ও উচ্চ শ্রেণীর পক্ষে নয়। এ মৌলনীতিকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে এবং এমন মৌলনীতি গ্রহণ করতে হবে যা উচ্চ শ্রেণীর কল্যাণের জন্য হয়।”
এ কথাটির অর্থ হলো নী’
চের দৃষ্টিতে কল্যাণ,সত্যপ্রিয়তা ও সৌন্দর্যের মতো বিষয়গুলো (যা যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য লক্ষণীয় বিষয়) আপেক্ষিক ও বাস্তব নয় এবং যা বাস্তব তা হলো সকলেই ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষী।
অতঃপর নী’
চে ধর্মগুলোর প্রতি আক্রমণ করে বলেছেন,“
ধর্মগুলো মানবতার প্রতি খেয়ানত করেছে যেহেতু মানুষকে ন্যায়বিচার এবং দুর্বল ও বঞ্চিতদের সাহায্যের আহবান জানিয়েছে।”
যখন ধর্ম ছিল না তখন যে জঙ্গলী বিধান চালু ছিল তা-ই ভালো ছিল। কারণ শক্তিশালীরা দুর্বলদের খেয়ে ফেলত এবং এভাবে দুর্বলরা নিশ্চিহ্ন হতো।”
তিনি আরো বলেছেন,“
প্রথমদিকে পৃথিবী শক্তিশালী মানুষদের ইচ্ছা ও মর্জিমাফিক পরিচালিত হতো এবং দুর্বল ও অনুগতরা তাদের দাস ছিল। কিন্তু শক্তিশালীরা সংখ্যায় স্বল্প এবং দুর্বলরা সংখ্যায় অধিক। তখন এ দুর্বলরা তাদের সংখ্যাধিক্যকে তাদের ভাগ্য উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করল এবং চক্রান্তের আদলে দয়া,অনুগ্রহ,নিঃস্বার্থতা,ন্যায়বিচার,সম্মান প্রভৃতিকে সুন্দর ও সত্য বলে প্রচার চালানো শুরু করল যাতে করে ক্ষমতাবানদের প্রভাবকে কমানো যায় এবং নিজরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। এ লক্ষ্য ধর্মের মাধ্যমে সর্বত্তোমরূপে অর্জিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ ও সত্যের আবরণে তারা নিজেদের রক্ষা করেছে।”
এ দৃষ্টিভঙ্গি কার্ল মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির ঠিক বিপরীত। নী’
চে ও মার্কস দু’
জনই ধর্মের বিরোধী। কিন্তু নী’
চের দাবি অনুযায়ী দুর্বলরা শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসেবে ধর্মকে উদ্ভাবন করেছে যেহেতু তিনি নিজেকে ক্ষমতাবানদের সমর্থক বলে মনে করেন। আর কার্ল মার্কস যিনি নিজেকে দুর্বল ও শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণীপন্থী বলে প্রচার করেন তার মতে ধর্মকে ক্ষমতাবানরা দুর্বলদের বিদ্রোহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে তৈরি করেছে’
।
নী’
চে অতঃপর সক্রেটিস,গৌতম বুদ্ধ ও ঈসা (আ.)-কে আক্রমণ করে বলেন,“
ঈসা মাসীহর চরিত্র দাসের চরিত্র এবং তা প্রভুদের চরিত্র ও নীতিকে ধ্বংস করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে ভ্রাতৃত,সাম্য,সন্ধি,শ্রমিক,নারী ও শিশু অধিকার রক্ষার যে সংলাপসমূহ প্রচলন লাভ করেছে তা ধর্ম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং এগুলো এক রকম ষড়যন্ত্র,প্রতারণা ও ধোঁকা বৈ কিছু নয়। এগুলো দারিদ্র্য,দুর্বলতা ও পতনের কারণ। এজন্যই এ সকল নীতিকে অপসারিত করে প্রভূত্বের উপযোগী নীতিমালা চালু করতে হবে। প্রভুসুলভ জীবনের নীতি কি? স্রষ্টা,পরকাল প্রভৃতিকে দূরে ছুড়ে ফেলতে হবে।...হৃদয়ের কোমলতা ও দুর্বলতাকে দূর করতে হবে। দয়া ও অনুগ্রহ মানুষের অক্ষমতার প্রকাশ; বিনয় ও নম্রতা ব্যক্তির নতজানুতার লক্ষণ; ধৈর্য,সহিষ্ণুতা,ক্ষমা ও করুণা হলো ভীরুতা ও কাপুরুষতা।আমাদের পৌরুষত্বকে গ্রহণ করতে হবে। শ্রেষ্ঠ মানব ভালো-মন্দের ঊর্ধ্বে এবং শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তির অধিকারী।”
পাশ্চাত্যে এ ধরনের বহু মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে এরূপ কোন মতবাদের সৃষ্টি হয়নি যা তাদের মধ্যে হয়েছে।
পাশ্চাত্যমনা প্রাণ এটাই। মানবাধিকারের যে সনদ তারা ঘোষণা করেন তা অন্যদের প্রতারণার জন্যই। পাশ্চাত্যের নৈতিকতা ও সভ্যতা নী’
চে আর ম্যাকিয়াভেলীর চিন্তাভুক্ত নৈতিকতা। সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীতে যা করছে তা এ চিন্তাধারার ভিত্তিতেই। পাশ্চাত্য চরিত্র- হোক তা আমেরিকান বা ইউরোপীয়- সে চরিত্র সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র এবং নী’
চের নৈতিকতা। যদিও কখনো কখনো তাদের কেউ আমাদের সামনে মানবাধিকারের কথা বললে আমরা দুর্ভাগারা ঢোক গিলে তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করে থাকি,তবুও কসম করে বলতে পারি এটা ভুল। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকা ভিয়েতনামে যে কাজটি করেছে তা নী’
চের দর্শনের প্রয়োগ বৈ অন্য কিছু? এটা যথার্থই নী’
চের দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ। পাশ্চাত্য যে এত অধিক মানবতা ও মানবসেবার শ্লোগান দেয় ও বলে,বারট্রান্ড রাসেল এরূপ বলেছেন,সারটার এরূপ বলেছেন,অথচ তার সকল চিন্তার ভিত্তি নী’
চের দর্শন। সম্ভবত দু’
একজন ব্যতিক্রমী দার্শনিকের সন্ধান পাওয়া যাবে যাদের চিন্তার ভিত্তি এটা নয় এবং খুব সম্ভব তাদের রক্তের সাথে প্রাচ্যের মিশ্রণ ঘটে থাকবে। হয়তো তাদের মাতৃকুল প্রাচ্য থেকে গিয়েছিলেন,নতুবা পাশ্চাত্য জাতি এরূপ নয়।
নী’
চে বলেন,“
আত্মনিয়ন্ত্রণ আবার কেন? বরং প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করতে হবে। পরোপকারই বা কেন? বরং নিজের উপাসনা কর এবং নিজের চাওয়াকে অর্জন কর। দুর্বল ও অক্ষমকে ত্যাগ কর যাতে তারা বিলুপ্ত হয় এবং পৃথিবীর সকল দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হবে... পুরুষকে অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে এবং শক্তিমত্তার সাথে জীবন যাপন করতে হবে যাতে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা যায়।”
পুরুষের শক্তিমত্তার মধ্যেই পূর্ণতার সমাপ্তি- সৃষ্টি এবং অস্তিত্বের সকল প্রস্তুতি তার জন্যই। এখন দেখুন,নী’
চের এ কথা থেকে কি বোঝা যায়। এর অর্থ হচ্ছে,কোন কিছুই এর প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়। তাই নৈতিকতা,দয়া,অনুগ্রহ,মানবতা,ন্যায় বিচার,উৎসর্গ ও বিসর্জন প্রভৃতি মূল্যবোধকে দূরে ছুড়ে ফেলতে হবে এবং নিজেকে এ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। এজন্য তিনি বলেছেন,“
নিজের প্রবৃত্তির ইচ্ছা পূরণ করুন। সুখী হোন,নিজেকে প্রভু ও কর্তা জানুন এবং নিজের প্রভূত্বের প্রতিবন্ধক সকল বস্তুকে সামনে থেকে অপসারিত করুন,কোন বিপদ ও যুদ্ধকে ভয় করবেন না।”
অতঃপর নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,“
পুরুষ ও নারীর সাম্যের বিষয়টি অযৌক্তিক এবং নারীর অধিকার রক্ষার বিষয়টিও অগ্রহণযোগ্য। পুরুষই সব কিছু। পুরুষ যুদ্ধংদেহী এবং নারী শৈল্পিক। তাই সে পুরুষকে আনন্দ দেবে এবং সন্তান আনয়ন করবে।”
তাই নী’
চের দৃষ্টিতে নারী আনন্দের উপকরণ,বাচ্চা উৎপাদনের যন্ত্র এবং পুরুষের ইচ্ছার দাস বৈ কিছু নয়। পূর্ণ মানবের পরিচয় লাভের জন্য এ পদ্ধতিটিও একটি মানদণ্ড হিসেবে পাশ্চাত্যে প্রচলিত। আদর্শ ও সর্বোত্তম মানব (তাদের ভাষায় সুপারম্যান) কে তা যাচাইয়ের মানদণ্ড হলো শক্তি ও ক্ষমতা।
এ মতবাদের বিপরীত যে মতবাদ- যা দুর্বলতার পক্ষে প্রচারণা চালায় এবং সকল কল্যাণকে দুর্বলতার মধ্যে বলে জানে- তা খ্রিষ্ট মতবাদ। খ্রিষ্টবাদ নৈতিকতার ক্ষেত্রে দুর্বলতার প্রচারণা চালায় । প্রচলিত একটি কথা‘
কেউ তোমার ডান গালে চড় বসিয়ে দিলে বাম গালটিকেও তার দিকে বাড়িয়ে দাও’
-এটা খ্রিষ্টবাদ হতে এসেছে।
 3%
3%
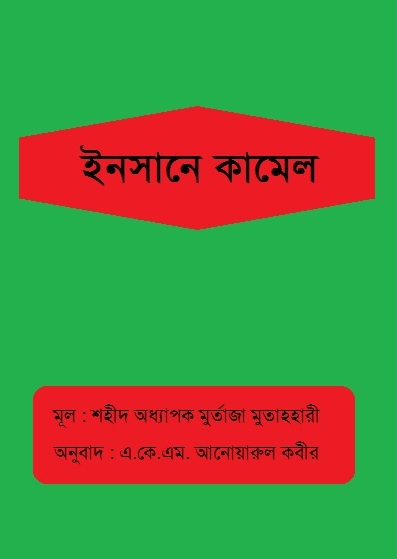 লেখক: শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী
লেখক: শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী





