স্নেহও সহানুভূতির সঠিক ও অযাচিত প্রকাশ
প্রথমে সা’
দীর একটি কবিতা ও পরে কোরআনের একটি আয়াত আপনাদের জন্য পড়ব। সা’
দীতার কবিতায় বলেছেন,
“
যদি দেখাও সহানুভূতি ধারালো দাঁতের নেকড়ের প্রতি
জুলুম করলে তুমি নিরীহ মেষ শাবকের প্রতি।”
কোন চিতা বা নেকড়ের প্রতি সহানুভূতি দেখানো মেষদের প্রতি জুলমের শামিল। অর্থাৎ শত শত মেষ হত্যাকারী কোন নেকড়েকে যদি হত্যা করা হয় আর তাতে কারো ঐ নেকড়ের প্রতি মায়া জন্মে, তবে মেষদের প্রতি অবিচার করা হলো। এটি অবশ্য সা’
দী উদাহরণ দিয়েছেন। মূলত তার উদ্দেশ্য অত্যাচারী এবং তার অধীন অসহায় ও বঞ্চিত মানুষরা। দুর্বল আত্মার লোকেরা অত্যাচারীদের প্রতি অজ্ঞতাবশত সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকে।
জেনাকারী পুরুষ ও নারীর ব্যপারে কোরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যদি স্ত্রী রয়েছে এরূপ কোন পুরুষ বা স্বামী রয়েছে এরূপ কোন নারী জেনা করে ইসলামে তার শাস্তি হচ্ছে তাদেরকে পাথর ছুড়ে হত্যা করতে হবে। কোরআন বলছে,এদের শাস্তিদান ও হত্যার সময় একদল মুমিনকে সেখানে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।
(
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
)
এ রকম ক্ষেত্রে দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ যারা সমাজের উচ্চতর সঠিক কল্যাণের দিকটি লক্ষ্য করে না তাদের সহানুভূতি জেগে উঠে বলতে পারে,এ কাজ না করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখানো উচিত।
কোরআন বলছে,وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ
“
আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি তোমাদের মনে যেন দয়ার উদ্রেক না হয়।”
এটা ঐশী বিধান কার্যকর করার স্থান যে ঐশী বিধান উচ্চতর কল্যাণ ও মানবতার সার্বিক শৃঙ্খলা বিধানের জন্য প্রণীত হয়েছে,তাই এখানে সহমর্মিতার স্থান নেই। কেউ এরূপ ক্ষেত্রে সহমর্মিতা দেখালে তা সমাজের প্রতি জুলমের শামিল।
এরূপ অপর একটি বিষয় যা অনেকেই বলে থাকেন তা হলো মৃত্যুদণ্ড আবার কেন? মৃত্যুদণ্ড অত্যন্তু অমানবিক বিষয়। অপরাধী যে অপরাধই করুক তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। এরা এদের এ কর্মকাণ্ডকে এভাবে ব্যাখ্যা করে যে,অপরাধীকে সংশোধন করতে হবে।
কত বড় ভুল কথা! এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে,মানুষকে সংশোধন করতে হবে,কিন্তু অবশ্যই তা অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে যাতে করে কোন অপরাধ সংঘটিত না হয়। কিন্তু অধিকাংশ সমাজেই শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই,বরং অনৈতিকতা ও বিশৃঙ্খলার উপাদান পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। কিংবা ধরি,কোন সমাজে নৈতিক প্রশিক্ষণের সকল সুবিধা বিদ্যমান,কিন্তু সমাজে সব সময় একদল অপরাধ প্রবণ বিচ্যুত ব্যক্তি রয়েছে যারা ঐ সমাজেও অপরাধে লিপ্ত হয়। এদের জন্য কি করা উচিত? আমরা অপরাধীকে সংশোধন করব- এ অজুহাতে অপরাধীকে অপরাধ করার সুযোগ দেব আর তারপর যখন অপরাধ সংঘটিত হবে তখন তাকে সংশোধন করতে যাব। এভাবে সকল অপরাধীকে গ্রীন সিগনাল দেয়া হবে এবং তারা অপরাধ করতে উৎসাহিত হবে। সে নিজেকে বলবে,সমাজ এতদিন আমার সংশোধনের চিন্তায় ছিল না- যখন আমি কিশোর ছিলাম তখন আমার পিতা আমাকে প্রশিক্ষিত করার ও সংশোধনের পদক্ষেপ নেননি,যখন বড় হয়ে সমাজে প্রবেশ করেছি তখনও সমাজ তা করেনি,এখন অপরাধ করার পর জেলে আমাকে প্রশিক্ষিত ও সংশোধন করা হবে। তাই প্রথমে একটি অপরাধ করি তাহলে সমাজ আমাকে সংশোধনের সুযোগ পাবে।
আরেক দল বলেন,চোরের হাত কাটা হবে কেন? যে সকল মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ তারাই এ কথা বলেন। আপনারা দৈনিক পত্রিকার পাতাগুলো লক্ষ্য করুন,দেখবেন চুরি-ডাকাতির কারণে কি পরিমাণ সম্পদ মানুষের হাতছাড়া হয় শুধু তাই নয়। কত মানব হত্যার মতো অপরাধ সংঘটিত হয় যদি চোরের যথাযথ শাস্তি হয় এবং চোর জানে যে,পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তার চার আঙ্গুল কাটা যাবে যা মৃত্যু পর্যন্ত তার দেহে চুরির সাক্ষ্য হিসেবে থাকবে তবে সে কখনই চুরি করবে না। যদি কয়েকজন,এমনকি একজন চোরকেও এ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়,তবে চুরির পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে।
যে সকল হাজী পঞ্চাশ-ষাট বছর (এ গ্রন্থটি প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বের) পূর্বে মক্কা গিয়েছিলেন তারা দেখেছেন,আর যারা না গিয়েছেন তারা হয়তো শুনেছেন যে,তখন সৌদি আরবে চুরি কিরূপ ভয়াবহ ছিল! সে সময় যেহেতু বাস বা প্লেন ছিল না,সবাই উট বা এরূপ অন্য কোন বাহনে হজ্ব করতে যেত। সশস্ত্র ব্যক্তিসহ দু’
হাজার ব্যক্তির কফেলা না হলে মরুপথে হাজীরা হজ্বে যাওয়ার সাহস পেতেন না। তদুপরি প্রতি বছর শোনা যেত অনেক ব্যক্তি মরুদস্যুদের হাতে নিহত হয়েছেন,তাদের সম্পদসমূহ লুণ্ঠিত হয়েছে। যদিও দস্যুরাও অনেকেই নিহত হতো,কিন্তু মৃত্যু তাদের জন্য একটি সম্ভাবনা বিধায় তারা এ কাজ হতে সহজেই নিবৃত্ত হতো না। সৌদি সরকার অন্তত এ একটি বিষয়ে পৃথিবীতে সফল হয়েছে (তাদের অন্য কর্মকাণ্ড খারাপ কি ভালো সে আলোচনায় না গিয়ে)। শুধু এক বা দু’
বছর চোরের হাত কাটার কারণে চুরি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্বে প্রতি বছরই শত শত চোর ও হাজী নিহত হতেন তাতে কোন প্রভাব পড়ত না। কিন্তু যখন চোরকে আরাফাত বা মিনা বা অন্য কোথাও এনে প্রকাশ্যে হাত কাটার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হলো এবং কয়েকবার এ কাজের পূনরাবৃত্তি করা হলো তখন দেখা গেল যারা এ কাজ করত তারা ভীত হয়ে এ কাজ হতে বিরত হলো এবং চুরি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। যে দেশটিতে চুরির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল সে দেশটিতেই হাজীদের সুটকেস ও মালপত্র কয়েকদিন এক স্থানে পড়ে থাকে,অথচ কেউ সাহস করে না তাতে হাত দেয়ার বা পা দিয়ে নেড়ে দেখার। যতক্ষণ পর্যন্ত এর মালিককে পাওয়া না যায় তা এভাবেই পড়ে থাকে। এর কারণ হলো চোরের যথাযথ শাস্তির বিধান কার্যকর করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,
(
وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ
)
তাই এরূপ অপরাধীর প্রতি যে কোনরূপ সহমর্মিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন অযৌক্তিক অর্থাৎ তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন নিরপরাধ ব্যক্তিদের প্রতি নিষ্ঠুরতারই নামান্তর। তাই এরূপ সহানুভূতির কোন স্থান ইসলামে নেই,বরং এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ শক্তিমত্তার প্রকাশ।
সুতরাং ক্ষমতার মতবাদের অনুসারী যারা সব সময় বলে পূর্ণ মানব হলো শক্তিমান মানব,তারা অন্য সকল মানবিক মূল্যবোধকে উপেক্ষাই শুধু করেনি,স্বয়ং ক্ষমতাকে বুঝতে ও সনাক্ত করতেও ব্যর্থ হয়েছে।
হাদীসসমূহের প্রকৃত ক্ষমতা
ক্ষমতা হচ্ছে এটাই যে,মানুষ অন্যের সহযোগিতায় তার হাত প্রসারিত করবে। শক্তিমান আত্মার অধিকারী ব্যক্তি তার সন্তানকে বলেন,
کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا
হযরত আলী (আ.) তার প্রিয় পুত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,“
হে আমার সন্তানেরা! সব সময় তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা মজলুমের সহযোগিতায় জালেমের প্রতিরোধে দ্রুত অগ্রসর হবে। এটা ক্ষমতার নিদর্শন।”
(নাহজুল বালাগাহ্,পত্র নং ৪৭)
বাস্তবত হিংসা,বিদ্বেষ,অন্যের অকল্যাণ কামনা এরূপ যে সব বিষয় নী’
চে জন্মদানের চেষ্টা করেছেন এর সবই দুর্বলতাপ্রসূত।
যে ব্যক্তি সব সময় অন্যদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায় এবং অন্যদের কষ্ট দেয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে এগুলো ক্ষমতাপ্রসূত নয়,বরং দুর্বলতাপ্রসূত। মানুষ যত শক্তিমান হবে তার মধ্য হিংসা-দ্বেষ তত কমে আসবে।
ইমাম হুসাইন (আ.)-এর একটি হাদীস খুবই আকর্ষণীয়। তিনি বলেছেন,
القدرة تذهت الحفیظة
“
ক্ষমতা মন হতে বিদ্বেষ দূর করে।”
অর্থাৎ যখন মানুষ নিজের মধ্যে ক্ষমতা অনুভব করে তখন অন্যদের প্রতি তার বিদ্বেষ আর থাকে না। (বালাগাতুল হুসাইন,পৃ. ৮৯)
দুর্বল ব্যক্তিরাই কেবল বিদ্বেষ পোষণ করে এবং হিংসাকে লালন করে থাকে। ইমাম হুসাইনের এ কথাটি যথার্থ মনোতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।
হযরত আলীর গীবত সম্পর্কে একটি বাণী রয়েছে। তাকে প্রশ্ন করা হলো কিরূপ ব্যক্তি গীবত করে অর্থাৎ মানুষের অনুপস্থিতিতে তার নিন্দা ও দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে আনন্দ পায়? আলী (আ.) বলেন,“
দুর্বল ও অক্ষমরা”
الغیبة جهد العاجز
অর্থাৎ গীবত অক্ষমদের সর্বশেষ প্রচেষ্টা। (নাহজুল বালাগাহ্,হেকমত ৪৬১)
একজন শক্তিমান মানুষ যে আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান,গীবত তার নিকট লজ্জার বিষয় এবং সে এ কাজকে নিকৃষ্ট ও দুর্বলদের কাজ বলে মনে করে। তাই প্রকৃত ক্ষমতাবান মানুষ যেমন অন্যদের গীবত করেন না তেমনি শুনতেও চান না। আলী (আ.) তাই গীবতকে দুর্বলতাপ্রসূত বলে উল্লেখ করে বলেছেন,শক্তিমান আত্মার অধিকারী মানুষ কখনও গীবত করে না।
ইমাম আলী (আ.) এমনকি জেনাকেও দুর্বলতাপ্রসূত মনে করেন। তিনি বলেছেন,ما زنی غیور قطّ
“
আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি জেনা করতে পারে না।”
পৃথিবীতে যে ব্যক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মসম্মানবোধ রয়েছে সে কান নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না। তাই কেবল আত্মসম্মানহীন ব্যক্তি যে নিজের মধ্যে এ বিষয়ে দুর্বলতা অনুভব করে সে-ই এরূপ কাজ করে। কারণ আত্মসম্মানহীন ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে যদি অন্য পুরুষ অনুরূপ কাজ করে তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয়না। এ জন্যই আলী (আ.) বলেছেন,ما زنی غیور قطّ
(নাহজুল বালাগাহ্,হেকমত ৩০৫)
কিন্তু জনাব নী’
চে এরূপ ক্ষমতাকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার দৃষ্টিতে ক্ষমতা পেশী শক্তি ও অস্ত্রবল অর্থাৎ তরবারী ধারণ করতঃ অন্যের উপর আঘাত হানা। তার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে মানুষরূপী শক্তিধর কোন পশু যার বাহুর শক্তি অধিক। তাই তার নিকট আত্মিক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান নেই। অতএব,ইসলামী মতাদর্শে নিঃসন্দেহে ক্ষমতা একটি মানবীয় মূল্যবোধ এবং মানুষের পূর্ণতার পথের অন্যতম পূর্ণরূপ। তাই ইসলাম দুর্বল ব্যক্তিকে পছন্দ করে না।
إنّ الله یبغض المؤمنین الضعیف
অর্থাৎ দুর্বল ও অক্ষম মুমিনকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। (কাফী,৫ম খণ্ড,পৃ. ৫৯)
সুতরাং প্রথমত ইসলাম ক্ষমতাকে মানুষের একমাত্র মূল্যবোধ বলে মনে করে না বরং এর পাশাপাশি পূর্ণতার অন্যান্য মূল্যবোধ রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়ত ইসলাম ক্ষমতা বলতে যা বুঝে তা নী’
চে,সংশয়বাদী দার্শনিক ম্যকিয়াভেলী এবং অন্যদের ধারণা হতে পৃথক। ইসলাম মানুষের মধ্যে এমন অনেক ক্ষমতায় বিশ্বাসী এবং সেগুলোর বিকাশে প্রয়াসী যার ফল নী’
চের ধারণার বিপরীত এবং যা সমাজের জন্য কল্যাণকর।
নী’
চে বলেন,দুর্বলের জন্য সহমর্মিতা দুর্বলতা হতে উদ্ভূত। তাকে বলতে চাই,সহমর্মিতা শুধু নয়,এখানে ভালোবাসা,ক্ষমা,দানশীলতা- সর্বোপরি কল্যাণকামিতা রয়েছে। কেন প্রতিটি বিষয়কে এক চোখে দেখেন? আপনার নিকট প্রশ্ন একজন ক্ষমতাবান মানুষের দান ও অনুগ্রহ অন্যদের নিকট পৌছে নাকি এক দুর্বলের? তাই জবাব দিন অনুগ্রহ ক্ষমতা হতে উৎসারিত নাকি দুর্বলতা হতে? অবশ্যই ক্ষমতা হতে,দুর্বলতা হতে নয়। যা হোক আমরা এখন অন্য আলোচনা শুরু করব।
 11%
11%
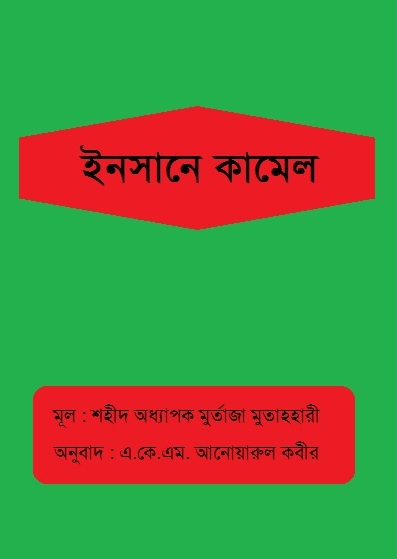 লেখক: শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী
লেখক: শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী





