দুর্বলতার মতবাদ
যেমনিভাবে অনেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদের বিরোধিতা করেছেন এবং অনেকেই প্রেমের মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক বলে মনে করেছেন তেমনিভাবে ক্ষমতার মতবাদেরও অনেকে বিরোধিতা করেছেন। কেউ কেউ ক্ষমতাকে বাড়াবাড়ি রকমভাবে সমালোচনা করেছেন এবং মানুষের পূর্ণতাকে প্রকৃতপক্ষে দুর্বল থাকার মধ্যেই মনে করেছেন। তাদের মতে পূর্ণ মানব হলো সে-ই যার কোন ক্ষমতা নেই। যেহেতু যদি ক্ষমতা থাকে তবে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনের সম্ভাবনা রয়েছে। শেখ সা’
দী তার এক কবিতায় এ রকম একটি ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন,
“
আমি সে পিপীলিকা,যে অন্যের পায়ে পদদলিত
হয় নই মৌমাছি যে তার আঘাতে অন্যকে কষ্ট দেয়।”
আবার বলেছেন,
“
কিরূপে করিব আমি এ নেয়ামতের শোকর স্বর্গপতি?
সে শক্তি দাওনি আমায় করিব সৃষ্টির ক্ষতি।”
না,জনাব সা’
দী,এমন নয় যে,মানুষকে হয় পিপীলিকা,না হয় মৌমাছি হতে হবে। ফলে আপনি এ দু’
য়ের মধ্যে পিপীলিকা হওয়াকে নিজের জন্য বেছে নিবেন। আপনার সেই পিপীলিকা হওয়ারও প্রয়োজন নেই যে অন্যের পায়ের নীচে পিষ্ট হয়,আবার মৌমাছি বা বোলতা হওয়ারও প্রয়োজন নেই যে অন্যকে কষ্ট দেয়। বরং আপনার এটা বলা উচিত,
“
আমি সে পিপীলিকাও নই,যে অন্যের পায়ে পিষ্ট হয়
নই মৌমাছিও,যে অন্যকে কষ্ট দেয়।
কিরূপে এ নেয়ামতের শোকর করব আমি?
রয়েছে শক্তি তবুও কষ্ট দেই না আমি।”
যদি মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা থাকে তদুপরি কাউকে কষ্ট না দেয় তখনই শোকরের প্রশ্ন আসে। নতুবা শক্তি না থাকার কারণে কাউকে কষ্ট দেয় না এরূপ হলে শিংবিহীন প্রাণীর মতো যে শিং না থাকার কারণে কাউকে গুঁতা দেয় না। যোগ্যতার প্রমাণ এখানেই যে,শিং থাকার পরও কাউকে গুঁতা দেয় না।
সা’
দী অন্য এক স্থানে বলেছেন,
“
দেখেছি এক সন্ন্যাসীকে থাকেন পর্বত চূড়ায়,
সন্তুষ্টির অন্বেষায় দুনিয়া ত্যাগীয়া নিয়েছেন আশ্রয় গুহায়।
জিজ্ঞাসিনু তারে কেন আসেন না মানুষের মাঝে
মানুষের বোঝা লাঘবের মহান কাজে?”
এক সাধক যিনি পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেখানে ইবাদতে মশগুল তার প্রশংসায় লিপ্ত হয়েছেন সা’
দী। (অবশ্য সা’
দী এ কবিতায় ভাবার্থের বিপরীতধর্মী কথাও অন্যস্থানে বলেছেন। যেমনবলেছেন,
“
খানকা থেকে এলেন এক বুজুর্গ মাদ্রাসায়,
ভেঙ্গে তার চুক্তি যা ছিল সে পথের পথিকের সাথে।
জিজ্ঞাসিনু তারে কি পার্থক্য রয়েছে আলেম ও আবেদের মাঝে
যে কারণে ছেড়েছেন সে পথ,ধরেছেন এ রথ?
বললেন,যে বাঁচাতে চায় নিজেরে শুধু,উত্তাল সমুদ্রের মাঝে,
সে আবেদ,আর যে অন্যকেও বাঁচাতে চায় তাকেই আলেম বলা সাজে।”
তিনি বলছেন,তাকে প্রশ্ন করলাম,“
কেন আপনি শহরে আসেন না,মানুষের খেদমত করেন না?”
সাধক তার জবাবে এক অজুহাত পেশ করেন। সা’
দী এখানেই নীরব হয়ে যান। মনে হয় তিনি সাধকের এ অজুহাতকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। তিনি বলছেন,
“
বললেন সাধক,সেথায় রয়েছে অপরূপ রূপসিগণ
ভয় পাই,যদি দেখিয়া তাদের রূপ হারাই নিয়ন্ত্রণ।”
(যেমনভাবে হাতী কাদাযুক্ত পথে চলতে ভয় পায়)
যেহেতু অপরূপ রূপসীরা সে শহরে বাস করে। তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতে আমার স্খলন ঘটতে পারে। যেহেতু নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় আছে তাই এ গুহায় নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছি।
বাহ্! কত সুন্দর এ পূর্ণতা! নিজেকে এক স্থানে বন্দি করে পূর্ণতায় পৌছার পথ খোঁজাকে কি পূর্ণতা বলা যায়? জনাব সা’
দী কোরআন আপানার জন্য সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছে। এ কাহিনী হযরত ইউসুফ (আ.)-এর। এ কাহিনী কোরআনের ভাষায় তাদের জন্য যারা তাকওয়া (খোদাভীতি) ও ধৈর্য অবলম্বন করে; যেহেতু কোরআন বলছে,“
নিশ্চয়ই যে তাকওয়া ও ধৈর্য অবলম্বন করে (অবশেষে সে সফলকাম হবে),যেহেতু আল্লাহ্পাক সৎকর্মশীলদের কর্মকে বিফল করেন না।”
(সূরা ইউসুফ : ৯০)অর্থাৎ কোরআন বলছে,তুমিও ইউসুফের মতো হও। প্রবৃত্তির ক্ষুধা মেটানোর সকল উপায়-উপকরণ প্রস্তত ছিল,এমনকি পালানোর পথও রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তদুপরি তিনি নিজের পবিত্রতাকে রক্ষা‘
করেছেন। মহান আল্লাহ্ তার জন্য বন্ধ দুয়ারগুলোও খুলে দিয়েছেন। যেহেতু হযরত ইউসুফ (আ.)অবিবাহিত এবং সৌন্দর্যের দিক থেকে ছিলেন অপূর্ব,সেহেতু তিনি নারীদের পেছনে নন,বরং নারীরাই তার পেছনে ছুটত। এমন দিন তার জন্য অতিবাহিত হতো না যে,কোন নারী তাকে পত্র দেয়নি বা তার খোঁজে আসেনি। তাও যেমন তেমন নারী নয়,বরং মিশরের শ্রেষ্ঠ ও কূলনারীরা তার জন্য চরমভাবে আসক্ত ছিল। স্বয়ং মিশরের অধিপতির স্ত্রী জুলাইখা তার প্রেমে বিভোর। তাকে পাওয়ার জন্য সব উপকরণ প্রস্তত করেছে। তার জন্য মরণ ফাঁদ পেতেছে- হয় তার ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতে‘
হবে,নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু হযরত ইউসুফ কি করলেন? আল্লাহর প্রতি হাত উঠিয়ে বললেন,“
হে পরওয়ারদিগার! যে বস্তুর প্রতি এরা আমাকে আহবান করছে তার থেকে জেলখানায় বন্দিত্ববরণকে আমি অধিক পছন্দ করি।”
(সূরা ইউসুফ : ৩৩)
অর্থাৎ এ স্ত্রীলোকদের ইচ্ছা পূরণ করার চেয়ে আমাকে বন্দিত্ব বরণের সুযোগ দিন যাতে করে এদের হাত থেকে রক্ষা পাই। যদিও আমার এ অপরাধ করার সামর্থ্য ও সুযোগ রয়েছে তদুপরি তা আমি করব না।
সুতরাং মানুষের পূর্ণতা তাদের দুর্বলতার মধ্যে নয়। যদিও আমাদের সাহিত্যে কখনো কখনো কেউ দুর্বলতাকে মানুষের পূর্ণতা মনে করেছেন। অন্য এক কবি বাবা তাহেরও এ রকম বলেছেন,
“
আমার এ চোখ ও অন্তর হতে আমি বাঁচতে চাই,
যা কিছু দেখে এ চোখ,অন্তর স্মরণ করে তা-ই।”
এ পর্যন্ত কথা ঠিকই আছে,কিন্তু এরপর বলছেন,
“
বানাব এক তরবারী যা লৌহ কঠিন শক্ত
হানব আঘাত এ চক্ষুতে অন্তর হবে মুক্ত।”
অর্থাৎ যা কিছুই চক্ষু দেখে অন্তর তা পেতে চায়। তাই অন্তরকে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্য এক তরবারী চাই যা দিয়ে এ চক্ষুকে অন্ধ করে দিব যাতে অন্তর কিছু না চাইতে পারে। যদি এমনই হয় তবে এমন অনেক অনেক কিছু আছে যা কর্ণ শুনে ও অন্তর পেতে চায় তাই কর্ণের মধ্যেও এক তরবারী প্রবেশ করান। আর পুরোদমে মুক্তি পেতে চাইলে খোজাও হতে হবে যাতে জৈবিক চাহিদার কথাও মনে না হয়। শেষ পর্যন্ত মাওলানা রুমীর মাসনভীর মাথা,পেট ও লেজবিহীন সিংহের গল্পের মতো হবে। বাবা তাহের অদ্ভুত এক ইনসানে কামেল তৈরি করেছেন। এই ইনসানে কামেলের না হাত আছে,না পা আছে,না চোখ,কান বা অন্য কিছু।
এ ধরনের দুর্বল চারিত্রিক প্রশিক্ষণের নির্দেশনা আমাদের সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায়। তাই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে মানুষ সব সময়ই ভুল করে। কখনো অতিরিক্ত,কখনো পরিহার তার জীবনে লক্ষণীয়। ইসলামে যেহেতু ত্রুটি নেই তাই বোঝা যায়,এটা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোথাও থেকে আসেনি। যদি মানুষ সক্রেটিস হয় তাহলে মূল্যবোধগুলোর হয়তো একটি দিক ধরে থাকেন ও ভুল করেন,প্লেটো হলে অন্য একটি দিক ধরে থাকেন ও ভুল করেন। তেমনিভাবে ইবনে সিনা একদিক,মহিউদ্দিন আরাবী ও মাওলানা রুমী অন্যদিক ধরে থাকেন। কার্ল মার্কস,জাপসে সারটার সকলেই এরূপ একদিক ধরে বসে রয়েছেন। তাই এঁদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব মানুষের পথ প্রদর্শক হওয়া? নবীয়ানী ও মতাদর্শ তো সর্বজনীন,সর্বব্যাপী ও পূর্ণ হতে হবে। তাই প্রকৃতপক্ষে এ সকল ব্যক্তি যেন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে একদল ছাত্র- নিজেদের চিন্তা-ভাবনা থেকে কিছু বলেছে। অবশেষে বিজ্ঞ শিক্ষকের কথা শুনলে বোঝা যাবে শিক্ষকের কথা তাদের থেকে কত উন্নত ও উত্তম!
 7%
7%
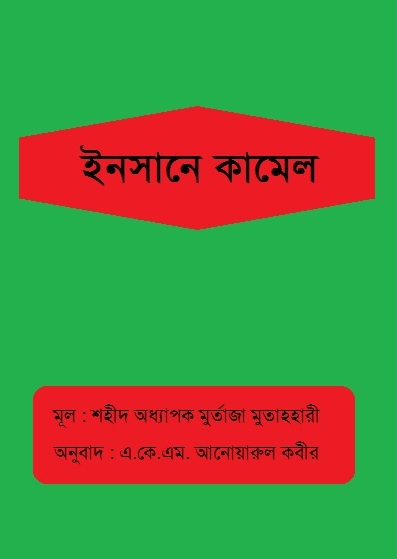 লেখক: শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী
লেখক: শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী





