(আর এখানে তিনটি আলোচনা রয়েছে)
একদম শুরু থেকেই যে দুই প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি মহানবীর জীবদ্দশায় ইসলামী উম্মাহর বিকাশ লাভের পাশাপাশি বিকাশ লাভ করেছিল তা হলঃ
প্রথমতঃ ধর্মীয় কৃচ্ছসাধনায় নিবিষ্টতা,ধর্মীয় দৃঢ়তা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধানের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণে বিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গি ।
দ্বিতীয়তঃ ঐ দৃষ্টিভঙ্গি,যা বিশ্বাস করে যে,ধর্মে বিশ্বাস কেবলমাত্র ইবাদত ও অদৃশ্য জগতের বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ভক্তি,আনুগত্য ও নিবিষ্টতার মাঝেই সীমাবদ্ধ এবং প্রাগুক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কল্যাণ,স্বার্থ ও সুবিধানুসারে ধর্মীয় বিধি-বিধানের পরিবর্তন ও ভারসাম্যপূর্ণ করণের ভিত্তিতে ইজতিহাদ এবং যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করা বৈধ ও সম্ভব ।
সাহাবাগণ মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাসী ও গৌরবোজ্জ্বল অগ্রগামী প্রজন্ম হিসেবে মুসলিম উম্মাহর বিকাশের সর্বোত্তম উৎস হওয়া সত্ত্বেও এমনকি মানব ইতিহাসে মহানবীর নিজ হাতে গড়া প্রজন্মের চেয়ে অধিকতর উত্তম,সম্ভ্রান্ত এবং পবিত্র কোন আদর্শিক প্রজন্ম না দেখা গেলেও আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই এমন এক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতার অস্তিত্ব মেনে নেয়ার আবশ্যিকতা প্রত্যক্ষ করি যা কল্যাণকামিতা ও সুবিধার আলোকে পুঙ্খানুপঙ্খরূপে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করার চাইতে ইজতিহাদ এবং পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে ফায়দা বা সুবিধা ভোগ করার বিষয়টিকে অত্যধিক প্রাধান্য দিতে ইচ্ছুক । আর এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতার কারণেই মহানবী (সা.)-কে অনেক ক্ষেত্রে এমনকি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়েও তিক্ততা সহ্য করতে হয়েছে । সামনে এতদসংক্রান্ত আরো বর্ণনা ও বিবরণ আসবে । তবে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রবণতা ছিল যা ধর্মীয় দৃঢ়তা,ধর্মের প্রতি চূড়ান্ত আত্মসমর্পণবোধ এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি-বিধানের নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত আনুগত্যে বিশ্বাসী ।
মুসলমানদের মাঝে ইজতিহাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রবণতার প্রসার লাভের অন্যতম একটি কারণ হয়তো এটাও হতে পারে যে,এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি,যে স্বার্থ-সুবিধা বা কল্যাণ মানুষ উপলব্ধি ও পরিমাপ করতে সক্ষম তদনুসারে যথেচ্ছা ভোগ করার প্রবণতার সাথে পূর্ণ সংগতিসম্পন্ন। পক্ষান্তরে যে বিধানের মর্মার্থ বা সারবত্বা সে উপলব্ধি করতে অক্ষম তা পালন করা তার স্বভাব ও প্রবৃত্তির পরিপন্থী । আর বড় বড় সাহাবার মাঝে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের মত কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁরা এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা ও প্রতিনিধিত্বকারী । হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব মহানবীর সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট শরয়ী দলীল-প্রমাণের বিপক্ষে ইজতিহাদও করেছেন । যে পর্যন্ত তিনি (হযরত উমর) প্রত্যক্ষ করতেন যে,ফায়দা বা কল্যাণকামিতার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ইজতিহাদে ভুল করেননি (অর্থাৎ তাঁর ইজতিহাদ ফায়দা বা কল্যাণ পরিপন্থী নয়) সে পর্যন্ত তিনি এমনকি নাস বা স্পষ্ট শরয়ী দলীল-প্রমাণের বিপক্ষেও ইজতিহাদ করার বৈধতায় বিশ্বাস করতেন । আর এতদপ্রসঙ্গে হুদাইবিয়ার সন্ধির ব্যাপারে তাঁর আচরণ ও নীতি অবস্থান
এবং এ সন্ধির বিপক্ষে তাঁর যুক্তি প্রদানের বিষয়টি আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি । একইভাবে আযানের ক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ ও আযান থেকেحی علی خیر العمل
বাদ দেয়া এবং যখন মহানবী (সা.) মুত’
আতুল হজ্ব
বা হজ্বে তামাত্তুর বিধান দেন তখন মহানবীর এ বিধানের ব্যাপারে নীতি অবস্থান ইত্যাদি সব কিছুই ছিল নাস বা স্পষ্ট শরয়ী দলীল- প্রমাণের মোকাবেলায় তাঁর গৃহীত ইজতিহাদী পদক্ষেপ ।
আর এ দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয় মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষভাগে কোন এক দিনে তাঁরই সামনে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল । হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে,তিনি বলেছেন,“
মহানবীর ওফাত তথা মৃত্যু নিকটবর্তী হলে একদিন ঘরে অনেক লোক উপস্থিত ছিল।আর তাদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাবও ছিলেন,তখন মহানবী (সা.) বললেন,“
এসো আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দিব যার পর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না ।”
তখন হযরত উমর বলে উঠলেন,“
মহানবীর উপর রোগযন্ত্রণা তীব্র আকার ধারণ করেছে । আর তোমাদের কাছে তো কোরানই রয়েছে । আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব তথা কোরানই যথেষ্ট । হযরত উমরের এ কথায় ঘরে উপস্থিত লোকদের মধ্যে মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হল । তারা ঝগড়া করতে লাগল । তাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বলল,“
তোমরা তাঁর নিকটবর্তী হও । নবী (সা.) তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দিয়ে যাবেন যার পর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না ।”
আবার কেউ কেউ হযরত উমর যা বলেছিলেন তাই বলল । এর ফলে মহানবীর সান্নিধ্যে বাক-বিতন্ডা,অযথা কথা-বার্তা,হট্টগোল,ঝগড়া-বিবাদ এবং মতপার্থক্য চরম আকার ধারণ করলে মহানবী (সা.) তীব্র অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে বললেন,“
আমার কাছ থেকে তোমরা সবাই বের হয়ে যাও।”
প্রাগুক্ত ঘটনাটি ঐ দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের ব্যাপকতা এবং এতদুভয়ের অন্তর্নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পার্থক্যের মাত্রা নিরূপণ ও প্রমাণ করার জন্য একাই যথেষ্ট ।
এ ইজতিহাদী দৃষ্টিভঙ্গি যে কতটা গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করেছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য উসামা বিন যায়েদকে সেনাপতি নিযুক্ত করার ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে যে তর্ক-বিতর্ক,ক্ষোভ ও মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা উপরোক্ত ঘটনার সাথে যোগ করতে পারি । এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল । যার ফলে মহানবী (সা.) অসুস্থাবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে জনসমক্ষে ভাষণ দান করেছিলেন এবং বলেছিলেন,“
হে লোক সকল উসামাকে সমরাধিনায়ক নিযুক্ত করার ব্যাপারে তোমাদের কারো কারো কথা (আপত্তি,ক্ষোভ,অসন্তোষ) আমার কাছে পৌঁছেছে । আর উসামাকে আমি সেনাপতি নিযুক্ত করেছি সে ব্যাপারে তোমরা যদি কটাক্ষ ও তিরষ্কার করতে থাক তাহলে তো তোমরা এর আগেও তার পিতাকে সমরাধিনায়ক নিযুক্ত করার ব্যাপারেও আমাকে কটাক্ষ ও নিন্দা করেছিলে। আল্লাহর শপথ,নিশ্চয়ই যায়েদ সেনাপতি হওয়ার যোগ্য এবং তার পুত্র উসামাও তারপর আমীর বা সেনাপতি হওয়ার যোগ্য ।”
মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এ দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পার্থক্য তাঁর (সা.) তিরোধানের পরও ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্ব সংক্রান্ত মুসলমানদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহেও ব্যাপকাকারে প্রতিফলিত হয়েছে । তাই যারা ধর্মীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে নিঃশর্ত অনুসরণ (تعبد
) সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা ও প্রতিনিধিত্বকারী তারা কোন ধরনের সিদ্ধান্তহীনতা এবং ভারসাম্যকরণ প্রক্রিয়া ছাড়াই মহানবীর হাদীসে এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার যথাযথ কারণও খুজে পেয়েছেন
।
তবে ইজতিহাদী দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টিতে তখনই মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত পদ্ধতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এর পক্ষে সম্ভব যখন এ দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা মতে ইজতিহাদী প্রক্রিয়া এমন এক পদ্ধতি পেশ করবে যা উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে মহানবীর প্রদত্ত পদ্ধতি অপেক্ষাও অধিকতর সংগতিসম্পন্ন হবে ।
আর এভাবে আমরা দেখতে পাই যে,মহানবীর ওফাত বা তিরোধানের সময় থেকেই শিয়া মাযহাবের প্রত্যক্ষ উৎপত্তি হয়েছে । তখন ঐ সকল মুসলমানই“
শিয়া”
বলে পরিচিত হয়েছে যারা কার্যতঃ ইসলামের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের তত্ত্ব মেনে নিয়েছিল । আর এ তত্ত্বটিকে মহানবী (সা.) স্বয়ং তাঁর ওফাতের পরপরই সরাসরি বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন । আর শিয়া দৃষ্টিভঙ্গি,ইমাম আলীর নেতৃত্ব ও ইমামত সংক্রান্ত তত্ত্বটি নিষ্ক্রিয় ও বানচাল করে শাসন-কর্তৃত্ব অন্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করার ব্যাপারে সকীফা বনী সায়েদার চত্বরে যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে । আব্বান বিন তাগলীব থেকে আল্লামা তাবারসী ইহতিজাজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,আব্বান বলেছেন,“
আমি ইমাম জাফর বিন মুহাম্মদ আস-সাদেক (আ.)-কে বললাম,“
আপনার জন্য আমার প্রাণ কোরবান (উৎসর্গ) হোক । মহানবীর সাহাবাদের মধ্যে কি এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন যিনি হযরত আবু বকরের শাসন কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন?”
তিনি (আ.) বললেন,“
যারা হযরত আবু বকরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তারা ছিলেন সংখ্যায় ১২ জন । মুহাজিরদের মধ্য থেকে খালিদ বিন সাঈদ বিন আবিল আস,সালমান আল-ফারেসী,আবুযার গিফারী,মিকদাদ বিন আসওয়াদ,আম্মার বিন ইয়াসির,বুরাইদাহ আল-আসলামী এবং আনসারদের মধ্যে আবুল হাইসান ইবনে আত্-তিহান,উসমান ইবনে হুনাইফ,খুযাইমাহ বিন সাবিত যুশ-শাহাদাতাইন,উবাই বিন কাব এবং আবু আইয়ুব আল-আনসারী । (দ্র: আল্লামা আত্-তাবারসী প্রণীত আল-ইহতিজাজ ১ম খণ্ড,পৃ: ৭৫ ও ১৮৬,মুআস্সাসাহ আল-আ’
লামী,বৈরুত কর্তৃক মুদ্রিত/১৯৮৩;তারীখুল ইয়াকুবী,২য় খণ্ড পৃ: ১০৩)
কেউ কেউ হয়তো বলতে পারে যে,শিয়া দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে নিছক একনিষ্ঠা সহকারে শরয়ী দলীল-প্রমাণ অনুসরণ করার বাস্তব নমুনা । আর এ শিয়া দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে রয়েছে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি যা ইজতিহাদের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে । আর এর অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে,শিয়া মাযহাব ইজতিহাদ প্রত্যাখ্যানকারী এবং শিয়া মতাবলম্বীগণ ইজতিহাদ করার অনুমতি দেয় না । অথচ আমরা দেখতে পাই যে,এরাই (শিয়া মতাবলম্বীগণ) আবার শরীয়তের খুঁটি-নাটি বিষয়ে সর্বদা ইজতিহাদের চর্চা অব্যাহত রেখেছে !!!
উত্তর : যে ইজতিহাদের চর্চা শিয়ারা করে এবং যা শিয়াদের দৃষ্টিতে শুধু জায়েযই নয় বরং ওয়াজিবে কেফায়াহ তা হল শরয়ী দলীল থেকে শরয়ী বিধি-বিধান (হুকুম-আহকাম) প্রণয়ন করা। আর তা মুজতাহিদের ব্যক্তিগত অভিমত ও অভিরুচি অনুসারে শরয়ী দলীল অথবা মুজতাহিদের কল্পিত (অনুমিত) কোন ফায়দা বা কল্যাণকামিতার পরিপ্রেক্ষিতে ইজতিহাদ নয় । কারণ এ ধরনের ইজতিহাদ অবৈধ । আর শিয়া দৃষ্টিভঙ্গি এতদ অর্থে ইজতিহাদের যে কোন ধরনের চর্চাকে প্রত্যাখ্যান করে ।
ইসলামের একদম প্রাথমিক যুগ থেকেই দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে,উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের একটি হচ্ছে শরয়ী দলীল অনুসরণের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও নিবিষ্টতা সম্বলিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপরটি হচ্ছে ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গি । আর এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের অর্থ হচ্ছে শরয়ী দলীল গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ইজতিহাদ ।
যে কোন ব্যাপক সংস্কারপন্থী রিসালত বা মিশন যা একদম গোঁড়া থেকেই সকল দূনীতি,বিশৃঙ্খলা এবং অন্যায়ের আমূল সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা চালায় তার ছত্রছায়ায় উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের উদ্ভব একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা । কেননা এ ধরনের মিশন পূর্ব হতে থেকে যাওয়া জাহেলী ধ্যান-ধারণাসমূহ,নতুন রিসালত বা মিশনের প্রতি প্রতিটি ব্যক্তির একাত্মতার মাত্রা এবং তার ভক্তি ও ভালবাসার পর্যায়ানুসারে বিভিন্ন হারে বা মাত্রায় প্রভাবিত হয়ে থাকে । আর এভাবে আমরা জানতে পারি যে,শরয়ী দলীল অনুসরণ করার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা ও নিবিষ্টতা প্রদর্শনকারী দৃষ্টিভঙ্গিই আসলে রিসালত বা মিশনের সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের একাত্মতা,পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও উৎসর্গের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে । এ দৃষ্টিভঙ্গি শরয়ী দলীলের সীমারেখার মধ্যে ইজতিহাদ এবং তা থেকে শরয়ী বিধি-বিধান প্রণয়ণ করার চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কখনোই অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করে না । এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া জরুরী । আর তা হচ্ছে যে,শরয়ী দলীল অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নিবিষ্টতার অর্থ কখনোই নিষ্ক্রিয়তা, স্থবিরতা (বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার অবসান) এবং বুদ্ধিহীনতা নয় যা মানব জীবনের বিবর্তন, বিকাশ,উন্নতি এবং সংস্কার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কার্যকারণ ও সমুদয় প্রয়োজনীয় উপাদানের পরিপন্থী । কেননা শরয়ী দলীল অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নিবিষ্টতা বা তা’
আব্বুদের অর্থই হচ্ছে ধর্ম অনুসরণ করার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা ও নিবিষ্টতা এবং আংশিকভাবে নয় বরং পূর্ণরূপে দ্বীন বা ধর্মকে আঁকড়ে ধরা । আর এ দ্বীন বা ধর্মের ভিতরেই আছে নমনীয়তার যাবতীয় প্রয়োজনীয় মৌল ও উপাদান,যুগের সাথে চলার শক্তি এবং সবধরনের সংস্কার ও বিবর্তনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় মৌল ও উপাদান ধারণ করার ক্ষমতা (সামর্থ) । তাই ধর্ম ও শরয়ী দলীল অনুসরণ করার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা ও নিবিষ্টতার অর্থই হচ্ছে ঐ সকল মৌল বা উপাদানের মধ্যে যা কিছুরই সৃজনশীলতা,উদ্ভাবনী শক্তি এবং সংস্কারকামিতা রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা ও নিবিষ্টতা । (দ্র: আল-মাআলিমুল জাদীদাহ লিল উসূল পৃ: ৪৮০) । এ সব কিছুই হচ্ছে ইসলাম প্রচার কার্যক্রমের অবকাঠামোর মধ্যে একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে“
তাশাইয়ু”
শব্দের ব্যাখ্যা সম্বলিত কিছু সর্বসাধারণ লেখ বা চিত্র ।
 11%
11%
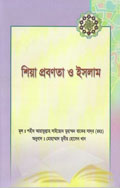 লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুহাম্মদ বাকের সাদর (রহঃ)
লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মুহাম্মদ বাকের সাদর (রহঃ)





