ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কালজয়ী বিপ্লব(৩য় খণ্ড)
 25%
25%
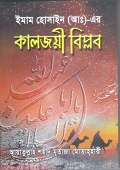 লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী
লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী
: আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
প্রকাশক: কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস -
বিভাগ: ইমাম হোসাইন (আ.)
 25%
25%
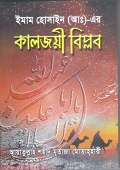 লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী
লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী
: আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
প্রকাশক: কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস -
বিভাগ: ইমাম হোসাইন (আ.)
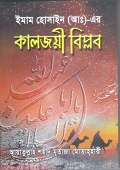
তাবলীগ (বা প্রচার) পদ্ধতি প্রসঙ্গে
হোসাইনী আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে একটি দিক হচ্ছে এর তাবলীগ তথা প্রচারমূলক দিক। এখানে‘ তাবলীগ’ শব্দটি তার প্রকৃত তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে,বর্তমান যুগে প্রচলিত অর্থে নয়। তাবলীগ বা প্রচার মানে জনগণের নিকট প্রচারকের নিজের বাণীকে পৌঁছে দেয়া এবং‘ ইসলাম প্রচার’ মানে স্বয়ং ইসলামকে পৌঁছে দেয়া। অন্যকথায়,মানুষের কাছে ইসলামের আহবান পৌঁছে দেয়া। এবার দেখা দরকার যে,হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) তার এ আন্দোলনে কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন,বিশেষ করে যার তাবলীগি গুরুত্ব রয়েছে। অর্থাৎ এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার যথেষ্ট প্রচারমূলক গুরুত্ব রয়েছে যে,হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) এ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে স্বীয় লক্ষ্যকে এবং তার কন্ঠ থেকে ইসলামের যে প্রকৃত ফরিয়াদ বেরিয়ে আসছিলো তা সর্বোত্তমভাবে জনগণের নিকট পৌঁছে দেন।
এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আজকের দিনে যাকে‘ পদ্ধতি’ (method) বা‘ কর্মপদ্ধতি’ বলা হয়-যা আসলে এক বিদেশী পরিভাষা,সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি।
বস্তুতঃ যে কোনো কাজে সাফল্যের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্বাচন। উদাহরণস্বরূপ,আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে,চিকিৎসা বিজ্ঞান একটি বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান,কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ বা আস্ত্রোপাচারকারীগণ পরস্পর থেকে পৃথক বিভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন এবং তাদের কারো কারো অনুসৃত পদ্ধতি অন্যদের অনুসৃত পদ্ধতি থেকে অধিকতর সাফল্যের অধিকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান এর সন্ধিকাল সম্পর্কিত এক আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে,কালের একটি অধ্যায়কে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে পুরনো বা প্রাচীন ও নতুন বা আধুনিক নামে অভিহিত করা চলে না,তবে একটি যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন বা আধুনিক যুগ বলে নামকরণ করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে ,জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাচীন যুগের সাথে এর আধুনিক যুগের পার্থক্য কী? আধুনিক যুগে বিজ্ঞান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ও অবিশ্বাস্য ভাবে উন্নতি করেছে। মনে হচ্ছে যেন সহসাই বিজ্ঞানের চাকার সামনে থেকে একটি বাধাকে অপসারণ করা হয়েছে এবং এর ফলে বিজ্ঞান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পথ চলতে শুরু করেছে,অথচ প্রাচীন কালে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার গতি ছিলো মন্থর। কিন্তু আধুনিক যুগে এরূপ দ্রুত গতির কারণ কী? তা কি এই যে,লুই পাস্তুর প্রমুখ আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীগণ বোক্বরাত (বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানী),জালিনুস (বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানী),ও ইবনে সীনার ন্যায় প্রাচীন বিজ্ঞানীগণের তুলনায় অধিকতর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন? অন্যকথায়,এর কারণ কি এই যে,আধুনিক বিশ্বে এমন সব অসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে প্রাচীন কালে যে ধরনের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে নি? না,মোটেই তা নয়। হয়তোবা আজকের দিনে এমন একজন লোকও পাওয়া যাবে না যে দাবী করবে যে,পাস্তুর বা অন্যান্য আধুনিক বিজ্ঞানীর প্রতিভা এরিষ্টোটল,প্লোটো,ইবনে সীনা,বোক্বরাত,জালিলুস বা খাজা নাসিরুদ্দীন তুসী’ র তুলনায় বেশী। তবে তা সত্বেও আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাজের ও সাফল্যের গতি অনেক বেশী। এর রহস্য কী?
বলা হয়,এর রহস্য এই যে,বিজ্ঞানীদের কাজের পদ্ধতি সহসাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের গবেষণার পদ্ধতি যখন পরিবর্তিত হয়ে গেলো তখন বিজ্ঞানের অগ্রগতির গতি বেড়ে গেলো। বস্তুতঃ কাজের পদ্ধতি সাফল্যের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এমনটাও হতে পারে যে,আপনি একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান ও সুচতুর কর্মঠ ব্যক্তির হাতে একটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন। কিন্তু তিনি সে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সাফল্যের অধিকারী হলেন না। অতঃপর একই প্রতিষ্ঠানে এমন এক ব্যক্তিকে তার স্থলে নিয়োগ করলেন যিনি স্মরণশক্তি ,সচেতনতা,প্রতিভা ও কোনো কিছু ভালোভাবে বুঝতে পারার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির সমপর্যায়ের নন,কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যক্তি অধিকতর উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করলেন। এর কারণ এই যে,তার কাজের পদ্ধতি অধিকতর উত্তম।
এ প্রসঙ্গে আমরা অধিকতর সুস্পষ্ট উদাহরণ দিতে পারি। আমরা এ ধরনের বহু লোককে দেখেছি যাদের সচেতনতা,মেধা-প্রতিভা ও স্মরণশক্তি অনেক বেশী। কিন্তু শেখার ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের মাত্রা কম। অথচ এমন অনেক লোক শেখার ক্ষেত্রে তাদের তুলনায় অধিকতর সাফল্যের অধিকারী যাদের সচেতনতা,স্মরণশক্তি ও কর্মক্ষমতা প্রথমোক্তদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ের। এর কারণ কী? এর কারণ এই যে,এই দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিদের কাজের পদ্ধতি অধিকতর উত্তম। উদাহরণস্বরূপ,একজন লোক প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী এবং তিনি দিনরাতে ষোল ঘন্টা পরিশ্রম করেন। কিন্তু তার কাজের ধরন কী? তিনি একটি গ্রন্থকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন এবং এরপর সাথে সাথেই তিনি আরেকটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অথচ এই প্রথম গ্রন্থটি এক বিষয়ের এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটি ভিন্ন এক বিষয়ের। এরপর তিনি অন্য একটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং পরে অন্য একটি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি এভাবে এলোমেলো ও বিশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলেন। অন্য দিকে এক ব্যক্তি হয়তো আট ঘন্টার বেশী পড়াশুনা করেন না। কিন্তু তিনি যখন কোনো গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন তখন অত্যন্ত মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেন;তাড়াহুড়া করে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি কোনো পঠণীয় বিষয়কে একবার পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না। তিনি আরো একবার গ্রন্থটিকে অধ্যয়ন করেন। তিনি যে গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছেন তার বিষয়বস্তু তার মস্তিস্কে প্রবেশ না করা পর্যন্তি তিন অন্য কোনো গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন না। তিনি অবশ্য এখানেই থেমে থাকেন না,বরং তিনি এ গ্রন্থে যে সব বিষয় অধ্যয়ন করেছেন তার মধ্যে যে সব বিষয়কে তিনি খুব ভালো জিনিস বলে দেখতে পেয়েছেন ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন সেগুলোকে কাগজের বুকে সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ তিনি তার অর্জিত জ্ঞানকে লিখিত আকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন যার ফলে সারা জীবনে তিনি যখনই প্রয়োজন মনে করবেন তখনই তাতে চোখ বুলালে বিষয়গুলো তার পুরোপুরি স্মরণ হবে। এভাবে তিনি একটি গ্রন্থের অধ্যয়ন ও তা থেকে নোট করার কাজ সমাপ্ত করার পর একই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো বিভিন্ন গ্রন্থ একই নিয়মে অধ্যয়ন করেন। এভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু দিন অধ্যয়ন করার পর তিনি এ বিষয়ে অধিকতর অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুখাপেক্ষিতাহীন হয়ে যান। এরপর তিনি অন্য একটি বিষয়ের ওপরে গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের কাজ শুরু করেন।
এর বিপরীতে যে ব্যক্তি আজ এ গ্রন্থ ,কাল ঐ গ্রন্থ ও পরশু অপর একটি বিষয়ের অধ্যয়ন করেন তিনি হচ্ছেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি খাবার খেতে এসে এখান থেকে এক লোকমা,ওখান থেকে এক লোকমা,অন্য এক ধরনের খাবার থেকে চার লোকমা,চতুর্থ এক ধরনের খাবার থেকে পাঁচ লোকমা ভক্ষণ করে। এভাবে সে তার পাকস্থলীকে ধ্বংসঠিকরে ফেলে। এতে তার কোনো ফায়দাই হয় না। বস্তুতঃ এ বিষয়টি কর্মপদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট ।
এভাবেই সঠিক ও প্রকৃত অর্থে তাবলীগ মানে জনগণের নিকট কোনো বাণী পৌঁছে দেয়া ও তাদেরকে বিষয়টির সাথে পরিচিত করে তোলা। তাদেরকে বাণীটির ব্যাপারে ওয়াকেফহাল করা,এতে বিশ্বাসী করে তোলা,তাদের মধ্যে এর প্রতি আগ্রহ তৈরী করা ও এর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কোনো বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। কারণ,কেবল সঠিক পন্থার অনুসরণ করা হলেই একটি বাণীর প্রচার সফল হওয়া সম্ভব। সঠিক পদ্ধতির বিপরীত পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে যে ইতিবাচক ফল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হবে শুধু তা-ই নয়,বরং তার বিপরীত ফল পাওয়া যাবে। মানুষ যখন কোনো বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং এরপর এ বিষয় সম্পর্কিত কোরআন মজীদের আয়াতের সন্ধান করে এবং এতদসংশ্লিষ্ট আয়াত নিয়ে চিন্তাগবেষণা করে তখন সে দেখতে পায় যে,কোরআন মজীদের আয়াত থেকে এ সংক্রান্ত কী কী বিষয় ( POINTS) পাওয়া যেতে পারে। প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই এ পদ্ধতি প্রযোজ্য ,যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাবলীগ বা প্রচার।
পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোরআন মজীদ যে সব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেاَلْبَلَاغُ الْمُبِينُ (আল-বালাগুল মুবীন ) কথাটির ব্যবহার। অর্থাৎ অত্যন্ত সুক্ষ্ণ ভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বক্তব্যকে পৌঁছে দিতে হবে। এ পরিভাষায় যে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়ার কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? এর লক্ষ্য হচ্ছে বাঞ্চিতভাবে,সহজ-সরলভাবে ও দুর্বোধ্যতা ছাড়াই বাণীটিকে পৌঁছে দিতে হবে যাতে শ্রোতা খুব সহজেই তা বুঝতে পারে।
কঠিন,জটিল ও দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলা,অনেক বেশী পরিভাষা ব্যবহার করা এবং এমন সব বাক্য ব্যবহার করা যা বুঝার জন্য বছরের পর বছর পড়াশুনা করতে হবে-এটা হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর প্রচার পদ্ধতিতে ছিলো না। তিনি এমনই সহজ-সরল ও সুস্পষ্টভাবে তার বক্তব্য তুলে ধরতেন যে,তা বড় বড় পণ্ডিত ও মনীষীগণ যেমন বুঝতে পারতেন তেমনি নিরক্ষর লোকেরাও‘ তাদের অনুধাবন ক্ষমতা অনুযায়ী’ তা সঠিকভাবেই বুঝতে পারতো। (এটা বলছি না যে,সকলে একই মাত্রায় বুঝতে পারতো।)
যে মুবাল্লিগ বা দীন প্রচারক নবী-রাসূলগণের (আঃ) ভাষায় কথা বলতে চান এবং তাদের পথে পথ চলতে চান তার প্রচার অবশ্যই‘ বালাগুল মুবীন’ হতে হবে। এ হচ্ছে‘ মুবীন’ -এর তাৎপর্যের একটি দিক। তবে এখানে আরো কয়েকটি সম্ভাবনাও রয়েছে। (আর সম্ভবতঃ এ সম্ভাবনাগুলোর সবগুলোই সঠিক।) এ সম্ভাবনাগুলোর অন্যতম হচ্ছে‘ মুবীন’ মানে কোনোরূপ রাখঢাক না করে কথা বলা। অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ (আঃ) কঠিন ও জটিল ভাষায় কথা বলতেন না শুধু তা-ই নয়,বরং লোকদের সাথে খোলাখুলি কথা বলতেন ও কোনোরূপ রাখঢাক না করে তাদের কাছে স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। তারা আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলতেন না। তারা যদি মনে করতেন যে,কোনো বিষয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন তাহলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায়ই তা তুলে ধরতেন। যেমন,তারা বলতেনঃ–
) اَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ(
‘‘ তোমরা কি সেই জিনিসের উপাসনা করছো যাকে নিজেরাই তৈরী করেছো?’’ (সূরা আস-সাফ্ফাতঃ ৯৫)
প্রচারের ক্ষেত্রে কোরআন মজীদ দ্বিতীয় যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে কোরআনের নিজের ভাষায় তা হচ্ছেنُصْح (নুছহ)। আমরা সাধারণতঃ‘ নুছহ’ কে‘ কল্যাণ কামনা’ অর্থে অনুবাদ করি। অবশ্য এ অর্থটাও সঠিক। কিন্তু দৃশ্যতঃ‘ কল্যাণ কামনা’ ‘ নুছহ’ -এর আক্ষরিক অর্থ নয়,বরং‘ নুছহ’ শব্দের অর্থটির আবশ্যিক অনুষঙ্গ । দৃশ্যতঃنُصْح (নুছহ) শব্দটিغَشّ (গ্বাশ) শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, আপনি কারো কাছে দুধ বিক্রি করতে চান। হয়তো আপনি তাকে খাঁটি দুধ সরবরাহ করবেন। অথবা,খোদা না করুন,পানি মেশানো দুধ সরবরাহ করবেন। অথবা আপনি কাউকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে চান;এ ক্ষেত্রে হয়তো আপনি তাকে খাঁটি স্বর্ণের মুদ্রা দেবেন (যাতে খাদের পরিমাণ সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্র মাত্রায় থাকে)। অথবা,খোদা না করুন,হয়তো অনেক বেশী খাদ মেশানো (গ্বাশ্যুক্ত ) স্বর্ণের মুদ্রা দেবেন।‘ নুছহ’ হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত‘ নাছেহ’ (নুছহকারী) যে পরিপূর্ণ আন্তরিকতার অধিকারী।‘ তাওবাতুন নাছুহ’ মানে খালেছ তওবা। মুবাল্লিগ ( প্রচারক) কে নাছেহ,খালেছ ও মোখেলছ (একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার অধিকারী) হতে হবে। অর্থাৎ তিনি যখন দীনের দাওয়াত দেবেন তখন তার অন্তরে শ্রোতার কল্যাণ কামনা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যই থাকবে না।
আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের সততার পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা। বলা হয়েছেঃ
اَلنَّاسُ کُلُّهُمْ هَالِکُونَ اِلَّا الْعَالِمُونَ وَ الْعَالِمُونَ هَالِکُونَ اِلَّا الْعَامِلوُنَ وَالْعَامِلُونَ هَالِکُونَ اِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلَی خَطَرٍ عَظِيمٍ.
‘‘ সকল মানুষই ধ্বংসের কবলে নিক্ষিপ্ত একমাত্র আলেমগণ ছাড়া,আলমদের সকলেই ধ্বংসের কবলে নিক্ষিপ্ত একমাত্র আমলকারীগণ ছাড়া,আমলকারীদের সকলেই ধ্বংসের কবলে নিক্ষিপ্ত একমাত্র মোখলেছ (একনিষ্ঠ) গণ ছাড়া,আর মোখলেছগণ বিরাট ঝুকির মধ্যে রয়েছে।’’
বর্ণিত হয়েছে যে,মরহুম আয়াতুল্লাহ বুরুজার্দী (আল্লাহ তার মকামকে উচ্চতর করুন) যখন শেষবারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়েন (যার দু’ একিদন পরে তিনি ইন্তেকাল করেন) তখন যারা তার কাছে ছিলেন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললেনঃ‘‘ আপনার নিজের স্মরণের জন্য এবং অন্যদের নিছহতের জন্য কিছু বলুন।’’ জবাবে তিনি বললেনঃ‘‘ জনাব,গেলাম কিন্তু কিছুই করলাম না,আর স্তুপীকৃত করলাম কিন্তু আল্লাহর কাছে জমা করি নি।’’ উপস্থিত ব্যক্তিদের একজন মনে করলেন যে,তিনি এটা বিনয় বশতঃ বলছেন,তাই তিনি বললেনঃ‘‘ হুজুর,আপনি এ কথা কেন বলছেন?’’ তারপর তিনি বলতে লাগলেন যে,আল– হামদুলিল্লাহ আপনি এই করেছেন,সেই করেছেন,মসিজদ তৈরী করেছেন,মাদ্রাসা তৈরী করেছেন,দ্বীনী জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন ইত্যাদি। তিনি একথা বললে আয়াতুল্লাহ বুরুজার্দী উপস্থিত সকলের দিকে ফিরে নিম্নোক্ত হাদীছটি পাঠ করলেন এবং নীরব হলেনঃ
خَلِّصِ الْعَمَلَ فَاِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ
‘‘ তোমার আমলকে নির্ভেজাল করো, কারণ সমালোচক সেই রকেমর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ঠিক যেমনটি হওয়া উচিৎ।’’ ( মাওয়ায়িযুল আদিদাহ , পৃষ্ঠাঃ ১২৪ )
বস্তুতঃ ইখলাছ (একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা) কোনো ছোটখাটো বিষয় নয়। এ কারণেই কোরআন মজীদে দৃশ্যতঃ সকল নবী-রাসূলের (আঃ) জবানীতেই বলা হয়েছেঃ
) مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ(
‘‘ আমি এর ( দ্বীনের দাওয়াতের) জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোনোরূপ পারিশ্রমিক চাই না।’’ (সূরা সোয়াদঃ ৮৬) অর্থাৎ যেহেতু আমি তোমাদের কল্যাণকামী সেহেতু এ কারণেই তোমাদের নিকট দ্বীনের প্রচার করছি। বস্তুতঃ নাছেহ বা কল্যাণকামীর জন্য পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা (ইখলাছ) থাকা অপরিহার্য।
অন্য একটি বিষয় হচ্ছে মোতাকাল্লেফ (مُتَکَلِّفْ ) না হওয়া।تَکَلُّفْ (তাকাল্লুফ ) শব্দটি (যা থেকেمُتَکَلِّفْ শব্দটি নিস্পন্ন হয়েছে) বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষেتَکَلُّفْ -এর অর্থ নিজের সাথে বাঁধা বা জড়িত করা। অর্থাৎ মানুষ যখন কোনো কিছুকে জোর করে নিজের সাথে বাঁধে তখন সে কাজকেتَکَلُّفْ বলা হয়। এটা কথা বা বক্তব্য সম্পর্কেও ব্যবহার করা হয়। কোনো লোক যখন সহজ-সরল ও গতিশীল তথা প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলার পরিবর্তে কঠিন কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দাবলী ব্যবহার করে তখন তাকে মোতাকাল্লেফ বলা হয়।
হাদীছে আছে,এক ব্যক্তি হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সামনে কথা বলতে গিয়ে কঠিন কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দাবলী ব্যবহার করছিলো। তখন রাসূলে আকরাম (সাঃ) বললেনঃ
اَنَا وَ اَتْقِيَاءُ اُمَّتِی بُرَآءٌ مِنَ التَّکَلُّفِ
‘‘ আমি ও আমার উম্মাতের মধ্যকার মুত্তাকী লোকেরা তাকাল্লুফ থেকে মুক্ত ।’’
মূলতঃ তাকাল্লুফ ও ফাছাহাত (فَصَاحَتْ -প্রঞ্জলতা) সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। প্রকৃতপক্ষে ফাছাহাত মানেই হচ্ছে ভাষার গতিশীলতা-যার দাবী হচ্ছে এই যে,তা কঠিনতা,দুর্বোধ্যতা ও জড়তা থেকে মুক্ত হবে। দ্বীন প্রচার সম্পর্কে কোরআন মজীদে নবী-রাসূলগণ (আঃ)-এর জবানীতে এরশাদ হয়েছেঃ
) مَا اَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّفِينَ(
‘‘ আমি মোতাকাল্লেফদের (যারা কথার ফুলঝুরি ছুটায়) অন্তর্ভুক্ত নই।’’ (সূরা সোয়াদঃ ৮৬)
মুফাসসিরগণের ভাষ্য অনুযায়ী,এ বাকে বাহ্যতঃ এটা বলতে চাওয়া হয় নি যে,আমি কথা বলার ক্ষেত্রে মোতাকাল্লেফ নই। বরং এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে,আমি যা বলছি তার ব্যাপারে মোতাকাল্লেফ নই অর্থাৎ আমি এমন নই যে,যে বিষয়ে জানি না জোর করে সে বিষয়ে জানার ভান করে কথা বলবো। আমার কাছে সুস্পষ্ট নয় এমন কোনো বিষয়ে মানুষের সামনে কথা বলছি না।
উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর-গ্রন্থ‘‘ মাজমা‘ উল বায়ান’’ -এ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ উদ থেকে বর্ণিত হয়েছে,তিনি বলেনঃ
اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ وَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللهُ اَعْلَمُ.
‘‘ হে লোক সকল! যে ব্যক্তি যা জানে সে যেন তা বলে,আর যা জানে না সে ব্যাপারে যেন বলেঃ আল্লাহই অধিকতর অবগত। নিঃসন্দেহে এ-ও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত,যে বিষয়ে জানে না সে বিষয়ে বলবে যে,আল্লাহই অধিকতর অবগত।’’ অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেনঃ
) قُلْ مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّفِينَ(
‘‘ (হে রাসূল!) বলুন,আমি এর ( দ্বীনের দাওয়াতের) জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোনোরূপ পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি মোতাকাল্লেফদের (যারা কথার ফুলঝুরি ছুটায়) অন্তর্ভুক্ত নই।’’ ( মাজমাউল বাইয়্যান , খণ্ড ৮ , পৃষ্ঠা ৪৮৬ )
এ থেকে সুস্পষ্ট যে,হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ উদ مَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ থেকে এ অর্থ গ্রহণ করেন যে,যা জানেন তা লোকেদেরকে বলবেন এবং যা জানেন না তা বলবেন না। বরং বলবেন যে,এ বিষয়ে জানি না।
বিখ্যাত সুবক্তা ইবনে জওযী একবার তিন ধাপ বিশিষ্ট একটি মিম্বারে বসা ছিলেন। এ সময় একজন মহিলা এসে তাকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। ইবনে জওযী জবাবে বললেনঃ‘‘ আমি জানি না।’’ মহিলা বললেনঃ‘‘ তুমি যখন জানো না তখন তিন ধাপ উপরে উঠেছো কেন?’’ জবাবে তিনি বললেনঃ‘‘ এই তিন ধাপ উপরে উঠেছি সেই সব বিষয়ে বলার জন্য যেগুলো আমি জানি কিন্তু আপনি জানেন না। আর যে সব বিষয়ে আমি জানি না সেগুলোর জন্য যদি মিম্বার তৈরী করা হতো তাহলে তা চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছে যেতো।’’
শেখ আনছারী ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের অন্যতম। তিনি একদিকে যেমন ফিকাহ ও উছুলের ক্ষেত্রে প্রকৃতই একজন মোহাক্কেক (গবেষক) ও প্রথম শ্রেণীর আলেম ছিলেন,তেমনি ছিলেন তাকওয়ার অধিকারী। এ কারণে অনেকে তার সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে কিছুটা অতিশয়োক্তি করে ফেলতেন। যেমন,বলা হতোঃ হুজুরের কাছে যা কিছুই জিজ্ঞেস করো না কেন,তা-ই তার জানা আছে;এটা অসম্ভব যে,কোনো বিষয়ে তিনি জানবেন না। (তিনি ছিলেন শুশ্তারের অধিবাসী। কথিত আছে যে,তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খুযেস্থানের আঞ্চলিক উচ্চারণে কথা বলতেন।) তাকে যে সব শারয়ী বিষয়ে প্রশ্ন করা হতো তিনি মুজতাহিদ হওয়া সত্বেও কোনো কোনো সময় তার কোনো বিষয় তার মনে থাকতো না। যখনই কোনো প্রশ্নের উত্তর তার মনে না থাকতো তখন তিনি অত্যন্ত জোরে বলতেনঃ‘‘ জানি না।’’ এর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে,শ্রোতাগণ ও তার শিষ্যগণ যাতে বুঝতে পারেন যে,কোনো বিষয়ে জানা না থাকলে তা স্বীকার করার মধ্যে লজ্জার কোনো কারণ নেই। অন্য দিকে তাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হতো সে সম্পর্কে জানা থাকলে তিনি আস্তে জবাব দিতেন এবং তার কন্ঠস্বর কেবল ততটুকু উচু হতো যাতে প্রশ্নকর্তা বুঝতে পারে। কিন্তু জানা না থাকলে জোরে জোরে বলতেনঃ‘‘ জানি না,জানি না,জানি না।’’
কোরআন মজীদ নবী-রাসূলগণ (আঃ)-এর প্রচারের পদ্ধতি সম্পর্কে অপর যে বিষয়টি উল্লেখ করেছে তা হচ্ছে বিনয় (যা অহঙ্কারের বিপরীত)। যে ব্যক্তি লোকদের কাছে কোনো বাণী পৌঁছাতে চান,বিশেষ করে মহান আল্লাহ বাণী পৌঁছাতে চান তার অবশ্যই পুরোপুরি বিনয়ী হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ তার জন্যে আমিত্বের অহঙ্কার বর্জন করা এবং লোকেদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। তাকে বিনয়ের মূর্ত প্রতীক হতে হবে। কোরআন মজীদে হযরত (আঃ)-এর জবানীতে তার কওমের একদল লোককে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ .
) اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ ( .
‘‘ এটা কি তোমাদেরকে বিস্মিত করছে যে,তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির ওপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যিকর (আল্লাহর বাণী) এসেছে?’’ ( সূরা আ ’ রাফঃ ৬১ )
উপরোক্ত আয়াতে‘‘ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে’’ (مِنْ رَبِّکُمْ ) কথাটির ব্যবহার বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । এ কথাটির ব্যবহার থেকে সুস্পষ্ট যে,হযরত (আঃ)‘‘ আমার প্রতিপালক’’ বলতে চান নি। কারণ,এরূপ বললে তার মধ্যে এমন এক ভাব প্রকাশ পেতো যে,তিনি তার প্রতিপালকের দিকে অন্যদেরকে আহবান করছেন। অন্য কথায়,তারা এমন তুচ্ছ লোক যে‘‘ প্রতিপালক’’ কে‘‘ তোমাদের প্রতিপালক’’ বলা চলে না। এরপর তিনি বলেন‘‘ তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির ওপর’’ عَلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ অর্থাৎ আমি নিজেও তোমাদেরই একজন।
আপনারা লক্ষ্য করুন এ আয়াতে একজন নবীর কতখানি বিনয়ের পরিচয় রয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) কে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ
) قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ يوُحَی اِلَیَّ(
‘‘ (হে রাসূল!) বলুন,অবশ্যই আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ,তবে আমার ওপর ওহী নাযিল হয়।’’ অর্থাৎ তোমাদের মতো একজন মানুষের ওপরই এ ওহী নাযিল হয়েছে। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ
) أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (
‘‘ অবশ্যই তোমোদের ইলাহ একজন মাত্র ইলাহ । অতএব,যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে যেন উত্তম কর্ম সম্পাদন করে এবং স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।’’ ( সূরা কাহাফঃ ১১০ )
দীন প্রচারের সাথে সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় হচ্ছে বন্ধু সুলভ ও নম্র আচরণ করা এবং রূঢ়তা পরিহার করা। যে ব্যক্তি মানুষের কাছে কোনো বাণী পৌঁছাতে চায়,বিশেষ করে যে মহান আল্লাহর বাণী পৌঁছাতে চায় এবং কামনা করে যে,তারা তা পছন্দ করুক ও এর ওপর ঈমান আনুক,তাকে অবশ্যই নম্র ভাষী হতে হবে এবং নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে।
বস্তুতঃ বস্তুগত সামগ্রীর ন্যায় কথাও নরম ও শক্ত হতে পারে। কোনো কোনো সময় মানুষ কোনো বক্তব্য সহজভাবেই গ্রহণ করে ঠিক যেভাবে কোনো কোনো খাদ্যদ্রব্য সহজেই গলাধঃকরণ করতে পারে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ একটি বক্তব্য গ্রহণ করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়;এটা যেন কোনো কাঁটাযুক্ত বস্তু গলাধঃকরণের ন্যায়। কথা যদি খুবই কর্কশ হয় বা তাতে যদি বহু রকমের আকার-ইঙ্গিত থাকে তাহলে লোকদের পক্ষে তা গ্রহণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।
মহান আল্লাহ যখন হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আঃ) কে ফেরাউনের নিকট পাঠালেন তখন তাদেরকে যেসব নির্দেশ দান করেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলো দাওয়াতের পদ্ধতি। মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ
) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (
‘‘ আর তার সাথে নরমভাবে কথা বলো,হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।’’ (সূরা তা হাঃ ৪৪) অর্থাৎ যদিও ফেরাউন সার্বিক অর্থেই একজন উদ্ধত অহঙ্কারী লোক তথাপি তার সামনেও এবং এ ধরনের যে কোনো লোকের সামনেই নম্রভাবে কথা বলতে হবে এবং নম্র ভাষায় আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে হবে। কারণ,এমনও হতে পারে যে,সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তার প্রতিপালককে ভয় করবে। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আঃ) ফেরাউনের নিকট সেভাবেই নম্রতার সাথে দাওয়াত পেশ করেন,কিন্তু ফেরাউন সে দাওয়াত গ্রহণ করার মতো লোক ছিলো না।
মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) কে সম্বোধন করে এরশাদ করেনঃ
) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ(
‘‘ আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি তাদের প্রতি নম্র । আর আপনি যদি তাদের প্রতি কঠোরহৃদয় হতেন তাহলে অবশ্যই তারা আপনার চারদিক থেকে দূরে সরে যেতো। অতএব,আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও তাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমার আবেদন করুন। আর (সামষ্টিক) কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন,অতঃপর যখন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন;নিঃসন্দেহে আল্লাহ (তার ওপর) ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।’’ (সূরা আল ইমরানঃ ১৫৯)
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকদের সাথে নম্র আচরণ করতেন এবং তাদের সাথে নম্র ভাবে কথা বলতেন। তার আচরণ ও কথা উভয়ই ছিলো নম্র এবং উভয় ক্ষেত্রেই তিনি রূঢ়তা পরিহার করে চলতেন। তার কথা বলার ধরন সম্পর্কে অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে,তিনি কীভাবে কথা বলার ক্ষেত্রে রূঢ়তা পরিহার করে চলতেন। কথা ও আচরণে এ নম্রতার গুরুত্ব এতই বেশী যে কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমগ্র কোরআন মজীদের বাহক,এত সব মু‘ জিযা ও অন্য সকল গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা‘ আলা বলছেন যে,আপনি নম্রতার অধিকারী না হলে ও কঠোর হৃদয় হলে লোকেরা আপনার চারদিক থেকে সরে যেতো;বস্তুতঃ আপনার নম্রতা দীনের প্রচার ও লোকদের হেদায়াত লাভের ক্ষেত্রে-তাদের আল্লাহর পরিচয় লাভ ও ঈমান আনয়নে বিরাট প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
শেখ সা‘ দী বলেনঃ
درشتی و نرمی بهم در به است |
چو رَگزن که جرّاح و مرهم نه است |
‘‘ কঠোরতা ও নম্রতার একত্র সমাবেশই উত্তম
শিঙ্গা লাগাতে যখম করে যে মলমও লাগায় সে।’’
অবশ্য এখানে আমরা কঠোরতা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই না। এ দ্বিপদীটি এ কারণে উদ্ধৃত করেছি যে,এ আমাদের উদ্দেশ্যের কাছাকাছি। নম্রতার সাথে কঠোরতা থাকারও কি প্রয়োজন নেই? বস্তুতঃ রূঢ়তা ও সহিংসতা এবং কঠোরতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ঝর্ণাধারার তলেদেশে যেসব নুড়ি পাথর পড়ে আছে তার ওপর দিয়ে বছরের পর বছর প্রচুর পানি প্রবাহিত হয়ে গেছে এবং এগুলোকে ক্ষয় করে ফেলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যখন ঝর্ণার তলদেশ থেকে এরূপ নুড়ি পাথর হাতে তুলে নেয় সে দেখতে পায় যে,সেগুলো আগের মতোই শক্তও কঠিন,কিন্তু মসৃণ-যা ধরলে মানুষের হাতে সামান্যতম কষ্টও অনুভূত হয় না। শুধু তা-ই নয়,বরং মনে হবে যে,নিজের গায়ের জামার ওপরে হাত বুলালে যত কর্কশতা অনুভূত হয় এসব নুড়ি পাথরের ওপর হাত বুলালে তত কর্কশতাও অনুভব করে না। যে তলোয়ারকে রেত দিয়ে অনেক বেশী ঘষা হয়েছে তাতেও এক ধরনের নম্রতা ও মসৃণতা আছে,এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এরূপ তলোয়ারকে স্পিং-এর ন্যায় বাঁকা করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা কঠিন বটে কঠোরতার অধিকারী হওয়া,দৃঢ়তার অধিকারী হওয়া,বীরত্বের অধিকারী হওয়া ও আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করা কর্কশতা ও সহিংসতা থেকে ভিন্ন বিষয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিকে যেমন লোকদের সাথে আচরণ ও কথা বলার ক্ষেত্রে বিনয় ও নম্রতার অধিকারী ছিলেন,অন্য দিকে স্বীয় পথের ব্যাপারে ছিলেন আপোসহীন। তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই ভয় করতেন না।
দীন প্রচারকের আরেকটি গুণ হচ্ছে সাহসিকতা। দীন প্রচারকদের এ গুণ সম্পর্কে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছেঃ
) اَلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَداً اِلَّا الله( .
‘‘ যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয় ও তাকে ভয় করে এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকেই ভয় করে না।’’ (সূরা আহযাবঃ ৩৯) বস্তুতঃ তারা আল্লাহকে ভয় করেন বলেই তার বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র এদিক-সেদিক করেন না এবং তাতে কোনোরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করেন না,সত্য পথ থেকে বঞ্চিত হন না। কিন্তু দীন প্রচারকের একটি গুণ যে,
) لَا يَخْشَوْنَ اَحَداً اِلَّا الله(
(আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকেই ভয় করে না।)-এ বৈশিষ্ট্য এখন খুব কম লোকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।
নবী-রাসূলগণ (আঃ) কর্তৃক দীন প্রচারের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে,তারা বলতেনঃ দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের ওপর আর কোনো দায়িত্ব নেই। তারা বলতেনঃ আমরা আল্লাহর বান্দা,আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর বাণীর বাহক। যাজকরা যেমনটি করতেন-এবং সম্ভবতঃ এখনো করেন-নবী-রাসূলগণ (আঃ) সেভাবে লোকেদেরকে সরাসরি বেহেশত বা দোযখের সার্টিফিকেট দেয়ার জন্য আগমন করেন নি। তারা এ ধরনের সনদ দান করতেন না যদিও তাদের নবী-রাসূল হওয়ার ব্যাপারে তাদের নিজেদের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিলো না। বরং তারা সাধারণভাবে বিষয়াদি তুলে ধরতেন। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করতো যে,আমার শেষ পরিণতি কেমন হবে? তাহলে তারা জবাব দিতেনঃ আল্লাহ জানেন। গুপ্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেও তারা বলতেনঃ আল্লাহ জানেন;তোমার শেষ পরিণতি কী হবে স্বয়ং আল্লাহ তা‘ আলাই ভালো জানেন।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবী ওসমান বিন মায‘ উন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে,রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরেতর পর পরই তিনিও হিজরত করেন। তিনি ছিলেন মদীনায় ইন্তেকালকারী প্রথম মুহাজির। তার ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জান্নাতুল বাকী‘ তে দাফন করার জন্য নির্দেশ দেন এবং সেদিন থেকেই জান্নাতুল বাকী‘ গোরস্থানে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসমান বি মায‘ উনকে খুবই ভালোবাসতেন এবং সকলেরই তা জানা ছিলো।
আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ)‘‘ নাহজুল বালাগ্বা’’ য় এরশাদ করেনঃ
کَانَ لِی فَبِمَا مَضَی اَخٌ فِی اللهِ، وَ کَانَ يُعَظِّمُهُ فِی عَيْنِی صِغَرُ الدُّنْيَا فِی عَيْنِهِ.
‘‘ অতীতে আমার একজন দীনী ভাই ছিলো আর যে জিনিস তাকে আমার চোখে মহান করে তুলে ধরে তা হচ্ছে ,তার চোখে এ দুনিয়াটা ছিলো খুবই তুচ্ছ।’’ ( নাহজুল বালাগা , হিকমাতঃ ২৮১ , পৃষ্ঠাঃ ১২২৫ )
‘‘ নাহজুল বালাগ্বা’’ র ভাষ্যকারগণ বলেছেন,এখানে হযরত আমীরুল মু’ মিনীন তার দীনী ভাই বলতে ওসমান বি মায‘ উনকে বুঝিয়েছেন। হযরত আমীরুল মু’ মিনীনের পুত্রদের একজনের নাম ওসমান। তার নামকরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,তিনি জন্ম গ্রহণ করলে হযরত আমীরুল মু’ মিনীন বলেনঃ আমি আমার ভাই ওসমান বি মায‘ উ-এর নামে তার নামকরণ করবো। এভাবে তিনি ওসমান বি মায‘ উ-এর স্মৃতিকে সদাজাগ্রত রাখতে চান।
এরূপ একজন ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। তিনি তখন একজন আনসারের গৃহে জীবন যাপন করতেন। সে গৃহে একজন মহিলা ছিলেন যিনি তার খেদমত করতেন যার নাম ছিলো উম্মে‘ আলা;সম্ভবতঃ তিনি তার আনসার ভাইয়ের স্ত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসমান বি মায‘ উ-এর নামাযে জানাযা পড়ার জন্য এলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সেই সব কাজ করেন যা তিনি তার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের বেলায় করতেন। সহসা উম্মে‘ আলা ওসমান বি মায‘ উন-এর লাশের দিকে মুখ করে বললেনঃ هَنِيّاً لَکَ الْجَنَّةُ ’‘ বেহেশত তোমার জন্য উপভোগ্য হোক।’’ তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে‘ আলার দিকে ফিরে কঠোর কণ্ঠে বললেনঃ‘‘ কে তোমার নিকট এহেন অঙ্গীকার করেছে?’’ উম্মে‘ আলা বললেনঃ‘‘ হে আল্লাহর রাসূল! তিনি আপনার সাহাবী। যেহেতু আপনি তাকে এত ভালোবাসতেন এ কারণে আমি এ কথা বলেছি।’’ তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ
) قُلْ مَا کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ مَا اَدْرِی مَا يُفْعَلُ بِی وَ لَا بِکُمْ(
‘‘ (হে রাসূল!) বলে দিন,আমি নতুন ধরনের কোনো রসূল নই;আমি জানি না আমার সাথে ও তোমাদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হবে।’’ (সূরা আহকাফঃ৯) এর তাৎপর্য অত্যন্ত সুগভীর। অনুরূপভাবে সূরা আল-জিন-এর শেষ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ
) قُلْ اِنِّی لَا اَمْلِکُ لَکُمْ ضَرّاً وَ لَا رَشَداً. قُلْ اِنِّی لَنْ يُجِيرَنِی مِنَ اللهِ اَحَدٌ وَ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً ( .
‘‘ (হে রাসূল!) বলে দিন,তোমাদের ক্ষতি করার বা কল্যাণ করার কোনো ক্ষমতাই আমার নেই। বলে দিন,আল্লাহর মোকাবিলায় কেউই আমাকে আশ্রয় দান করতে সক্ষম হবে না এবং আমি তার নিকটে ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয়স্থল পাবো না।’’ ( সূরা জিনঃ ২১ - ২২ )
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রচার পদ্ধতির আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লোকদের অবস্থার পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা। জাহেলিয়াতের যুগে আরব জনগণের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের শ্রেণীপ্রথা বিদ্যমান ছিলো। তখন এমনকি দরিদ্রদেরকেও মানুষ বলে গণ্য করা হতো না,দাস-দাসীদের মানুষ গণ্য করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তৎকালীন অভিজাত লোকেরা-কোরআন মজীদে যাদেরকে মালা’ (مَلأ ) বলা হয়েছে,তারা নিজেদেরকে সব কিছুর মালিক-মোখতার ও অধিকারী বলে মনে করতো এবং যাদের কিছুই ছিলো না তাদের কিছু পাবার অধিকার আছে বলে মনে করতো না। শুধু তা-ই নয়,তারা এটা মনে করতো না এবং স্বীকার করতো না যে,তারা এ দুনিয়ার বুকে সব কিছুর অধিকারী হলেও এবং অন্যরা কিছুরই অধিকারী না হলেও পরকালীন জীবনে হয়তো এর বিপরীত অবস্থা হতে পারে। বরং তারা বলতো যে,দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের অবস্থার নিদর্শন;যেহেতু দুনিয়ার জীবনে আমরা সব কিছুর অধিকারী,সেহেতু তা এটাই প্রমাণ করে যে,আমরা আল্লাহ তা‘ আলার প্রিয়;আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসেন এবং এ কারণেই আমাদেরকে সব কিছু দিয়েছেন। অতএব,আখরাতের অবস্থাও এমনই হবে;তোমরাও আখরাতে এ রকম অবস্থারই সম্মুখীন হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে হতভাগ্য সে পরকালীন জীবনেও হতভাগ্য ।
আরবের অভিজাত লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতোঃ তোমার কাজে ত্রুটি কোথায় জানো? তুমি জানো,কেন আমরা তোমার রিসালাতের দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত নই? এর কারণ হলো এই যে,তুমি নীচ স্তরের ও ইতর শ্রেণীর লোকেদেরকে তোমার চারদিকে জমায়েত করেছো। এদেরকে দূরে সরিয়ে দাও,তখন আমরা অভিজাত লোকেরা তোমার কাছে চলে আসবো। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সম্বোধন করে এরশাদ করেনঃ হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলে দিন,
) وَ مَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنيِنَ( .
‘‘ আমি মু’ মিনদেরকে বিতাড়নকারী নই।’’ (সূরা শুআরাঃ ১১৪) অর্থাৎ আমি এমন লোক নই যে,এই লোকেরা আমার ওপর ঈমান আনা সত্ত্বেও কেবল দরিদ্র ও ক্রীতদাস হওয়ার কারণে আমি তাদেরকে আমার কাছ থেকে বিতাড়িত করবো। আল্লাহ তা‘ আলা অন্য এক আয়াতেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ করেনঃ .
) وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَ الْعَشِیِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.(
‘‘ (হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবেন না যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় সকাল-বিকাল তাকে ডাকে।’’ (সূরা আনআমঃ ৫২) অর্থাৎ এতে অভিজাত লোকেরা যদি আপনার কাছ থেকে সরে যায় তো যাক;ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে অবশ্যই তাদের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে এবং মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করতে হবে।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রবর্তিত এবং তার নিজের জীবনে আচরিত একটি নিয়ম ছিলো এই যে,প্রথমতঃ তার মজলিসে বসার ক্ষেত্রে মর্যাদাগত উুঁচু-নীচু অবস্থার অস্তিত্ব ছিলো না;সাধারণতঃ তার মজলিসে আগমনকারীরা গোল হয়ে বসতেন। ফলে মর্যাদাগত উঁচু-নীচু অবস্থার সৃষ্টি হতো না। দ্বিতীয়তঃ তিনি মজলিসে প্রবেশ করলে লোকেদেরকে তার সম্মানার্থে দাঁড়াতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন যে,এটা আ‘ জামীদের অর্থাৎ অনারবদের রীতি। তিনি আরো বলতেনঃ যে ব্যক্তি যখনই মজলিসে প্রবেশ করবে সে যে জায়গাই খালি পাবে সেখানেই বসে পড়বে;লোকেরা যেন কাউকে সম্মানজনক জায়গায় তথা মর্যাদাগত বিচারে উচ্চতর বিবেচিত স্থানে,যেমনঃ সামনে,বসতে দেয়ার জন্যে তাদের জায়গা থেকে সরে বসতে বাধ্য না হয়। কারণ,এটা ইসলামের রীতি নয়।
একবার ইসলাম গ্রহণকারী একজন অভিজাত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিসে বসে ছিলেন। এ সময় জীর্ণবাস পরিহিত একজন গরীব লোক মজলিসে প্রবেশ করলেন এবং উক্ত অভিজাত ব্যক্তির পাশে খালি জায়গা পেয়ে সেখানে বসে পড়লেন। দরিদ্র ব্যক্তি সেখানে বসে পড়ার সাথে সাথেই অভিজাত ব্যক্তি জাহেলিয়াত যুগের অভ্যাস অনুযায়ী নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে তার কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে বসলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘটনাটি লক্ষ্য করলেন;তিনি অভিজাত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তুমি এরূপ করলে কেন? তুমি কি এ ভয়ে সরে গেলে যে,তোমার ধনসম্পদ থেকে কিছুটা তার গায়ে লেগে যাবে? অভিজাত ব্যক্তি জবাব দিলেনঃ না,হে আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তুমি কি এ ভয় করেছো যে,তার দারিদ্রের কিছুটা তোমার গায়ে লেগে যাবে? অভিজাত ব্যক্তি বললেনঃ না,হে আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তাহলে তুমি এমন করলে কেন? তখন অভিজাত ব্যক্তি বললেনঃ আমি ভুল করেছি;অন্যায় করেছি। এ ধরনের অন্যায়ের শাস্তি স্বরূপ আমি আপনার এই মজলিসেই আমার সমস্ত ধন সম্পদের অর্ধেক আমার এই মুসলমান ভাইকে দান করলাম। তখন উপস্থিত লোকেরা তার দরিদ্র মু’ মিন ভাইকে বললেনঃ এবার তোমার সম্পদ নিয়ে নাও। জবাবে দরিদ্র ব্যক্তি বললেনঃ না,নেবো না। উপস্থিত লোকেরা বললেনঃ তোমার তো ধন সম্পদ নেই,তাহলে নেবে না কেন?
তিনি বললেনঃ ভয় করছি যে,তা গ্রহণ করলে একদিন হয়তো এই ব্যক্তির ন্যায় অহঙ্কারী হয়ে পড়বো।
দীন প্রচারের পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় হচ্ছে ধৈর্য-স্থৈর্য ও দৃঢ়তা। মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ
) فَاصْبِرْلِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ( .
‘‘ অতএব,(হে রাসূল!) আপনি আপনার প্রতিপালকের ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করুন এবং সেই মাছওয়ালার (ইউনুসের) ন্যায় হবেন না।’’ (সূরা নূন ওয়াল কালামঃ ৪৮) আল্লাহ তা‘ আলা আরো এরশাদ করেন :
) فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُسُلِ.(
‘‘ অতএব,(হে রাসূল!) আপনি দৃঢ়তার অধিকারী রাসূলগণের ন্যায় ধৈর্য ধারণ করুন।’’ ( সূরা আহকাফঃ ৩৫ ) আরো এরশাদ হয়েছেঃ
) فَاسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ( .
‘‘ অতএব,(হে রাসূল!) আপনাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে অবিচল থাকুন।’’ ( সূরা হূদঃ ১১২ ) . فَاسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ . কথাটি দুটি সূরায় এসেছেঃ সূরা আশ্-শূরায় এবং সূরা-হূদে কথাটি এভাবে এসেছেঃ
) فَاسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَکَ(
‘‘ অতএব,(হে রাসূল!) আপনাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে আপনি নিজে এবং আপনার সঙ্গী-সাথী তাওবাকারীগণ অবিচল থাকুন।’’ ( সূরা হূদঃ ১১২ ) আর সূরা আশ-শূরায় কেবল হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) কে উদ্দেশ্য করে এ আদেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,তিনি এরশাদ করেছেনঃ
شَيَّبَتْنِی سُورَةُ هُودٍ
‘‘ সূরা হূদ আমার দাড়িকে সাদা করে দিয়েছে।( মাজমাউল বায়ান , খণ্ড ৫ , পৃষ্ঠা ১৪০ ) যেখানে বলা হয়েছেঃ
) فَاسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ(
‘‘ অতএব,(হে রাসূল!) আপনাকে যেভাবে আদশ দেয়া হয়েছে সেভাবে আপনি নিজে এবং আপনার সঙ্গী-সাথী তাওবাকারীগণ অবিচল থাকুন।’’ তবে কেবল আমাকেই বলা হয়নি,বরং স্বয়ং আমার ও অন্যদের কথা বলা হয়েছে;বলা হয়েছেঃ তাদেরকেও অবিচল রাখো।’’
এবার আমরা হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) প্রসঙ্গে ফিরে যাবো এবং তার প্রচার পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি দেবো।
আবু আব্দুল্লাহ হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) তার আন্দোলন ও সংগ্রামে এমন কতগুলো কাজ করেন যেগুলোকে কর্মপদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা চলে। এ ব্যাপারে পরবর্তিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে আমরা রণাঙ্গনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করবো। অবশ্য এটা একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে যে,মহররমের নবম দিবস (তাসূ‘ আ) উপলক্ষে হযরত আবুল ফজল আব্বাস (সালামুল্লাহি আলাইহ)কে স্মরণ করা হয়।
হযরত আবুল ফাজল আব্বাস-এর মর্যাদা অত্যন্ত। আমাদের নিস্পাপ ইমামগণ বলেছেনঃ
. اِنَّ لِلْعَبَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَغْبَطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ.
‘‘ অবশ্যই আল্লাহর নিকট আব্বাসের মর্যাদা এমন যে,সমস্ত শহীদ তাতে গর্ব করবে।’’ ( আবসারুল আইন ফি আনসারিল হোসাইন , পৃষ্ঠাঃ ২৭ ; বিহারুল আনোয়ার , খণ্ড ৪৪ , পৃষ্ঠা ২৯ ; আমালী সাদুক , মজিলসঃ ৭০ , নম্বরঃ ১০ ) দুঃখের বিষয় এই যে,ইতিহাস এ মহান শহীদ সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করে নি। অর্থাৎ কেউ যদি তার জীবন কাহিনী সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করতে চায় তাহলে তিনি যথেষ্ট তথ্য খুজে পাবেন না। কিন্তু অনেক বেশী তথ্যের প্রয়োজন কী? ক্ষেত্রবিশেষে একজন মানুষের জীবনের একটি দিন বা দু’ টি দিন বা পাঁচ দিনের ঘটনাবলী-যার পূর্ণ বিবরণ হয়তো পাঁচ পৃষ্ঠার বেশী হবে না,এমনই প্রোজ্জ্বল হতে পারে যে,যা সেই ব্যক্তির এমন মর্যাদার পরিচায়ক যার গুরুত্ব কয়েক ডজন খণ্ড সম্বলিত জীবনী গ্রন্থের চেয়ে অনেক বেশী। আর হযরত আবুল ফজল আব্বাস ছিলেন এ ধরনেরই একজন ব্যক্তি ।
কারবালার ঘটনার সময় আবুল ফজল আব্বাসের বয়স ছিলো প্রায় ৪৫ বছরের মতো। তিনি ছিলেন কয়েক জন সন্তানের পিতা;এদের মধ্যে একজন ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আলী ইবনে আবি তালেব যিনি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে,একিদন হযরত ইমাম যায়নুল আবদীন (আঃ) তাকে দেখলেন;তখন কারবালার ঘটনাবলী তার মনে পড়ে গেলো এবং ইমামের’ চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এলো। .
আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ)-এর শাহাদাতের সময় আবুল ফজল আব্বাস ছিলেন চৌদ্দ বছরের কিশোর।‘‘ নাসেখুত তাওয়ারীখ’’ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে,আবুল ফজল আব্বাস সিফফীনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তখন তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোর ছিলেন (মোটামুটি বারো বছরের ছিলেন,কারণ,আমীরুল মু’ মিনীনের শাহাদাতের প্রায় তিন বছর আগে সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়),সেহেতু আমীরুল মু’ মিনীন তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি দেন নি। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে,সিফফীনের যুদ্ধের সময় যদিও তিনি বালক মাত্র ছিলেন তথাপি তিনি এক কালো রঙ্গের ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছিলেন। এর বেশী কিছু জানা যায় না। তবে এ বিষয়টি অনেকেই লিখেছেন। যুদ্ধ বিষয়ক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতে লিখিত আছে যে,আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ) এক সময় তার ভাই‘ আক্বীলকে বলেনঃ‘‘ আমার জন্য এমন একজন স্ত্রী নির্বাচন করে দাও যে বীর বংশধর জন্ম দেবে।’’ ‘ আক্বীল ছিলেন নসবনামা (বংশধারা শাস্ত্রীয়) বিশেষজ্ঞ । আর এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিস্ময়কর দক্ষতার অধিকারী। তিনি লোকদের গোত্র পরিচয় ও পিতা-মাতা সম্বন্ধে এবং কখন কোথায় সংশ্লিষ্ট গোত্রের উদ্ভব ঘটে সে সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত ছিলেন। তাই আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ) স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে তার সহায়তা চাইলে সাথে সাথেই তিনি বলেনঃ
. عنَیِّ لَکَ بِاُمِّ الْبَنِينَ بِنْتِ خَالِدٍ
‘‘ আমি তোমার জন্য উম্মুল বানীন বিনতে খালেদ-এর প্রস্তাব দিচ্ছি ।’’
উল্লেখ্য ,‘‘ উম্মুল বানীন’’ মানে‘ কয়েক জন পুত্রের জননী’ । তবে এটা‘‘ উম্মে কুলসুম’’ -এরই অনুরূপ;বর্তমানে আমরা এর দ্বারা নাম রেখে থাকি। ইতিহাসে আছে যে,উম্মুল বানীন-এর পূর্ববর্তী বংশধারায় তার পরদাদী বা আরো পূর্ববর্তী কারো নাম ছিলো উম্মুল বানীন;হয়তো তার কথা স্মরণ করেই এর নাম উম্মুল বানীন রাখা হয়েছিলো।
যা-ই হোক,আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ) উম্মুল বানীনকে বিবাহ করেন এবং তার গর্ভে চারজন পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করে। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে মনে হয় যে,তিনি কোনো কন্যা সন্তান জন্ম দেননি। এভাবে তিনি শুধু নামে নয়,কার্যতঃও উম্মুল বানীন বা কয়েক জন পুত্র সন্তানের মাতা হিসেবে প্রমাণিত হন।
আমীরুল মু’ মিনীন হযরত আলী (আঃ) আরো কয়েক জন বীর সন্তানের অধিকারী ছিলেন। প্রথমতঃ স্বয়ং হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) উভয়ই ছিলেন বীরপুরুষ। বিশেষ করে হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) যে কত বড় সাহসী ছিলেন কারবালায় তিনি তার প্রমাণ রাখেন। প্রমাণিত হয় যে,তিনি তার পিতার সাহসিকতা ও বীরত্ব উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছেন। দ্বিতীয় আমীরুল মু’ মিনীনের আরেক পুত্র মুহাম্মাদ বিন হানাফীয়াও বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি আবুল ফজলের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। তিনি জঙ্গে জামালে (উটের যুদ্ধে ) অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বীরত্বের অধিকারী,খুবই শক্তিশালী ও শৌর্যের অধিকারী। বলা হয় যে,আমীরুল মু’ মিনীন (আঃ) তাকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন।
সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী কারবালার রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিবার থেকে সর্ব প্রথম যিনি শাহাদাত বরণ করেন তিনি হলেন হযরত আলী আকবর,আর হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতের পূর্বে সর্বশেষ যিনি শাহাদাত বরণ করেন তিনি হলেন হযরত আবুল ফজল আব্বাস। অর্থাৎ আবুল ফজল যখন শহীদ হন অতঃপর হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর পুরুষ সঙ্গীসাথী ও অনুসারীদের মধ্যে একমাত্র তার অসুস্থ পুত্র হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) ছাড়া আর কেউ বেঁচে ছিলেন না।
বর্ণিত হয়েছে,আবুল ফজল আব্বাস রণাঙ্গনে যাবার আগে এ জন্য হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর নিকট অনুমতি চাইতে আসনে এবং বলেনঃ‘‘ প্রিয় ভাইজান! আমাকে রণাঙ্গনে যাবার অনুমতি দিন। আমি বেঁচে থাকাতে খুবই অশান্তি বোধ করছি।’’
আবুল ফজল আব্বাস নিজে রণাঙ্গনে যাবার আগে তার তিন সহোদর ভাইকে (যাদের সকলেই বয়সে তার চেয়ে ছোট ছিলেন) রণাঙ্গনে পাঠান। তিনি তাদেরকে বলেনঃ‘‘ ভাইেয়রা! তোমারা যাও;আমি আমার ভাইদের বিপদের (শাহাদাতের) বিনিময়ে পুরস্কার পেতে চাই।’’ তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন যে,তার তিন সহোদর ভাই তার আগেই শহীদ হয়েছেন এবং তিনি মনস্থ করেছিলেন যে,এরপরই তিনি তাদের সাথে যুক্ত হবেন।
এই হলো উম্মুল বানীন ও তার চার পুত্রের ঘটনা। তবে আশূরার সময় উম্মুল বানীন কারবালায় ছিলেন না। তিনি তখন মদীনায় ছিলেন। যারা মদীনায় ছিলেন তারা কারবালার ঘটনার কোনো খবরই রাখতেন না। চারটি পুত্র সন্তানের জননী এই মহিলার গোটা জীবন বলতে তার এই পুত্রগণই ছিলেন। তার নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে,তার চার সন্তানই কারবালায় শহীদ হয়েছেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন একজন পূণ্যবতী মহিলা। তিনি ছিলেন একজন বিধবা,যার একমাত্র সম্বল ছিলো তার এই পুত্রগণ,কিন্তু তাদের সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন। তিনি অনেক সময় মদীনা থেকে কুফা অভিমুখী পথের পাশে বসে তার সন্তানদের স্মরণে শোকগাঁথা গাইতেন।
ইতিহাসে লেখা হয়েছে যে,এই মহিলা স্বয়ং ছিলেন বনি উমাইয়্যার প্রশাসনের বিরুদ্ধে এক বিলষ্ঠ প্রচার। যে কেউ ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করতো সে-ই থমকে থেমে যেতো এবং তার শোকগাঁথা শুনে অশ্রু বিসর্জন করতো। এমন কি আহলে বাইতের ঘোরতর দুশমনদের অন্যতম মারওয়ান ইবনে হাকাম যখন মদীনার আমীর (গভর্ণর) ছিলো,সে যখনই ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করতো তখন উম্মুল বানীনের শোকগাঁথা শুনে নিজের মনের অজান্তই বসে পড়তো এবং উম্মুল বানীনের বিলাপের সাথে সাথে ক্রন্দন করতো।
উম্মুল বানীন বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। এর মধ্যে একটি কবিতায় তিনি বলেনঃ
لَا تَدْعُونِی وَيْکَ اُمَّ الْبَنِينِ |
تُذَکِّرِينِی بِلُيُوثِ الْعَرِينِ |
|
کَانَتْ بَنُونَ لِی اُدْعَی بِهِمْ |
وَ الْيَوْمَ اَصْبَحْتُ وَ لَا مِنْ بَنِينٍ |
‘‘ হে আর আমাকে ডেকো না উম্মুল বানীন বলে
এ ডাক তাজা করে দেয় বেদনার স্মৃতি মোর
ছিলো মোর ক’ টি পুত্র,ডাকা হতো তাই এই নামে মোরে
আজ আমি আছি শুধু মোর কোনো পুত্র নেই।’’
(মুন্তাহাল আমাল,খণ্ড ১,পৃষ্ঠা ৩৮৬)
উম্মুল বানীনের জৈষ্ঠ পুত্র ছিলেন হযরত আবুল ফজল আব্বাস। তাই তিনি বিশেষভাবে আবুল ফজলের স্মরণে এক মর্মবিদারক শোকগাঁথা রচনা করেন। এতে তিনি বলেনঃ
يَا مَنْ رَأَی الْعَبَّاسَ کَرَّ عَلَی جَمَاهِيرِ النَّقَدِ
وَ وَرَاهُ مِنْ اَبْنَاءِ حَيْدَرَ کُلُّ لَيْثٍ ذِی لَبَدٍ
اُنْبِئْتُ اَنَّ ابْنِی اُصِيبَ بِرَأْسِهِ مَقْطُوعَ يَدٍ
وَيْلِی عَلَی شِبْلِی اَمَالَ بِرَأْسِهِ ضَرْبُ الْعَمَدِ
لَوْ کَانَ سِيْفُکَ فِی يَدَيْکَ لِمَا دَنَی مِنْهُ اَحَدٌ
‘‘ হে,যে জন দেখেছো আব্বাসকে নীচ গোষ্ঠীর মোকাবিলায়
আর তার পশ্চাতে ছিলো হায়দারের পুত্রগণ প্রত্যেকেই সিংহ দৃঢ়পদ
আমাকে জানানো হলো,আমার কর্তিতহস্ত পুত্রের শিরোপরি আপতিত হলো
আফসোস তবু সে সিংহ শাবকের শিরে স্বেচ্ছায় হেনেছে আঘাত
হায়! তোমার হাতে থাকলে তরবারী কেউই আসতো না তার কাছে।’’ (প্রাগুক্ত)
উম্মুল বানীন জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ আমার পুত্র সাহসী বীরপুরুষ আব্বাস কীভাবে শহীদ হলো? বস্তুতঃ হযরত আবুল ফজল আব্বাসের সাহসিকতা ও বীরত্বের বিষয় ইতিহাসের অকাট্য বিষয় সমূহের অন্যতম। তিনি ছিলেন অসাধারণ সুন্দর। এ কারণে শৈশব কালেই তাকে‘‘ ক্বামারে বানী হাশেম’’ (বনি হাশেমের পূর্ণচন্দ্র ) বলা হতো যিনি বনি হাশেমের মাঝে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুদ্ভাসিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দীর্ঘদেহী। অনেক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী,তিনি যখন ঘোড়ায় সওয়ার হতেন তখন রেকাব থেকে পা বের করে ঝুলিয়ে দিলে তার পায়ের আব্দুল ভূমি স্পর্শ করতো। তার বাহুও ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ ও শক্তিশালী এবং বক্ষ ছিলো খুবই প্রশস্ত। উম্মুল বানীন বলতেন যে,এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তার পুত্র নিহত হবেন না। উম্মুল বানীন লোকদের জিজ্ঞেস করেন,তার পুত্রকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিলো? তাকে জানানো হয় যে,প্রথমে তার হাত দু’ টি কেটে ফেলা হয়,এরপর তাকে হত্যা করা হয়। একথা শুনে উম্মুল বানীন এ নিয়ে মার্সিয়া (শোকগাঁথা) রচনা করেন। তিনি বলতেনঃ‘‘ হে কারবালা প্রত্যক্ষকারী নয়নগুলো! হে কারবালা থেকে আগত লোকেরা! তোমরা তো আমার আব্বাসকে দেখেছো যে,সে শৃগালদের দলের ওপর হামলা করেছিলো এবং দুশমন পক্ষের লোকেরা শৃগালের মতো তার সামনে থেকে পলায়ন করছিলো।’’ তিনি বলেনঃ
يَا مَنْ رَأَی الْعَبَّاسَ کَرَّ عَلَی جَمَاهِيرِ النَّقَدِ
وَ وَرَاهُ مِنْ اَبْنَاءِ حَيْدَرَ کُلُّ لَيْثٍ ذِی لَبَدٍ
‘‘ হে,যে জন দেখেছো আব্বাসকে নীচ গোষ্ঠীর মোকাবিলায়
আর তার পশ্চাতে ছিলো হায়দারের পুত্রগণ প্রত্যেকেই সিংহ দঢ়পদ।’’
তিনি তার শোকগাঁথায় বলেনঃ‘‘ আলীর অন্যান্য পুত্র তার পিছনে দাড়িয়ে ছিলো;তারা সিংহের পিছনে সিংহের ন্যায় আব্বাসের পিছনে দাড়িয়ে ছিলো। আফসোস! আমাকে জানানো হয়েছে,তোমার নরিসংহ পুত্রের শরীরে লৌহশলাকা ঢুকানো হয়েছিলো। আব্বাস! প্রাণপ্রিয় পুত্র আমার! আমি জানি,তোমার শরীরে যদি হাত থাকতো তাহলে কেউই তোমার সামনে আসতে সাহসী হতো না।’’
হোসাইনী আন্দোলনে অন্যতম উপাদান“ তাবলীগ”
‘ তাবলীগ’ -এর তাৎপর্য
মানুষের উক্তির মধ্যে যেমন সহজ অথবা দুর্বোধ্য হওয়া অর্থাৎ সরলভাবে একটিমাত্র অর্থপ্রকাশক কিম্বা বহুমাত্রিক ও একাধিক অর্থ প্রকাশক হওয়ার দিক থেকে পার্থক্য থাকে,তদ্রুপ মানুষের আন্দোলন ও বিপ্লবসমূহও একইভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আমাদের উক্তি দু’ প্রকারের হতে পারেঃ যে উক্তির একটিমা অর্থ থাকে আর যে উক্তির একাধিক অর্থ বা দিক থাকতে পারে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ। কোরআন তার আয়াতমালাকে দু-ভাগে ভাগ করেছেঃ আয়াতে মুহকামাত তথা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত আর আয়াতে মুতাশাবিহাত তথা দ্ব্যর্থক আয়াত। প্রথম প্রকারের আয়াত হলো যার একটিমাত্র অর্থ থাকে। অর্থাৎ উক্ত ভাষা বা শব্দ থেকে একটার বেশী অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত থেকে একই সময়ে কয়েকটি অর্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে আমরা যাতে সদৃশ্য অর্থাবলীর মধ্যে বিভ্রান্তির কবলে না পড়ি এজন্যে মুহকাম আয়াতগুলোকেই মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করতে হবে। কারণ সেগুলোই হলো‘‘ উম্মুল কিতাব’’ তথা কিতাবের মূল স্বরূপ।
মানুষের আন্দোলনসমূহ এবং বিপ্লবসমূহও ঠিক তদ্রুপ। কোনো আন্দোলনের একটি মাত্র অর্থ বা লক্ষ্য থাকতে পারে আবার একাধিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিতও হতে পারে। অর্থাৎ একই সময়ে একাধিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সে আন্দোলন পরিচালিত হয় আবার যেন সে সবগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিণতিতে একটি মূল লক্ষ্যে প্রত্যাবর্তিত হয়। এভাবে একটি আন্দোলন একই সময়ে বিভিন্ন দিক ও মাত্রা সম্বলিত হতে পারে।
ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর আন্দোলন হলো এরূপ একটি বহু মাত্রা এবং বহু দিক সম্বলিত আন্দোলন। এই যে ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর আন্দোলনকে ঘিরে নানান ব্যাখ্যা আর নানান মত,এর কারণ হলো এর মধ্যে একাধিক উপাদানের সমান্তরাল উপস্থিতি। আমরা যখন কিছু কিছু উপাদান এবং নিয়ামকের দিক বিবেচনায় এ আন্দোলনের দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই যে ক্ষমতাসীন স্বৈরাচার ও শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় দাবীর বিপরীতে কেবলই প্রতিবাদী দৃঢ়তা এবং একগুয়েমী অবাধ্যতা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ আন্দোলনটি হলো এক নাকচ ঘোষণা এবং আত্ম-সমর্পণ না করা। আমরা সকলে জানি যে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর এবং ইয়াযিদের ক্ষমতায় আরোহণ আর এ উদ্দেশ্যে যতসব চক্রান্ত চালানো হয় তারপর ইয়াযিদ অপরিহার্য মনে করলো যে ইসলামী বিশ্বের কতিপয় ব্যক্তিত্ব যাদের সর্বাগ্রে ছিলেন ইমাম হোসাইন (আঃ),যাকে নিয়ে ইয়াযিদের হিসাব নিকাশ ছিল সবচেয়ে বেশী,এদের থেকে বাইয়াত আদায় করা। তাহলে জনসাধারাণও সবাই চুপ হয়ে যাবে এবং প্রকৃতপক্ষে ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করতে সক্ষম হবে।
মুয়াবিয়ার মৃত্যু পর ইয়াযিদ কালক্ষেপণ না করে একটি চিঠি মদীনার গভর্ণর,তারই চাচাতো ভাই ওয়ালীদ ইবনে উতবা ইবনে আবি সুফিয়ানের কাছে প্রেরণ করে। তার মাধ্যমে সে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর সংবাদ এবং নিজের ক্ষমতারোহনের কথা তাকে অবগত করে। আর আলাদা একটি চিরকুটে সে কয়েক জনের নাম লিখে পাঠায় যাদের শিরোনামে ছিল ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর নাম,তাদের কাছ থেকে অবশ্যই বাইয়াত গ্রহণ করার নির্দেশ দান করে। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আঃ) বাইয়াত করতে রাজি হলেন না। তারপর আরো কয়েকদিন মদীনায় অবস্থান করার পর যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এরা ছেড়ে দেবার পাত্র নয়,তখন স্বীয় আহল পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর পবিত্র নিরাপদ ঘরের অভিমুখে রওনা হন। অর্থাৎ রজব মাসের শেষ ভাগে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর খবর মদীনায় পৌছে এবং ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর নিকট বাইয়াতের দাবী জানায়।
সম্ভবত 27 রজব ইমাম হোসাইন (আঃ) মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং 3রা শাবান তারিখে মক্কায় প্রবেশ করেন। সেদিন তার জন্ম দিবসও ছিল। 8ই জিলহজ্ব অবধি তিনি সেখানে অবস্থান করেন। তবে কোনো অবস্থাতেই তিনি তার কাছে যে দাবী জানানো হয়েছিল তার প্রতি সাড়া দিতে রাজি হননি। এই নাকচ করে দেয়াটা হলো একটি উক্তি । যে উক্তি এই আন্দোলনকে এক বিশেষ প্রাণ দান করে। এ প্রাণসত্তাটি হলো যুগের শাসন ক্ষমতা দখলকারী এক স্বৈরাচারী দাবীর বিরুদ্ধে‘ না’ বলা এবং আত্মসমর্পণ না করা।
এই আন্দোলনে ভূমিকা পালনকারী আরেকটি উপাদান হলো‘‘ সৎকাজের আদেশ আর অন্যায় কাজে নিষেধ’’ -এই নীতিটি । ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (আঃ)-এর বক্তব্যে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবৃতি রয়েছে। এমর্মে সাক্ষ্য প্রমাণও অনেক রয়েছে। অর্থাৎ যদি ধরে নেয়া হয় যে তার কাছে বাইয়াতের দাবী নাও করতো তাহলেও তিনি নীরব থাকতেন না।
আরেকটি উপাদান হলো হুজ্জাত তথা প্রমাণ পূর্ণ করা এবং চরম পত্র প্রদান করা। তৎকালে মুসলিম জাহানের তিনটি বড় কেন্দ্র ছিলঃ মদীনা-যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হিজরতের ভূমি নামে পরিচিত ছিল,শ্যাম-যা খেলাফতের ভূমি নামে পরিচিত ছিল এবং পূর্বে আমিরুল মুমিনীন আলী (আঃ) এর দারুল খেলাফত ছিল। এছাড়া এটা ছিল একটি নতুন শহর যা মুসলমান সৈন্যদের দ্বারা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের সময়ে স্থাপিত হয়েছিল এবং একে ইসলামী সৈন্যদের সেনানিবাসও বলা হতো। আর একারণে একে শ্যামের সমান বলে তুলনা করা হতো। এই শহরের অর্থাৎ মুসলিম সেনানিবাসের জনগণ যখন অবগত হলো ইমাম হোসাইন (আঃ) ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত করতে রাজি হননি তখন তাদের নিকট থেকে প্রায় আঠারো হাজার চিঠি এসে পৌঁছে ইমামের কাছে। চিঠি গুলোকে কেন্দ্রে পাঠায় এবং ঘোষণা করে যে আপনি যদি কুফায় আসনে তাহলে আমরা আপনাকে সাহায্য করবো। এখানে ইমাম হোসাইন (আঃ) ইতিহাসের দুই রাস্তার মোড়ে এসে উপনীতঃ যদি তাদের আহবানের প্রতি সাড়া না দেন তাহলে অনিবার্যভাবে ইতিহাসের রায়ে তিনি নিন্দিত হবেন। ভবিষ্যতের ইতিহাস তখন বিচার করে বলবে যে অভাবনীয় একটি অনুকূল পরিবেশ ছিল। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আঃ) এ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেন নি। অথবা তিনি চাননি কিম্বা তিনি ভয় পেয়েছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি অপব্যাখ্যা। ইমাম হোসাইন (আঃ) যাতে এই লোকগুলো যারা এভাবে সাহায্যের হাত তার দিকে প্রসারিত করেছে,তাদের কাছে হুজ্জাত তথা প্রমাণকে চুড়ান্ত করতে পারেন এজন্যে তাদের আহবানে সাড়া জানান। ইতিপূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে। এপর্যায়ে এই আন্দোলন আরেক সত্তা এবং আরেক রূপ ও বর্ণ ধারণ করে।
এই আন্দোলনের আরো একটি মাত্রা বা দিক হলো এর তাবলীগ তথা প্রচারের দিক। অর্থাৎ,এই আন্দোলন একই সাথে যেমন সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধ এবং একইসাথে যেমন প্রমাণ চুড়ান্তকরণ (ও যুগের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ না করার ঘোষণা) তদ্রুপ এটা একটি প্রচার এবং বার্তাবাহীও বটে। ইসলামকে পরিচিত করা এবং চিনিয়ে দেবার এক আন্দোলনও বটে।
আলোচনার শুরুতে‘‘ তাবলীগ’’ এর সঠিক অর্থকে আগে ব্যাখ্যা করার দরকার। বিশেষ করে সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ-এই নীতির সাথে এর পার্থক্য কি সেটা নির্ধারণ করতে হবে যাতে বুঝা যায় যে,হোসাইনী আন্দোলনে‘ তাবলীগ’ উপাদানটি‘ আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার’ উপাদান থেকে ভিন্ন ।
‘ তাবলীগ’ এমন একটি শব্দ যা পবিত্র কোরআনে অনেক ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কোরআন নবীগণের ভাষায় বর্ণনা করে যে,
) يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ(
‘‘ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের বার্তা পৌছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাস না।’’ (আ’ রাফঃ 79)
কিম্বা নবীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেঃ
) مَا عَلَي الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ(
‘‘ রসুলের উপর কোনো দায়িত্ব নেই কেবল পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া।’’ (মায়িদাঃ 99)
মোদ্দকথা হলো,‘‘ বালাগ’’ ,‘‘ তাবলীগ’ ,‘‘ ইউবাল্লিগুনা’’ ইত্যাদি শব্দগুলো পবিত্র কোরআনে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দের অর্থ কি? দুর্ভাগ্যেরকথা হলো বর্তমানে এই শব্দটি একটি করুণ পরিণতির শিকার হয়েছে। অর্থাৎ এক অশুভ এবং ঘৃণ্য অর্থ লাভ করেছে। এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে আজ (উদাহরণস্বরূপ ফার্সী ভাষাভাষীদের কাছে তাবলীগ বলতে বুঝায় সত্য মিথ্যার তেলেসমাতি করা এবং প্রকৃতপক্ষে ঠগবাজি ও বোকা বানিয়ে মানুষের হাতে কোনো পন্য ধরিয়ে দেয়া। অর্থাৎ বোকা বানানোর অর্থেই এখন এর প্রয়োগ। আর একারণেই দেখা যায় যখন কেউ বলতে চায় যে এসবের কোনো ভিত্তি নেই তখন বলে দেয় যে জনাব,এসব কিছুই আসলে তাবলীগ,সবকিছুই মিথ্যা আর ধোকাবাজি। এজন্যে দেখতে পাই অনেকে ধর্মীয় ব্যাপারে এ শব্দটি প্রয়োগের পক্ষপাতি নয়। কিন্তু কথা হলো যদি কোনো শব্দের সঠিক অর্থ থাকে আর সেই সঠিক অর্থ পবিত্র কোরআন এবং নাহজুল বালাগার মধ্যে প্রয়োগ হয়ে থাকে তাহলে উক্ত শব্দের অর্থ বিভ্রান্ত ঘটার অপরাধে সেটাকে শাস্তি দেয়া আমাদের উচিত হবে না। বরং সবসময় এর সঠিক অর্থটিই মানুষের কাছে বলা আমাদের কর্তব্য ।
تبلیغ (তাবলীগ) কথাটিوصول (উসুল) এবংایصال (ইসাল) কথা দুটির সাথে খুব নিকটবর্তী অর্থ বহন করে। আরবী ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে এমন কিছু সূক্ষ্ণও নিখুঁত কাজ থাকে যা অন্য ভাষায় (এমনকি ফার্সীর মতো মিষ্টি ও সমৃদ্ধ ভাষাতেও) দেখা যায় না। আরবী ভাষায় একটি শব্দ হলোایصال (ইসাল) এবং আরেকটি শত্রুহলোابلاغ (ইবলাগ)।ایصال (ইসাল) এর অর্থ কি? যেমন ধরুন,আমি কোনো এক কাপড়কেایصال (ইসাল) করেছি। এর অর্থ হবে আমি ওটাকে পৌছে দিয়েছি।ابلاغ (ইবলাগ) ফার্সী ভাষায় কি অর্থ দেয়? যদি বলা হয় যে অমুক জিনিসটাকেابلاغ (ইবলাগ) করেছি,সে ক্ষেত্রে ও বলি যে এর অর্থ হলো পৌছে দিয়েছি। ফার্সী ভাষায় এ উভয়ের বলোয়‘ পৌছানো’ এবং‘ পৌছে দেয়া’ অর্থে ব্যাবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু আরবী ভাষায়ایصال (ইসাল) কেابلاغ (ইবলাগ) এর স্থলে প্রয়োগ করা যায় না। তদ্রুপابلاغ (ইবলাগ) কেওایصال (ইসাল) এর স্থলে প্রয়োগ করা যায় না।ایصال (ইসাল) শব্দটি সচরাচর কোনো জিনিসকে কারো হাত দ্বারা অথবা কারো আয়ত্বাধীনে পৗছানোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ জড়বস্তুগত বিষয়ে। কেউ যদি একটি পার্সেলকে কারো নিকটে পৌছাতে চায়,এ ক্ষেত্রেایصال (ইসাল) শব্দকে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিম্বা কেউ যদি আপনার কাছে কোনো আমানত (বস্তুগত) রেখে থাকে এবং আপনি সে আমানতকে তার কাছে পৌছে দিতে চান,এ ক্ষেত্রে বলা হয় যে আমানতকে তার মালিকের নিকটایصال (ইসাল) করেছে।
কিন্তুابلاغ (ইবলাগ) কথা কোনো চিন্তা কিম্বা বার্তাকে পৌছে দেবার সময় বলা হয়। অর্থাৎ কোনো জিনিসকে কারো মন,মানস,চিন্তা ও অন্তরে পৌছে দেবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একারণেابلاغ (ইবলাগ) এর বিষয়বস্তু কোনো জড়বস্তু হতে পারে না। অবশ্যই তা কোনো অজড় এবং আধ্যাত্মিক কিছু হতে হবে। একটি চিন্তা অথবা একটি অনুভব। অন্যকথায়,সাধারণতঃ কোনো বার্তা,সালাম বা অনুরূপ কোনো কিছু প্রেরণের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয়। বলা হয় সালামابلاغ (ইবলাগ) করেছে,বার্তাابلاغ (ইবলাগ) করেছে। যখন বার্তাابلاغ (ইবলাগ) করে তখন কোনো চিন্তাকে অন্যদের কাছে পৌছায়। আর যখন সালামابلاغ (ইবলাগ) করে তখন আবেগ ও ভক্তিকে পৌছায়। এরূপ বিষয়ের ক্ষেত্রেইابلاغ (ইবলাগ) বাتبلیغ (তাবলীগ) কথাটি ব্যবহৃত হয়। আর পবিত্র কোরআন এই শব্দকে রেসালাত তথা বার্তাসমূহের বেলায় প্রয়োগ করেছে।
সুতরাং,تبلیغ (তাবলীগ) হলো কোনো বার্তাকে একজনের নিকট থেকে আরেক জনের নিকটে পৌছানো। ফার্সী ভাষায় যে পয়গম্বর (বা বার্তাবাহক) কথা এসেছে তা‘ রাসুল’ শব্দের অনুবাদ। এর অর্থ হলো রেসালাতের মুবাল্লিগ তথা বার্তা প্রচারক।‘ রেসালাত’ শব্দ এমন একটি শব্দ যা শুভ পরিণতি লাভ করেছে। অবশ্য আমরা রেসালাহ বলতে যেসব জিনিসকে বুঝি তা কোরআনে ব্যবহৃত‘ রেসালাত’ এর থেকে ভিন্ন । আমরা সাধারনত কিছু লিখিত কাগজের সেট যার সমষ্টি একটি পুস্তকের মতো নয় সেটাকে রেসালাহ বলে থাকি। যদিও উক্ত রেসালাহ’ র বিষয়বস্তুর বার্তার সাথে কোনো সম্পর্ক নাও থাকে। যেমন ধরুন,কেউ একটি পুস্তিকা লিখলো কোনো ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে,ফার্সী কিম্বা আরবীর। তখন বলা হয় যে অমুক লোক অমুক বিষয়ে একটি রেসালাহ লিখেছে। যদিও এ নামটি উক্ত বিষয়বস্তুর ( যেমন ভাষার ব্যাকরণ) সাথে সঙ্গতিশীল নয়।‘ রেসালাহ’ কে এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে যেখানে কোনো বার্তা থাকবে। কিন্তু কেউ যদি কোনো জ্ঞানগত বা ভাষাগত সমস্যার সমাধান করে থাকে তাহলে সে কারো জন্য কোনো বার্তা আনেনি। এক্ষেত্রে এশব্দটি প্রয়োগ সঙ্গত নয়। কিন্তু সম্প্রতি‘ রেসালাত’ শব্দটি ফার্সী ভাষায় ব্যাবহার করা হচ্ছে । যেমন বলা হয় অমুকের সমাজের প্রতি‘ রোসালাত’ রয়েছে। অর্থাৎ,বর্তমানে যার সম্পর্কে অনুভব করা হয় যে স্বীয় সমাজের প্রতি তার কোনো দায়িত্ব রয়েছে যা তার পালন করা উচিত,তার ক্ষেত্রে বলা হয় যে,তার একটা রেসালাত রয়েছে। এই ভাষাটি কোরআনে রেসালাতকে যে ভাষায় প্রয়োগ করা হয়েছে তার সাথে যদি অনুরূপ নাও হয়,খুবই কাছাকাছি হবে। অর্থাৎ,এই অর্থটি কোরআনে ব্যবহৃত রেসালাত’ র অর্থের খুবই কাছাকাছি। ইরশাদ হচ্ছেঃ
) اَلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَداً اِلَّا اللهُ(
‘‘ সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাকে ভয় করতেন। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। (আহযাবঃ 39)
এটা হলো বার্তাবাহকের জন্য সবচেয়ে বড় পূর্বশর্ত।
যখন প্রতিপন্ন হলো যেابلاغ (ইবলাগ) এবংتبلیغ (তাবলীগ) এর অর্থ হলো বার্তা পৌছে দেয়া তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে,تبلیغ (তাবলীগ) যা কোরআনে এসেছে আর‘ আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনীল মুনকার’ -সেটাও যে কোরআনে এসেছ-এ দুটি আলাদা বিষয়। যদিও একে অপরের সাথে জড়িত,তবে বিষয় দুটি।
তাবলীগ হলো পরিচিত করার এবং উত্তমভাবে পৌছানোর পর্যায়। সুতরাং এটা হলো জানা বা পরিচিতর স্তর। কিন্তু আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের পর্যায়টি হলো কার্যকর এবং বাস্তবায়নের পর্যায়। তাবলীগ নিজেই একটি সার্বজনীন কর্তব্য সকল মুসলমানের জন্য । যেমনভাবে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারও এক সার্বজনীন কর্তব্য । তাবলীগের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যে কর্তব্য রয়েছে সেটা হলো তার মধ্যে যেন এমন অনুভূতি কাজ করে যে তার স্থান থেকে সে যেন ইসলামের বার্তা বহন করে। কিন্তু যে কর্তব্যটি‘ আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার’ এর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর রয়েছে তা হলো তার মধ্যে যেন এই অনুভূতি কাজ করে যে সেও একজন বাস্তবায়নকারী এবং সমাজে এই বার্তা বাস্তবায়নকারী শক্তির সেও একটি অংশ। একারণেই আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার হলো এক বিষয়,আর তাবলীগ হলো ভিন্ন আরেকটি বিষয়। তাই হোসাইনী আন্দোলনে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার’ র মাত্রা তথা দিক ছাড়াও আরেকটি মাত্রা তথা দিক রয়েছে। আর সেটা হলো তাবলীগ। এই মুতাশাবিহ তথা দ্ব্যর্থক এবং বহুমাত্রিক আন্দোলন যে কাজটি করেছে তা হলো ইসলামের স্বরূপকে ঠিক যেভাবে আছে সেভাবেই পরিচিত করেছে। ইসলামের বার্তাকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত ও উত্থাপিত করেছে। তাও আবার কতো দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্টভাবে! ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে উক্তি দু’ প্রকারেরঃ মুহকাম তথা দ্ব্যর্থহীন আর মুতাশাবিহ তথা দ্ব্যর্থক। আরেকটি বিচারেও উক্তি দু’ প্রকারের হয়। যথাঃ স্বচ্ছ ও পরিণত উক্তি আর অস্বচ্ছ ও অপরিণত উক্তি ।
মুসলিম পণ্ডিতরা কিছু কিছু বাচনকে বিশুদ্ধ ও পরিণত বলে থাকেন। বিশুদ্ধ ও পরিণত বচন হলো সেটাই যা বক্তার মনোভাব ও উদ্দেশ্যকে উত্তম ও যথার্থভাবে শ্রোতার মন ও অনুভূতিতে পৌছাতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ এমন উক্তি যা প্রকৃতই বক্তার উদ্দেশ্যকে পৌছে দিতে পারে।
আন্দোলনও এরূপ। স্বচ্ছ আন্দোলন যেমন রয়েছে,অস্বচ্ছ আন্দোলনও তেমনি রয়েছে। স্বচ্ছ আন্দোলন হলো সেটা,যা,যে বার্তাকে মনসমুহ,চিন্তাসমূহ এবং অনুভূতিসমুহের কাছে পৌছাতে চায়,তাকে ভালোভাবে পৌছে দিতে সক্ষম হয়। এই দিক থেকে যখন তাকাই তখন দেখি যে,হোসাইনী আন্দোলনের চেয়ে অধিকতর,পরিণত এবং পৌছে দিতে সক্ষম কোনো আন্দোলনই খুজে পাওয়া যাবে না। এটা এমন এক আন্দোলন যা একদিক থেকে দেখা যায় যে স্থানিক ব্যপ্তির বিবেচনায় তা বিশ্বময় বিস্তৃতি লাভ করেছে। আবার কালের বিবেচনায় প্রায় চৌদ্দশ’ বছর পেরিয়ে এসেও আজ তার প্রভাব ও পৌছে দেবার শক্তি শুধু কমে যায়নি,তা নয়,বরং বলীয়ান হয়েছে। অসাধারণ শক্তিশালী এক আন্দোলন।
এপর্বে খোদ তাবলীগ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক যাতে ইমাম হোসাইন (আঃ) এর আন্দোলনে‘ তাবলীগ’ উপকরণ কে সঠিকভাবে চিনতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারি। তাবলীগ এর অর্থ ও তাৎপর্য ইতিপূর্বে অবগত হয়েছি। দেখা গেছে যে পবিত্র কোরআন তাবলীগ শব্দটির ওপর নির্ভর করেছে। নবীগেণর প্রেরণের দর্শন সম্পর্কে নাহজুল বালাগায় প্রসিদ্ধ একটি বাক্য রয়েছে। বাক্যটিতে বলা হয়েছেঃ
فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ، وَ وَاتَرَ اِلَيْهِمْ اَنْبِيَائَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيُذَآّکرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ—
আল্লাহ নবীগণকে একের পর এক প্রেরণ করলেন। কি জন্যে ? প্রথমতঃ এজন্যে যে আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে মানুষের স্বভাবে প্রতিশ্রুতি নিহিত রেখেছেন। (বলতে চান যে দীন কোনো চাপিয়ে দেয়া বিষয় নয় যে মানুষের ওপর আরোপ করা হবে,বরং মানুষের সহজাত আহবানের প্রতিই সাড়া দেয়া। আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন তা কোনো কাগজের নয়। অক্ষর,ধ্বণি কিম্বা বাইয়াতের মাধ্যমে নয়,বরং তকদীরের কলম দ্বারা,মানবের স্বভাব ও আত্মার গহীনে)। বলছেন যে,নবীগণ এসেছেন একথা বলতে যে,হে মানব! তোমরা তোমাদের সহজাত স্বভাব ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি যে অস্বীকারবদ্ধতা হয়েছে,আমরা তোমাদের সে প্রতিশ্রুতি পালন দেখতে চাই। অন্য কিছু নয়।
وَ يُذَکِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ অর্থাৎ নবীরা হলেন স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে ।
وَ يَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ আর আল্লাহর বার্তাকে মানুষের কাছে পৌছে দেন যাতে এর মাধ্যমে মানুষের জন্য হুজ্জাত বা দলীলকে পূর্ণ করেন।
وَ يُثيِرُوا لَهُمْ دَفائِنَ الْعُقُولِ
(কি অদ্ভুত বাক্যগুলো!)অর্থাৎ বলেছেন যে, মানুষের অভ্যন্তরে তথা বিবেক ও আত্মার মধ্যে গুপ্ত ধন লুকিয়ে রয়েছে। তাদের মগজে নিহিত রয়েছে চিন্তার গুপ্তধন। কিন্তু এসব গুপ্তধনকে ঢেকে ফেলেছে ধুলা ময়লার আস্তরণ। নবীগণ এসেছেন এসব ধুলা ময়লাকে ঝেড়ে ফলতে এবং মানুষের নিজের মধ্যে যেসব গুপ্তধন রয়েছে সেগুলো তাকে দেখিয়ে দিতে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজের মন ও আত্মার ঘরের ভেতর মূল্যবান গুপ্তধনের অধিকারী রয়েছে কিন্তু সে তা থেকে বেমালুম বেখবর। নবীগণ মানুষকে তার এই মূল্যবান গুপ্তধনের সন্ধান দিতে চান যাতে প্রত্যেকে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে তার গুপ্তধন বের করে আনার কাজে ব্রতী হয়।( উদ্ধৃত বাণীটির জন্য দেখুন নাহজুল বালাগা , ফয়জুল ইসলাম , খুতবা 1 , অংশ 36 , পৃষ্ঠা 33 )
তাবলীগের এই যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো নবীগণ ছিলেন সে অর্থে মুবাল্লিগ। কিন্তু সকলে শরীয়ত প্রবর্তক ছিলেন না। একারণে আল্লাহর নবীগণ ছিলেন দুই শ্রেণীরঃ এক শ্রেণীর নবী হলেন যারা মুবাল্লিগ এবং শরীয়তেরও প্রবর্তক। আর আরেক শ্রেণীর নবী যারা শুধুই মুবাল্লিগ। শরীয়ত প্রবর্তনকারী নবী হলেন আইন ও বিধান প্রণয়ণকারী নবী যাদের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। তাদের মোট সংখ্যা হলো পাঁচজন। যথাঃ হযরত নূহ,ইব্রাহীম,মূসা,ঈসা আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। কিন্তু সকল নবীই ঐশী বার্তার মুবাল্লিগ তথা প্রচারক। যেমনভাবে তারা আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার কারীও বটে। এই যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এসেছেন,প্রত্যেক নবীই মানুষের জন্যে আইন নিয়ে আসেননি। যারা আইন নিয়ে এসেছেন তারা সীমিত। অবশিষ্ট নবীরা সেই বার্তা পৌছানোর দায়িত্ব পালন করতেন যা শরীয়ত প্রবর্তনকারী নবীগণ নিয়ে এসেছেন। এরা হলেন তাবলীগের নবী। আর শেষনবীর পরে যেমন কোনো শরীয়তের নবীও আসবেন না তদ্রুপ কোনো তাবলীগের নবীও আসবেন না। কিন্তু মুবাল্লিগ থাকতে হবে। কিভাবে? যেহেতু শেষ যুগ হলো মানুষের প্রাপ্ত বয়স্ক ও পরিপূর্ণতার যুগ। এসময়ে ঐ যে দায়িত্ব এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী (পাঁচজন ব্যতীত) পালন করতেন অর্থাৎ তাবলীগের কাজ (যদিও প্রকৃত অর্থে স্বয়ং আল্লাহই তা করতেন অর্থাৎ নবীদেরকে একাজ পালন করার জন্যে প্রেরণ করতেন),সেকাজ এখন সাধারণ মানুষকে পালন করতে হবে। অ-নবীরাই এখন সেকাজ পালন করবে,আলেম এবং অ-আলেমরাই এখন তা পালন করবে। আর এজন্যেই ইসলামের প্রকৃত মুবাল্লিগরা হলেন নবীদের নবী। অর্থাৎ,নবীদের বার্তাকে তারা মানুষের কাছে পৌছায়।
তবে,একটি বার্তার সফলতার পূর্বশত কি? ইসলাম নিজে কি একটি সফল বার্তা ছিল? যদি উত্তর ইতিবাচক হয় তাহলে এই সফলতার পেছনে রহস্য কি ছিল? একটি বার্তা সফল হওয়ার চারটি শর্ত রয়েছে। যদি সে শর্ত চারটি একত্রে জমা হয় তাহলেই উক্ত বার্তার সফলতা শতভাগ নিশ্চিত হবে। কিন্তু যদি তা একত্রে জমা না হয় তাহলে তখন বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করবে।
একটি বার্তা সফল হওয়ার প্রথম শর্ত হলো সেটা বুদ্ধিবৃত্তিক হওয়া এবং এর বিষয়বস্তুর শক্তিদীপ্ত হওয়া। অর্থাৎ উক্ত বার্তা মানুষের জন্যে কি নিয়ে এসেছ এবং মানুষের যুগ জিজ্ঞাসা স্মরণে কত সামঞ্জস্যশীল এবং কিভাবে তা পূরণ করতে সক্ষম হবে? মানুষের চাহিদার অন্ত নেই। মানিসক,চিন্তাগত,আবেগ অনুভূতিগত,ব্যবহারিক,সামাজিক,বস্তুগত ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি বার্তা শুধু যে মানুষের চাহিদার বিরুদ্ধ হবে না তাই নয়,বরং,সে চাহিদাগুলোর অনুকূল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এক বার্তার প্রথম কথাই হলো তাকে যুক্তিসিদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ,মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধির সাথে সঙ্গতিশীল। তা এমন হবে যেন মানুষের বুদ্ধির আকর্ষণ ক্ষমতাকে সে নিজের দিকে টেনে আনে। কেননা,কোনো বার্তা যদি মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধির পরিপন্থি হয় এমনকি যদি আবেগপ্রসূতও হয় তাহলে তার স্থিতিকাল খুব সামান্যই থাকে। চিরকাল তা টিকতে পারে না। একারণে কোরআন সর্বদা চিন্তা ও অনুধ্যানের ওপর জোরারোপ করে থাকে। কোরআন কখনোই বুদ্ধি ও যুক্তিকে পরিত্যাগ করেনি। বরং,যুক্তি ও বুদ্ধিকে সব সময় নিজের জন্য একটি খুঁটি হিসাবে কাজে লাগিয়েছে এবং মানুষকে বুদ্ধি খাটানোর জন্যে আহবান জানিয়েছে।
তদ্রুপ,একটি বার্তা যাতে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয় এজন্য তাকে মানুষের আবেগের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। মানুষের একটি দিক রয়েছে যা তার বুদ্ধি ও চিন্তার দিক থেকে ভিন্ন । যার নাম‘ আবেগ’ এবং যাকে উপেক্ষা করার জো নেই। বার্তাকে মানুষের এই আবেগের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলোর উন্নত ও সূক্ষ্ণগুলোকে একটা পর্যায় পর্যন্ত পরিতৃপ্ত করা এবং মানুষের জীবনের বাস্তব প্রয়োজন সমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া হলো ঐ বার্তার বিষয়বস্তুর বলীয়ান হওয়ার মূলকথা। যদি কোনো বার্তা মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদাসমূহের বিরুদ্ধ হয় তাহলে সফল হতে পারবে না।
একটি হাদীস রয়েছে,ফেকাহ’ র মধ্যেও যার উদ্ধৃতি দেয়া হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ الْاِسْلامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَي عَلَيْهِ অর্থাৎ,ইসলামই বিজয়ী হয় এবং অন্যের ওপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে,কোনো কিছুই ইসলামের ওপর বিজয়ী হয় না।( নাহজুল ফাসাহা , পৃষ্ঠা 214 , হাদীস নং 1056 )
এটা হলো এমন একটি হাদীস যা ইসলামের সকল শ্রেণীর আলেমবৃন্দ সমান দৃষ্টিতে যার মূল্যায়ন করেছেন। ফেকাহর আলেমগণ যারা সবকিছুকেই ফেকহী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পছন্দ করেন,তারা এই হাদীসের থেকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ইসলামে সামাজিক বিধি বিধানে এমন কোনো বিধান নেই যা পরিণামে অমুসলমানদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয়ী করবে। ইসলাম এধরনের বিধানকে অনুমোদন করে না। উদাহরণস্বরূপ,ইসলামী সমাজে একজন আহলে যিম্মা (যেমন ইহুদী,খৃষ্টান কিম্বা যরথুষ্ট্রীয়) কি এমন মর্যাদা বা অবস্থায় উপনীত হতে পারে যে সে-ই শাসক হবে আর একজন মুসলমান হবে তার শাসনাধীন? কিম্বা একজন মুসলমানকে তার নিজের এখতিয়ারে নিয়ে নিবে? ফকীহবৃন্দ উত্তরে বলেন,:
الْاِسْلامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَي عَلَيْهِ অর্থাৎ ইসলামের হাত সব সময় উপরে থাকতে হবে। ইসলাম নীচের হাতকে কখনো মেনে নেয় না। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে কতিপয় বিধান নিঃসরণ করে থাকেন।
কালাম শাস্ত্রের পণ্ডিতবর্গ আবার বিষয়টিকে দেখেন অন্যভাবে। তারা কালাম শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর দিকে তাকান। (যেহেতু তাদের কাজ হলো যুক্তি প্রমাণ আর দলীল দস্তাবেজ নিয়ে একারণে) তারা বলেন যে,:الْاِسْلامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَي عَلَيْهِ এর অর্থ হলো ইসলামের যুক্তি-প্রমাণ অন্য সব যুক্তি প্রমাণের চেয়ে শ্রেয়তর। যুক্তি-প্রমাণের ময়দানে ইসলামের যুক্তি প্রমাণই জয়যুক্ত হবে। এটা হলো উক্ত হাদীসের আরেক ধরনের ব্যাখ্যা । আবার যারা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবিষটি মূল্যায়ন করেছেন তারা বলেনঃالْاِسْلامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَي عَلَيْهِ অর্থাৎ,কার্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতা ইসলামেরই। কারণ,ইসলামের বিধি বিধান অন্য যে কোনো বিধি বিধানের চেয়ে মানুষের চাহিদা ও প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে তার পথকে বাস্তবক্ষেত্রে সহজতর করে তোলে।
কেউ যখন স্বীয় প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমগুলোর দিকে তাকায়,উন্নত কলা-কৌশল,দক্ষ জনবল,ব্যাপক পরিকল্পনা,বিশাল বাজেট এবং সর্বোপরি তাদের ব্যাপকতা দেখে বলে ওঠে যে,তাদের প্রোপাগাণ্ডার এতসব কিছুর পরেও কি ইসলাম টিকে থাকতে পারে? সত্যিই আজব ব্যাপার! যখন আমাদের নিজেদের দিকে তাকাই তখন দেখি,তাবলীগের উপায় উপকরণের দিক দিয়ে আমরা একবারে শুন্যের কোঠায় রয়েছি। পৃথিবীর কোনো ধর্মই তাবলীগের উপকরণ আর মুবাল্লিগের দিক থেকে ইসলামের চেয়ে দুর্বল নয়। এমনকি ইহুদীরা যাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়,কিন্তু তাদের কোমর শক্ত করে বাধা। কিছু না হলেও অন্তত বিকৃতির দ্বারা। তাদের ইতিবাচক কিছু নেই যা দ্বারা মানুষদেরকে ইহুদীবাদের প্রতি আহবান জানাতে পারে। কিন্তু তাদের বিধ্বংসী ক্ষমতা প্রবল অন্য ধর্মগুলোকে বিনষ্ট করে দেবার জন্য । একজন ইহুদী তার জীবনভর ইসলামের কোনো একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা চালায়। তার লক্ষ হলো কোনো একটি বিশ্ব বিদ্যালয়ে একটি আসন দখল করা। আর ঐ আসনে বসেই সে তার কাজ সেরে ফেলে। এমন একটি বই লিখবে এবং উক্ত বইয়ের মধ্যে সে তার নিজ চিন্তার প্রসার ঘটাবে। আপনারা কি জানেন যে বিশ্বে ইসলামিক ষ্টাডিজ এর নববই শতাংশেরও বেশি চেয়ার ইহুদীদের দখলে রয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বে ইসলামের এক্সপার্টরা হলো সব ইহুদী! তাহলে বুঝতে হবে যে তাদের আঘাত শক্তি কতো জোরদার। ঐ হলো খৃষ্টানদের কথা আর এই হলো ইহুদীদের কথা।
কিন্তু এতসব কিছু সত্বেও,বিশ্বে কি হারে মানুষ মুসলমান হচ্ছে পত্র পত্রিকা খুললেই চোখে পড়বে। এটা কোন তাবলীগের জোরে? কোনো মুবাল্লিগও ছিল না। বড়জোর একটা রেডিও থেকে মাঝে মাঝে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশের অনুষ্ঠান শুনেছে হয়তো। আমি (ওস্তাদ মুতাহহারী) ইউরোপ ফেরত একজন খোঁজ-খবর রাখা ব্যক্তির সাথে এ বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম। ভদ্রলোকটি যিনি বহু বছর ধরে ইউরোপে থাকেন তিনি লোমণ্ড সংবাদপত্রে বিগত কয়েক বছরে 14 মিলিয়ন লোকের মুসলমান হওয়া মর্মে প্রকাশিত খবরের প্রসঙ্গে জনৈক খৃষ্টান ব্যক্তির অভিমত তুলে ধরে বলেন যে ঐ খৃষ্টান লোকটি বলেছিল,লোমণ্ড-এর তথ্য ভুল। আসলে বিগত বছরগুলোতে মুসলমান হওয়া লোকের সংখ্যা পচিশ মিলিয়ন। লোকটি আরো বলে যে আফ্রিকায় দুইটি শক্তি ক্রমবর্ধমানঃ ইসলাম এবং কম্যুনিজম। খৃষ্টবাদ যতই তৎপরতা চালাক,উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটেনি। যদিও তাদের প্রচার মাধ্যমসমূহ শক্তিশালী এবং ব্যাপক;পক্ষান্তরে ইসলামের প্রচারমাধ্যম দুর্বল। এর পার্থক্য হলো দুটোর বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একটির বিষয়বস্তু শক্তিশালী এবং যুক্তিনির্ভর,আর অপরটির বিষয়বস্তু আবেগ নির্ভর। আবেগের দৃষ্টিতে তা খুবই শক্তিশালী। এর বিষয়বস্তু বাস্তবমুখী এবং মানুষের ব্যবহারিক জীবনাচার কেন্দ্রিক। পক্ষান্তরে অন্যটির বিষয়বস্তু হলো চাপিয়ে দেয়া। ইসলামের প্রথম কথাটি একজন পিপাসার্তের গলায় পানির মতো পরম আগ্রহে গলাধঃকরণ হয়। ইসলাম বলে, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা আল্লাহ ও তার একত্ববাদকে প্রমাণিত করতে হবে। কিন্তু খৃষ্টবাদের প্রথম কথাই হলো বুদ্ধিবৃত্তিকে বিদায় করে ত্রিত্ববাদের কথা বলতে হবে।
মহররম ও আশুরাকে ঘিরে আলোচনা এতাটা বিস্তারিত করার উদ্দেশ্য হলো হোসাইনী বার্তাকে মানুষের কাছে পৌছানো। অতঃপর ব্যাখ্যা প্রদান করবো যে কিভাবে এ আন্দোলন ইসলামের বার্তা বহনকারী ছিল। অর্থাৎ ইমাম হোসাইন (আঃ) কিভাবে ইসলামের বার্তাকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌছাতে সক্ষম হয়েছেন।
ইমাম হোসাইন (আঃ) 8ই জিলহাজ্ব তারিখে যখন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে হাজীরা দলে দলে মক্কায় প্রবেশ করছিল,আর ঠিক যে দিনটাতে তাদের আরাফাত ও মিনার দিকে যাত্রা করতে হয়,তখন তিনি মক্কা থেকে প্রস্থান করলেন। তিনি রওনা হয়ে গেলেন এবং ইবনে তাউসের মারফত বর্ণিত সেই বিখ্যাত ভাষণটি প্রদান করেন। এক মঞ্জিল অতিক্রম করে অন্য মঞ্জিলে পৌছিলেন এবং একসময় ইরাকের সীমান্তের নিকটবর্তী হলেন। কুফায় তখনও কি সংবাদ আল্লাহ মাবুদই ভালো জানেন। সেখানে হযরত মুসলিম ইবনে আকিলের ওপর নির্যাতনের করুণ কাহিনী ঘটে গেছে। ইমাম হোসাইন (আঃ) পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখলেন কুফার দিক থেকে আসছে। ইমাম ক্ষণিক যাত্রাবিরিত করলেন তার সাথে কথা বলার জন্যে । বলা হয় যে,ঐ লোকটি ইমাম হোসাইন (আঃ) কে চিনতো। অপরদিকে সে কুফার করুণ ঘটনার খবর রাখতো। কাজেই সে বুঝতে পারলো যে যদি ইমাম হোসাইন (আঃ) এর নিকটে যায় তাহলে ইমাম নিশ্চয় তাকে কুফার সংবাদ জিজ্ঞাসা করবেন। তখন তাকে ঐ দুঃসংবাদের কথা জানাতে হবে। সে উক্ত খবর ইমামকে বলতে চাইলো না। অগত্যা নিজের রাস্তা ঘুরিয়ে দিলো এবং অন্য পথ দিয়ে অগ্রসর হলো। বিন আসাদ গোত্রীয় দুইজন লোক যারা হজ্জ পালনের জন্যে মক্কায় ছিল এবং ইতিমধ্যে তাদের হজ্জ পালন সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল,যেহেতু তারা ইমামকে সহযোগিতা করার মনস্থ করেছিল একারণে দ্রুততার সাথে পেছন থেকে রওনা হয়েছিল ইমাম হোসাইন (আঃ) এর কাফেলায় যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ।
এরা প্রায় এক মঞ্জিল পিছিয়ে ছিল। দেখা হয়ে গেল ঐ লোকটির সাথে যে কুফা থেকে আসছিল। পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ার পর সালাম বিনিময়ের পরে আরবের প্রথা অনুযায়ী ইন্তিসাবের খবর জানতে চাইলো অর্থাৎ কে কোন গোত্রভূক্ত তার পরিচয় জানতে চাইলো। লোকটি বললো,আমি বনি আসাদ গোত্রের। তারা বললো,অবাক ব্যাপার! আমরাও তো বনি আসাদ গোত্রের! তাহলে বলো দেখি তোমার বাবা কে আর দাদা কে? সে উত্তর দিল। তারাও নিজেদের পরিচয় দিল। তখন মদীনা থেকে আসা লোক দুজন বললো,কুফার সংবাদ কি? সে বললোঃ সত্যি বলতে কি কুফার অবস্থা আসলে খুবই দুঃখজনক। ইমাম হোসাইন (আঃ) মক্কা থেকে কুফার দিকে যাচ্ছেন এবং পথিমধ্যে আমাকে দেখে তিনি থেমে যান কুফার সংবাদ নেবার উদ্দেশ্যে । কিন্তু আমি এ দুঃসংবাদ তাকে বলতে পারবো না বলে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছি। তারপর সে কুফার সব ঘটনা এ দুজনকে খুলে বললো।
তারা দুজন চলতে চলতে ইমামের কাফেলায় পৌছে যায়। প্রথম মঞ্জিলে পৌছে তারা এ ব্যাপারে মুখ খুললো না। তারা অপেক্ষা করলো যতক্ষণ না ইমাম আরেকটি মঞ্জিলে অবতরণ করলেন এবং গতকাল তারা কুফার যে লোকটির সাথে পথিমধ্যে সাক্ষাত করেছিল তখন থেকে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেল। ইমাম তাবুর ভেতরে একদল সঙ্গী সাথী নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় সে দুজন লোক সেখানে প্রবেশ করলো এবং আরজ করলো,হে ইমাম! আমাদের কাছে একটি সংবাদ রয়েছে। সেটাকে এখানেই সকলের সম্মুখে বলার অনুমতি দান করবেন নাকি আড়ালে শুনবেন? তিনি বললেন,আমি আমার সঙ্গীদের থেকে কিছুই গোপন করবো না। যে সংবাদই হোক এখানেই সকলের সামনে তা বলো। দু’ জনের একজন বললো,হে ইমাম! আমরা গতকাল যে লোকটি আপনাকে দেখে না থেমে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল তার সাথে সাক্ষাত করেছি। সে একজন আস্থাশীল লোক। আমরা তাকে চিনি। আমাদেরই স্বগোত্রীয় বনি আসাদের লোক। আমরা তাকে কুফার সংবাদ জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে খুব খারাপ সংবাদ দিল। বললো,আমি কুফা থেকে এমন অবস্থায় বের হয়েছি যখন নিজের চোখে দেখেছি যে মুসলিম ইবনে আকিল এবং হানি ইবনে উরওয়াকে শহীদ করা হয়েছে। আর তাদের লাশকে পায়ে রশি বেঁধে গলিতে আর বাজারে টেনে বেড়ানো হচ্ছিল। ইমাম হযরত মুসলিমের শাহাদাতের সংবাদ শুনলেন। তার দুচোখ অশ্রুতে ভরে গেল। সাথে সাথে তিনি এই আয়াতখানি পাঠ করলেনঃ
) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَي نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً(
অর্থাৎ,মুমীনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যু বরণ করেছে আর কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (আহযাবঃ 23)
এমন অবস্থায় ইমাম কিন্তু বললেন না যে,কুফাকে যেহেতু কব্জা করে নিয়েছে আর মুসলিম ও হানীকে যেহেতু শহীদ করে ফেলেছে কাজেই আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে। আমরা পরাজিত হয়ে গেছি। কাজেই এখান থেকেই ফিরে যাই। বরং তিনি এমন এক বাক্য বললেন যা প্রতিপন্ন করে যে ব্যাপারটা অন্য কিছু । উপরোক্ত আয়াতটি সম্ভবতঃ আহযাবের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইমাম বোঝালেন যে মুসলিম ইবনে আকিল তার কর্তব্য পালন করেছেন। এখন আমাদের পালা। কবির ভাষায়ঃ
کاروان شهيد رفت از پيش |
وان ما رفته گير و مي انديش |
‘‘ শহীদের কাফেলা আগই গেছে চলি
আমরা এখনো বেধে আছি চিন্তার খাতা খুলি’’
ইমামের একথা শুনে যারা দুর্বল চিত্তের ছিল এবং পার্থিব আশা নিয়ে ইমামের সঙ্গী হয়েছিল তারা প্রস্থান করে। (যেমনটা সব আন্দোলনেই দেখা যায়)।
لَمْ يَبْقَ مَعَهُ اِلَّا اَهْلَ بَيْتِهِ وَ صَفْوَتِهِ
অর্থাৎ তার সাথে অবিশষ্ট থেকে গেল কেবল তার আহলে বাইত ও নিষ্ঠাবান সঙ্গীদল। যাদের সংখ্যা সে সময়ে খুবই কিঞ্চিত ছিল। (খোদ কারবালায় এসে কিছুসংখ্যক লোক যারা প্রথমে ধোকার শিকার হয়েছিল এবং ওমর ইবনে সা’ দের দলে যোগ দিয়েছিল তারা একজন একজন করে জাগ্রত হয়ে ইমামের সাথে এসে যোগদান করেছিল)। হয়তো বা বড়জোর কুড়ি জনের বেশী হবে না তারা। এমন অবস্থাতেই হযরত মুসলিম ইবনে আকিল এবং হানী ইবনে উরওয়ার মর্মান্তিক শাহাদাতের খবর এসে পৌছে।‘ লিসানুল গাইব’ গ্রন্থের লেখক বলেন,কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন,ইমাম হোসাইন (আঃ) যেহেতু কোনো কিছুকেই তার সঙ্গীদের কাছে গোপন করছিলেন না,কাজেই এই খবরটি শোনার পরে সমীচিন ছিল শিশু ও নারীদের তাঁবুতেও গিয়ে মুসলিমের সংবাদটা তাদেরকে প্রদান করা যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করছিলো হযরত মুসলিমের পরিবার,তার ছোট শিশুরা,ছোট ভাইয়েরা,বোনেরা এবং আরো কতিপয় চাচাতো বোনেরা।
এখন কিভাবে ইমাম তাদেরকে এ সংবাদ জানাবেন। হযরত মুসলিমের ছোট একটি মেয়ে ছিল। ইমাম হোসাইন (আঃ) যখন বসলেন তাকে ডেকে পাঠালেন। তাকে আনা হলো। তিনি তাকে কোলে বসালেন এবং আদর করতে শুরু করলেন। কন্যাটি বুদ্ধিমতী ছিল। সে বুঝতে পারলো এ আদর কোনো সাধারণ আদর নয়। পিতৃসুলভ আদর। একারণে সে জিজ্ঞেস করলো,চাচাজী! যদি আমার বাবা মারা যান তাহলে আমাদের কি হবে? ইমাম তার একথায় বিগলিত হলেন। বললেন,মা আমার,আমি তোমার পিতার জায়গায় আছি। তার অবর্তমানে আমিই তোমার বাবার জায়গায় থাকবো। ইমাম পরিবারে কান্নার রোল পড়ে গেল। আকিলের সন্তানদের প্রতি উদ্দেশ্য করে ইমাম ঘোষণা দিলেন,হে আকিলের সন্তানেরা! তোমরা একজন মুসলিমকে উৎসর্গ করেছো। এটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট । এখন তোমরা চলে যেতে চাইেল চলে যেতে পারো। তারা প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলো,হে ইমাম! আমরা এতক্ষণ কোনো মুসলিমকে শহীদ দান করিনি তখন আপনার সাথে ছিলাম। আর মুসলিমকে দান করে এখন আমরা ছেড়ে যাব? কক্ষনোই তা হতে পারে না। আমরা আপনার খেদমতে থেকে যাবো যতক্ষণ না মুসলিমের ভাগ্যে যা ঘটেছে আমাদের ভাগ্যেও তা ঘটে।





