ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কালজয়ী বিপ্লব(৩য় খণ্ড)
 12%
12%
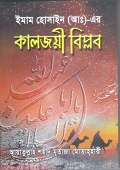 লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী
লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী
: আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
প্রকাশক: কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস -
বিভাগ: ইমাম হোসাইন (আ.)
 12%
12%
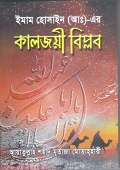 লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী
লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী
: আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
প্রকাশক: কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস -
বিভাগ: ইমাম হোসাইন (আ.)
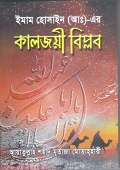


হোসাইনী আন্দোলনের প্রচারে আহলে বাইতের নারীদের ভূমিকা
হোসাইনী আন্দোলন ও ইসলাম প্রচারে সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর সম্মানিত আহলে বাইতের তথা তার পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার আগে দু’ টি ভূমিকা পেশ করা প্রয়োজন। প্রথম ভূমিকা হচ্ছে এই যে,বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুযায়ী এবং আমরা যারা ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর ইমামতের আক্কীদা পোষণ করি তাদের আক্কীদা অনুযায়ী,তিনি প্রথম দিন থেকেই যত কাজ সম্পাদন করেছেন তার সব কিছুই গভীর চিন্তাভাবনা ও নিখুঁত হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে করেছেন। তিনি বিনা চিন্তাভাবনা ও হিসাব-নিকাশে এবং বিনা কারণে কোনো অযৌক্তিক কাজ সম্পাদন করেন নি। অর্থাৎ আমরা একথা বলতে পারি না যে,তার সাথে সংশ্লিষ্ট অমুক ঘটনাটি ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছিলো। বরং সব কিছুই সুচিন্তিতভাবে ও হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছিলো। আর এ বিষয় যে ঐতিহাসিক দলীল-প্রমাণের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট শুধু তা-ই নয়,যুক্তি ,বিচার বুদ্ধি ,প্রাপ্ত রেওয়ায়েত সমূহ এবং ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর ইমামতের প্রতি আমাদের আক্কীদাও তা সমর্থন করে।
আশূরার ঘটনাবলী প্রসঙ্গে যে সব প্রশ্নে ইতিহাসবিদগণও আলোচনা করেছেন এবং দীনী সূত্রের রেওয়ায়েতও উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) তার এ বিপজ্জনক সফরে তার আহলে বাইত (পরিবার-পরিজন)কে সাথে নিয়ে গেলেন কেন? এ সফর যে এক বিপজ্জনক সফর হবে সে ব্যাপারে সকলেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অর্থাৎ এ সফর বিপজ্জনক হওয়ার বিষয় এমনকি সাধারণ লোকদের জন্যও ভবিষ্যদ্বাণী করার উর্ধ্বে ছিলো না। এ কারণে তার রওনা হবার আগে যারাই তার কাছে এসেছিলেন তাদের প্রায় সকলেই বাস্তবতার আলোকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কর্মপন্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন এবং পরিবার-পরিজনদের তার সাথে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্তকে মঙ্গল চিন্তার (مصلحت ) সাথে সাংঘর্ষিক বলে মতামত ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ তারা তাদের সাধারণ জ্ঞানস্তরের হিসাব-নিকাশ ও বুদ্ধির ভিত্তিতে এবং ইমাম হোসাইন (আঃ) ও তার পরিবার-পরিজনের প্রাণরক্ষার মানদেণ্ডের আলোকে সকলে প্রায় সর্বসম্মতভাবে বলেন,হচ্ছে ইমাম! আপনার এ যাত্রা আপনার নিজের জন্যও বিপজ্জনক,অতএব,এ সফর বাঞ্চনীয় নয়। অর্থাৎ এ সফরে আপনার নিজের জীবনই হুমকির সম্মুখীন হবে;পরিবার-পরিজন নিয়ে যাবার তো কোনোই যৌক্তিকতা নেই। ইমাম হোসাইন (আঃ) জবাব দেন,না-আমাকে অবশ্যই তাদেরকে সাথে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে সাথে নিয়ে যাওয়া তার জন্য অপরিহার্য বলে তিনি জানিয়ে দেন।
তিনি তাদেরকে এমন দৃঢ়তার সাথে জবাব দেন যে,এরপর আর তাদের পক্ষে কোনো কথা বলা সম্ভব ছিলো না। তিনি তাদের সামনে ঘটনার আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরেন। আপনারা শুনেছেন যে,ইমাম হোসাইন (আঃ) বার বার তার স্বপ্নের কথা বলেছেন যা ছিলো আল্লাহ তা‘ আলার পক্ষ থেকে তার প্রতি অকাট্য ইলহাম। তিনি বলেন, স্বপ্নের জগতে আমার নানা আমাকে বলেছেনঃ
اِنَّ اللهَ شَاءَ اَنْ يَرَاکَ قَتِيلاً
নিশ্চয় আল্লাহ চান যে,তুমি নিহত হবে।’’ ( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ ৪৪ , পৃষ্ঠাঃ ৩৬৪ , মাকতালুল হোসাইন , পৃষ্ঠাঃ ১৯৫ )
বলা হলো,যদি তা-ই হয়,তো পরিবার-পরিজন ও শিশুদেরকে সাথে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? জবাবে তিনি বললেন যে,এদেরকে নিয়ে যাওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে;বললেনঃ
اِنَّ اللهَ شَاءَ اَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَا
নিশ্চয় আল্লাহ চান যে,তারা বন্দিনী হবে।( প্রাগুক্ত )
এখানে সংক্ষেপে একটি ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। তা হচ্ছে ,এখানে ;
اِنَّ اللهَ شَاءَ اَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايَا বা اِنَّ اللهَ شَاءَ اَنْ يَرَاکَ قَتِيلاً
বাক্য দু’ টির প্রকৃত তাৎপর্য কী?
এর প্রকৃত তাৎপর্য যা,নিঃসন্দেহে ঐ সময় ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত সকলেই তা বুঝতে পেরেছিলেন। আজকে যেমন অনেকে এ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত তাৎপর্য সন্ধান করেন তার বিপরীতে প্রকৃত পক্ষে এতে কোনো প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত তাৎপর্য ছিলো না। কারণ কোরআন মজীদে আল্লাহ তা‘ আলার‘ মাশিয়্যাত’ বা‘ ইরাদাহ’ শব্দ দু’ টির প্রতিটিই দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি অর্থকে পারিভাষিকভাবে‘ ইরাদায়ে তাকভীনী’ (সৃষ্টি-ইচ্ছা) বলা হয়,আর অপরটি হচ্ছে‘ ইরাদায়ে তাশরী‘ য়ী’ (শরয়ী ইচ্ছা)।
‘ ইরাদায়ে তাকভীনী’ বলতে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত বুঝায়। অর্থাৎ আল্লাহ যখন চান যে,কোনো কাজ অবশ্যই সংঘটিত হোক সে ক্ষেত্রে এর মোকাবিলায় কারো কিছুই করার থাকে না। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আল্লাহর‘ ইরাদায়ে তাশরী‘ য়ী’ র মানে হচ্ছে এই যে,আল্লাহ পছন্দ করেন যে,বান্দা এ কাজটি করুক,কিন্তু তিনি বান্দাকে এ কাজটি সম্পাদনে বাধ্য করেন না। উদাহরণস্বরূপ,মহান আল্লাহ যখন রোযা সম্বন্ধে বলেনঃ
) يُرِيدُ اللهُ بِکُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِکُمُ الْعُسْرَ( .
‘‘ আল্লাহ তোমোদের জন্য সহজ করতে চান,কঠিন করতে চান না।’’ ( বাক্বারাঃ ১৮৫ ) অথবা অন্য কোনো প্রসঙ্গে,যেমনঃ যাকাত প্রসঙ্গে বলেনঃ
) يُرِيدُ لِيُطَهِّرَکُمْ(
‘‘ তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।’’ ( মায়িদাঃ ৬ ) এখানে মহান আল্লাহর ইরাদা বা চাওয়া মানে হচ্ছে তিনি এরূপ আদেশ দিয়েছেন তথা এ কাজের মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। অতএব,ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ইচ্ছা করেন বা চান মানে হচ্ছে আল্লাহ তার শহীদ হওয়া পছন্দ করেন,তেমনি তার পরিবার-পরিজনের বন্দী হওয়ার মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। বস্তুতঃ আল্লাহ যে কাজে সন্তুষ্ট তাতেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে প্রকৃত কল্যাণ হচ্ছে ব্যক্তি ও মানবতার পূর্ণতা।
যা-ই হোক,ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর জবাবের পর আর কেউ কোনো কথা বললেন না। অর্থাৎ কারো পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব ছিলো না। সকলের নীরব মন্তব্য যেন এই যে,প্রকৃত ব্যাপার যখন এই যে,আপনার নানা অবস্তুগত জগতে এসে আপনাকে জানিয়েছেন যে,আপনার নিহত হওয়ার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে তাহলে এর বিপরীতে আমাদের আর কিছুই বলার নেই।
যারাই ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর এ উক্তি দুটো শুনেছেন তাদের সকলেই এভাবেই বর্ণনা করেছেন;কেউই বলেন নি যে,তিনি বলেছেন,মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নিহত হওয়া নির্ধারিত হয়ে গেছে,অতএব তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ইমাম হোসাইন (আঃ) নিজেও স্বপ্নে শ্রুত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তিটির এরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করেন নি। তেমনি পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন নি যে,এ ব্যাপারে আমার কিছু করা বা না করার এখিতয়ার নেই,কারণ,এটাই নির্ধারিত হয়ে আছে। বরং তিনি বলেন যে,স্বপ্নে আমাকে যে ইলহাম করা হয়েছে তা থেকে আমি এ তাৎপর্যই গ্রহণ করেছি যে,তাদেরকে সাথে নিয়ে যাওয়াটাই আল্লাহর পছন্দ এবং তাতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আমি আমার নিজ এখতিয়ারের সাহায্যে এ কাজ সম্পাদন করছি-পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি ,তবে আমি তার ভিত্তিতেই এ কাজ করছি যা থেকে আমি এর কল্যাণময়তার উপসংহারে উপনীত হয়েছি।
এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে,অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই সকলে এক রকম ধারণা পোষণ করতেন,কিন্তু ইমাম হোসাইন (আঃ) ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন;আর তার ধারণা ছিল অত্যন্ত উচু স্তরের। সবাই যেখানে অভিন্ন অভিমতে উপনীত হতেন সেখানে ইমাম হোসাইন (আঃ) ভিন্ন অভিমতে উপনীত হতেন এবং বলতেন যে,বিষয় এ রকম নয়;আমি অন্যভাবে পদক্ষেপ নেবো।
এ থেকে সুস্পষ্ট যে,ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর কাজকর্ম ছিলো সুচিন্তিত এবং সূক্ষ্ণ ও নির্ভুল হিসাব-নিকাশি ভিত্তিক। তিনি তার ওপরে অর্পিত বিশেষ দায়িত্ব পালন করছিলেন। তেমনি তিনি তার পরিবার-পরিজনকে স্বীয় পোষ্য হিসেবে সাথে নিয়ে যান নি। তিনি এরূপ চিন্তা করেন নি যে,আমি যখন যাচ্ছি তখন আমার পরিবার-পরিজনকে কী করবো,কোথায় কার কাছে রেখে যাবো? তার চেয়ে বরং সাথে নিয়ে যাওয়াই ভালো।
ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে মাত্র তিন ব্যক্তি ছাড়া কেউই স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে নিয়ে যান নি। বস্তুতঃ কোনো ব্যাক্তি যখন কোনো বিপজ্জনক সফরে যায় তখন সে তার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সাথে নিয়ে যায় না। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আঃ) তার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তার সাথে নিয়ে গেলেন। তবে এ চিন্তা থেকে তাদেরকে সাথে নিয়ে যান নি যে,আমি যখন যাচ্ছি তখন আমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকেও সাথে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কী! (উদ্দেশ্য,ইমাম হোসাইন (আঃ) মদীনায় বসবাস করতেন;মক্কায় তার কোনো বাড়ীঘর ছিলো না।) বরং তিনি কেবল এ কারণে তাদেরকে সাথে নিয়ে যান যে,তাদেরকে একটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে।
এই হলো একটি ভূমিকা। দ্বিতীয় ভূমিকাটি হচ্ছে‘ ইতিহাসে নারীর ভূমিকা’ প্রসঙ্গ। প্রশ্ন তোলা হয় যে,মূলগতভাবেই ইতিহাস বিনির্মাণে নারীর কোন ভূমিকা আছে, নাকি নেই ? আসলে নারীর পক্ষে কি ইতিহাসে কোনো ভূমিকা পালন করা সম্ভব ? তাদের কি ইতিহাস বিনির্মাণে কোনো কোনো ভূমিকা পালন করা উচিৎ,নাকি উচিৎ নয়? তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতে কীভাবে এ বিষয়টির মূল্যায়ন করা হবে?
ইতিহাসে সব সময়ই নারী একটি ভূমিকার অধিকারী ছিলো এবং এখনো রয়েছে;কেউই নারীর এ ভূমিকা অস্বীকার করে নি। তা হচ্ছে ইতিহাস সৃষ্টিতে নারীর পরোক্ষ ভূমিকা। বলা হয়,নারী পুরুষকে তৈরী করে আর পুরুষ ইতিহাস তৈরী করে। এর মানে হচ্ছে নারীকে গড়ে তোলার ব্যাপারে পুরুষের ভূমিকা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ পুরুষকে গড়ে তোলার ব্যাপারে নারীর ভূমিকা তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা বড় ধরনের প্রশ্ন যে,পুরুষ নারীর চেতনা,মন-মানস ও ব্যক্তিত্ব তৈরী করে দেয় কি না,তা মা হিসেবেই হোক বা স্ত্রী হিসেবেই হোক? নাকি নারীই তার সন্তানদেরকে,এমনকি স্বামীকে গড়ে তোলে? বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, স্বামীকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভূমিকা বেশী,নাকি স্ত্রীকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্বামীর ভূমিকা বেশী? বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে,ইতিহাস গবেষণা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে যা প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে ,নারীর ব্যক্তিত্ব গঠনে পুরুষের ভূমিকা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ সে তুলনায় পুরুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে নারীর ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে ইতিহাস সৃষ্টিতে নারীর পরোক্ষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। নারী যে পুরুষকে গড়ে তুলেছে এবং পুরুষ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেল তা হবে এক সুদীর্ঘ আলোচনা।
এবার আমরা দেখবো যে,ইতিহাস দৃষ্টিতে নারীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা কী ধরনের এবং কী ধরনের হওয়া উচিৎ ও কী ধরনের হওয়া সম্ভব। এ ব্যাপারে একটি অবস্থা হতে পারে এই যে,মূলগতভাবেই ইতিহাস দৃষ্টিতে নারীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকতে পারে অর্থাৎ নারীর ভূমিকা পুরোপুরি নেতিবাচক হতে পারে। বিশ্বের অনেক মানব সমাজে সন্তান জন্মদান,লালন-পালন ও গৃহের অভ্যন্তরের বিষয়াদি পরিচালনা ছাড়া নারীর পালনীয় আর কোনো ভূমিকা থাকতে পারে বলে মনে করা হয় না। অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজে নারীর কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই,কেবল পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। অতএব,এরুপ সমাজে নারীর ভূমিকা পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ আর পরিবারে গড়ে ওঠা পুরুষের ভূমিকা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ নারী অনেক সমাজেই পুরুষের মাধ্যমে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করা ছাড়া সমাজে কোনোরূপ প্রত্যক্ষ ভূমিকার অধিকারী নয়।
কিন্তু এ ধরনের সমাজ সমূহে নারী যে ইতিহাস ও সমাজ গঠনে কোনোরূপ প্রত্যক্ষ ভূমিকার অধিকারী ছিলো না,শুধু তা-ই নয়,বরং নিঃসন্দেহে এবং এ ব্যাপারে পরিচালিত প্রচারের বিপরীতে নারী একটি মূল্যবান জিনিস রূপে অস্তিত্বমান থাকতো। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি হিসেবে সে খুবই সামান্য ভূমিকার অধিকারী ছিলো,কিন্তু সে ছিলো একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। আর সে এভাবে মূল্যবান জিনিস হবার কারণেই পুরুষের ওপর তার ভূমিকার প্রভাব ছিলো। সে এমন সস্তা ছিলো না যে পথে ঘাটে ছড়িয়ে থাকবে এবং তার থেকে সুবিধা হাসিলের জন্য শত সহস্র পাবলিক প্লেস বা উদ্যান থাকবে। বরং কেবল পারিবারিক জীবনের বৃত্তের মধ্যেই তার কাছ থেকে সুবিধা লাভ করা সম্ভব ছিলো। অতএব,অনিবার্যভাবেই পরিবারের পুরুষ সদস্যের জন্য সে ছিলো একটি অত্যন্ত মূল্যবান অস্তিত্ব । কারণ,সে ছিলো একমাত্র অস্তিত্ব যে পুরুষের যৌন ও স্নেহ-মমতার প্রয়োজন পূরণ করতো। অতএব,অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কার্যতঃ পুরুষ তার খেদমতে নিয়োজিত থাকতো। কিন্তু নারী ছিলো একটি জিনিস,একটি মূল্যবান জিনিস,ঠিক যেমন হীরা একটি মূল্যবান রত্ন। তবে সে ব্যক্তি ছিলো না,সে ছিলো একটি জিনিস একটি মূল্যবান জিনিস।
ইতিহাসে নারীর অন্য এক ধরনের ভূমিকাও ছিলো এবং প্রাচীন সমাজে নারীর এ ধরনের ভূমিকা অনেক দেখা যায়। তা হচ্ছে ,নারী ইতিহাসে প্রভাব বিস্তারকারী এক উপাদান রূপে ভূমিকা পালন করেছে। সে ইতিহাসে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে এবং ব্যক্তি হিসেবে এ ভূমিকা পালন করেছে,জিনিস হিসেবে নয়। কিন্তু সে ছিলো মূল্যহীন ব্যক্তি-যার ও পুরুষের মধ্যকার সম্মানার্হ দেয়াল (حریم ) তুলে নেয়া হয়েছিলো। সুক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে,নারীকে প্রিয় করে তোলা ও রাখার জন্য তার মনস্তাত্ত্বিক গঠনকে অত্যন্ত সূক্ষ্ণভাবে পরিকল্পনা করে তৈরী করা হয়েছে। আর যখনই এ সীমারেখা উঠে গেছে এবং এ সম্মানার্হ দেয়াল পুরোপুরি ধ্বসে পড়েছে তখনই সম্মান,মর্যাদা ও সম্ভ্রমের বিচারে নারীর ব্যক্তিত্ব নীচে নেমে এসেছে। অবশ্য অন্য কোনো দিক থেকে তার ব্যক্তিত্ব উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়ে থাকতে পারে,যেমনঃ সে শিক্ষিতা হয়েছে,সে জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞানী হয়েছে,কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরুষের কাছে সে যেরূপ মহামূল্য অস্তিত্ব ছিলো অতঃপর আর তা থাকে নি।
অন্যদিকে নারী নারী না হয়ে পারে না। নারীর প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে,সে পুরুষের জন্য অত্যন্ত মহামূল্য হবে। আর নারীর প্রকৃতি থেকে এ বৈশিষ্ট্যটি যদি বিলুপ্ত করে দেয়া হয় তাহলে নারীর গোটা চেতনাই বিলুপ্ত হয়ে পড়তে বাধ্য । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের কাছে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে একটি মহামূল্য অস্তিত্ব হিসাবে নারীকে নিজের এখতিয়ারে পাওয়া;নারী তার জন্য একটি মহামূল্য অস্তিত্ব বিধায় নিজেকে তার এখতিয়ারে সোপর্দ করা পুরুষের লক্ষ্য নয়। অন্য দিকে নারীর প্রকৃতিতে যা নিহিত তা এটা নয় যে,পুরুষ তাকে একটি মহামূল্য অস্তিত্ব হিসাবে স্বীয় এখতিয়ারে নিয়ে নিক। বরং তার প্রকৃতির দাবী হচ্ছে এই যে,একটি মহামূল্য অস্তিত্ব হিসেবে সে-ই পুরুষকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে।
নারী যখন তার বিশেষ অবস্থা থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হলো (এজন্য প্রচলিত বিবাহ প্রথা পরিত্যাগ অপরিহার্য নয়),অর্থাৎ নারী যখন সস্তা হয়ে গেলো,তাদেরকে প্রকাশ্য জায়গাগুলোতে ব্যাপকভাবে দেখা গেলো,সস্তা পুরুষদের দ্বারা তাদেরকে ব্যবহারের জন্য হাজারো উপায় উদ্ভাবিত হলো,রাস্তাঘাট ও অলি গলি নারীর প্রদর্শনীস্থলে পরিণত হলো যেখানে নারী নিজেকে পুরুষের কাছে প্রদর্শন করতে পারে এবং পুরুষ নারীর শরীরের যৌন আকর্ষণীয় অঙ্গ– প্রত্যঙ্গসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করার ও তাকিয়ে দেখার,নারীর বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর শোনার ও তাকে স্পর্শ করার সুযোগ পেলো এবং এভাবে তাকে সস্তায় সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহারের সুযোগ পেলো তখন নারী তার মূল্য-পুরুষের কাছে তার যে মূল্য থাকা উচিৎ ছিলো সে মূল্য-হারিয়ে ফেললো। অর্থাৎ অতঃপর আর নারী পুরুষের কাছে মহামূল্য অস্তিত্ব নেই,যদিও হতে পারে যে,সে অন্য অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে গেছে,উদাহরণস্বরূপ,সে শিক্ষিতা হয়েছে,পড়াশুনা করেছে,সে শিক্ষিকা হতে পারে,ক্লাস নিতে পারে,সে ডাক্তার হয়ে থাকতে পারে। সে এর সব কিছুই হতে পারে,কিন্তু এ অবস্থায় অর্থাৎ সে যখন সস্তা হয়ে যায়,তখন একজন নারীর প্রকৃতিতে যে মূল্য নিহিত রয়েছে সে মূল্য আর তার থাকে না। প্রকৃত পক্ষে এহেন অবস্থায়ই নারী পুরুষ সমাজের কাছে ভিন্ন এক ধরনের খেলনায় পরিণত হয়,কিন্তু পুরুষ সমাজের একজন সদস্যের কাছে তার যে মর্যাদা ও সম্মান থাকা উচিৎ তা আর থাকে না।
ইউরোপীয় সমাজ এদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে । অর্থাৎ সেখানে একদিকে যেমন নারীর জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছা ইত্যাদি কতগুলো মানবিক প্রতিভা ও সম্ভাবনার বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে ব্যক্তিত্ব প্রদান করা হয়েছে,অন্য দিকে তার মূল্যও গুরুত্বের বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে।
এ দুই অবস্থার বাইরে একটি তৃতীয় অবস্থারও অস্তিত্ব রয়েছে। তা হচ্ছে,নারী একজন‘ মহামূল্যবান ব্যক্তি’ হিসেবে গড়ে উঠবে। সে একদিকে যেমন হবে ব্যক্তি অন্যদিকে একই সাথে হবে মহামূল্য । অর্থাৎ একদিকে সে চৈন্তিক,নৈতিক ও আত্মিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে,জ্ঞান,সচেতনতা ইত্যাদি আত্মিক ও মানিবক পূর্ণতার অধিকারী হবে। বলা বাহুল্য যে,জ্ঞান ও সচেতনতা নারীর ব্যক্তিত্বের অন্যতম স্তম্ভ এবং স্বাধীন এখতিয়ারের অধিকারী হওয়া,ইচ্ছার অধিকারী থাকা,শক্তিশালী মনের অধিকারী হওয়া ও সাহসী হওয়া তার ব্যক্তিত্বের অপর একটি স্তম্ভ। সৃজনশীলতা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো মানুষের মানসিক ব্যক্তিত্বের আরেকটি স্তম্ভ। ইবাদতকারিনী হওয়া,স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সাথে সরাসরি সম্পর্ক থাকা ও তার অনুগত থাকা,তার সাথে এমনকি অত্যন্ত উচু স্তরের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক থাকা-যে স্তরের সম্পর্ক ছিলো নবী-রাসূলগণের (আঃ)-এ সব হচ্ছে সেই সব বৈশিষ্ট্য যা নারীকে ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে। অন্যদিকে নারী সামাজিক অঙ্গনে অশ্লীলভাবে উপস্থিত হবে না ও অশ্লীলতার কারণ হবে না। অর্থাৎ কোনো কোনো সমাজে নারীর ওপরে যে কঠোর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে তার ওপর সে সীমাবদ্ধতা যেমন থাকা উচিৎ নয়,তেমনি তার জন্য পুরুষের সাথে মিশে যাওয়াও উচিৎ নয়। না নারীর জন্য কঠোর সীমাবদ্ধতা থাকবে,না অবাধ মেলামেশা থাকবে,বরং উভয়ের মাঝে এক সম্মানার্হ সীমারেখা থাকবে। সম্মানার্হ সীমারেখা (حریم ) হচ্ছে নারীর ওপরে কঠোর সীমাবদ্ধতা আরোপ ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা-এই দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ একটি অবস্থা।
আমরা যখন এ ব্যাপারে ইসলামী সূত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন আমরা দেখতে পাই যে,ইসলাম নারীর ব্যাপারে যা চায় তা হচ্ছে ,সে যেমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে তেমনি সে হবে মহামূল্য । তার এই ব্যক্তিত্ব ও মহামূল্যতার কারণেই ইসলামী সমাজে লজ্জাশীলতা ও শালীনতা বিরাজ করে এবং মনগুলো নির্মল ও সুস্থ থাকে,সমাজের বুকে পরিবার রূপ সংগঠনগুলো টিকে থাকে এবং সব দিক থেকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুস্থ মানসিকতার অধিকারী মানুষ গড়ে ওঠে।
ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মহামূল্য হওয়ার মানে হচ্ছে এই যে,ইসলাম তার ও পুরুষের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে তা উভয়ের জন্যেই সম্মানার্হ। অর্থাৎ ইসলাম এর অনুমতি দেয় না যে,পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে অর্থাৎ সমাজের মঞ্চে নারীর কাছ থেকে পুরুষের সুবিধা গ্রহণ তথা যৌন আস্বাদনের সুযোগ থাকবে,তা সেটা পুরুষ কর্তৃক নারীর শরীর ও যৌন উদ্দীপক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাতই হোক,বা তার শরীর স্পর্শ করাই হোক,তার শরীরের সুবাস গ্রহণই হোক বা তার পায়ের ধ্বনি (প্রচলিত কথায় যা উচ্ছাস সৃষ্টিকারী) শুনেই হোক। ইসলাম এগুলোকে অনুমোদন দেয় না। প্রশ্ন উঠতে পারে,জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা,এখতিয়ার ও ইচ্ছাশক্তি,ঈমান ও ইবাদত,শিল্পকলা,সৃজনশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম কী বলে? হ্যাঁ,এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। ইসলাম নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে কতগুলো কাজকে হারাম করেছে,কিন্তু যে সব কাজ হারাম করে নি তা কারো জন্যই হারাম করে নি। বস্তুতঃ ইসলাম নারীর জন্য ব্যক্তিত্ব চায়, তবে তার জন্য অশ্লীলতা চায় না।
অতএব,ইতিহাস গঠনে কেবল পুরুষের ভূমিকা ছিলো অথবা নারী ও পুরুষ উভয়ের পারস্পরিক ভূমিকা ছিলো-এ বিষয়টির তিনটি রূপ পাওয়া যেতে পারে। একটি হচ্ছে এই যে,ইতিহাস মানেই পুরুষের ইতিহাস অর্থাৎ যে ইতিহাস সরাসরি পুরুষদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে-যাতে নারীদের কোনোই ভূমিকা নেই।
আরেকটি ইতিহাস হচ্ছে নারী ও পুরুষের যৌথভাবে গড়ে তোলা ইতিহাস,তবে সেখানে নারী ও পুরুষ সংশ্রিত;সেখানে পুরুষ তার অক্ষের সীমারেখার মধ্যে থাকবে এবং নারী তার অক্ষের সীমারেখার মধ্যে থাকবে এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ তা এমন এক ইতিহাস যেখানে এসে এ ছন্দের পতন ঘটেছে। পুরুষরা নারীর বৃত্তে অবস্থান নিয়েছে এবং নারীরাও পুরুষের বৃত্তে অবস্থান নিয়েছে। আমরা যদি বর্তমান যুগের কতক ছেলে ও মেয়ের বা নারী ও পুরুষের পোশাকের ধরনের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই কীভাবে তারা পরস্পরের জায়গাকে বদল করেছে।
আর তৃতীয় ধরনের ইতিহাস হচ্ছে নারী ও পুরুষের ইতিহাস যে ইতিহাস একদিকে যেমন পুরুষের হাতে গড়ে উঠেছে,তেমনি তা নারীর হাতেও গড়ে উঠেছে। তবে পুরুষ তার অক্ষের সীমারেখার ভিতরে থেকেছে এবং নারীও তার অক্ষের সীমারেখার ভিতরে থেকেছে। আমরা যখন কোরআন মজীদে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখতে পাই যে,পবিত্র কোরআন ধর্মের ইতিহাসকে যেভাবে তুলে ধরেছে তা নারী ও পুরুষের এক যৌথ ইতিহাস,সে ইতিহাসে নারী ও পুরুষের সংমিশ্রণ নেই,বরং পুরুষ নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ভূমিকা পালন করেছে এবং নারী তার নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ভূমিকা পালন করেছে।
কোরআন মজীদ তার নির্বাচিত ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে একই সাথে ইতিহাসের সত্যপন্থী ও পবিত্র পুরুষদের কথা বলেছে এবং ইতিহাসের সত্যপন্থী ও পবিত্র নারীদের কথা বলেছে। হযরত আদম (আঃ) ও তার স্ত্রীর কাহিনীতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রণিধানযোগ্য বিষয় রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা অপরিহার্য মনে করি।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে নয় যে,খৃষ্টানরা বিশ্বের ধর্মীয় ইতিহাসে অত্যন্ত ভুল একটি ধারণা প্রবিষ্ট করিয়েছে যা প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য । [আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিবাহ না করার যুক্তিতে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের বিবাহ বর্জন ও কৌমার্য ব্রত গ্রহণ এ ধারণাকে শক্তিশালী করেছে।] খৃষ্টানদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এরূপ ধারণা তৈরী হয়ে যায় যে,মূলগতভাবেই নারী হচ্ছে পাপ ও প্রতারণার হাতিয়ার তথা ছোট শয়তান। পুরুষ লোক নিজে নিজেই তথা স্ব-উদ্যোগে পাপকার্যে লিপ্ত হয় না,বরং নারী হচ্ছে ছোট শয়তান-যে সব সময় পুরুষকে কুমন্ত্রণা দেয় ও তাকে পাপকার্যে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। তারা বলে যে,মূলতঃ আদম ও হাওয়ার ঘটনা এভাবে শুরু হয় যে,শয়তান আদমেক প্রভাবিত করতে পারছিলো না,তাই সে হাওয়ার কাছে এসে তাকে প্রতারিত করে এবং হাওয়া আদমকে প্রতারিত করেন। আর মানব জাতির গোটা ইতিহাস জুড়ে সব সময়ই এমনই ঘটেছে যে,বড় শয়তান নারীকে ও নারী পুরুষকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে।
বস্তুতঃ খৃষ্টানদের মধ্যে হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী এভাবেই প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদ এর বিপরীত কথা বলে,আর যারা তা জানে না তাদের কাছে তা বিস্ময়কর বলে মনে হতে পারে।
কোরআন মজীদ যখন হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করে তখন কাহিনীর মূলনায়ক হিসেবে হযরত আদম (আঃ)কে তুলে ধরেছে এবং হযরত হাওয়া (আঃ) কে দেখিয়েছে তার অনুসরণকারী হিসেবে। মহান আল্লাহ প্রথমে বলেন যে,আমি তাদের উভয়কে (শুধু আদমকে নয়) বললাম যে,তোমরা বেহেশতে বসবাস করো,তবে
) لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ(
‘‘ তোমরা দু’ জন এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না।” ( বাক্বারাঃ ৩৬ ) (সে বৃক্ষটি যে বৃক্ষই হোক না কেন তা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।) এরপর আল্লাহ বলেনঃ .
) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ(
‘‘ অতঃপর শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিলো।’’ ( আ ‘ রাফঃ ১৯ )
এখানে কোরআন বলেনি যে,শয়তান তাদের একজনকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলো এবং তিনি অপর জনকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলেন। অতঃপর কোরআন বলেঃ
) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ(
‘‘ এরপর সে উভয়ের নিকট প্রতারণা মূলক যুক্তি উপস্থাপন করলো।’’ ( আ ‘ রাফঃ ২১ ) এখানে দ্বিবচন বাচকهما সর্বনামটির ব্যবহার প্রণিধানযোগ্য অর্থাৎ সে যা বলে প্রতারণা করতে চাচ্ছিলো তা উভয়ের সামনে উপস্থাপন করেছিলো।
আর قَاسَمَهُمَا اِنِّی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ “ সে তাদের উভয়ের কাছে কসম খেয়ে বললো যে,অবশ্যই আমি তোমাদের উভয়ের কল্যাণকামীদের অন্যতম।’’ ( আ ‘ রাফঃ ২০ ) এখানেও‘ তাদের উভয়ের’ (هُمَا ) ও‘ তোমাদের উভয়ের’ (کما ) সর্বনামের ব্যবহার প্রণিধানযোগ্য । এ থেকে সুস্পষ্ট যে,এ ব্যাপারে হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) উভয়ের বিচ্যুতির পরিমাণ সমান।
এ ঘটনার ধর্মীয় ইতিহাসে যে ভ্রান্ত চিন্তা স্থান দেয়া হয়েছে এবং যে মিথ্যা রচনা করা হয়েছে ইসলাম তাকে অপসারিত করেছে এবং সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে,মহান আল্লাহর নিষেধ না মানার ঘটনা এমন নয় যে,শয়তান নারীকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে আর নারী পুরুষকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে,অতএব,নারী মানে পাপের হাতিয়ার। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোরআন মজীদ মহান পবিত্র পুরুষদের কথা উল্লেখের পাশাপাশি মহান পবিত্রা নারীদের কথা উল্লেখ করেছে এবং তাদের সকলেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে পবিত্র পুরুষ ব্যক্তিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনীতে হযরত সারাহ (আঃ) কে কতই না প্রশংসিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে! হযরত ইবরাহীম (আঃ) যেভাবে ফেরেশতাদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্কের অধিকারী ছিলেন এবং তাদেরকে দেখতে পেতেন ও তাদের কথা শুনতে পেতেন হযরত সারা (আঃ) ও একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। ফেরেশতা যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে বললো যে,আপনাদের প্রতিপালক আপনাদেরকে সন্তান দিতে ইচ্ছা করেছেন তখন হযরত সারা তা একইভাবে শুনতে পেলেন এবং বিস্মিত হয়ে বললেনঃ
) اَ اَلِدُ وَ اَنَا عَجُوزٌ وَ هَذَا بَعْلِی شَيْخاً( .
‘‘ আমাদের কি সন্তান হবে যখন আমি বন্ধ্যা আর এই আমার স্বামী বৃদ্ধ !’’ ( হুদঃ ৭২ ) ফেরেশতা তখন হযরত সারা (আঃ) কে সম্বোধন করে জবাব দেয়,হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে সম্বোধন করে নয়,বলেঃ
) اَ تَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ الله(
‘‘ আপন কি আল্লাহর কাজে বিস্মিত হচ্ছেন?’’ ( হুদঃ ৭৩ ) একইভাবে মহান আল্লাহ কোরআন মজীদে যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর মায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তখন বলেনঃ
) وَ اَوْحَيْنَا اِلَی اُمِّ مُوسَی اَنْ اَرْضِعِيه(
‘‘ আর আমরা মূসার মাকে ওহী করলাম যে,তাকে (মূসাকে) দুধ পান করাও।’’ ( আল - ক্বাছাছঃ ৭ ) আল্লাহ তা‘ আলাও হযরত মূসা (আঃ)-এর মাকে সম্বোধন করে ওহী মারফত আরো বলেনঃ
) فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِی الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِی وَ لَا تَحْزَنِی اِنَّا رَادُّوهُ اِلَيْکَ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ( .
‘‘ আর তুমি যখন তার ব্যাপারে ভয় করবে তখন তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও আর তার ব্যাপারে ভয় করো না ও দুশ্চিন্তা করো না;নিঃসন্দেহে আমরা তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো। আর অবশ্যই আমরা তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করেছি।’’ ( প্রাগুক্ত আয়াত )
কোরআন মজীদ হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর কাহিনী বলতে গিয়ে বিস্ময়কর সব তথ্য উপস্থাপন করেছে। নাবীগণ (আঃ) পর্যন্ত এ মহীয়সী নারীর মর্যাদার কাছে শ্রদ্ধায় নতজানু হন। তার খালু হযরত যাকারিয়া (আঃ) যখন তার কাছে আসনে তখন দেখতে পান যে,মাইয়ামের কাছে এমন সব নে‘ আমত (তাজা ফলমূল) রয়েছে যা সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের কোথাও পাওয়া যায় না। তাই তিনি বিস্মিত হন। কোরআন মজীদ বলে,মারইয়াম যখন মেহরাবে ইবাদতে রত ছিলেন তখন ফেরেশতারা এসে তার সাথে কথা বলে।
) اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللهَ يُبَشِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَی بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِی الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ(
‘‘ ফেরেশতারা যখন বললোঃ হে মারইয়াম! অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে তার পক্ষ থেকে তার এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন যার নাম ঈসা মসী ইবনে মারইয়াম-যিনি এই দুনিয়ায় ও পরকালে অত্যন্ত সম্মানিত এবং তিনি (আল্লাহ তা‘ আলার) নৈকট্যের অধিকারীদের অন্যতম।’’ ( আল ‘ ইমরানঃ ৪৫ )
এখানে দেখা যাচ্ছে যে,ফেরেশতারা সরাসরি হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর সাথে কথা বলছে। হযরত মারইয়াম (আঃ) কে নবী হিসেবে পাঠানো হয় নি। আল্লাহ এ নিয়ম করেন নি যে,একজন নারীকে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবেন। তাই হযরত মারইয়াম (আঃ)-এর এত বড় মর্যাদা সত্ত্বেও তাকে নবী হিসেবে পাঠানো হয় নি,কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মর্যাদা ছিলো অনেক নবীর (আঃ) চেয়ে উচ্চতর। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে,হযরত যাকারিয়া (আঃ) নবী হওয়া সত্ত্বেও এবং হযরত মারইয়াম (আঃ) নবী না হওয়া সত্ত্বেও মারইয়াম (আঃ)-এর মর্যাদা যাকারিয়া (আঃ)-এর চেয়ে বেশী ছিলো।
মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সম্বোধন করে হযরত ফাতেমা (আঃ) সম্বন্ধে কোরআন মজীদে এরশাদ করেনঃ
) اِنَّا اَعْطَيْنَاکَ الْکَوْثَرَ(
‘‘ অবশ্যই আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি।’’ ( আল - কাওছারঃ ১ )
বস্তুতঃ একজন নারীর মর্যাদা তুলে ধরার জন্য তাকে‘‘ কাওছার’’ হিসেবে অভিহিত করার চেয়ে উন্নততর আর কোনো পরিভাষা পাওয়া যেতে পারে না। যে দুনিয়ায় নারীকে নিরঙ্কুশ অনিষ্ট বলে গণ্য করা হতো এবং তাকে প্রতারণা ও পাপের হাতিয়ার মনে করা হতো সেই দুনিয়ায় কোরআন মজীদ একজন নারী সম্পর্কে বলছে,না,সে কল্যাণের আকর;সে শুধু কল্যাণের আকরই নয়,বরং সে হচ্ছে‘ কাওছার’ -বিপুল কল্যাণের আকর;দুনিয়াজোড়া কল্যাণের উৎস।
এ প্রসঙ্গে আসুন আমরা ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হবার পর সেই প্রথম দিনেই দুই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা হলেনঃ হযরত আলী (আঃ) ও হযরত খাদীজা (আঃ)। তাদের উভয়ই ইসলামের ইতিহাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হিজরতের দেড়শ’ বছর পরে ইবনে ইসহাক যে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন তাতে তিনি হযরত খাদীজার মর্যাদা এবং নবী করীম (সাঃ)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তার ভূমিকা,বিশেষ করে তার সান্তনাদায়ক ভূমিকা তুলে ধরেছেন। ইবনে ইসহাক লিখেছেন,হযরত খাদীজার ইন্তেকালের পর-যে বছর হযরত আবু তালেবও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন,সত্যি সত্যিই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য দুনিয়া সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ) যখনই হযরত খাদীজার নাম উল্লেখ করতেন তখনই তার পবিত্র চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরে যেতো। হযরত আয়শা বলেনঃ‘‘ একজন বৃদ্ধার গুরুত্ব তো এত বেশী নয়;কী ব্যাপার!’’ জবাবে নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ‘‘ তুমি কি মনে করছো যে,আমি খাদীজার শরীরের জন্য কান্না করছি? কোথায় খাদীজা,আর কোথায় তুমি ও অন্য সকলে!’’
আপনারা যদি ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে,ইসলামের ইতিহাস হচ্ছে নারী-পুরুষের ইতিহাস। তবে এ ইতিহাসে পুরুষ তার অক্ষের চারদিকে এবং নারী তার অক্ষের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যেমন পুরুষ সাহাবী ছিলেন তেমনি নারী সাহাবীও ছিলেন। এখন থেকে হাজার বছর পূর্বে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাতে যেমন পুরুষ বর্ণনাকারীর (راوی ) বর্ণিত হাদীস ও রেওয়ায়েত নেয়া হয়েছে তেমনি নারী বর্ণনাকারীর (راوی ) বর্ণিত হাদীস ও রেওয়ায়েত রয়েছে। আমাদের কাছে এমন বিপুল সংখ্যক হাদীস ও রেওয়ায়েত এসেছে যার বর্ণনাকারী নারী। একটি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে যার নাম“ বালাগ্বাতুন নেসা” যাতে নারীদের প্রাঞ্জল ও সুউচ্চ সাহিত্যিক মানসম্পন্ন ভাষণ স্থানলাভ করেছে। বাগদাদী হিজরী ২৫০ সালের দিকে-হযরত ইমাম হাসান‘ আসকারী (আঃ)-এর জীবদ্দশায় এ গ্রন্থটি সংকলিত করেন। (স্মর্তব্য ,ইমাম হাসান আসকারী হিজরী ২৬০ সালে শহীদ হন।) বাগদাদী তার এ গ্রন্থে যে সব ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে ইবনে যিয়াদের মজলিসে ইয়াযীদের মসজিদে প্রদত্ত হযরত যায়নাব (আঃ)-এর ভাষণ এবং হযরত আবু বকরের খেলাফতের শুরুর দিকে মসজিদে নববীতে প্রদত্ত হযরত ফাতেমা যাহরা (সাঃ আঃ)-এর ভাষণ অন্যতম।
সাম্প্রতিক কালে হযরত মা‘ ছূমা (আঃ) (হযরত ফাতেমা মা‘ ছূমা (আঃ) ছিলেন হযরত ইমাম মূসা কাযেম (আঃ)-এর কন্য ও হযরত ইমাম রেযা (আঃ)-এর বোন। ইরানের দ্বীনী জ্ঞানকেন্দ্র কোম নগরীতে তার মাযার রয়েছে এবং তার মাযারকে কেন্দ্র করেই কোম ইরানের অন্যতম জ্ঞান নগরীতে পরিণত হয়েছে)-এর মাযারের জন্য যে নতুন রেলিং তৈরী করা হয়েছে তার ওপর যেসব হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার সবগুলোর বর্ণনাকারীই হচ্ছেন নারী-যেসব হাদীসের বর্ণনা হযরত নবী করীম (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখানে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার এই যে,এজন্য কেবল সেই সব হাদীস বেছে নেয়া হয়েছে যেগুলোর বর্ণনাকারীদের সকলের নামই ফাতেমা এবং তাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ জন। বর্ণনার ধারাক্রম এরূপ যে,অমুকের কন্যা ফাতেমা অমুকের কন্যা ফাতেমা থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি অমুকের কন্যা ফাতেমা থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে তা ফাতেমা বিনতে মূসা ইবনে জা‘ ফর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরপর এর ধারাবাহিকতা এগিয়ে চলে ফাতেমা বিনতে হোসাইন বিন আলী বিন আবি তালেব এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত নবী-তনয়া হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে।
এ থেকেই বুঝা যায় যে,নারীদের হাদীস শ্রবণ ও জ্ঞান আহরণের বিষয়টি কতখানি প্রচলিত ছিলো। কিন্তু তারা কখনোই অবাধ মেলামেশা করতেন না। অনেক বর্ণনাকারীই হাদীস বর্ণনা করেছেন যাদের কাছ থেকে নারী ও পুরুষ উভয়ই হাদীস শ্রবণ করেছেন। তবে নারীরা এক পাশে বসতেন এবং পুরুষরা আরেক পাশে বসতেন;কখনোবা নারীরা একটি কক্ষে এবং পুরুষরা অন্য একটি কক্ষে বসতেন। তারা এজন্য আসতেন না যে,এমনভাবে চেয়ার পাতা হবে যে,একজন নারী ও একজন পুরুষ পাশাপাশি বসবে এবং নারী এমনভাবে মিনি স্কার্ট পরিধান করবে যে,তার উরুর উর্ধাংশ পর্যন্ত দেখা যাবে। হ্যাঁ,বলা হয় যে,মহিলা জ্ঞানার্জনের জন্য এসেছেন। বুঝাই যায় যে,বাইরে এক ও ভিতরে অন্য কিছু । এর বিপরীতে ইসলাম জ্ঞানার্জনের কথা বলে। বলে,এমন পরিবেশে জ্ঞানচর্চা করতে হবে যার সাথে প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থ করার সংযোগ থাকবে না, প্রতারণা থাকবে না,থাকবে ব্যক্তিত্বের পরিচয়।
হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ) ও হযরত আলী (আঃ)-এর মধ্যে বিবাহ হওয়ার পর তারা তাদের সংসারের কাজগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে চাইলেন। কিন্তু তারা চাচ্ছিলেন যে,রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই তা ভাগ করে দিবেন। কারণ,এটা তাদের কাছে আনন্দজনক হবে বলে তারা মনে করছিলেন। তাই তারা তার কাছে গেলেন এবং বললেন,হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মন চায় যে,আপনি আমাদের সংসারের কাজগুলো আমাদের দু’ জনের মধ্যে ভাগ করে দিন;বলে দিন কে কোন কাজ করবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘরের বাইরের কাজগুলো হযরত আলীর জন্য এবং ঘরের ভিতরের কাজগুলো হযরত ফাতেমার জন্য নির্ধারণ করে দিলেন। হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ) বলেন,তোমরা জানো না যে,আমার পিতা বাইরের কাজগুলোর দায়িত্ব থেকে আমাকে রেহাই দেয়ায় আমি কত খুশী হয়েছি। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী নারী এমনই যিনি লোভ বা ঈর্ষা করবেন না।
এবার লক্ষ্য করুন এই যে হযরত ফাতেমা যাহরা,তার ব্যক্তিত্ব কেমন ছিলো? তার ভিতরে নিহিত সম্ভাবনা ও প্রতিভার বিকাশ কী ধরনের ছিলো? তার জ্ঞান কোন পর্যায়ের ছিলো? তার ইচ্ছা শক্তি কেমন ছিলো? তার ভাষণ ও বক্তব্যে প্রঞ্জলতা কেমন ছিলো?
হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ) খুব কম বয়সে দুনিয়া ত্যাগ করেন। আর ঐ সময় তার দুশমনের সংখ্যা ছিলো অনেক। এ কারণে তার জ্ঞানসম্পদের খুব কমই পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলো। তার আয়ুস্কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিতর্ক আছে। ইন্তেকালের সময় তার বয়স আঠারো থেকে সর্বোচ্চ সাতাশ বছর ছিলো বলে উল্লিখিত হয়েছে। এ বয়সে অর্থাৎ মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি যে একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ( প্রায় এক ঘন্টা ব্যাপী) ভাষণ দেন। সৌভাগ্যক্রমে তা পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের কাছে পৌছেছে। আর এটা কেবল শিয়া মাযহাবের সূত্রেই বর্ণিত হয় নি,বরং হিজরী তৃতীয় শর্তাব্দীতে বাগদাদী তার গ্রন্থে এ ভাষণটি উদ্ধৃত করেছেন। তার এই একটি ভাষণই এটা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে,মুসলিম নারী পুরুষের কাছ থেকে নিজের মর্যাদার সীমারেখা সংরক্ষণ করেও এবং নিজেকে পুরুষদের কাছে প্রদর্শন না করেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে কত উচুঁস্তরে উঠতে পারেন এবং সমাজের কাজকর্মে নারী অংশ নিলে তা কতখানি হওয়া উচিৎ।
হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ)-এর ভাষণে তাওহীদের আলোচনা রয়েছে এবং তা‘ নাহজুল বালাগ্বা’ র সম পর্যায়ের অর্থাৎ তা এমনই উচুঁ স্তরের যে,দার্শনিকগণ পর্যন্ত সে স্তরে উপনীত হতে সক্ষম নন। তিনি যখন আল্লাহর সত্তা ও তার গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন মনে হয় যে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকগণের অন্যতম। এমনকি ইবনে সীনার মতো এত বড় দার্শনিকের পক্ষেও এ ধরনের ভাষণ দান করা সম্ভব ছিলো না। এরপর সহসাই তিনি শারয়ী আহকামের দর্শন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেনঃ আল্লাহ তা‘ আলা নামাযকে এজন্য ফরয করেছেন,রোযাকে এ কারণে ফরয করেছেন,হজ্ব কে এজন্য ফরয করেছেন,আমর বিল মা‘ রুফ ওয়া নাহি‘ আনিল মুনকার (ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ) ফরয হবার কারণ এই,যাকাতকে অমুক কারণে ফরয করা হয়েছে ইত্যাদি। এরপর তিনি ইসলাম-পূর্ব যুগের আরব গোত্রসমূহের অবস্থা পর্যালোচনা করতে শুরু করেন এবং ইসলাম তাদের জীবনে কী পরিবর্তন এনে দিয়েছে তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে,তোমরা আরবরা এই রকম ছিলে,ঐ রকম ছিলে ইত্যাদি। ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবদের বস্তুগত ও নৈতিক-আত্মিক অবস্থা কেমন ছিলো সে সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের বস্তুগত ও নৈতিক-আত্মিক অবস্থায় যে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে দিয়েছেন তা স্মরণ করিয়ে দেন। এরপর তিনি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।
হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ) মসজিদে নববীতে হাজার হাজার লোকের সামনে তার এ ভাষণ পেশ করেন। কিন্তু তিনি আত্ম প্রদর্শনীর জন্য মিম্বারে ওঠেন নি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত একটি রীতি ছিলো এই যে,মজলিসে নারী ও পুরুষরা আলাদা বসতেন এবং তাদের মাঝখানে একটি পর্দা টানিয়ে দেয়া হতো। হযরত ফাতেমা যাহরা’ (সাঃ আঃ) পর্দার আড়াল থেকে তার পুরো ভাষণ পেশ করেন এবং মজলিসে উপস্থিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই অভিভূত করে ফেলেন।
এর মানে হচ্ছে এই যে,ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি,মুসলিম নারী একদিকে যেমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী অন্য দিকে লজ্জাশীলতারও অধিকারী,যেমন পবিত্রতার অধিকারী তেমনি স্বীয় মর্যাদার সীমারেখাকে মেনে চলেন;কখনো নিজেকে পুরুষদের ক্ষুধার্ত চোখের সামনে পেশ করেন না। কিন্তু মুসলিম নারী এমন কোনো হস্তপদ বিহীন অর্থব সত্তা নয় যার মাথায় কিছুই ঢোকে না এবং দুনিয়ার কোনো কিছুরই খবর রাখে না।
কারবালার ইতিহাস হচ্ছে নারী-পুরুষের ইতিহাস। এ হচ্ছে এমন একটি ঘটনা যাতে নারী ও পুরুষ উভয়েরই ভূমিকা ছিলো,কিন্তু পুরুষরা স্বীয় অক্ষের চারদিকে এবং নারীরাও স্বীয় অক্ষের চারদিকে আবর্তিত হয়েছেন। এগুলো হচ্ছে ইসলামের মু’ জিযা। ইসলাম চায় আজকের দুনিয়া ও ভবিষ্যত দুনিয়া এগুলোকে গ্রহণ করুক;জাহান্নাম গ্রহণ না করুক।
হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) স্বীয় পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়ে যান। কারণ,তিনি চাচ্ছিলেন যে,তারা কাফেলার নেত্রী হযরত যায়নাব (আঃ)-এর নেতৃত্বে স্বীয় অক্ষের সীমারেখা থেকে বাইরে না এসেও এ বিরাট ইতিহাসে একটি বড় ধরনের দায়িত্ব পালন করবেন-এ ইতিহাস সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবেন।
আশূরার দিন বিকালে হযরত যায়নাব স্বমহিমায় সমুদ্ভাসিত হলেন। এর পরবর্তী দায়িত্ব তার ওপরে অর্পিত হয়েছিলো। তিনি হলেন কাফেলার নেত্রী। কারণ,এ কাফেলার একমাত্র পুরুষ সদস্য ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) এ সময় গুরুতরভাবে অসুস্থ ছিলেন এবং এ কারণে তার নিজেরই সেবাশুশ্রূষার প্রয়োজন ছিলো। অবশ্য ইবনে যিয়াদের সাধারণ নির্দেশ ছিলো এই যে,হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্যই যেন জীবিত না থাকেন। তদনুযায়ী ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) কে হত্যা করার উদ্দেশ্য শত্রুরা বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়েছিলো। কিন্তু তারা তার অবস্থা দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেঃ‘‘ নিঃসন্দেহে সে নিজেই সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে ।’’ ( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ ৪৫ , পৃষ্ঠাঃ ৬১ ; এ ’ লামুল ওয়ারা , পৃষ্ঠাঃ ২৪৬ ; ইরশাদ - শেখ মুফীদ , পৃষ্ঠাঃ ২৪২ ) অর্থাৎ তিনি তো এমনিতেই মারা যাচ্ছেন।
বস্তুতঃ এ ছিলো মহান আল্লাহর কল্যাণ-ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ চাচ্ছিলেন যে,এভাবে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) বেঁচে থাকুন এবং তার মাধ্যমে ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর পবিত্র বংশধারা টিকে থাকুক।
হযরত যায়নাব (আঃ) এ সময় যে সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ)-এর সেবা-শুশ্রূষা।
১১ই মহররম বিকালে বন্দীদেরকে বাহনে (উটের বা খচ্চরের বা উভয়ের পিঠে) সওয়ার করানো হলো। এগুলোর জিন ছিলো কাঠের তৈরী। বন্দীদেরকে মানসিক কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে জিনের ওপরে কাপড় বিছাতে বাধা দেয়া হয়। রওয়ানা হওয়ার আগে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে একটি অনুরোধ জানানো হয় এবং সে অনুরোধ রক্ষা করা হয়।
قُلْنَ بِحَقِّ اللهِ اِلَّا مَا مَرَرْتُمْ بِنَا عَلَی مِصْرَعِ الْحُسَيْنِ.
‘‘ তারা (বন্দী নারীরা) বললেনঃ আল্লাহর দোহাই,আমাদেরকে হোসাইনের শাহাদাতস্থল ছাড়া অন্য কোনো জায়গা দিয়ে নিয়ে যেয়ো না।’’ ( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ ৪৫ , পৃষ্ঠাঃ ৫৮ ; আল - লুহুফ , পৃষ্ঠাঃ ৫৫ , মাকতালু হোসাইন , পৃষ্ঠাঃ ৩৯৬ , মাকতালু খরাযমী , খণ্ডঃ ২ , পৃষ্ঠাঃ ৩৯ )
শেষ বারের মতো শহীদগণকে খোদা হাফেযী করার উদ্দেশ্যেই তারা তাদেরকে ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতস্থল হয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।
বন্দীদের মধ্যে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) খুবই অসুস্থ ছিলেন বিধায় বাহনের ওপর ঠিকভাবে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না। এ কারণে তার পা বাহনের পেটের নীচে বেঁধে দেয়া হয়। অন্য সকলেই বাহনের ওপর মুক্তভাবে বসে যান। তারা যখন শাহাদাতস্থলে পৌঁছিলেন তখন সকলেই নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন এবং বাহন থেকে নীচে পড়ে গেলেন। এরপর হযরত যায়নাব হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর পবিত্র লাশের নিকট পৌঁছে গেলেন। তিনি তাকে এমন এক অবস্থায় দেখলেন যেরূপ ইতিপূর্বে কখনো কাউকে দেখেন নি। ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর লাশ মাথা বিহীন অবস্থায় পড়ে ছিলো। তিনি তার ভাইয়ের সাথে কথা বলতে থাকেন,তাদের পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার কথা বলতে থাকেন। অন্তরে যত বেদনা ছিলো তার সবই ঢেলে দেন। আর তিনি এতই বিলাপ করেন যে,বর্ণনাকারী বলেনঃ
فَأَبْکَتْ وَ اللهِ کُلَّ عَدُوٍّ وَ صِدِّيقٍ.
‘‘ আল্লাহর শপথ,তিনি দুশমন ও বন্ধু নির্বিশেষে প্রত্যেককেই কাঁদালেন।’’ ( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ ৪৫ , পৃষ্ঠাঃ ৫৯ ; আল - লুহুফ , পৃষ্ঠাঃ ৫৬ , মাকতা মুকাররম , পৃষ্ঠাঃ ৩৯৬ )
বস্তুতঃ সর্ব প্রথম যিনি ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতে শোকানুষ্ঠান করেন তিনি হলেন হযরত যায়নাব (আঃ)। কিন্তু এ সময়ও তিনি তার মূল দায়িত্ব বিস্মৃত হন নি। ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ)-এর সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব ছিলো তারই। তিনি ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ)-এর দিকে তাকালেন। তিনি দেখলেন যে,এ অবস্থা দেখে ইমামক সহ্য করতে পারেছন না,মনে হচ্ছিলো যেন তার প্রাণ দেহের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। হযরত যায়নাব (আঃ) সাথে সাথে হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর লাশ রেখে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ)-এর নিকট চলে এলেন। তিনি বললেনঃ‘‘ ভাতিজা! তোমার এ অবস্থা কেন যে,মনে হচ্ছে তোমার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে ?’’ জবাবে তিনি বললেনঃ‘‘ ফুফুজান! এটা কী করে সম্ভব যে,প্রিয়জনদের লাশ দেখে কষ্ট না পাবো?’’ তখন হযরত যায়নাব (আঃ) তাকে সান্তনা দিতে শুরু করেন।
ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) কে সান্তনা দিতে গিয়ে হযরত যায়নাব (আঃ) তাকে উম্মে আইমান থেকে শোনা একটি হাদীস বর্ণনা করে শোনান। উম্মে আইমান ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের একজন সম্মানিতা মহিলা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবী। যতটা জানা যায়,প্রথমে তিনি ছিলেন হযরত খাদীজা (আ):-এর ক্রীতদাসী যাকে পরে মুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু মুক্ত হওয়ার পরেও নবী-পরিবারের প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর গৃহে হযরত খাদীজা (আঃ)-এর খেদমতে ও তার ইন্তেকালের পরে হযরত ফাতেমা (আঃ)-এর খেদমতে থেকে যান। তিনি হযরত নবী করীম (সাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
দীর্ঘ বহু বছর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গৃহে অবস্থানকারী এ মহিলা পরবর্তী কালে হযরত যায়নাব (আঃ)-এর নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেন। যেহেতু হাদীসটি ছিলো আহলে বাইতের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাই হযরত যায়নাব (আঃ) একদিন তার পিতা হযরত আলী (আঃ)-এর খেদমতে এ হাদীসটি পেশ করে এর বক্তব্যের যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার প্রচেষ্টা করেন। তিনি পুরো হাদীসটি পেশ করলে তা শোনার পর হযরত আলী (আঃ) বললেনঃ উম্মে আইমান ঠিকই বলেছেন।
কারবালার ঐ পরিস্থিতিতে হযরত যায়নাব (আঃ) উম্মে আইমান থেকে শোনা এ হাদীস ইমাম যায়নুল আবেদীন (আঃ) কে শোনালেন। বস্তুতঃ এ হাদীসের মধ্যে একটি বিশেষ দর্শন নিহিত রয়েছে। আর তা হচ্ছে,কেউ যেন মনে না করে যে,হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতের ফলে সব শেষ হয়ে গেলো। হযরত যায়নাব (আঃ) বললেনঃ‘‘ ভাতিজা! আমাদের নানা (রাসূলুল্লাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,এখন যেখানে হোসাইনের লাশ দেখতে পাচ্ছো সেখানে কাফন পরানো ছাড়াই তার লাশ দাফন করা হবে এবং এখানে হোসাইনের কবর যিয়ারতগাহে পরিণত হবে।’’ কবি বলেনঃ
بر سر تربت ما چون گذری همت خواه
که زيارتگه رندان جهان خواهد بود.
‘‘ আমার কবরের পাশ দিয়ে যাবে যখন হিম্মত চাহো
কারণ তা একদিন বিশ্বের আধ্যাত্মবাদীদের যিয়ারতগাহ হবে।’’
হযরত যায়নাব (আঃ) তার ভ্রাতুস্পুত্রকে জানিয়ে দেন যে,একদিন হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর শাহাদতগাহ ইখলাছের অধিকারী মুসলমানদের যিয়ারতগাহে পরিণত হবে।
১১ই মহররম বিকালে বন্দীদের কাফেলাকে পুনরায় রওয়ানা করানো হয়। অন্যদিকে ইয়াযীদী বাহিনীর সেনাপতি ওমর ইবনে সা‘ দের নেতৃত্বে তার সৈন্যরা তাদের নিহত সহযোদ্ধাদের দাফন করার জন্য থেকে যায়। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আঃ) ও তার সঙ্গীসাথী শহীদগণের লাশ রণাঙ্গনেই পড়ে থাকে।
বন্দীদের কাফেলাকে প্রথমে কারবালা থেকে ১২ ফারসাখ (৩৬ মাইল) দূরবর্তী নাজাফে নিয়ে আসা হয়। আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে,ঢাক-ঢোল ও বাশী বাজিয়ে এবং বিজয় পতাকা উড়িয়ে আনন্দ-উৎসব সহকারে ১২ই মহররম বন্দীদেরকে কুফায় প্রবেশ করানো হবে। তারা এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আহলে বাইতের ওপর সর্বশেষ আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছিলো।
হযরত যায়নাব (আঃ) সম্ভবতঃ ৯ই মহহরম থেকে মোটেই ঘুমাননি। এহেন এক অবস্থায় বন্দীদেরকে কুফার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। শহীদগণের পবিত্র শিরগুলো আগেই নিয়ে যাওয়া হয়। সূর্যদয়ের দুই-তিন ঘন্টা পরে বন্দীদেরকে কুফায় প্রবেশ করানো হয়। আদেশ দেওয়া হলো যে,বন্দীদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যেন শহীদদের পবিত্র কর্তিত শিরগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন এমন এক বিস্ময়কর মর্মান্তিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার বর্ণনা প্রদান বর্ণনাশক্তির উর্ধ্বে। কুফা নগরীর প্রবেশদ্বারে পৌঁছার পর ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর কন্যা ফাতেমা স্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হলেন। এ সাহসী বীর নারী স্বীয় নারীসুলভ মর্যাদা বজায় রেখেই সেখানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন।
বর্ণনাকারীগণ বলেন,এ পর্যায়ে এক বিশেষ সময়ে হযরত যায়নাব (আঃ) পরিস্থিতিকে তার নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য যথোপযুক্ত গণ্য করলেন এবং সকলের প্রতি নীরব হওয়ার জন্য ইশারা করলেন। ইতিহাসের উক্তি এরূপঃ
وَ قَدْ اَوْمَأَتْ اِلَی النَّاسِ اَنْ اُسْکُتُوا فَارْتَدَّتِ الْاَنْفَاسُ، وَ سَکَنَتِ الْاَجْرَاسُ.
‘‘ (সেই গোলযোগ ও হৈ চৈ পূর্ণ পরিস্থিতিতে) তিনি লোকদের প্রতি ইশারা করে নীরব হতে বললেন,ফলে নিঃশ্বাসগুলো (তাদের বুকের মধ্যে ) আটকে গেলো এবং (বাহনগুলো দাড়িয়ে যাওয়ায় তাদের গলায় বাধা) ঘন্টাগুলো নীরব হয়ে গেলো।’’ ( বিহারুল আনোয়ার , খণ্ডঃ ৪৫ , পৃষ্ঠাঃ ১০৮ ; আল - লুহুফ , পৃষ্ঠাঃ ৪২ , মাকতালু মুকাররম , পৃষ্ঠাঃ ৪০২ ; মাকতালু খরাযমী , খণ্ডঃ ২ , পৃষ্ঠাঃ ৪০ ) এরপর হযরত যায়নাব (আঃ) সকলের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ
وَلَمْ اَرَ وَ اللهِ خَفِرَةً قَطُّ اَنْطَقَ مِنْهَا
‘‘ আল্লাহর শপথ, এমন আর কোনো লজ্জাশীলা নারীকে কখনো এমন ভাষণ দিতে দেখিনি।’’ ( প্রাগুক্ত ) এখানে বর্ণনাকারীর ব্যবহৃতخَفِرَةً শব্দটি খুবই গুরুত্বের অধিকারী। কারণ,এ থেকে সুস্পষ্ট যে,তিনি ছিলেন একজন লজ্জাশীলা মহিলা। তিনি কোনো নির্লজ্জ নারীর ন্যায় ভাষণ দিতে আসেন নি। হযরত যায়নাব (আঃ) অত্যন্ত শৌর্যপূর্ণ ও বীরত্বব্যঞ্জক ভাষণ দেন। কিন্টতু তা সত্ত্বেও তার দুশমন পক্ষের বর্ণনাকারীরাও বলতে বাধ্য হনঃ‘‘ আল্লাহর শপথ,এমন আর কোনো লজ্জাশীলা নারীকে কখনো এমন ভাষণ দিতে দেখি নি।’’ অর্থাৎ তিনি নারীসুলভ লজ্জাশীলতা সহকারেই লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তার ভাষণে হযরত আলী (আঃ)-এর বীরত্ব আর নারীসুলভ লজ্জাশীলতা সংমিশ্রি ত হয়েছিলো।
বিশ বছর আগে শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আলী (আঃ) যখন তৎকালীন মুসলিম জাহানের খলীফা ছিলেন তখন তিনি কুফায় ছিলেন। কুফা ছিলো তার রাজধানী। তিনি প্রায় পাঁচ বছর খলীফা ছিলেন। এ সময় তিনি বহু ভাষণ প্রদান করেন। তখনো (কারবালার ঘটনার সময়) লোকদের মধ্যে হযরত আলী (আঃ)-এর ভাষণ প্রবাদ বাক্যের মতো প্রচলিত ছিলো। বর্ণনাকারী বলেন,মনে হচ্ছিলো যেন হযরত যায়নাব (আঃ)-এর কণ্ঠ থেকে হযরত আলী (আঃ)-এর ভাষণ বেরিয়ে আসছে। এ সময় হযরত যায়নাব (আঃ) কোনো দীর্ঘ ভাষণ দেন নি (মাত্র দশ-বারো বাক্যে তিনি তার ভাষণ শেষ করেন)। বর্ণনাকারী বলেনঃ‘‘ দেখলাম যে,লোকেরা সকলেই তাদের আঙ্গুল মুখে ঢুকিয়ে কামড়াচ্ছিলো।’’
এই হচ্ছে নারীর এক ধরনের ভূমিকা,যে ধরনের ভূমিকা ইসলাম তার কাছ থেকে আশা করে। লজ্জাশীলতা,সতীত্ব ,পবিত্রতা ও নারী-পুরুষের মধ্যকার অলঙ্ঘনীয় সীমারেখার সংরক্ষণ সহকারে নারী ব্যক্তিত্বই ইসলামের কাম্য । কারবালার ইতিহাস এ কারণে নারী-পুরুষের ইতিহাস যে,এ ইতিহাসের সৃষ্টিতে পুরুষ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তেমনি নারীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে পুরুষের ভূমিকা পুরুষের অক্ষের চারদিকে আবর্তিত হয় এবং নারীর ভূমিকা নারীর অক্ষের চারদিকে আবর্তিত হয়। এভাবে এ ইতিহাস নারী ও পুরুষ উভয়ের হাতে গড়ে ওঠে।




