চিরভাস্বর মহানবী (সা.)-প্রথম খণ্ড
 0%
0%
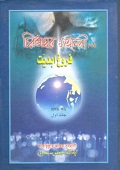 লেখক: আয়াতুল্লাহ্ জাফার সুবহানী
লেখক: আয়াতুল্লাহ্ জাফার সুবহানী
: মোহাম্মাদ মুনীর হোসেন খান
প্রকাশক: কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস -
বিভাগ: হযরত মোহাম্মদ (সা.)
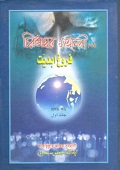
লেখক: আয়াতুল্লাহ্ জাফার সুবহানী
: মোহাম্মাদ মুনীর হোসেন খান
প্রকাশক: কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস -
বিভাগ:
ডাউনলোড: 10513
পাঠকের মতামত:
- প্রথম অধ্যায় : আরব উপদ্বীপ : ইসলামী সভ্যতার সূতিকাগার
- পবিত্র মক্কার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- মদীনা আল মুনাওয়ারাহ্
- দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাক ইসলামী যুগে আরব জাতি
- হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে আরব উপদ্বীপ
- ইসলামপূর্ব আরব জাতি কি সভ্য ছিল?
- আরবের ধর্মীয় অবস্থা
- মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আরবদের চিন্তা
- সাহিত্য একটি জাতির মন-মানসিকতা প্রকাশকারী দর্পণ
- জাহেলী আরব সমাজে নারীর মর্যাদা
- আরব জাতির মাঝে নারীর সামাজিক অবস্থান
- আরবদের সাহস ও বীরত্ব
- জাহেলিয়াত যুগের আরবদের সাধারণ চরিত্র
- জাহেলিয়াত যুগের আরবগণ কুসংস্কার পূজারী ছিল
- জাহেলিয়াত যুগের আরবদের বিশ্বাসে কুসংস্কার
- কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইসলামের সংগ্রাম
- ইসলামের আবির্ভাবের সময়ে আরবের সামাজিক অবস্থা
- হীরা ও গাসসান রাজ্যসমূহ
- হিজাযে প্রচলিত ধর্ম
- তৃতীয় অধ্যায় : দুই পরাশক্তি ইরান ও রোমের অবস্থা
- ইরান : তদানীন্তন সভ্যতার লালনভূমি
- খসরু পারভেজের অপরাধসমূহের পর্দা উন্মোচন
- সাসানী সম্রাটদের ব্যাপারে ইতিহাসের ফয়সালা
- ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাসানীয় ইরানের দুরবস্থা
- ইরান ও রোম সাম্রাজের মধ্যকার যুদ্ধসমূহ
- চতুর্থ অধ্যায় : মহানবী (সা.)-এর পূর্বপুরুষগণ
- হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.)
- মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সংগ্রাম
- সংলাপ ও আলোচনায় মহান নবীদের পদ্ধতি
- হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর হিজরত
- যমযম কূপ আবিষ্কার
- কুসাই বিন কিলাব
- আবদে মান্নাফ
- হাশিম
- উমাইয়্যাহ্ ইবনে আবদে শামস-এর ঈর্ষা
- হাশিম-এর বিবাহ
- আবদুল মুত্তালিব
- যমযম কূপ খনন
- চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা
- হাতির বছরের গোলযোগ
- আবরাহার শিবিরে আবদুল মুত্তালিব-এর গমন
- মুজিযা সংক্রান্ত আলোচনা
- কুরাইশদের কল্পরাজ্য
- মহানবীর পিতা আবদুল্লাহ্
- ফাতিমা খাসআমীয়ার কাহিনী
- পঞ্চম অধ্যায় : বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর শুভ জন্ম
- মহানবী (সা.)-এর নামকরণ
- মহানবীর স্তন্যপানের সময়কাল
- ষষ্ঠ অধ্যায় : মহানবী (সা.)-এর শৈশবকাল
- সপ্তম অধ্যায় : মাতৃক্রোড়ে প্রত্যাবর্তন
- ইয়াসরিবে সফর
- আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু
- আবু তালিবের অভিভাবকত্ব
- শামদেশ (সিরিয়া) সফর
- অষ্টম অধ্যায় : মহানবী (সা.)-এর যৌবনকাল
- মহানবীর আধ্যাত্মিক শক্তি
- ফিজারের যুদ্ধসমূহ
- হিলফুল ফুযূল (প্রতিজ্ঞা-সংঘ)
- নবম অধ্যায় : মেষ পালন থেকে বাণিজ্য
- ইসলামের মহীয়সী নারী হযরত খাদীজাহ্
- হযরত খাদীজার বিবাহের প্রস্তাব
- হযরত খাদীজার বয়স
- দশম অধ্যায়: বিবাহ থেকে নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত
- মহানবীর যৌবনকাল
- খাদীজার গর্ভজাত সন্তানগণ
- মহানবীর পালক পুত্র
- মহানবী হযরত আলীকে নিজ গৃহে নিয়ে আসেন
- নবুওয়াতের পূর্বে তাঁর ধর্ম
- একাদশ অধ্যায় : সত্যের প্রথম প্রকাশ
- সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নবীদের ভূমিকা
- হিরা পর্বতে মহানবী (সা.)
- ওহী অবতরণের শুভ সূচনা
- একজন বস্তুবাদী ব্যক্তির বিশ্বদৃষ্টি
- জ্ঞান অর্জনের উৎসত্রয়
- ওহীর শ্রেণীবিভাগ
- দ্বাদশ অধ্যায়: প্রথম ওহী
- কোন্ দিন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল
- ত্রয়োদশ অধ্যায় : সর্বপ্রথম যে পুরুষ ও মহিলা মহানবীর প্রতি ঈমান এনেছিলেন
- মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজাহ্
- ঈমানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন আলী
- আমিই সিদ্দীকে আকবর
- ইসহাকের সাথে খলীফা মামুনের কথোপকথন
- ওহী অবতীর্ণ বন্ধ থাকা প্রসঙ্গ
- চতুর্দশ অধ্যায় : গোপনে দাওয়াত
- নিকটাত্মীয়দেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান
- নিকটাত্মীয়দের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান পদ্ধতি
- নবুওয়াত ও ইমামত পরস্পর নিত্যসঙ্গী
- পঞ্চদশ অধ্যায় : প্রকাশ্যে দাওয়াত
- লক্ষ্য অর্জনের পথে দৃঢ়তা
- মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য ও দৃঢ়তা
- মহানবী (সা.)-কে কুরাইশদের প্রলোভন
- কুরাইশ বংশের উৎপীড়নের একটি নমুনা
- মহানবী (সা.)-এর পিছনে আবু জাহলের ওঁৎ পেতে থাকা
- মুসলমানদের ওপর উৎপীড়ন ও নির্যাতন
- ইসলামের প্রথম আহবানকারী
- গিফার গোত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ
- হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শত্রুগণ
- দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ
- ষোড়শ অধ্যায় : কোরআন সম্পর্কে কুরাইশদের অভিমত
- ওয়ালীদের রায়
- কুরাইশদের অদ্ভুত অজুহাত
- কুরাইশ নেতৃবর্গের বিরুদ্ধাচরণের কারণ
- মুশরিকদের কতিপয় আপত্তি
- পবিত্র কোরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতীর্ণ হওয়া
- ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হওয়ার অন্তর্নিহিত মূল রহস্য
- কোরআন ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হওয়ার অন্যান্য কারণ
- সপ্তদশ অধ্যায় : হিজরত
- প্রথম হিজরত
- হাবাশার রাজদরবারে কুরাইশ প্রতিনিধি
- হাবাশা থেকে প্রত্যাবর্তন
- মক্কা নগরীতে খ্রিষ্টানদের অনুসন্ধানী দল
- কুরাইশদের প্রেরিত প্রতিনিধিদল
- অষ্টাদশ অধ্যায় : মরিচাপড়া অস্ত্রশস্ত্র
- ভিত্তিহীন অপবাদ
- মহানবীকে পাগল বলে আখ্যায়িত করা
- পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করার চিন্তা
- কুরাইশগণ কর্তৃক পবিত্র কোরআন শ্রবণ বর্জন
- আইন ভঙ্গকারী আইন প্রণেতাগণ
- জনগণের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধা দান
- ঊনবিংশ অধ্যায় : ‘গারানিক’-এর উপাখ্যান
- গারানিকের উপাখ্যান কি?
- ভাষাগত দিক থেকে কাল্পনিক এ উপাখ্যানটি রদ করার দলিল
- বিংশতিতম অধ্যায় : অর্থনৈতিক অবরোধ ও সামাজিক বয়কট
- কুরাইশদের ঘোষণা
- উপত্যকায় বনি হাশিমের নাজুক অবস্থা
- একুশতম অধ্যায় : হযরত আবু তালিব (রা.)-এর মৃত্যু
- আবু তালিবের হৃদ্যতা ও আবেগের উদাহরণ
- সফরের কর্মসূচীতে পরিবর্তন
- বিশ্বাসের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা
- আবু তালিবকে উদ্বুদ্ধ করার প্রকৃত কারণ
- আবু তালিব (রা.)-এর ত্যাগের কতিপয় নমুনা
- আলোচনার রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- আবু তালিবের ঈমানের প্রমাণ
- আবু তালিবের সাহিত্যকর্ম
- আবু তালিবের ঈমান প্রমাণ করার দ্বিতীয় পদ্ধতি
- মৃত্যুর সময় আবু তালিবের অসিয়ত
- শিয়া আলেমদের অভিমত
- বাইশতম অধ্যায় : মিরাজ
- কোরআন,হাদীস ও ইতিহাসের দৃষ্টিতে মিরাজ
- মিরাজের কোরআনী ভিত্তি
- মিরাজ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ
- মিরাজ কখন সংঘটিত হয়েছিল
- মহানবী (সা.)-এর মিরাজ কি দৈহিক ছিল?
- আত্মিক মিরাজ কী?
- মিরাজ ও বর্তমানের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ
- অস্তিত্বজগতের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য
- তেইশতম অধ্যায় : তায়েফ যাত্রা
- আরবদের প্রসিদ্ধ বাজারসমূহে বক্তব্য দান
- হজ্বের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রপতিদের প্রতি দাওয়াত
- চব্বিশতম অধ্যায় : আকাবার চুক্তি
- বুয়া’সের যুদ্ধ
- খাজরাজদের ইসলাম গ্রহণ
- আকাবার প্রথম শপথ
- আকাবার দ্বিতীয় শপথ
- আকাবা চুক্তির পর মুসলমানদের অবস্থা
- আকাবা চুক্তি ও কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া
- ইসলামের নৈতিক প্রভাব
- কুরাইশদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার
- পঁচিশতম অধ্যায় : হিজরতের প্রথম বছরের ঘটনাপ্রবাহ
- গায়েবী সাহায্য
- নবুওয়াতের গৃহে শত্রুদের আক্রমণ
- সওর পর্বতের গুহায় মহানবী
- মহানবীর সন্ধানে কুরাইশ গোত্র
- সত্যের পথে জীবন বাজি রাখা
- ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য
- নবী (সা.)-এর হিজরত পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ
- গুহা হতে বহির্গমন
- হিজরী সালের প্রথম পৃষ্ঠা উন্মোচিত হলো
- কেন হিজরী বর্ষকে কেন্দ্র করে ইসলামী ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে
- মহানবীর হিজরতকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব তারিখের সূচনা
- হিজরী বর্ষের প্রবর্তনকারী কে?
- হিজরী তারিখ সম্বলিত মহানবীর কয়েকটি পত্র
- হিজরতের সফরনামা
- কুবা গ্রামে রাসূল (সা.)-এর প্রবেশ
- মদীনায় আনন্দের ঢল
- নবীর প্রতি মদীনার আনসারদের ভালোবাসার কিছু ক্ষুদ্র নমুনা
- নিফাকের উৎপত্তি
- ছাব্বিশতম অধ্যায় : হিজরতের প্রথম বর্ষের ঘটনাপ্রবাহ
- মহানবীর প্রথম ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ
- হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের ঘটনা
- ভ্রাতৃত্ব বন্ধন : ঈমানের সর্বোত্তম বিচ্ছুরণ
- হযরত আলীর দু’টি শ্রেষ্ঠত্ব
- ইয়াসরিবের ইয়াহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা চুক্তি
- ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সনদ (চুক্তিনামা)
- ইসলামী হুকুমতকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র
- সাতাশতম অধ্যায় : দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ
- যুদ্ধ ও সামরিক মহড়া
- কুরাইশের বাণিজ্য পথ হুমকির সম্মুখীন
- সামরিক অভিযান ও মহড়ার উদ্দেশ্য
- মধ্যপ্রাচ্যবিদগণের দৃষ্টিতে এ অভিযানসমূহ
- আটাশতম অধ্যায় : কিবলা পরিবর্তন
- মহানবীর বৈজ্ঞানিক মুজেযা
- উনত্রিশতম অধ্যায় : বদরের যুদ্ধ
- যাফরান নামক স্থানের দিকে মহানবীর যাত্রা
- কুরাইশ যে সমস্যার মুখোমুখি হলো
- সামরিক পরামর্শ সভা
- পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত ও আনসার দলপতির মত
- শত্রুর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ
- আবু সুফিয়ানের পলায়ন
- কুরাইশদের মতদ্বৈততা
- নেতৃত্ব মঞ্চ
- কুরাইশ গোত্রের কার্যক্রম
- কুরাইশদের পরামর্শ সভা
- যে ঘটনা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলল
- মল্লযুদ্ধের শুরু
- সম্মিলিত আক্রমণ শুরু হলো
- উমাইয়্যা ইবনে খালাফকে হত্যা
- জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ
- যে কবিতাটিতে স্থায়িত্বের রং লেগেছে
- বদর যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ
- মদীনায় মহানবী (সা.)-এর সুসংবাদ প্রেরণ
- মক্কাবাসীদের নিকট তাদের নেতাদের নিহত হওয়ার সংবাদ
- ক্রন্দন ও শোকগাথা পাঠ নিষিদ্ধ হলো
- বন্দীদের ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত
- ত্রিশতম অধ্যায় : ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া
- বর্তমান যুগে বিবাহের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ
- এ সব সমস্যার বিরুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সংগ্রাম
- হযরত ফাতিমার বিবাহের উপহার সামগ্রীর বিবরণ
- বিবাহ অনুষ্ঠান
- একত্রিশতম অধ্যায় : বনী কাইনুকা গোত্রের ইয়াহুদীদের অপরাধসমূহ
- একটি স্ফুলিঙ্গ থেকে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত হওয়া
- মদনীয় বেশ কিছু নতুন খবর আসতে থাকা
- গাযওয়াতু যিল আমর
- কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার গতিপথ পরিবর্তন
- তথ্যসূচী ও টিকা






