মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ
কার্যকারণ নীতি সৃষ্টিজগতকে ব্যতিক্রমহীনভাবে শাসন করছে । এ সৃষ্টিজগতের সর্বত্রই এ নীতি বলবৎ রয়েছে । কার্য-কারণ নীতি অনুসারী এ বিশ্বের সকল কিছুই তার সৃষ্টির ব্যাপারে এক বা একাধিক কারণ বা শর্তের উপর নির্ভরশীল । আর ঐসব কারণ বা শর্ত সমূহ (পূর্ণাঙ্গ কারণ) বাস্তবায়নের পর সংশ্লিষ্ট বস্তুর বাস্তব রূপ লাভ (ফলাফল) অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে । আর তার প্রয়োজনীয় কারণ বা শর্ত সমূহের সবগুলো বা তার কিছু অংশের অভাব ঘটলে সংশ্লিষ্ট বস্তুর সৃষ্টি লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে । উপরোক্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত দু’
টো বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ঃ
১. যদি আমরা কোন একটি সৃষ্টি বস্তুকে (ফলাফল) তার সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ কারণ সমূহের সাথে আনুপাতিক তুলনা করি , তাহলে ঐ সৃষ্ট বস্তুর (ফলাফল) অস্তিত্ব এবং তার কারণ সমূহের (পূর্ণাঙ্গ) অনুপাত হবে অপরিহার্যতা । কিন্তু আমরা যদি ঐ সৃষ্টি বস্তুকে তার সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ কারণের সাথে তুলনা না করে বরং তার আংশিক কারণের সাথে তুলনা করি , তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব (ফলাফল) আর তার আংশিক কারণের অনুপাত হবে সম্ভাব্যতা । কেননা , অসম্পূর্ণ বা আংশিক কারণ তার ফলাফল সংঘটনের ক্ষেত্রে শুধু সম্ভাব্যতাই দান করে মাত্র , অপরিহার্যতা নয় । সুতরাং এ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই তার সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণঙ্গ কারণের উপর আবশ্যিকভাবে নির্ভরশীল । এই আবশ্যিকতা ও বাধ্যবাধকতা সৃষ্টিজগতের সর্বত্রই ক্ষমতাসীন । আর এর কাঠামো এক ধরণের আনুক্রমিক ও আবশ্যিক গুণক সমূহের ( Factors) দ্বারা সুসজ্জিত । তথাপি , প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর (যা তার সৃষ্টির আংশিক কারণের সাথে সম্পর্কিত) মধ্যে তার সৃষ্টির সম্ভাব্যতার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত থাকবে । পবিত্র কুরআনে এই আবশ্যিক নীতিকে‘
ক্বায’
বা‘
ঐশী ভাগ্য’
হিসেবে নামকরণ করেছে । কেননা , এই আবশ্যিকতা স্বয়ং অস্তিত্ব দানকারী স্রষ্টা থেকেই উৎসারিত । এ কারণেই ভাগ্য এক অবশ্যম্ভাবী ও অপরিবর্তনশীল বিষয় । যার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম বা পক্ষপাত দুষ্টতা কখনোই ঘটার নয় । মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন : (জেনে রাখ) সৃষ্টি ও আদেশ দানের অধিকার তো তারই । (সূরা আল্ আ’
রাফ , ৫৪ নং আয়াত ।)
মহান আল্লাহ বলেন :“
যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন , তখন বলেন হও , আর তা হয়ে যায়”
। (সূরা আল্ বাকারা , ১১৭ নং আয়াত ।)
মহান আল্লাহ আরও বলেন : আর আল্লাহই্ আদেশ করেন যা বাধা দেয়ার (ক্ষমতা) কারো নেই (সূরা আর রা’
দ , ৪১ নং আয়াত ।)
২ । পূর্ণাঙ্গ কারণের প্রতিটি অংশই তার নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী বিশেষ মাত্রা ও প্রকৃতি দান করে। আর এভাবেই সম্মিলিত কারণ সমূহের (পূর্ণাঙ্গ কারণ) প্রদত্ত মাত্রা ও প্রকৃতি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ কারণ নির্দেশিত পরিমাণ অনুযায়ী কারণ সমূহ (পূর্ণাঙ্গ কারণ) প্রদত্ত মাত্রা ও প্রকৃতির সমষ্টিই এই অনুকুল ফলাফল (সৃষ্টবস্তু) । যেমনঃ যেসব কারণ মানুষের শ্বাসক্রিয়া সৃষ্টি করে , তা শুধুমাত্র নিরংকুশ শ্বাসক্রিয়ারই সৃষ্টি করে না । বরং তা মুখ ও নাকের পার্শ্বস্থ নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুকে নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার শাসনালী দিয়ে ফসফুস যন্ত্রে পাঠায় । একইভাবে যেসমস্ত কারণঃ মানুষের দৃষ্টিশক্তি দান করে , তা কোন শর্ত বা কারণবিহীন দৃষ্টিশক্তির জন্ম দেয় না । বরং একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ও পরিমাণে ঐ দৃষ্টিশক্তির সৃষ্টি করে । এ জাতীয় বাস্তবতা সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টিনিচয় ও তাতে সংঘটিত সকল কর্মকান্ডেই বিরাজমান , যার কোন ব্যতিক্রম নেই । পবিত্র কুরআনে এ সত্যটিকে‘
কাদর’
বা ভাগ্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।
আর সকল সৃষ্টির উৎস মহান আল্লাহর প্রতি এ বিষয়টিকে আরোপিত করা হয়েছে । মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন : আমি প্রতিটি বস্তুকেই তার (নির্দিষ্ট) পরিমাণে সৃষ্টি করেছি । (সূরা আল্ কামার , ৪৯ নং আয়াত ।)
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন : আমারই নিকট রয়েছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরাবরাহ করে থাকি ।
(সূরা আল্ হাজার , ২১ নং আয়াত ।)
একারণেই মহান আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী যে কোন কাজ বা ঘটনারই উদ্ভব ঘটকু না কেন , তার সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে । এভাবে আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী যা কিছু সৃষ্টি বা সংঘটিত হোক না কেন , তা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিশেষ পরিমাণ ও মাত্রা অনুযায়ীই হবে । এ ব্যাপারে সামান্যতম ব্যতিক্রমও কখনো ঘটবে না ।
মানুষ ও স্বাধীনতা
মানুষ যে সকল কাজ সম্পাদন করে , এ সৃষ্টি জগতের অন্যসব সৃষ্টির ন্যায় তাও এক সৃষ্টি । তার সংঘটন প্রক্রিয়া ও এজগতের অন্য সকল সৃষ্টির মতই পূর্ণাঙ্গ কারণ সংঘটিত হওয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল । কারণ , মানুষও এসৃষ্টি জগতেরই অংশ স্বরূপ । এ জগতের অন্য সকল সৃষ্টির সাথেই তার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান । তাই তার সম্পাদিত ক্রিয়ায় সৃষ্টির অন্য সকল অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে মনে করা যাবে না । যেমন : মানুষের একমুঠো ভাত খাওয়ার কথাই চিন্তা করে দেখা যাক । এ সামান্য কাজের মধ্যে আমাদের হাত , মুখ , দৈহিক শক্তি , বুদ্ধি , ইচ্ছা সবই ওতপ্রোতাভাবে জড়িত । ভাতের অস্তিত্ব ও তা হাতের নাগালে থাকা , তা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন বাধা বিঘ্নের অস্তিত্ব না থাকাসহ স্থান-কাল সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তের উপস্থিতির প্রয়োজন । ঐসব শর্ত বা কারণের একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে ঐ কাজ সাধ্যের বাইরে চলে যায় । আর ঐ সকল শর্ত বা (পূর্ণাঙ্গ কারণের উপস্থিতি) কারণ সমূহের উপস্থিতির ফলে সংশ্লিষ্ট কাজটির সম্পাদন অপরিহার্য হয়ে পড়ে । পূর্বে যেমনটি আলোচিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ কারণের উপস্থিতির ফলে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ার সংঘটন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে । তেমনি কোন ক্রিয়া মানুষের দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার সময় , মানুষ যেহেতু পূর্ণাঙ্গ কারণের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত , তাই মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ার সম্পর্ক হচ্ছে‘
সম্ভাব্যতার’
সম্পর্ক । (কারণ মানুষ একাই পূর্ণাঙ্গ কারণ নয় । বরং মানুষও ঐ ক্রিয়ার অন্যান্য অপূর্ণাঙ্গ কারণগুলোর মতই একটি আংশিক কারণ মাত্র ।) কোন ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে । ঐ ক্রিয়ার সাথে সামগ্রিক (পূর্ণাঙ্গ কারণ) কারণের সম্পর্ক হচ্ছে‘
অপরিহার্যতার’
(অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ কারণ ঘটলেই এ ক্রিয়ার সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে) সম্পর্ক ।
কিন্তু মানুষ নিজে যেহেতু একটি অপূর্ণাঙ্গ বা আংশিক কারণ , তাই তার সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক অবশ্যই‘
অপরিহার্যতা মূলক’
হবে না । মানুষের সহজ-সরল নিষ্পাপ উপলদ্ধিও উপরোক্ত বিষয়টিকে সমর্থন করবে । কারণ , আমরা দেখতে পাই যে , মানুষ সাধারণতঃ খাওয়া পান করা , যাওয়া আসা সহ ইত্যাদি কাজের সাথে সুস্থতা , ব্যাধি , সুন্দর হওয়া বা কুশ্রী হওয়া , লম্বা হওয়া বা খাটো হওয়া ইত্যাদির মত বিষয়গুলোকে এক দৃষ্টিতে দেখে না । প্রথম শ্রেণীর কাজগুলো মানুষের ইচ্ছার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত । ঐসব কাজ করা বা না করার ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে । ঐ ধরণের কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে মানুষ আদেশ , নিষেধ , প্রশংসা বা তিরস্কারের সম্মুখীন হয় । কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর (সুন্দর বা কুশ্রী হওয়া , লম্বা বা খাটো হওয়া) কাজ বা বিষয়গুলোর ব্যাপারে মানুষের আদৌ কোন দায়িত্ব নেই । ইসলামের প্রাথমিক যুগে‘
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের’
মধ্যে মানুষের সম্পাদিত কাজের ব্যাপারে দু’
টো বিখ্যাত মতাবলম্বি দলের অস্তিত্ব ছিল । তাদের একটি দলের বিশ্বাস অনুসারে মানুষের সম্পাদিত কাজসমূহ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল । অর্থাৎ মানুষ তার কাজকর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে পরাধীন । তাদের মতে মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার কোন মূল্যই নেই । আর দ্বিতীয় দলটির মতে মানুষ তার কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কাজের সাথে আল্লাহর ইচ্ছার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই । তাদের দৃষ্টিতে মানুষ আল্লাহ নির্ধারিত ভাগ্য সংক্রান্ত নিয়মনীতি থেকে মুক্ত । কিন্তু আ হলে বাইতগণের (আ.) শিক্ষানুযায়ী (যাদের শিক্ষা পবিত্র কুরআনের শিক্ষারই অনুরূপ) মানুষ তার কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন । তবে এক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয় । বরং মহান আল্লাহ আপন স্বাধীনতার মাধ্যমে ঐ কাজটি সম্পাদন করতে চেয়েছেন । অর্থাৎ মানুষের কাজ নির্বাচন করার স্বাধীনতা অন্যান্য অপূর্ণাঙ্গ কারণসমূহের মতই একটি আংশিক কারণ মাত্র । তাই কারণের পূর্ণতা অর্জন মাত্রই তা বাস্তবায়নের‘
অপরিহার্যতা’
আল্লাহই প্রদান করেছেন এবং তা আল্লাহর ইচ্ছারই প্রতিফলন । তাই এর ফলে আল্লাহর এ ধরণের ইচ্ছা ,‘
অপরিহার্য’
ক্রিয়াস্বরূপ আর মানুষও ঐ ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন বটে । অর্থাৎ ঐ ক্রিয়া সম্পাদিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার সামগ্রিক (পূর্ণাঙ্গ) কারণ সমূহের মোকাবিলায় ক্রিয়ার বাস্তবায়ন অপরিহার্য । আর মানুষের কার্যনির্বাচন বা সম্পাদনের স্বাধীনতা তার কার্য সম্পাদনের অসংখ্য অসম্পূর্ণ কারণগুলোর মত একটি আংশিক কারণ মাত্র । তাই তার ঐ স্বাধীনতা (যা পূর্ণাঙ্গ কারণের একটি অংশ মাত্র) প্রেক্ষাপটে ঐ কাজটি ঐচ্ছিক ও সম্ভাব্য (অপরিহার্য নয়) একটি বিষয় মাত্র ।
ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন : মানুষ তার কাজে সম্পূর্ণ পরাধীনও নয় আবার সম্পূর্ণ সার্বভৌমও নয় । বরং এ ক্ষেত্রে মানুষ এ দু’
য়ের মাঝামাঝিই অবস্থান করছে ।
লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য গণ হেদায়েত
যদি একটি ধানের বীজ উপযুক্ত পরিবেশে মাটির বুকে পোতাঁ হয় , তাহলে তাতে দ্রুত অংকুরোদগম ঘটে ও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে । তখন ঐ অংকুরটি প্রতি মূহুর্তেই একেকটি নতুন অবস্থা ধারণ করতে থাকে । এভাবে প্রকৃতি নির্ধারিত একটি সুশৃংখল পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পথ অতিক্রম করে তা একটি পূর্ণাঙ্গ ধান গাছে রূপান্তরিত হয় , যার মধ্যে নতুন ধানের শীষ শোভা পেতে থাকে । এখন আবার যদি ঐ ধানের শীষ থেকে একটি ধানের বীজ মাটিতে পড়ে , তাহলে তাও পুনরায় পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ঐ নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে অবশেষে তা একটি পূর্ণাঙ্গ ধান গাছে রূপান্তরিত হবে । একটি ফলের বীজ যদি মাটির বুকে প্রবেশ করে , তাহলে এক সময় তার আবরণ ভেদ করে সবজু ও কচি অংকুর বের হয় । এরপর ঐ কচি অংকুরটিও সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় এবং সুনির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করার পর একটি পূর্ণাঙ্গ ও ফলবান বৃক্ষে রূপান্তরিত হয় । প্রাণীজ শুক্রানু যদি ডিম্বানু বা মাতৃগর্ভে স্থাপিত হয় , তাহলে তা দ্রুত বিকাশ লাভ করতে শুরু করে । এরপর তা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট পরিবেশ এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্তের পর তার পূর্ণবিকাশ ঘটে এবং তা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয় । উক্ত সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও পথ অতিক্রমের নির্দিষ্ট একটি পরিণতিতে উন্নীত হওয়ার এই নিয়ম নীতি এ সৃষ্টিজগত ও প্রকৃতির সর্বত্রই বিরাজমান । ধানের বীজ বিকশিত হয়ে কখনোই একটি গরু বা ছাগেল বা ভেড়ায় রূপান্তরিত হয় না । তেমনি প্রাণীর বীর্য সমগোত্রীয় প্রাণীর গর্ভে স্থাপিত হয়ে কখনোই তা ধান বা ফল গাছে পরিণত হবে না । এমনকি ঐ গাছ বা প্রাণীর গর্ভ ধারণ ক্রিয়ায় যদি ত্রুটিও থেকে থাকে , তাহলে দৈহিক ত্রুটিসম্পন্ন গাছ বা প্রাণীর জন্ম হতে পারে কিন্তু তার ফলে বিষম গোত্রীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের জন্ম লাভ ঘটবে না ।
এ প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু , উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যেই একটি সুশৃংখল ও সুনির্দিষ্ট বিকাশ প্রক্রিয়ার নিয়মনীতি নিহিত রয়েছে । এ জগতের প্রতিটি সৃষ্টির মাঝে সুপ্ত বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট বিকাশ প্রক্রিয়া ও তার নিয়মনীতির অস্তিত্ব এক অনস্বিকার্য ও বাস্তব সত্য । উল্লেখিত সূত্র থেকে দু’
টো বিষয় আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । সেগুলো নিম্নরূপঃ
১ । জগতের প্রতিটি সৃষ্টিই তার জন্মের পর থেকে শেষ পর্যন্ত বিকাশ লাভের যে স্তরগুলো অতিক্রম করে , সেগুলোর মধ্যে অবশ্যই একটি গভীর ও সুশৃংখল সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে । যার ফলে বিকাশ লাভের প্রতিটি স্তর অতিক্রমের পর তা তার পরবর্তী স্তরের দিকে অগ্রগামী হয় ।
২ । বিকাশের এ স্তরগুলোর মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সংযোগ ও সুশৃংখল সম্পর্কের কারণেই তার সর্বশেষ স্তরে উপনীত হওয়ার পর ঐ নির্দিষ্ট উদ্ভিদ বা প্রাণীর পূর্ণাঙ্গরূপই লাভ করতে দেখা যায় । আর এ নীতির বৈপরীত্য সৃষ্টি জগতে বা প্রকৃতির কোথাও পরিলক্ষিত হয় না । যেমনঃ পূর্বেই বলা হয়েছে ধানের বীজ বিকশিত হয়ে কোন প্রাণীতে পরিণত হয় না । তেমনি নির্দিষ্ট কোন প্রাণীর বীর্য্য বিকশিত হয়ে কোন উদ্ভিদ বা অন্য কোন প্রাণীর জন্ম দেয় না । প্রকৃতির সর্বত্রই সকল প্রাণী বা উদ্ভিদের প্রত্যেকেই তার সুনির্দিষ্ট বিকাশ প্রক্রিয়ায় তার গোত্রীয় স্বকীয়তা বজায় রাখে ।
পবিত্র কুরআনে , প্রকৃতিতে বিরাজমান এই সুশৃংখল নীতির পরিচালক হিসেবে মহান আল্লাহকেই্ পরিচিত করানো হয়েছে । তিনি এ প্রকৃতির একমাত্র ও নিরংকুশ প্রতিপালক ।
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন , অতঃপর পথ নির্দেশনা দিয়েছেন । (সূরা আত‘
ত্বা’
হা’
৫০ নং আয়াত ।)
পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে : যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন এবং পথ পদর্শন করেছেন । (সূরা আল আ’
লা , ২ ও ৩ নং আয়াত ।)
মহান আল্লাহ এর ফলাফল স্বরূপ বলেন : প্রতিটি জিনিসেরই একটি লক্ষ্য রয়েছে , যে (দিকে) লক্ষ্য পানে সে অগ্রসর হয় । (সূরা আল বাকারা , ১৪৮ নং আয়াত ।)
আমরা নভো-মণ্ডল ও ভুমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে (লক্ষ্যহীন ভাবে) সৃষ্টি করিনি ; আমরা এ গুলোকে যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি (প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে) করেছি ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না । (সূরা আদ্ দুখান ৩৯ নং আয়াত ।)
বিশেষ হেদায়েত
এটা একটা সর্বজনবিদিত ব্যাপার যে , মানব জাতিও এ সকল সাধারণ ও সার্বজনীন নীতি থেকে মুক্ত নয় । সৃষ্টিগত ঐশী নির্দেশনা নীতি যা সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আছে , তা মানুষের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করবে । যেমন করে এ বিশ্বের প্রতিটি অস্তিত্ব তার সর্বস্ব দিয়ে পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে অগ্রগামী হয় এবং নির্ধারিত পথও প্রাপ্ত হয় । একইভাবে মানুষও ঐ প্রাকৃতিক ঐশী পথ নির্দেশনার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের পথে পরিচালিত হয় । একই সাথে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সাথে মানুষের যেমন অসংখ্য সাদৃশ্য রয়েছে , তেমনি অসংখ্য বৈসাদৃশ্যও তার রয়েছে । ঐ সব বৈসাদৃশ্য মূলক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই মানুষকে অন্য সকল উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে পৃথক করা যায় । বুদ্ধিমত্তাই মানুষকে চিন্তা করার ক্ষমতা দান করেছে । আর এর মাধ্যমেই মানুষ তার নিজের স্বার্থে মহাশূন্য মহাসাগরের গভীর তলদেশকেও জয় করতে সক্ষম হয়েছে । মানুষ এই ভুপৃষ্ঠের সকল বস্তু প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের উপর তার প্রভুত্ব বিস্তার করে , তাকে নিজ সেবায় নিয়োজিত করতে সমর্থ হয়েছে । এমনকি যতদুর সম্ভব , মানুষ তার স্বজাতির কাছ থেকেও কম বেশী লাভবান হয় ।
মানুষ তার প্রাথমিক স্বভাব অনুযায়ী নিরংকুশ স্বাধীনতা অর্জনের মাঝেই তার বিশ্বাসগত সৌভাগ্য এবং পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে বলে মনে করে । কিন্তু মানুষের অস্তিত্বের গঠন প্রকৃতিই সামাজিক সংগঠন সদৃশ্য ।
মানব জীবনে অসংখ্য প্রয়োজন রয়েছে । এককভাবে ঐসব প্রয়োজন মেটানো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । একমাত্র পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক ভাবেই এই মানব জীবনের ঐসব অভাব মেটানো সম্ভব । অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে মানুষ তার স্বজাতীয় স্বাধীনতাকামী ও আত্মঅহংকারী মানুষের সহযোগিতা গ্রহণে বাধ্য । এর ফলে মানুষ তার স্বাধীনতার কিয়দংশ এ পথে হারাতে বাধ্য হয় । এক্ষেত্রে মানুষ অন্যদের কাছ থেকে যতটকু পরিমাণ লাভবান হয় , তার মোকাবিলায় সমপরিমাণ লাভ তাকে পরিশোধ করতে হয় । অন্যদের কষ্ট থেকে সে যতদুর লাভবান হয় , অন্যদের লাভবান করার জন্য ঐ পরিমাণ কষ্টও তাকে সহ্য করতে হয় । অর্থাৎ পারস্পরিক সামাজিক সহযোগিতা গ্রহণ ও প্রদানে মানুষ বাধ্য । নবজাতক ও শিশুদের আচরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই এ সত্যের মর্ম উপলদ্ধি করা সম্ভব হবে । নবজাতক শিশু শুধুমাত্র কান্না এবং জিদ ছাড়া নিজের চাহিদা পূরণের জন্য আর অন্য কোন পন্থার আশ্রয় নেয় না । কোন নিয়ম-কানুনই তারা মানতে চায় না । কিন্তু শিশুর বয়স যতই বাড়তে থাকে ততই তার চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে । এর ফলে ক্রমেই সে বুঝতে শেখে যে , শুধুমাত্র জিদ ও অবাধ্যতা এবং গায়ের জোর খাটিয়ে জীবন চালানো সম্ভব নয় । বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমেই সে সমাজের লোকজনের সংস্পর্শে আসে । এরপর ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে সে পূর্ণাঙ্গ এক সামাজিক বিশ্বাসত্বে রূপান্তরিত হয় এবং এভাবে সে সামাজিক আইন-কানুনের পরিবেশর কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় । পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ সমাজ মেনে নেয়ার পাশাপাশি মানুষ আইনের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে । যে আইন সমগ্র সমাজকে শাসন করবে , এবং সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিতে দায়িত্বও নির্ধারণ করবে । সেখানে আইন লংঘনকারীর শাস্তিও নির্দিষ্ট থাকবে । উক্ত আইন সমাজে প্রচলিত হওয়ার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই সৌভাগ্যের অধিকারী হবে । সৎ ব্যক্তি তার প্রাপ্য হিসেবে উপযুক্ত সামাজিক সম্মানের অধিকারী হবে । আর এটাই সেই সার্বজনীন আইন , যা সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মানব জাতি যার আকাংখী ও অনুরাগী হয়ে আছে । মানব জাতি চিরদিন তার ঐ কাংখিত সামাজিক আইনকে তার হৃদয়ের আশা-আকাংখার শীর্ষে স্থান দিয়ে এসেছে । আর তাই মানুষ সব সময়ই তার ঐ কাংখিত আইন প্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে । তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে , ঐ কাংখিত আইন প্রতিষ্ঠা যদি অবাস্তব হত , এবং মানব জাতির ভাগ্যে যদি তা লেখা না থাকতো , তাহলে চিরদিন তা মানব জাতির কাংখিত বস্তু হয়ে থাকতো না ।
মহান আল্লাহ এই পবিত্র কুরআনে মানব সমাজের এই সত্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ“
আমরাই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং এক জনকে অন্যের উপর মর্যাদায় উন্নিত করি , যাতে একে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে ।”
মানুষের আত্ম-অহমিকা ও স্বার্থপরতার ব্যাপারে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন : মানুষতো অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে সৃষ্টি হয়েছে । যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে , তখন সে হয় হা-হুতাশকারী । আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় অতিশয় কৃপণ । (সূরা আল্ মাআ’
রিজ , ২১ নং আয়াত ।)
বুদ্ধিবৃত্তি ও আইন‘
ওহী
’
নামে অভিহিত
আমরা যদি খুব সূক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করি , তাহলে দেখতে পাব যে , মানুষের আজন্ম কাংখিত আইন , যার প্রয়োজনীয়তা মানুষ বিশ্বাসগত বা সমষ্টিগতভাবে তার খোদাপ্রদত্ত স্বভাব দ্বারা উপলদ্ধি করে , যে আইন মানব জাতির সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধান করে । সেটা একমাত্র সেই আইন , যা এই মনুষ্য জগতকে মনুষ্য হওয়ার কারণে কোন বৈষম্য বা ব্যতিক্রম ছাড়াই সাফল্যের শীর্ষে পৌছায় । এ ছাড়া তা মানব জাতির সার্বজনীন পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে । আর এটাও সর্বজন বিধিত ব্যাপার যে , মানব জাতির ইতিহাসে মানুষের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা প্রসূত এমন কোন আদর্শ আইন আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি । মানুষ যদি প্রাকৃতিক ভাবে তার বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এমন কোন আদর্শ আইন রচনা করতে সক্ষম হত , তাহলে এই সুদীর্ঘ মানব ইতিহাসে তা অবশ্যই আমাদের সবার গোচরীভূত হত । বরঞ্চ , উচ্চ মেধা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যে কোন বিশ্বাস ঐ আদর্শ আইন সম্পর্কে সম্যক উপলদ্ধির জ্ঞানের অধিকারী হতেন , যেমনটি বুদ্ধিমান সমাজ তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলদ্ধি করে । আরও স্পষ্ট করে এভাবে বলা যায় যে , মানব সমাজের সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধায়ক পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন আইন , যার মাধ্যমে এ সৃষ্টিজগত প্রাকৃতিক ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত , তা প্রণয়নের দায়িত্ব ও ক্ষমতা যদি মানুষের বুদ্ধিমত্তার উপর অর্পিত হত তাহলে বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন প্রতিটি মানুষই তা উপলদ্ধি করতে সক্ষম হত । ঠিক যেমন করে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে তার লাভ ক্ষতি এবং জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় গুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হয় , তেমনি ঐ জাতীয় আইনের উপলদ্ধি তার জন্য অতি সহজ ব্যাপারই হত । কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে , মানব রচিত এমন কোন আদেশের আইনের সন্ধানই খু্জে পাওয়া যায় না । মানব ইতিহাসে একক কোন ব্যক্তির , গোষ্ঠি বা জাতি সমূহের দ্বারা যেসব আইন এ যাবৎ প্রণীত হয়েছে , তা কোন একটি জনসমষ্টির কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত হলেও অন্যদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য বা স্বীকৃত নয় । অনেকেই ঐ নির্দিষ্ট আইন সম্পর্কে জ্ঞাত হলেও অনেকেই আবার সে সম্পর্কে জ্ঞাত নয় । খোদা প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এবং সৃষ্টিগতভাবে সমান মানুষ ঐ ধরণের মানব রচিত আইন সম্পর্কে সমপর্যায়ের সৃষ্টি মানব জাতিও উপলদ্ধি পোষণ করে না ।
‘
ওহী’
নামে অভিহিত রহস্যাবৃত উপলদ্ধি
পূর্বের আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে , বুদ্ধিমত্তা , মানব জীবনের সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধায়ক নীতিমালা উপলদ্ধি করতে অক্ষম । অথচ মানব জাতিকে সত্য পথে পরিচালনার লক্ষ্যে এ আদর্শ বিধান উপলদ্ধির ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপস্থিতি মানব সমাজের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ঐ ধরণের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিশ্বাসই মানুষকে জীবনের প্রকৃতপক্ষে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবেন এবং আপামর জনসাধারণের কাছে সে ধারণা পৌছে দেবেন । আদর্শ বিধান অনুধাবনের ঐ বিশেষ ক্ষমতা , যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও সাধারণ অনুভুতির বাইরে , তা ওহী বা ঐশীবাণী উপলদ্ধির ক্ষমতা হিসেবে পরিচিত । মানব জাতির মধ্যে বিশেষ কোন ব্যক্তির এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার অর্থ এই নয় যে , একইভাবে অন্য লোকেরাও ঐ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রতিটি মানুষের মধ্যেই জন্মগতভাবে যৌন ক্ষমতা নিহিত রয়েছে । কিন্তু যৌন তৃপ্তির উপলদ্ধি ও তা উপভোগ করার মত যোগ্যতা শুধুমাত্র সেসব ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যাবে , যারা সাবালকত্বের বয়সে উপনীত হয়েছে । নাবালক শিশুর কাছে যৌন তৃপ্তির প্রকৃতি যেমন দূর্বোধ্য এবং রহস্যাবৃত , ওহী বা ঐশীবাণী অনুধাবনে অক্ষম মানুষের কাছে তার মর্ম উপলদ্ধির বিষয়টিও তেমনি রহস্যাবৃত ।
মহান আল্লাহ তার পবিত্র ঐশীবাণী অনুধাবনে সাধারণ মানুষের বুদ্ধিমত্তার অক্ষমতা সম্পর্কে কুরআনে বলেন :“
আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি , যেমনটি নুহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম । আমরা সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি , যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে ।”
(সূরা আন্ নিসা , ১৬২ নং আয়াত ।)
নবীগণ ও‘
ইসমাত
’
বা নিষ্পাপ হওয়ার গুণ
মানবজাতির মাঝে নবীগণের আবির্ভাব পূর্বের আলোচনার সত্যতাই প্রমাণ করে । আল্লাহর নবীগণ এমনসব ব্যক্তি ছিলেন , যারা ওহী বা ঐশীবাণী বহন ও নবুয়তের দাবী করেছেন । তারা তাদের ঐ দাবীর স্বপক্ষে অকাট্য দলিল-প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন । মানবজাতির সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধায়ক ঐশী বিধানই মানুষের মাঝে প্রচার ও আপামর জনসাধারণের কাছে তার অমিয়বাণী তারা পৌছে দিয়েছেন । আল্লাহর নবীগণ ওহী বা ঐশীবাণী এবং নবুয়তের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ছিলেন । তাই যে যুগেই নবীর আবির্ভাব ঘটেছে , সেখানে একই যুগে একজন অথবা অল্পসংখ্যক নবীর বেশী একই সাথে আবির্ভূত হননি । মহান আল্লাহ নবীদেরকে তার ঐশী বিধান প্রচারের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণকে সত্য পথে (হেদায়েত) পরিচালনার দায়িত্বের কাজ পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করেছেন । এ থেকেই বোঝা যায় যে , আল্লাহ নবীকে অবশ্যই‘
ইসমাত’
বা‘
নিষ্পাপের গুণে গুনান্বিত হতে হবে । অর্থাৎ মহান আল্লাহর ওহী বা ঐশীবাণী গ্রহণ , ধারণ এবং তা জনগণের কাছে পৌছে দেয়ার ব্যাপারে তাকে অবশ্যই যে কোন ধরণের ভুল বা ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে নিরাপদ থাকতে হবে । তেমনি যেকোন ধরণের পাপ বা অবাধ্যতা (ঐশী বিধানের লঘংন) থেকে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে । যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে , মহান ঐশীবাণী গ্রহণ , সংরক্ষণ ও জনগণের কাছে তা প্রচারের বিষয়টি খোদাপ্রদত্ত সৃষ্টিগত হেদায়েতের প্রক্রিয়ার তিনটি মৌলিক ভিত্তি বিশেষ । আর সৃষ্টিগত (প্রাকৃতিক) প্রক্রিয়ায় ভুলের কোন স্থান নেই । আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে পাপ বা অবাধ্যতা (ঐশী বিধান লংঘনমূলক) প্রচারকার্যের বাস্তব বিরোধিতা বটে । শুধু তাই নয় , এর ফলে প্রচারকারী পাপজনিত কারণে প্রচারের ব্যাপারে তার প্রতি জনগণের আস্থা ও স্বীয় বিশ্বস্ততা হারায় । এর মাধ্যমে ঐশী আদর্শ প্রচারের মহতী উদ্দেশ্য ধ্বংস হয়ে যায় । তাই মহান আল্লাহ নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার (ইসমাত) ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত দিয়েছেন , তিনি বলেছেন :“
তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম । (সূরা আল্ আনআম , ৮৭ নং আয়াত ।)
তিনি আরও বলেছেন : তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী । তিনি তার অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না , শুধুমাত্র তার মনোনীত রাসূল ছাড়া । সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের আগে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন । রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌছে দিয়েছে কিনা , তা জানার জন্য । (সূরা জ্বিন , ২৬ থেকে ২৭ নং আয়াত ।)
নবীগণ ও ঐশীধর্ম
মহান আল্লাহর নবীগণ ওহীর মাধ্যমে যা পেয়েছেন এবং জনগণের মাঝে আল্লাহর পবিত্র ঐশীবাণী হিসেবে প্রচার করেছেন , তাই দ্বীন হিসেবে পরিচিত । অর্থাৎ মানুষের জীবনযাপনের সঠিক পদ্ধতি ও জীবনের পালনীয় ঐশী দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ , যা মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য ও সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধান করে , তারই নাম দ্বীন ।
এই ঐশী‘
দ্বীন’
বা ধর্ম বিশ্বাসগত ও ব্যবহারিক এই দু’
টি অংশ নিয়ে গঠিত । বিশ্বাসগত অংশটি এক ধরণের মৌলিক বিশ্বাস ও কিছু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে গঠিত , যার উপর ভিত্তি করে মানুষ তার জীবনযাপন পদ্ধতি নির্ধারণ করে । এই মৌলিক বিশ্বাসের তিনটি মূল অংশ রয়েছে :
১. একত্ববাদ
২. নবুয়ত
৩. পুনরূত্থান বা কেয়ামত
এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের একটিতেও যদি বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় , তাহলে‘
দ্বীন’
বা ধর্ম সেখানে অস্তিত্ব লাভ করতে পারবে না ।‘
দ্বীনের’
ব্যবহারিক অংশ : এ অংশটিও বেশ কিছু ব্যবহারিক ও আচরণগত দায়িত্ব ও কর্তব্যের সমন্বয়ে রচিত । মূলত সর্বস্রষ্টা আল্লাহ ও সমাজের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর ভিত্তি করেই এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য রচিত । এ কারণেই ঐশীবিধান নির্দেশিত মানুষের দায়িত্ব সাধারণতঃ দু’
ভাগে বিভক্ত :
১ । ব্যবহারিক কিছু কাজের দায়িত্ব এবং
২ । শিষ্টাচারগত কর্তব্য
এদু’
টি অংশ আবার দু’
ভাগে বিভক্ত যেমনঃ বেশ কিছু ব্যবহারিক কাজ ও শিষ্টাচার শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সাথেই সংশ্লিষ্ট যথাঃ সচ্চরিত্র , ঈমান , সততা , নিষ্কলুষতা , আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পন , তার প্রতি সন্তুষ্টি পোষণ , নামায , রোযা , কুরবানী এবং এ জাতীয় অন্যান্য ইবাদত , আল্লাহর প্রতি ভক্তি পোষণ ইত্যাদি মানুষকে আল্লাহর প্রকৃত ও অনুগত দাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে । আবার বেশ কিছু শিষ্টাচার ও কাজ আছে যা সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট । যেমন মানুষের সদাচারণ , মানুষের কল্যাণ কামনা , ন্যায়বিচার , দানশীলতা , মানুষের পারস্পরিক মেলামেশা সংক্রান্ত দায়িত্ব , পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদি । এ অংশটি সাধারণতঃ পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় হিসেবে পরিচিত । ওদিকে মানব জাতি সর্বদাই ক্রম উন্নয়নমুখী । সর্বদাই মানুষ পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বকামী । তাই মানব সমাজ সময়ের আবর্তনে ক্রমশই উন্নততর হয় । তাই ঐশী বিধানের ক্রমোন্নতি বা বিকাশও অপরিহার্য । আর পবিত্র কুরআনও এই ক্রমোন্নতি ও বিকাশকে (যেমনটি বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে) সমর্থন করে । যেমন : কুরআনে বলা হয়েছে , এযাবৎ অবতির্ণ প্রতিটি ঐশী বিধানই তার পূর্বের ঐশী বিধানের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ এবং উন্নততর ।
তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন : আমি আপনার প্রতি সত্যসহ ঐশীগ্রন্থ (কুরআন) অবতির্ণ করেছি যা এর পূর্বে অবতির্ণ ঐশীগ্রন্থের (যেমন ইঞ্জিল , তৌরাত) সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী স্বরূপ । (সূরা আল্ মায়েদা , ৪৮ নং আয়াত ।)
বিজ্ঞান এবং কুরআনের দৃষ্টিতে মানব জীবন অমর ও চিরন্তন নয় । তাই তার উন্নয়ন ও বিকাশও অন্তহীন নয় । এ কারণে বিশ্বাস ও কাজের দিক থেকে মানুষের দায়িত্বও একটি বিশেষ স্তরে এসে থেম যেতে বাধ্য । একইভাবে মৌলিক বিশ্বাসের পূর্ণতা ও ব্যবহারিক ঐশী বিধানের বিস্তৃতি চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছার কারণে নবুয়ত ও শরীয়তের (ঐশীবিধান) বিকাশ ধারার সমাপ্তি ঘটাতে বাধ্য । এ কারণেই পবিত্র কুরআন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বশেষ নবী এবং ইসলামকে পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠত্ব্ম ঐশীধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছে । আর একথাও বলেছে যে , এই ঐশীগ্রন্থ (পবিত্র কুরআন) চির অপরিবর্তনীয় ও মহানবী (সা.) নবুয়তের ধারা সমাপণকারী । আর ইসলাম ধর্মকে মানুষের সকল প্রয়োজনীয় দায়িত্বের আধার হিসেবে পরিচিত করিয়েছেন ।
তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :“
এটা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ এর সামনে বা পিছনে কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না ।”
(সূরা ফসুসিলাত , ৪১-৪২ নং আয়াত ।)
মহান আল্লাহ আরও বলেন :‘
মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন , বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী ।’
পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে : আমি তোমাদের জন্যে প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখা স্বরূপ এই ঐশীগ্রন্থ (কুরআন) অবতির্ণ করেছি । (সূরা আন্ নাহল , ৮৯ নং আয়াত ।)
নবীগণ ও‘
ওহী’
জনিত প্রমাণ এবং নবুয়ত
বর্তমান পৃথিবীর অনেক বিজ্ঞানী , গবেষক ও পণ্ডিতগণই ওহী (ঐশীবাণী) ও নবুয়ত এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলিয়েছেন এবং তাদের গবেষণালদ্ধ ফলাফলকে সামাজিক মনস্তত্বের ভিত্তিতে ব্যাখাও দিয়েছেন । তাদের ব্যাখা অনুসারে পৃথিবীর ইতিহাসে আগত আল্লাহর নবীগণ ছিলেন পবিত্র অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি । তারা ছিলেন অত্যন্ত মহতী উদ্দেশ্যের অধিকারী , মানব হিতাকাংখী । তাঁরা মানব জাতির পার্থিব ও আত্মিক উন্নয়ন ও দূর্নীতিপূর্ণ সমাজ সংস্কারের জন্য আদর্শ আইন প্রণয়ন করেন এবং মানুষকে তা গ্রহণের আহবান জানান । যেহেতু সে যুগের মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিগত যুক্তির কাছে আত্মসমর্পন করতো না , তাই বাধ্য হয়ে তাদের আনুগত্য ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই তারা নিজেদেরকে এবং স্বীয় চিন্তাধারাকে উচ্চতর ও ঐশীজগতের সাথে সম্পর্কিত বলে ঘোষণা করেন । তারা নিজেদের পবিত্র আত্মাকে‘
রূহুল কুদুস্’
(পবিত্র আত্মা) এবং তা থেকে নিঃসৃত চিন্তাধারাকে‘
ওহী’
ও‘
নবুয়ত’
হিসেবে ঘোষণা করেন । আর তদসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সমূহকে‘
শরীয়ত’
বা ঐশীবিধান এবং যে গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ আছে তাকে‘
ঐশীবাণী’
হিসেবে অভিহিত করেন ।
কিন্তু ন্যায়বিচারপূর্ণ সুগভীর দৃষ্টিতে ঐ ঐশী গন্থসমূহ , বিশেষ করে পবিত্র কুরআন এবং নবীগণের শরীয়ত (ঐশী বিধানসমূহ) পর্যবেক্ষণ করলে অবশ্যই এ ব্যাপারে সবাই একমত হতে বাধ্য যে নিঃসন্দেহে উপরোক্ত মতামতটি সঠিক নয় ।
আল্লাহর নবীগণ কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না । বরং তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যের প্রতিভু । কোন ধরণের অতিরঞ্জন ছাড়াই তারা তাদের অনুভুতি ও উপলদ্ধির কথা প্রকাশ করতেন । যা তারা বলতেন , তাই তারা করতেন ।‘
ওহী’
প্রাপ্তির যে দাবীটি তারা করতেন , তা ছিল এক রহস্যাবৃত বিশেষ উপলদ্ধি , যা অদৃশ্য সহযোগীতায় তাদের সাথে যুক্ত হত । এভাবে তারা বিশ্বাসগত ব্যবহারিক কাজের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হতেন এবং তা জনগণের কাছে পৌছে দিতেন । উপরের আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে , নবুয়তের দাবী মেনে নেয়ার জন্য যথেষ্ট যুক্তি ও দলিল প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে । নবীদের আনীত ঐশীবিধান (শরীয়ত) বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞার অনুকুলে হওয়াই নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট নয় । কারণ নবুয়তের দাবীদার নবী রাসূলগণ নিজেদের আনীত ঐশীবিধানের (শরীয়ত) সত্যতা ও পরিশুদ্ধতার পাশাপাশি উচ্চতর ও ঐশীজগতের সাথে নিজেদের সংযুক্ত (ওহী ও নবুয়ত) দাবী করেন । তারা দাবী করেন যে , মানুষকে সৎপথের দিকে আহবান করার জন্যে তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত । আর এই দাবী অবশ্যই তার সত্যতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে । আর একারণে প্রতি যুগেই (যেমনটি পবিত্র কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে) মানুষ তাদের সাধারণ বুদ্ধির উপর ভিত্তি করেই নবুয়তের দাবীর সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এর দাবীকারীদের কাছে নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ বিশেষ অলৌকিক ঘটনা (মু’
জিযা) প্রদর্শনের দাবী জানিয়েছে । আর মানুষের এই সহজ সাধারণ বুদ্ধিপ্রসূত যুক্তি এটাই প্রমাণ করে যে , নবুয়তের দাবীদার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অবশ্যই অন্য সকল সাধারণ মানুষের মধ্যে খুজে পাওয়া যাবে না । এই বিশেষ পদের জন্যে এমন বিশেষ এক অদৃশ্য ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য , যা মহান আল্লাহ অলৌকিক ভাবে একমাত্র তার নবীগণকেই দান করেন । আল্লাহ প্রদত্ত ঐ বিশেষ ক্ষমতা বলে নবীগণ আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত হন এবং দায়িত্ব স্বরূপ জনগণের কাছে তা পৌছে দেন । তাই তাদের দাবী যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে , তাদের ঐ দাবীর সত্যতা প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহর কাছে অলৌকিক কোন কান্ড পদর্শনের আবেদন জানানো উচিত , যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাদের দাবীর সত্যতা বিশ্বাস করতে পারে । এ বিষয়টি পরিস্কার যে যুক্তি ও বুদ্ধির দৃষ্টিতে নবীদের কাছে তাদের নবুয়তের দাবীর সত্যতা প্রমাণ স্বরূপ অলৌকিক কোন কান্ড (মু’
জিযা) প্রদর্শনের দাবী নিঃসন্দেহে অত্যন্ত যৌক্তিকতাপূর্ণ একটি ব্যাপার । তাই নবীদেরকে তাদের সত্যতার প্রমাণের উদ্দেশ্যেপ্রথমেই জনগণের দাবী অনুযায়ী অলৌকিক ঘটনা (মু’
জিযা) পদর্শন করা উচিত । এমনকি পবিত্র কুরআনও এই যুক্তিকে জোরালো ভাবে সমর্থন করেছে । তাই পবিত্র কুরআনেও নবীদের ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে , তাঁরা তাদের নবুয়ত প্রমাণের স্বার্থে প্রথমেই অথবা জনগণের দাবী অনুযায়ী অলৌকিক কান্ড (মু’
যিজা) প্রদর্শন করেছেন । অবশ্য অনেক খুতখুতে লোকই নবীদের ঐসব অলৌকিক কান্ডের (মু’
যিজা) অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে । কিন্তু তাদের ঐ অস্বীকৃতির পেছনে শক্তিশালী কোন যুক্তি তারা দাড়ঁ করাতে সক্ষম হয়নি । কোন ঘটনার জন্যে আজ পর্যন্ত যেসব কারণ সাধারণতঃ অনুভবযোগ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে , সেগুলোর চিরন্তন ও স্থায়ী হবার পেছনে কোন দলিল বা যুক্তিই নেই । আর কোন ঘটনাই তার নিজস্ব ও স্বাভাবিক শর্ত ও কারণ সমূহ পূর্ণ হওয়া ব্যতীত বাস্তবায়িত হয় না । যেসব অলৌকিক কান্ড আল্লাহর নবীদের সাথে সম্পর্কিত , তা প্রকৃতঅর্থে মৌলিকভাবে অসম্ভব এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞা বিরোধী (যেমন , জোড় সংখ্যা বিজোড় সংখ্যায় রূপান্তরিত হওয়া যা অসম্ভব) ব্যাপার নয় বরং তা ছিল অস্বাভাবিক ব্যাপার , যেমনটি বহু সাধু পরুষের ক্ষেত্রেই অতীতে দেখা ও শোনা গিয়েছে ।
আল্লাহর নবীদের সংখ্যা
ইতিহাসের সাক্ষানুসারে আল্লাহর অসংখ্য নবীই এ পৃথিবীতে এসেছেন । পবিত্র কুরআনও এ বিষয়েরই সাক্ষী দেয় । যাদের মধ্যে অনেকের নাম ও ইতিহাসই পবিত্র কুরআন উল্লেখ করেছে । আবার তাদের অনেকের নামই পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়নি ।
কিন্তু নবীদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য কারো কাছেই নেই । এ ব্যাপারে হযরত আবুজার গিফারী (রা.) বর্ণিত রাসূল (সা.)-এর এ সংক্রান্ত হাদীসই আমাদের একমাত্র সম্বল । ঐ হাদীসের তথ্য অনুসারে নবীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার ।
শরীয়ত প্রবর্তক‘
উলুল আযম’
নবীগণ
পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অনুসারে প্রত্যেক নবীই শরীয়তের (ইসলামী আইন শাস্ত্র) অধিকরী ছিলেন না । নবীদের মধ্যে শুধুমাত্র পাঁচজনই ছিলেন‘
শরীয়ত’
প্রবর্তক । যারা হচ্ছেন : হযরত নুহ (আ.) , হযরত ইব্রাহীম (আ.) , হযরত মুসা (আ.) , হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) । অন্ যান্য নবীগণ এসব‘
উলুল আয্ম’
নবীদের আনীত শরীয়তের অনুসারী ছিলেন ।
মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন : তিনি তোমাদের জন্যে দীনকে বিধিবদ্ধ করেছেন , যার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন তিনি নুহ কে-আর যা আমি‘
ওহী’
(প্রত্যাদেশ) করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়ে ছিলাম ইব্রাহীম , মুসা ও ঈসাকে । (সূরা আশ শুরা , ১২ নং আয়াত ।)
মহান আল্লাহ আরো বলেন যে ,“
স্মরণ কর , যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নবীদের নিকট হতে , তোমার নিকট হতে , এবং ইব্রাহীম , মুসা ও মারিয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে , আর তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম সুদৃঢ় অঙ্গীকার । (সূরা আল্ আহযাব ,৭ নং আয়াত ।)
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বশেষ নবী । পবিত্র কুরআন তার উপর অবতির্ণ হয়েছে এবং তিনিই‘
শরীয়ত’
প্রবর্তক । বিশ্বের সকল মুসলমানই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে । হযরত মুহাম্মদ (সা.) হিজরী চন্দ্র বর্ষ শুরু হওয়ার প্রায় তিপ্পান্ন বছর পূর্বে পবিত্র মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশের বনি হাশিম গোত্রের (সম্মানিত বংশ হিসেবে খ্যাত) জন্ম গ্রহণ করেন । তার বাবার নাম ছিল আব্দুল্লাহ এবং মায়ের নাম ছিল আমিনা । শৈশবের পাক্কালেই তিনি তার বাবা ও মাকে হারান । এরপর তাঁর দাদা জনাব আব্দুল মুত্তালিব তাঁর অভিভাবক হন । কিন্তু এর অল্প ক’
দিন পর তার স্নেহময় দাদাও পরলোক গমন করেন । তারপর তার চাচা জনাব আবু তালিব দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং নিজের ঘরে তাকে নিয়ে যান । তারপর থেকে মহানবী চাচার বাড়িতেই মানুষ হতে লাগলেন । মহানবী (সা.) সাবালকত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই চাচার সাথে ব্যবসায়িক সফরে দামেষ্ক গিয়েছিলেন । মহানবী (সা.) কারো কাছেই লেখাপড়া শেখেননি । কিন্তু সাবালক হওয়ার পর থেকেই তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ , ভদ্র এবং বিশ্বস্ত হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন । তাঁর এই বিজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার কারণেই মক্কার জনৈকা বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী মহিলা তাকে তার ব্যবসা পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব অর্পন করেন । ঐ ব্যবসার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) আবারও দামেষ্ক ভ্রমণ করেন । ঐ ব্যবসায়িক ভ্রৃমনে নিজের অতুলনীয় যোগ্যতার কারণে মহানবী (সা.) সেবার প্রচুর পরিমাণে লাভবান হন । মহানবী (সা.)-এর ঐ অতুলনীয় যোগ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর অল্প ক’
দিন পরই মক্কার ঐ বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী মহিলা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন । মহানবী (সা.)-ও ঐ পস্তাব মেনে নেন । অতঃপর মহানবী (সা.)-এর সাথে ঐ ভদ্র মহিলার বিয়ে হয় । বিয়ের সময় মহানবী (সা.)- এর বয়স ছিল পচিশ বছর । বিয়ের পর চল্লিশ বছর বয়সে পৌছা পর্যন্ত এভাবেই মহানবী (সা.) তার দাম্পত্য জীবন কাটান । এসময় অসাধারণ বিজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার জন্যে জনগণের মধ্যে তিনি ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেন । কিন্তু কখনোই তিনি মূর্তি পুজা করেননি । অথচ মূর্তি পুজোই ছিল সে যুগের আরবদের ধর্ম । তিনি প্রায়ই নির্জনে গিয়ে সর্বস্রষ্টা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও ধ্যান করতেন । এভাবে একবার যখন তিনি মক্কার নিকটবর্তী‘
তাহামা’
পাহাড়ের‘
হেরা’
গুহায় বসে নির্জনে মহান আল্লাহর ধ্যানে গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন । তখনই আল্লাহ তাকে নবী হিসেবে নির্বাচন করেন এবং ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেন । পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম সূরাটি (সূরা আলাক) তখনই তার প্রতি অবতির্ণ হয় । এ ঘটনার পর তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে যান । বাড়ী ফেরার পথে স্বীয় চাচাতো ভাই হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের সাথে তার সাক্ষাত হয় । তিনি সব কিছু তাকে খুলে বলেন । হযরত আলী (আ.) সাথে সাথেই তাকে নবী হিসেবে মেনে নেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন । অতঃপর বাড়িতে ফিরে স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)-কেও সব কিছু খুলে বলেন এবং হযরত খাদিজা (রা.)-ও সাথে সাথেই নবী হিসেবে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন । মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম যখন জনগণকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান জানান , তখন তিনি অত্যন্ত কষ্টকর ও বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হন । যার ফলে বাধ্য হয়ে বেশ কিছু দিন যাবৎ তিনি গোপনে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যান । পুনরায় তিনি নিজ আত্মীয়স্বজনের কাছে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন । কিন্তু তার ঐ প্রচেষ্টা সফল হয়নি । আত্মীয়দের মধ্যে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) ছাড়া আর কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি । (অবশ্য নির্ভরযোগ্য শীয়া সূত্র অনুযায়ী যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে , তিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু তিনি মহানবী (সা.) এর একমাত্র সহযোগী ছিলেন , তাই ইসলাম জনসমক্ষে শক্তিশালী রূপধারণ করা পর্যন্ত কুরাইশদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জনগণের কাছে নিজের ঈমানের বিষয়টি গোপন রেখে ছিলেন ।) গোপনে ইসলাম প্রচারের কিছুদিন পরই আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (সা.) প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং তার বাস্তবায়ন শুরু করেন । আর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথেই এর কঠিন ও বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায় । মহানবী (সা.) ও নব মুসলিমদের প্রতি মক্কাবাসীদের সমস্ত ধরণের অত্যাচার শুরু হয় । এমনকি মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যে , শেষ পর্যন্ত বেশ কিছু মুসলমান তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে দেশত্যাগ করে‘
আবিসিনিয়ায়’
(ইথিওপিয়া) গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় । আর মহানবী (সা.) তার প্রিয় চাচা হযরত আবু তালিব এবং বনি হাশিম গোত্রের আত্মীয়বর্গসহ মক্কার উপকন্ঠে‘
শো’
বে আবি তালিব’
নামক এক পাহাড়ী উপত্যকায় দীর্ঘ তিনটি বছর বন্দী জীবনের কষ্ট ও দূর্ভোগ সহ্য করেন । মক্কাবাসীরা সব ধরণের লেনদেন ও মেলামেশা ত্যাগ করে এবং একই সাথে মহানবী (সা.) ও তার সমর্থকদেরকে সম্পূর্ণ রূপে এক ঘরে করে রাখে । ঐ অবস্থা থেকে মহানবী (সা.) ও তার অনুসারীদের বেরিয়ে আসার সুযোগও ছিল না । মক্কার মূর্তি পুজারীরা অত্যাচার অপমান , বিশ্বাসঘাতকতা সহ মহানবী (সা.)-এর উপর যে কোন ধরণের চাপ প্রয়োগেই কুন্ঠিত হয়নি । তথাপি মহানবী (সা.) কে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে কুরাইশরা নম্রতার পথও বেছে নেয় । তারা মহানবী (সা.)-কে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও মক্কার নেতৃত্ব পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেয় । কিন্তু কাফেরদের এধরণের হুমকি ও অর্থ লোভ প্রদর্শন , দু’
টোই ছিল বিশ্বনবী (সা.)-এর কাছে সমান । তাই হুমকি ও লোভ দেখিয়ে তারা বিশ্বনবী (সা.)-এর মহতী লক্ষ্য ও পবিত্র প্রতিজ্ঞাকে অধিকতর দৃঢ় করা ছাড়া আর কিছুই করতে সক্ষম হয়নি । একবার কুরাইশরা বিশ্বনবী (সা.)-কে যখন বিপলু অংকের অর্থ এবং মক্কার নেতৃত্ব পদগ্রহণের প্রস্তাব দেয় । মহানবী (সা.) তার প্রত্যুত্তরে বলেনঃ তোমরা যদি সূর্যকে আমার ডান হাতে আর চাঁদকে আমার বাম হাতে এনে দাও , তবুও এক আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর প্রদত্ত দায়িত্ব পালন থেকে কখনোই বিরত হব না । নবুয়ত প্রাপ্তির পর দশম বছরে শো’
বে আলী ইবনে আবি তালিবে’
র বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরই তাকে সাহায্যকারী একমাত্র চাচাও (হযরত আলী ইবনে আবি তালিব) পরকাল গমন করেন । এ ঘটনার কিছুদিন পরই তার একমাত্র জীবনসংঙ্গিনী হযরত খাদিজা (রা.)ও পরলোক গমন করেন । অতঃপর বাহ্যত: মহানবী (সা.)-এর আশ্রয়ের আর কোন স্থান অবশিষ্ট রইল না । সুযোগ বুঝে মক্কার মূর্তি উপাসক কাফেররা গোপনে মহানবী (সা.)-কে হত্যার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আটে । তাদের পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কোন একরাতে মহানবীর বাড়ী ঘেরাও করে এবং শেষরাতে তারা মহানবী (সা.)-এর বাড়ী আক্রমণ করে । তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহানবী (সা.)-কে শায়িত অবস্থাতেই তার বিছানায় টুকরা টুকরা করে ফেলা । কিন্তু ঐ ঘটনা ঘটার পূর্বেই মহান আল্লাহ তার প্রিয় নবী (সা.)-কে ঐ চক্রান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে অবহিত করেন এবং মদীনা গমনের নির্দেশ দেন । সে অনুযায়ী মহানবী (সা.)-ও তার বিছানায় হযরত আলী (আ.)-কে শুইয়ে রেখে রাতের আধারে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নিরাপত্তার মাধ্যমে শত্রুদলের মাঝ দিয়ে‘
ইয়াসরিবের’
(মদীনা) পথে পাড়ি দেন । মহানবী (সা.) বাড়ী থেকে বেরিয়ে বেশ ক’
মাইল পার হবার পর মক্কার বাইরে এক পাহাড়ী গুহায় আশ্রয় নেন । এদিকে মক্কার কাফের শত্রুরা একটানা তিনদিন যাবৎ ব্যাপক খোজাখুজির পরও মহানবী (সা.)-কে না পেয়ে নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরে যায় । শত্রুরা ফিরে যাওয়ার পরই মহানবী (সা.) ঐ গুহা থেকে বের হয়ে পুনরায় মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন । মদীনাবাসীরা ইতিপূর্বেই মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তার হাতে‘
বায়াত’
(আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেছিল । তারা অতিশয় আন্তরিক সংবর্ধনার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানায় । তারা তাদের প্রাণ ও অর্থ সম্পদ সহ সম্পূর্ণ রূপে মহানবী (সা.)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করে । বিশ্বনবী (সা.) তার জীবনে এই প্রথমবারের মত মদীনায় ছোট্র একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন । ইসলামী সমাজ গঠনের পাশাপাশি ইয়াসরেব (মদীনা) ও তার আশেপাশে বসবাসরত ইহুদী ও অন্যান্য শক্তিশালী আরব গোত্রদের সাথে চুক্তি সাক্ষর করেন । অতঃপর তিনি ইসলাম প্রচারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রবৃত্ত হন । রাসূল (সা.)-এর ইয়াসরেবে আগমনের পর থেকে ইয়াসরেব নগরী‘
মদীনাতুর রাসূল (সা.)’
(রাসূলের শহর) তথা মদীনা হিসাবে খ্যাতি লাভ করে । যার ফলে ইসলাম ক্রমেই বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করতে থাকে । ওদিকে কাফেরদের অত্যাচারে জর্জরিত মক্কার মুসলমানরাও একের পর এক বাপদাদার ভিটেমাটি ত্যাগ করে মদীনায় পাড়ি দিতে লাগল । এভাবে অগ্নিমুখ পতঙ্গের মত মুসলমানরা ক্রমেই বিশ্বনবী (সা.)-এর চারপাশে ভীড় জমাতে থাকল । দেশ ত্যাগকারী মক্কার এসব মুসলনরাই ইতিহাসে মহাজির হিসাবে পরিচিত । আর মক্কা থেকে আগত মহাজিরদেরকে সাহা্য্য করার কারণে মদীনাবাসী মুসলমানরাও ইতিহাসে‘
আনসার’
(সাহায্যকারী) নামে খ্যাতি লাভ করে । এভাবে ইসলাম তার সর্বোচ্চ গতিতে উন্নতি লাভ করতে থাকে । কিন্তু এতদসত্ত্বেও মক্কার মূতি পুজারী কুরাইশ এবং আরবের ইহুদী গোত্রগুলো মুসলমানদের সাথে বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস ঘাতকতামূলক কার্য-কলাপ চালিয়ে যেতে কোন প্রকারের দ্বিধাবোধ করেনি । এর পাশাপাশি ওদিকে মুসলমানদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকা অজ্ঞাত পরিচয় মুসলমান নামধারী মুনাফিকরা ঐসব ইহুদী ও কাফেরদের সহযোগীতায় প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন ধরণের জটিল সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকল । অবশেষে ঐসব সমস্যা একসময় যুদ্ধ-বিগ্রহে পর্যবসিত হয় । যার ফলে মূর্তি পুজারী কাফের ও ইহুদীদের সাথে ইসলামের অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয় । তবে সৌভাগ্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামী বাহিনী বিজয়ী ভূমিকা লাভ করে । মহানবী (সা.)-এর জীবনে ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় ৮০ টিরও বেশী যুদ্ধ সংঘটিত হয় । যার মধ্যে বদর , ওহুদ , খন্দক ও খাইবারের মত বড় বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলোর সবগুলোতেই বিশ্বনবী (সা.) স্বয়ং নিজেই অংশ গ্রহণ করেন । ইসলামের সকল বড় বড় এবং বেশ কিছু ছোট যুদ্ধে হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর সেনাপতিত্বেই বিজয় অর্জিত হয় । ইসলামের ইতিহাসে একমাত্র হযরত ইমাম আলী (আ.)-ই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি , যিনি কখনোই যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেননি । হিজরতের পরে অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর মদীনা গমনের পরের দশ বছরে সংঘটিত ঐসব যুদ্ধে সর্বমোট প্রায় দু’
শত মুসলমান এবং প্রায় এক হাজার কাফের নিহত হয় । বিশ্বনবী (সা.)-এর অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টা এবং মহাজির ও আনসার মুসলমানদের আত্মত্যাগের ফলে হিজরত পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ইসলাম সমগ্র আরবের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । ইতিমধ্যে পারস্য , রোম , মিশর ও ইথিওপিয়ার সম্রাটদের কাছেও ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে বিশ্বনবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র পাঠানো হয় । বিশ্বনবী (সা.) আজীবন দরিদ্রদের মধ্যে তাদের মতই জীবনযাপন করেন । তিনি আপন দারিদ্রের জন্যে গর্ববোধ করতেন । তিনি জীবনে কখনোই সময় নষ্ট করেননি । বরং তিনি তার সময়কে মোট তিন অংশে ভাগ করতেন । একাংশ শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্য । অর্থাৎ , আল্লাহর ইবাদত ও তার স্মরণের জন্যে নির্ধারিত রাখতেন ।
আর একাংশ তিনি নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ব্যয় করতেন । আর বাকী অংশ জনগণের জন্যে ব্যয় করতেন । সময়ের এই তৃতীয় অংশকে বিশ্বনবী (সা.) ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা ও তার প্রচার , ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা , সমাজ সংস্কার , মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানো , রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিন বৈদেশিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ সহ বিভিন্ন কাজে ব্যয় করতেন । বিশ্বনবী (সা.) পবিত্র মদীনা নগরীতে দশ বছর অবস্থানের পর জনৈকা ইহুদী মহিলার বিষ মিশানো খাদ্য গ্রহণে অসুস্থ হয়ে পড়েন । অতঃপর বেশ ক’
দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে তিনি পরলোক গমন করেন । যেমনটি হাদীসে পাওয়া গেছে , শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্বে বিশ্বনবী (সা.) ক্রীতদাস ও নারী জাতির সাথে সর্বোত্তম আচরণ করার জন্যে সমগ্র মুসলিম উম্মার প্রতি বিশেষভাবে‘
ওসিয়ত’
করে গেছেন ।
মহানবী (সা.) ও পবিত্র কুরআন
অন্যান্য নবীদের মত বিশ্বনবী (সা.)-এর কাছেও নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ মু’
জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনের দাবী জানানো হয় । এক্ষেত্রে বিশ্বনবী (সা.) নিজেও তার পূর্বতন নবীদের মু’
জিযা অলৌকিক নিদর্শনের অস্তিত্বের বিষয়টি সমর্থন করেন । যে বিষয়টি পবিত্র কুরআনেও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে । বিশ্বনবী (সা.)-এর দ্বারা প্রদর্শিত এধরণের মু’
জিযা বা অলৌকিক নিদর্শনের ঘটনার অসংখ্য তথ্যই আমাদের কাছে রয়েছে । ঐ সকল লিপিবদ্ধ ঘটনার অনেকগুলোই নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত । বিশ্বনবী (সা.)-এর প্রদর্শিত অলৌকিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে নিদর্শনটি আজও জীবন্ত হয়ে আছে , তা হচ্ছে ঐশীগ্রন্থ‘
পবিত্র কুরআন’
। এই পবিত্র ঐশী গ্রন্থে ছোট বড় মোট ১১৪ টি সূরা রয়েছে । যা মোট ৩০টি অংশে বিভক্ত । বিশ্বনবী (সা.) এর ২৩ বছর যাবৎ নবুয়তী জীবনে ইসলাম প্রচারকালীন সময়ে ধীরে ধীরে সমগ্র কুরআন অবতির্ণ হয় । একটি আয়াতের অংশবিশেষ থেকে শুরু করে কখনও বা পূর্ণ একটি সূরাও একেকবারেরই অবতির্ণ হত । অবস্থানরত অবস্থায় বা ভ্রমণ কালে , যুদ্ধ অবস্থায় বা সন্ধিকালে , দূরযোগপূর্ণ কঠিন দিনগুলোতে বা শান্তিপূর্ণ সময়ে এবং দিন ও রাতে যে কোন সময়েই ঐ পবিত্র ঐশীবাণী বিশ্বনবী (সা.)-এর কাছে অবতির্ণ হত । পবিত্র কুরআন তার আয়াতের মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুদৃঢ় ভাষায় নিজেকে এক মু’
জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে ঘোষণা করেছে । ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে , পবিত্র কুরআন অবতির্ণের যুগে আরবরা ভাষাগত উৎকর্ষতার দিক থেকে উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিল । শুদ্ধ , সুমিষ্ট , আকর্ষণীয় ও সাবলীল ভাষা ও বক্তব্যের অধিকারী হিসেবে তারা খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছিল । পবিত্র কুরআন ঐক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দিকতায় নামার জন্যে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে । পবিত্র কুরআন তাদেরকে আহবান করে বলেছে , তোমরা কি মনে কর যে , কুরআনের বাণী মানুষের বক্তব্য এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই তা রচনা করেছেন ? অথবা কারও কাছে তিনি তা শিখেছেন ? তাহলে তোমরাও পবিত্র কুরআনের মতই একটি কুরআন
বা এর যেকোন দশটি সূরা
বা অন্ততপক্ষে একটি সূরাও যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় রচনা করে নিয়ে এসো । আর এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যে কোন ধরণের পন্থা তোমরা অবলম্বন করতে পার ।
কিন্তু সে যুগের খ্যাতিসম্পন্ন শীর্ষ স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকরা পবিত্র কুরআনের ঐ চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তর দিতে ব্যর্থ হন । বরঞ্চ ঐ চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে যা তারা বলেছিল , তা হলঃ কুরআন একটি যাদুর নামান্তর সুতরাং এর সদৃশ্য রচনা আমাদের সাধ্যের বাইরে ।
এটাও লক্ষ্যণীয় যে , পবিত্র কুরআন শুধুমাত্র ভাষাগত উৎকর্ষতার ব্যাপারেই চ্যালেঞ্জ বা প্রতিদ্বন্দ্বীতার আহবান ঘোষণা করেনি , বরং এর অন্তর্নিহিত গুঢ় অর্থের ব্যাপারেও মানুষ ও জীন জাতির সামগ্রিক মেধাশক্তি খাটিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অংশ গ্রহণের জন্যে চ্যালেঞ্জ করেছে ।
কেননা , এই পবিত্র ঐশী গ্রন্থে সমগ্র মানব জীবনের কর্মসূচী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বর্ণিত হয়েছে । যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয় , তাহলে দেখা যাবে যে , পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই জীবন বিধান অত্যন্ত ব্যাপক , যা মৌলিক বিশ্বাস , আচরণ বিধি ও কাজকর্ম সহ মানব জীবনের সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে পরিবৃত করে । আর অত্যন্ত সূক্ষ্ণ ভাবে এবং দক্ষতার সাথে কুরআন মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে । মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই জীবন পদ্ধতিকেই একমাত্র সঠিকও সত্য ধর্ম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন । (ইসলাম এমন এক ধর্ম , যার আইন-কানুন সত্য ও প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ থেকে উৎসরিত । যার আইন মানুষের খুশীমত রচিত হয়নি । অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মতামতের উপর ভিত্তি করেও রচিত হয়নি । আর কোন এক শক্তিশালী শাসকের যাচ্ছেতাই সিদ্ধান্ত অনুসারে রচিত হয়নি ।) শুধুমাত্র এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টিকেই বিস্তৃত ঐশী কর্মসূচীর ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে । আর এ বিষয়টিই হল এ কর্মসূচীর সর্বোচ্চ সম্মানিত ঐশীবাণী । ইসলামের সকল মৌলিক বিশ্বাস এবং জ্ঞানের উৎসই হচ্ছে আল্লাহর এই একত্ববাদ বা তৌহিদ । আর মানুষের সুন্দর সদাচরণও ঐ মৌলিক বিশ্বাস ও জ্ঞানের ভিত্তিতেই রচিত এবং ঐ ঐশী কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে । এরপর মানুষের বিশ্বাসগত বা সামাজিক জীবনের কর্মসূচীর অসংখ্য সাধারণ ও বিশেষ বা সুক্ষ্ণাতিসুক্ষ্ণ বিষয় সমূহের বিশ্লেষণ এবং তদসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সমূহও আল্লাহর সেই একত্ববাদ বা তৌহিদের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে । ইসলামের মৌলিক ও ব্যবহারিক অংশদ্বয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এতই নিবিড় যে , যদি ব্যবহারিক অংশের অর্থাৎ আইনগত অংশের সূক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করা হয় , তাহলে দেখা যাবে যে , তাও আল্লাহর একত্ববাদ থেকেই উৎসারিত । আর আল্লাহর একত্ববাদও ঐসব বিধান সমূহেরই সামষ্টিকরূপ । মহাবিস্তৃত ইসলামী বিধানের এই সুসজ্জিত ও সুশৃংখলিতরূপ ছাড়াও এতে নিহিত পারস্পরিক ঐক্য ও নিবিড় সম্পর্ক সত্যিই এক অলৌকিক বিষয় । এমনকি এর প্রাথমিক সূচীপত্রের বিন্যাসও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আইনবিদের স্বাভাবিক ক্ষমতার বাইরে ।
সুতরাং , বিশ্বাসগত ও সামাজিক জান-মালের নিরাপত্তাহীনতা জনিত সমস্যা , রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ , আভ্যন্তরিণ ও বৈদেশিক বিশ্বাস ঘাতকতাসহ হাজারও সমস্যা সংকুল ও অশান্ত পরিবেশ জীবন যাপন করে এত স্বল্প সময়ে কারো পক্ষে এমন এক ঐশী বিধান রচনা নিঃসন্দেহে এক অসম্ভব ব্যাপার । আর বিশেষ করে সমগ্র বিশ্ববাসীর মোকাবিলায় আজীবন যাকে একই সংগ্রামে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে , এমন বিশ্বাসের পক্ষে এ ধরণের কিছু করা সত্যিই অসম্ভব ।
এ ছাড়া বিশ্বনবী (সা.) শুধু যে পৃথিবীর কোন শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করেননি তাই নয় । বরং লিখতে বা পড়তেও তিনি শিখেননি । এমনকি নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ বিশ্বনবী (সা.) এর জীবনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময়ই এমন এক জাতির মধ্যে বসবাস করেছেন , যারা সাংস্কৃতিক দিক থেকে ছিল নীচু মানের ।
সভ্যতা ও আধুনিকতার এতটকু ছোয়াও তাদের মধ্যে পাওয়া যেত না । গাছপালা ও পানিবিহীন এবং শুষ্ক ও জ্বলাকর বায়ুমণ্ডলপূর্ণ দূর্গম মরু এলাকার কঠিন ও কষ্টপূর্ণ পরিবেশে তারা জীবনযাপন করত । প্রতিনিয়তই তারা কোন না কোন পতিবেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির করতলগত হত । এছাড়াও পবিত্র কুরআন আরো অন্য পন্থায়ও তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করেছে । আর তা হচ্ছে এই যে , এই পবিত্র ঐশী গ্রন্থ সূদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ যুদ্ধকাল , সন্ধিকাল , সমস্যাকীর্ণ মূহুর্তে , শান্তি পূর্ণ যুগে , দুর্বল মূহুর্তে এবং ক্ষমতাসীন যুগে তথা বিভিন্ন পরিবেশে ধীরে ধীরে অবতির্ণ হয়েছে । আর এ জন্যেই , এটা যদি একমাত্র আল্লাহর রচিত না হয়ে মানব রচিত গ্রন্থ হত , তাহলে অবশ্যই এই গ্রন্থে অসংখ্য পরস্পর বিরোধী বিষয় পরিলক্ষিত হত । ঐ অবস্থায় ঐ গ্রন্থের শেষের অংশ অবশ্যই তার প্রথম অংশের চেয়ে উত্তম ও উন্নত হবে । কারণ এটা মানুষের ক্রমোন্নয়ন ধারার অপরিহার্য পরিণতি । অথচ পবিত্র কুরআনের মক্কায় অবতির্ণ আয়াত সমূহ , মদীনায় অবতির্ণ আয়াত সমূহের সাথে একই সুরে গাথা । এই গ্রন্থের প্রথম অংশের সাথে শেষ অংশের মৌলিক কোন ব্যবধান খুজে পাওয়া যায় না । যার প্রতিটি অংশই সুষম , এবং মনোমুগ্ধকর ও আশ্চর্যজনক বর্ণনাশক্তির ভঙ্গীমা একই রূপে বিরাজমান ।
 5%
5%
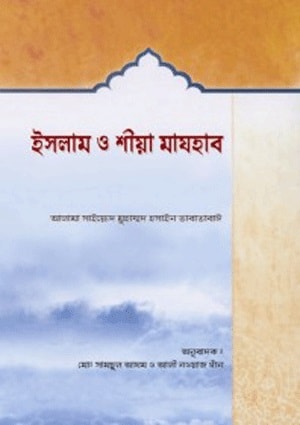 লেখক: আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ
লেখক: আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ 





