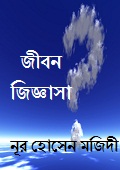কোরআন: অবিনশ্বর মু‘
জিযাহ্
আমরা ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি , একজন নবীর জীবন প্রত্যক্ষকরণ ও মুতাওয়াতির্ বর্ণনা থেকে তাঁর নবুওয়াত সম্বন্ধে প্রত্যয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু মু‘
জিযাহ্ দর্শনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মাত্রার প্রত্যয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ কারণে যিনি মু‘
জিযাহ্ দর্শন করেছেন এবং যিনি তা দর্শন করেন নি এতদুভয়ের প্রত্যয়ের মধ্যে বিরাট মাত্রাগত ব্যবধান থাকে। এটাই স্বাভাবিক।
বস্তুতঃ মু‘
জিযাহ্ প্রত্যক্ষকারীদের অন্তরে নবীর নবী হওয়া সম্পর্কে যেভাবে পূর্ণ মাত্রায় প্রত্যয় সৃষ্টির পাশাপাশি মানসিক পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তির সৃষ্টি হয় , তাদের তুলনায় , যারা প্রত্যক্ষ করে নি , কেবল বিচারবুদ্ধির দ্বারা মুতাওয়াতির্ বর্ণনার ভিত্তিতে প্রত্যয়ের অধিকারী হয়েছে , তাদের প্রত্যয়ের গভীরতা ও দৃঢ়তা যেমন কম হওয়ার সম্ভাবনা আছে , তেমনি তাদের অন্তরে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনাও কম।
এ দুই ব্যক্তির প্রত্যয়ের তুলনা হতে পারে কোনো বস্তুর মিষ্টতা সম্বন্ধে ঐ দুই ব্যক্তির ধারণার সাথে যাদের মধ্যকার একজন কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বক্তব্যের ভিত্তিতে বস্তুটির উপাদানসমূহ সম্বন্ধে অবগত হয়ে তার মিষ্টতা সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে , অপর জন ঐ বস্তু থেকে কিছুটা ভক্ষণ করে তার মিষ্টতা সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করেছে।
তাই অতীতের নবী-রাসূলগণের (আঃ) মু‘
জিযাহ্ সংক্রান্ত তথ্যাদিতে দেখা যায় যে , তাঁদের অনেকেই বিপুল সংখ্যক মানুষের সামনে মু‘
জিযাহ্ প্রদর্শন করেছেন। তেমনি কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের মু‘
জিযাহ্ প্রদর্শন করেছেন। আবার কেউ কেউ একই মু‘
জিযাহ্ বার বার প্রদর্শন করেছেন। রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)ও বিভিন্ন ধরনের মু‘
জিযাহ্ প্রদর্শন করেছেন। যেমন: তিনি চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করেছেন , সাপ তাঁর সাথে কথা বলে , কাঠের মিম্বার (জুমু‘
আহ্ মসজিদে ইমাম বা খতীবের খোত্ববাহ্ দানকালে দাঁড়াবার প্লাটফরম) তাঁর সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবার কারণে ক্রন্দন করে , বৃক্ষ তাঁকে সালাম ও সম্মান প্রদর্শন করে , তাঁর দো‘
আর ফলে সীমিত খাদ্যে বরকত (প্রচুর প্রবৃদ্ধি) হয় , ইত্যাদি।
এভাবে দেখা যায় যে , নবী-রাসূলগণের (আঃ) জীবদ্দশায় তাঁদের পারিপার্শ্বিক প্রায় সকল মানুষই কোনো না কোনো মু‘
জিযাহ্ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়। কিন্তু স্থানগত ও কালগত ব্যবধানজনিত কারণে অন্যরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। ফলে স্বভাবতঃই তাদের প্রত্যয় মু‘
জিযাহ্ প্রত্যক্ষকারীদের প্রত্যয় থেকে দুর্বলতর হতে পারে এবং এ ব্যবধান যতো বেশী হবে দুর্বলতাও ততোই বেশী হতে পারে। তাছাড়া মানব জাতির ইতিহাসে দেখা গেছে , অনেক ক্ষেত্রেই দ্বীনী ব্যক্তিত্ব বা ধর্মনেতাদের ভক্তরা তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও লোকদেরকে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁদের নামে বহু মিথ্যা অলৌকিক কাহিনী রচনা করেছে। ফলতঃ শত-সহস্র বছর ব্যবধানের কোনো কোনো ব্যক্তির মনে নবীর মু‘
জিযাহ্ সম্পর্কে প্রাপ্ত বর্ণনার ওপর প্রত্যয় সৃষ্টি না-ও হতে পারে এবং এ ব্যাপারে তাদের মনে সংশয় উঁকি দিতে পারে। তাই এরূপ ব্যক্তিদের প্রকৃতি মু‘
জিযাহ্ প্রত্যক্ষ করতে চায়। কিন্তু একজন নবীর ইন্তেকালের পর আর তাঁর পক্ষে মু‘
জিযাহ্ প্রদর্শন সম্ভব নয়। অবশ্য বিশেষ স্থান-কালের জন্য প্রেরিত নবীর জন্যে মৃত্যুর পরে মু‘
জিযাহ্ প্রদর্শনের প্রয়োজনও থাকে না।
কিন্তু যে নবীর নবুওয়াত বিশ্বজনীন ও কালোত্তীর্ণ তাঁর জন্যে এমন এক মু‘
জিযাহ্ পেশ করা অপরিহার্য যা হবে স্থানগত ও কালগত সীমাবদ্ধতার উর্ধে। এ কারণেই বিশ্বজনীন ও কালোত্তীর্ণ নবুওয়াতের অধিকারী নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-কে এমনই এক মু‘
জিযাহ্ প্রদান করা হয় যা স্থানগত ও কালগত সীমাবদ্ধতার উর্ধে। তা হচ্ছে তাঁর ওপর নাযিলকৃত ঐশী গ্রন্থ কোরআন মজীদ।
কোরআনের মু‘
জিযাহ্ সম্বন্ধে আরবী ও ফার্সী সহ বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। [অত্র গ্রন্থকারেরও কোরআনের মু‘
জিযাহ্ শীর্ষক একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে।] এখানে অতি সংক্ষেপে কোরআনের মু‘
জিযাহ্ সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে:
কোরআন মজীদ নিজেকে মু‘
জিযাহ্ হিসেবে পেশ করেছে একটি গ্রন্থ হিসেবে স্বীয় জ্ঞানগর্ভতা , সাহিত্যগুণ ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে।
এটা অনস্বীকার্য বিষয় যে , যে কোনো ভাষায় সাহিত্যিক গুণ ও শৈল্পিক সমৃদ্ধির বিচারে শ্রেষ্ঠতম রচনাগুলো হচ্ছে নিছকই সাহিত্য। তত্ত্বকথা , দর্শন , ধর্ম , নৈতিকতা , সমাজ , আইন , রাষ্ট্রব্যবস্থা , যুদ্ধ , বিচার ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক কোনো গ্রন্থে সর্বোত্তম সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও শিল্পগুণ ফুটিয়ে তোলাকে কখনোই কোনো ভাষায়ই সম্ভব গণ্য করা হয় নি। কিন্তু কোরআন মজীদ ঐসব বিষয়ে পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যগুণ ও শিল্পসমৃদ্ধ গ্রন্থের মর্যাদা অধিকার করেছে।
এ প্রসঙ্গে আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সামান্য আভাস দেয়া যরূরী মনে করছি।
সূক্ষ্মতম , গভীরতম ও ব্যাপকতম ভাব প্রকাশের জন্য আরবী ভাষা এমনই বিরাট সম্ভাবনার অধিকারী যে , বিশ্বের অন্য কোনো উন্নত ভাষা তার শতকরা দশ ভাগ সম্ভাবনারও অধিকারী নয়। আরবী ভাষায় একেকটি ক্রিয়াবিশেষ্য থেকে কয়েকশ’
ক্রিয়ারূপ ও শব্দরূপ (বিশেষ্য-বিশেষণ) নিষ্পন্ন হয়। অন্যদিকে আরবী বাক্যপ্রকরণের সম্ভাবনাও ব্যাপক। কম কথায় , ব্যাপক ও গভীর ভাব প্রকাশ এবং নতুন বাক্য বা শব্দ যোগ না করে কেবল বাক্যমধ্যস্থ শব্দে সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন করে অথবা শব্দ অগ্রপশ্চাত করে বা উহ্য রেখে ভাবপ্রকাশে সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের সম্ভাবনাও আরবী ভাষায় বিস্ময়করভাবে বেশী। নিজেদের ভাষার এ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবগত ছিলো বলেই এ ভাষাভাষী লোকেরা নিজেদেরকে বলতো‘
আরাবী - সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশক্ষম প্রাঞ্জল ভাষী এবং অন্যদেরকে বলতো‘
আজামী- বোবা।
বস্তুতঃ মানুষের ব্যাপক ভাবপ্রকাশক্ষমতার তুলনায় পশুপাখীদের সীমিত সংখ্যক ধ্বনির মাধ্যমে ভাববিনিময় বা কথোপকথনের দৃষ্টিতে মানুষ যেভাবে এ সব প্রাণীকে (তাদের নিজস্ব ভাষা থাকা সত্ত্বেও)‘
বোবা প্রাণী’
বলে থাকে , ঠিক একইভাবে , আরবী ভাষার তুলনায় অন্যান্য ভাষার প্রকাশক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দৃষ্টে আরবরা অন্যান্য ভাষার লোকদেরকে‘
বোবা’
বলে অবজ্ঞা করতো।
হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর নবুওয়াত-দাবীর সমসময়ে আরবী ভাষা তার বিকাশ ও উৎকর্ষের চরমতম শিখরে উপনীত হয়েছিলো এবং ঐ সময় এ ভাষার শ্রেষ্ঠতম কবি ও বাক্যবাগীশ বা বাচনশিল্পীদের আবির্ভাব ঘটেছিলো। আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবিতাগুলো মোটামুটি ঐ সময়ই রচিত হয়েছিলো এবং এ ভাষার প্রাঞ্জলতম ও বলিষ্ঠতম গদ্য বক্তব্যসমূহও একই সময় কথিত হয়েছিলো।
ঐ সময় আরবদের সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্রীয় , অথবা বলা চলে , একমাত্র বিষয় ছিলো কবিতা ও শিল্পগুণ সমৃদ্ধ গদ্য বক্তব্য। এ বিষয়ে আরবদের মধ্যে প্রতি বছর বিরাট এক জনাকীর্ণ মেলায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শ্রেষ্ঠতম কবি ও কবিতাকে সম্মানিত করা হতো। আর , ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে , শ্রেষ্ঠতম কবিতাগুলোকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে কা‘
বাহ্ গৃহের গাত্রে টানিয়ে রাখা হতো।
কবিতা ও বক্তব্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত বিষয়গুলো ছিলো:
*সংক্ষিপ্ততম কথার মাধ্যমে ব্যাপকতম ও সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশ।
*বিষয়বস্তু ও উদ্দিষ্ট ভাবের জন্য উপযুক্ততম শব্দের ব্যবহার ও সুবোধ্যতা।
*বক্তব্যের মাধুর্য , প্রাঞ্জলতা , ওজস্বিতা , বলিষ্ঠতা ও ঝঙ্কার-ব্যঞ্জনা।
*উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও ইশারা-ইঙ্গিতের সার্থক ব্যবহার।
*তত্ত্ব ও তথ্য ইত্যাদি উপস্থাপন।
বলা বাহুল্য যে , যে কোনো ভাষায়ই শ্রেষ্ঠতম কবিতা ও গদ্য বক্তব্য নির্ণয়ের মানদণ্ড এগুলোই। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে , কোনো একটি কবিতা বা গদ্য বক্তব্যে এর সবগুলো বৈশিষ্ট্যের স্থান দেয়া সম্ভব হয় না। যেমন: ওজস্বিতকে চরম মাত্রায় উন্নীত করতে গেলে মাধুর্যের মাত্রা চরমে উপনীত করা সম্ভব হয় না। তত্ত্ব ও তথ্য তুলে ধরতে গেলে মাধুর্য ও ওজস্বিতাকে চরমে উপনীত করা যায় না এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও ইশারা-ইঙ্গিত ব্যবহার কঠিন হয়ে পড়ে । এ সব সমস্যা মোকাবিলা করে সার্বিকভাবে তুলনামূলক বিচারে কবিতা বা বক্তব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা হয়।
এখানে আরেকটি উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে এই যে , আরবী ভাষায় সংক্ষেপে সূক্ষ্মতম , ব্যাপকতম ও সুন্দরতম ভাব প্রাঞ্জল বা ওজস্বি ভাষায় প্রকাশের সম্ভাবনা‘
প্রায় সীমাহীন’
বিধায় কোনো মানুষের পক্ষেই এর সর্বোচ্চ সম্ভাবনা ব্যবহার করে কিছু লেখার নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় , সুদক্ষ লোকেরা শ্রেষ্ঠতম কবিতা ও বক্তব্য বিশ্লেষণ করেও নির্দেশ করতে সক্ষম হন যে , এর মান আরো উন্নত করা যেতো। যেমন: এ শব্দটির পরিবর্তে অমুক শব্দটি অধিকতর উপযোগী ছিলো বা বাক্যবিন্যাসে এরূপ রদবদল হলে আরো উত্তম হতো। তবে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কবিতা ও বক্তব্য পরীক্ষা করে তুলনামূলক বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কোরআন মজীদ এ দিক থেকে অনন্য।
সার্বিক বিচারে কোরআন মজীদ এবং তার সূরা ও আয়াতগুলো উন্নততম মানের অধিকারী। কোনো একটি ক্ষেত্রেও এরূপ নির্দেশ করা সম্ভব নয় যে , এ আয়াত বা সূরায় যে ভাব প্রকাশ করতে চাওয়া হয়েছে সে বিচারে অমুক শব্দটির পরিবর্তে অমুক শব্দটির ব্যবহার অধিকতর উপযোগী হতো বা বাক্যবিন্যাসে অমুক পরিবর্তন বেহতর হতো।
বস্তুতঃ ভাব , ভাষা ও তাৎপর্য সব কিছুই শতকরা একশ’
ভাগ বজায় রাখা কেবল কোরআন মজীদেই সম্ভব হয়েছে , মানব রচিত কোনো কবিতা বা গদ্যে তা সম্ভব হয় নি এবং হবে না - এটা সুনিশ্চিত। কোরআন মজীদ এর ভিত্তিতেই নিজেকে মু‘
জিযাহ্ বলে দাবী করে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে। কোরআন বলেছে , লোকেরা যদি কোরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মনে না করে , হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর রচিত বলে মনে করে , তাহলে তারা এর একটি সূরার (এমনকি তিন আয়াত বিশিষ্ট ছোট সূরা হলেও) সমমানের একটি সূরা রচনা করে আনুক ; এ কাজে তারা যে কারো সাহায্য নিতে পারে , এমনকি সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও জিন্ একত্রিত হয়ে পারলেও তা করে দেখাক।
কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে কেউ সক্ষম হয় নি। তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠতম কবি ও বাগ্মীগণ পর্যন্ত এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-কে‘
জাদুকর’
ও কোরআনকে‘
জাদু’
বলে আখ্যায়িত করেন - যে দাবীর অসারতা নতুন করে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।
পরবর্তীকালেও কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের অর্থাৎ কোনো কোনো ছোট সূরার সম মানসম্পন্ন একই বিষয়বস্তু সম্বলিত সূরা রচনার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু এরূপ সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কারণ , দেখা গেছে , জ্ঞানগর্ভতা ও সাহিত্যিক সৌন্দর্য উভয়ের উচ্চ মানের একত্র সমাবেশ কোরআন মজীদের সমপর্যায়ে সম্ভব নয়।
কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান রয়েছে। কোরআন যদি আল্লাহর কিতাব না হয়ে হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর রচিত হতো তাহলে অন্য লোকদের (শ্রেষ্ঠতম কবি-সাহিত্যিক , জ্ঞানী-গুণী , দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের) পক্ষে একত্র হয়ে তার সম মানসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হতো। আরবী ভাষাভাষী এ ধরনের যোগ্যতা-সম্পন্ন বহু অমুসলিম কবি-সাহিত্যিক , জ্ঞানী-গুণী , দার্শনিক ও বিজ্ঞানী সব যুগেই ছিলেন এবং এখনো রয়েছেন। এমনকি অনারবদের মধ্যেও সব যুগেই আরবী ভাষা-সাহিত্য ও কোরআনের জ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এ ধরনের সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ (প্রাচ্যবিদগণ) ছিলেন এবং রয়েছেন। তাঁরা সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোরআনের বিকল্প রচনার চেষ্টা করতে পারেন।
বস্তুতঃ যারা ইসলামকে মোকাবিলা করার জন্য অপপ্রচার , ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধবিগ্রহে হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করছেন তাঁরা এর চেয়ে অনেক কম ব্যয়ে একটি সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করে কোরআনের বিকল্প উপস্থাপনের চেষ্টা করতে পারেন। এতে তাঁরা সফল হলে ইসলামের ঐশী ধর্ম হবার দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হতো এবং এর ফলে নিজে নিজেই ইসলামের বিলুপ্তি ঘটতো। কিন্তু তাঁরা সে পথে অগ্রসর হচ্ছেন না। কারণ , যারাই কোরআনের সাথে ভালোভাবে পরিচিত তাঁরা - মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে - জানেন যে , কোরআনের বিকল্প উপস্থাপন করা মানবিক ক্ষমতার (এমনকি গোটা মানব জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলেও) উর্ধে।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে , যে কোনো বিষয়ের অলৌকিকতা বা মু‘
জিযাহ্ চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা থেকে অনুধাবন করা অপরিহার্য। যেমন: মু‘
জিযাহ্ হিসেবে প্রদর্শিত বিষয়টি বা ঘটনাটি যদি জাদুর সাথে মিল বিশিষ্ট হয় তাহলে কেবল জাদুকরদের পক্ষেই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যে , কাজটি কি মু‘
জিযাহ্ , নাকি জাদু। আর যারা জাদুকর নয় তারা জাদুকরদের প্রতিক্রিয়া থেকে এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় উপনীত হতে পারে। অর্থাৎ তা যদি জাদু হয়ে থাকে তাহলে অন্য জাদুকররা অবশ্যই তার মোকাবিলা করতে বা তাকে ভণ্ডুল করে দিতে সক্ষম হবে বা তার জারিজুরি ফাশ করে দিতে পারবে। একজন জাদুকরের একার ক্ষমতায় সম্ভব না হলেও সম্মিলিতভাবে তারা অবশ্যই সফল হবে। কিন্তু জাদুকররা যদি ঐ কাজটিকে মোকাবিলা করতে , বা ভণ্ডুল করে দিতে বা তার জারিজুরি ফাশ করে দিতে সক্ষম না হয় তাহলে এটাই প্রমাণিত হবে যে , কাজটি জাদু নয় , বরং মু‘
জিযাহ্। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের জন্য তাকে মু‘
জিযাহ্ বলে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।
চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে মিলযুক্ত বা অন্য কোনো শাস্ত্রের সাথে মিলযুক্ত মু‘
জিযাহ্ রূপে উপস্থাপিত কোনো কাজ প্রকৃতই মু‘
জিযাহ্ কিনা সে ক্ষেত্রেও নিশ্চিত হবার পন্থা এটাই। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিজেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলে নিজেই সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের চেষ্টা করে দেখবেন যে , তা কি মু‘
জিযাহ্ , নাকি মানবিক বিশেষজ্ঞত্বের কাজ। আর উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হলে সে লক্ষ্য করবে যে , এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সফল হয়েছেন , নাকি হন নি , নাকি চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে গেছেন।
অতএব , যারা আরবী ভাষা-সাহিত্য ও কোরআন মজীদের জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ নন , তাঁদের জন্য কোরআন মু‘
জিযাহ্ কিনা সে প্রশ্নে সিদ্ধান্তহীনতায় থাকার কোনো সুযোগ নেই। তাঁরা‘
জানি না’
বলে বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না। বরং তাঁদেরকে দেখতে হবে যে , এ ব্যাপারে আরবী ভাষা-সাহিত্য ও কোরআন বিষয়ক অমুসলিম বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা কী ? তাঁরা যখন কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে , এমনকি তার তিন আয়াত বিশিষ্ট একটি ছোট সূরার সম মানসম্পন্ন বিকল্প সূরা রচনা করতেও সক্ষম হন নি , তখন কোরআন যে একটি মু‘
জিযাহ্ এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ থাকে না।
কোরআন মজীদের অবিনশ্বর মু‘
জিযাহ্ হওয়ার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এটাই অর্থাৎ কোরআন মজীদের ভাষা-সাহিত্যগত মান ও জ্ঞানগর্ভতা এতোই উঁচু মানের যে , এ উভয় দিকের মান বজায় রেখে কোরআনের বা তার কোনো সূরার সম মানসম্পন্ন বিকল্প রচনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।
তবে এ ছাড়াও কোরআন মজীদের মু‘
জিযাহ্ হওয়ার আরো কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে। যেমন:
*কোরআন তার তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারীর মন-মগয , চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণকে বিস্ময়করভাবে প্রভাবিত করে। এমনকি ভাষাগত ব্যবধানের কারণে কোরআনের তাৎপর্য যে বুঝতে পারে না তার ওপরেও এর প্রভাব কমবেশী বিস্তার লাভ করে। এ প্রভাব কেবল সাময়িকভাবে ভালো লাগা ও হৃদয় আপ্লুত হয়ে যাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় , বরং পাঠকারী ও শ্রবণকারীর চরিত্রের ওপরও কমবেশী স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। কোনো মানবরচিত গ্রন্থেরই এ ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।
*কোরআনের তেলাওয়াত বা তার শ্রবণের বার বার পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও মানবরচিত শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থাবলী বা যুগান্তকারী কবিতা ও ভাষণসমূহের ন্যায় এর আকর্ষণ মোটেই হ্রাস পায় না বা হাল্কা হয়ে যায় না , বরং ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।
*একটি মধ্যম আয়তনের গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও পুরো কোরআন মজীদ মুখস্ত করা ও মুখস্ত রাখা খুবই সহজ কাজ এবং বিশ্বে একই সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের তা মুখস্ত আছে। মানব জাতির ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো পুস্তকের , এমনকি কোনো ক্ষুদ্র পুস্তিকার ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে নি।
*কোরআন মজীদে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন: দর্শন , সৃষ্টিতত্ত্ব , তত্ত্বকথা , নীতিশাস্ত্র , ধর্মীয় বিধান , সমাজবিজ্ঞান , আইন , রাজনীতি , অর্থনীতি , সমাজতত্ত্ব , নৃবিজ্ঞান , নক্ষত্রবিজ্ঞান , প্রাকৃতিক বিজ্ঞান , মনস্তত্ত্ব , ইতিহাস ইত্যাদি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার ঘটেছে। মানবজাতির ইতিহাসে দ্বিতীয় এমন কোনো গ্রন্থ পাওয়া যাবে না যাতে এতো বিপুল সংখ্যক বিষয় স্থান পেয়েছে। মানবরচিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে ভাবাই যায় না যে , এমন স্বল্পায়তনে এতো বেশী সংখ্যক বিষয় স্থান দেয়া যেতে পারে।
*কোরআন মজীদের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে , তা যতোই অধ্যয়ন করা হয় ততোই তা থেকে নতুন নতুন তত্ত্ব , তথ্য ও তাৎপর্য বেরিয়ে আসে এবং যতো বার নতুন করে অধ্যয়ন করা হয় ততো বারই তা থেকে আরো নতুন নতুন জ্ঞান বেরিয়ে আসে। এভাবে বিগত চৌদ্দশ’
বছরে কোরআন থেকে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বেরিয়ে এসেছে এবং এখনো পুনঃঅধ্যয়ন থেকে আরো নতুন নতুন জ্ঞান বেরিয়ে আসা অব্যাহত রয়েছে।
*কোরআন মজীদের বাচনভঙ্গি ও রচনাকৌশল মানুষের রচিত বৈজ্ঞানিক , দার্শনিক বা ধর্মীয় গ্রন্থের রচনারীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানুষের রচিত যে কোনো গ্রন্থ পুরোপুরি না পড়া পর্যন্ত গ্রন্থকারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোরআন মজীদের রচনাকৌশল এমন যে , তার একটি ছোট সূরা অধ্যয়ন করলেও তাতে সমগ্র কোরআনের শিক্ষা ও পথনির্দেশের নির্যাস পাওয়া যায়। এ যেন একটি প্রাকৃতিক ফলবান বৃক্ষ যার ছোট-বড় যে কোনো শাখায়ই পুরো বৈশিষ্ট্য - অভিন্ন পাতা , ফুল ও ফল - বিরাজমান , কেবল পরিমাণে কম আর বেশী। মানবরচিত কোনো গ্রন্থেই এ বৈশিষ্ট্য পাওয়া সম্ভব নয়।
*কোরআন মজীদে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যা কালের প্রবাহে যথাসময়ে কার্যে পরিণত হয়। যেমন: (1) কোরআন মজীদের মক্কায় অবতীর্ণ একটি সূরায় (সূরা লাহাব) মক্কার কাফেরদের অন্যতম নেতা আবু লাহাবের ও তার শক্তির (রূপকার্থে‘
দুই হাত’
) ধ্বংসের এবং তার স্ত্রীর লাকড়ি বহনকালে খেজুর পাতার রশিতে গলায় ফাঁস লেগে মারা যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। এ ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু বাস্তবায়িত হয়। (2) রোমান ও পারস্য সম্রাটের মধ্যকার যুদ্ধে রোম সম্রাট পরাজিত হবার পর কোরআন মজীদের সূরা আর্-রূম্-এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে ,‘
কয়েক’
(আরবী ভাষার প্রচলন অনুযায়ী দশ-এর কম) বছরের মধ্যেই পুনরায় রোম পারস্যের ওপর বিজয়ী হবে এবং কার্যতঃও তা-ই ঘটে। (3) হুদায়বিয়ায় রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) ও মক্কাহর কাফেরদের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় কার্যতঃ তা ছিলো মুসলমানদের জন্য অপমানজনক , কিন্তু কোরআন মজীদে (সূরা আল্-ফাত্হ্) একে‘
সুস্পষ্ট বিজয়’
হিসেবে অভিহিত করে আশু মক্কাহ্ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় এবং অচিরেই সে ভবিষ্যদ্বাণী কার্যে পরিণত হয়।
*কোরআন মজীদে এমন বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা কোরআন নাযিলের সময়কার মানুষের জানা ছিলো না এবং বহু পরে বিজ্ঞানীরা তা আবিষ্কার করেন। যেমন: (1) উদ্ভিদের প্রাণ থাকার কথা। (2) মাতৃগর্ভে মানুষের ভ্রুণ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুতে পরিণত হওয়ার বিভিন্ন স্তর। (3) বায়ুর দ্বারা উদ্ভিদজগতে পরাগায়ণপ্রক্রিয়া। (4) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সূর্যের উদায়াস্ত ঘটা। (5) ভূপৃষ্ঠে দু’
টি প্রাচ্য ভূখণ্ড (এশিয়া-ইউরোপ ও আফ্রিকা) ছাড়াও দু’
টি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা) অস্তিত্ব থাকা। (6) মিঠা পানি ও লোনা পানির সমুদ্র পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও এবং মাঝখানে কোনোরূপ প্রাকৃতিক বাধা না থাকা সত্ত্বেও দুই ধরনের পানি পরস্পর মিশে না যাওয়া। কোরআন মজীদে এ ধরনের আরো অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে এবং কোরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।
মোদ্দা কথা , কোরআন মজীদ যে মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত গ্রন্থ এবং একমাত্র অবিকৃত ঐশী গ্রন্থ হিসেবে সকল মানুষেরই কর্তব্য এ মহাগ্রন্থ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করা - এটাই সুস্থ বিচারবুদ্ধির রায়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ-অবিশেষজ্ঞ নির্বিশেষে কারো মনেই সন্দেহ পোষণের অবকাশ নেই।
 0%
0%
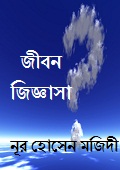 লেখক: নূর হোসেন মজিদী
লেখক: নূর হোসেন মজিদী