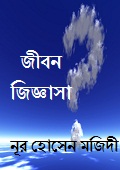রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) উত্তরাধিকারিত্ব: বিচারবুদ্ধির দাবী
আল্লাহ্ তা‘
আলা যে সব মুখ্য উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে স্বীয় বাণী সহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে (আঃ) পাঠিয়েছেন তা হচ্ছে লোকদেরকে আল্লাহ্ ও পরকাল সংক্রান্ত সঠিক ধারণার সাথে পরিচিত করা , তাদের কাছে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সমূহ পৌঁছে দেয়া , আল্লাহর বাণী ও আদেশ-নিষেধের ব্যাখ্যা প্রদান , মূল বিধিবিধানের ছোটখাট শাখা-প্রশাখা প্রণয়ন , সর্বাবস্থায় স্বীয় অনুসারীদের নেতৃত্ব প্রদান এবং সম্ভবপর হলে তথা রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্তাধীন হলে জনগণের ওপর শাসনক্ষমতা পরিচালনা।
পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নাযিল হওয়ার পরে নতুন কোনো ওয়াহী নাযিলের প্রয়োজন নেই , অতএব , নতুন কোনো নবী আগমনেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু মওজূদ ওয়াহীর ব্যাখ্যাকরণ , মুসলমানদেরকে পথনির্দেশ প্রদান এবং তাদের ওপর শাসনকর্তৃত্ব পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থেকে যায়। মূলতঃ এ সব কাজের জন্যই নবীর প্রয়োজন হতো , নইলে আল্লাহ্ তা‘
আলা ফেরেশতার মাধ্যমে স্বীয় পরিচয় ও আদেশ-নিষেধ সম্বলিত কিতাব পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা পাঠান নি , বরং সব সময়ই তা নবী-রাসূলগণের (আঃ) মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে , নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে যাবার পর নবীর অবর্তমানে যিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন তাঁর জন্য কী ধরনের গুণাবলীর অধিকারী হওয়া প্রয়োজন ?
বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী , এ কাজ সম্পাদনকারীর জন্য যে সব গুণাবলীর অধিকারী হওয়া প্রয়োজন সেগুলোকে সংক্ষেপে তিনটি গুণের মধ্যে সমন্বিত করা যায় , তা হচ্ছে: জ্ঞান , পাপমুক্ততা ও অন্তর্দৃষ্টি বা দূরদর্শিতা। অবশ্য একজন নেতার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি বা দূরদর্শিতা আছে কিনা তা কেবল কালের প্রবাহে উদ্ভূতব্য সঙ্কটের অবস্থাগুলোতে তাঁর দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে ; আগেই তা জানা যায় না। কিন্তু অপর দু’
টি গুণ তাঁর মধ্যে আছে কিনা তা তাঁর দায়িত্বগ্রহণকালেই সুস্পষ্ট থাকা প্রয়োজন।
আমাদের এ কথার মানে হচ্ছে , নবীর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মধ্যে নবীর রেখে যাওয়া জ্ঞান পরিপূর্ণ ও উচ্চতম মাত্রায় থাকা অপরিহার্য এবং সেই সাথে তাঁর দ্বারা পাপ সংঘটিত না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত থাকতে হবে।
ইমাম বা শাসক যদি নবীর রেখে যাওয়া পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী না হন তাহলে তিনি ভুল করবেন এবং তাঁর ভুলের দ্বারা উম্মাহকে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। অন্যথায় তাঁকে তাঁর চেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের পরামর্শ ও পথনির্দেশের ওপর নির্ভর করতে হবে। সে ক্ষেত্রে তা হবে তাঁর দুর্বলতার পরিচায়ক। কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কেন্দ্র দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হওয়া কাম্য নয়। তাছাড়া জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য না হলে তিনি সঠিক ও ভুল পরামর্শের মধ্যে পার্থক্য করতে ও সঠিক পরামর্শ অনুসরণ করতে সক্ষম হবেন তারও নিশ্চয়তা নেই। শুধু তা-ই নয় , পদের মর্যাদা রক্ষার্থে তিনি তাঁর তুলনায় অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ থেকে পুরোপুরিও বিরত থাকতে পারেন , বা সব সময় তা গ্রহণ না করে কখনো কখনো স্বীয় ভিত্তিহীন মতের অনুসরণ করতে পারেন।
অন্যদিকে ইমাম যদি পাপমুক্ত না হন তাহলে তিনি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের সঠিক বাস্তবায়ন করবেন না , সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচার করবেন না , পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত থাকবেন না , বায়তুল মালের (রাষ্ট্রীয় কোষাগারের) সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করবেন না। মোট কথা , পাপমুক্ত না হলে তিনি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি রূপে নিজেকে পেশ করবেন না এবং নবীর যথার্থ উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিজেকে অন্যদের সামনে দৃষ্টান্তে পরিণত করতে পারবেন না। ফলে তাঁর প্রশাসন যালেম , দুর্নীতিবায , চাটুকার ও স্বার্থান্বেষী আত্মসাৎকারীদের থেকে মুক্ত থাকার কোনোই নিশ্চয়তা থাকবে না ।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ,‘
ইলমী যোগ্যতা ও পাপমুক্ততার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ , কোনো ব্যক্তি পরিপূর্ণ দ্বীনী‘
ইলমের অধিকারী না হলে তার পক্ষে ছোট-বড় প্রতিটি ফরয ও হারাম সম্বন্ধে জানা না থাকার কারণে প্রতিটি ফরয আঞ্জাম দেয়া ও প্রতিটি হারাম থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়।
অবশ্য কেউ‘
ইলমের অধিকারী হলেই গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই , কিন্তু‘
ইলমের অধিকারী না হলে গুরুদায়িত্ব কাঁধে বহনকারী ব্যক্তি কোনোভাবেই পাপমুক্ত থাকতে পারবে না।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে , আমরা যদি মেনে নেই যে , ইমামের অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর স্থলাভিষিক্তের জন্য পরিপূর্ণ দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী ও পাপমুক্ত হওয়া প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যক্তিকে বেছে নেয়ার দায়িত্ব কার ? আল্লাহ্ই কি এ ধরনের ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন , নাকি জনগণ তাকে বেছে নেবে ?
আমরা লোকদের জ্ঞানের অধিকারী হওয়া-নাহওয়ার বিষয়টি মোটামুটি নির্ণয় করতে পারি , কিন্তু পাপমুক্ততার ক্ষেত্রে কারো প্রকাশ্যে পাপ না করা সম্বন্ধে জানতে পারলেও তার গোপন পাপ থাকলে তা জানা কেবল আল্লাহ তা‘
আলার পক্ষেই সম্ভব।
এমতাবস্থায় বিচারবুদ্ধির দাবী হচ্ছে এই যে , স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘
আলার পক্ষ থেকে এ ধরনের ব্যক্তিকে বেছে নেয়া হলে তা হবে বান্দাহদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘
আলা এ ধরনের কোনো ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে নামোল্লেখপূর্বক মনোনয়ন দিয়েছেন কিনা তা যদি আমাদের জানা না থাকে তাহলে আমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে এতদসংক্রান্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পথনির্দেশ কী আছে তা দেখতে হবে এবং এতদুভয়ে নিহিত ইঙ্গিত যার বেলায় প্রযোজ্য তাঁকে খুঁজে বের করে তাঁকেই আল্লাহর পসন্দনীয় ব্যক্তি মনে করে তাঁর হাতে এ দায়িত্ব সোপর্দ করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে পরিপূর্ণ‘
ইলমের অধিকারী ব্যক্তির ও পাপমুক্ত ব্যক্তির কথা উল্লেখ থাকলে তা যার বেলায় প্রযোজ্য হয় তাঁকেই ইমাম ও শাসক হিসেবে বরণ করে নিতে হবে।
যদিও বিচারবুদ্ধির উপরোক্ত রায়ের সাথে দ্বিমত করার এবং অপেক্ষাকৃত কম জ্ঞানের অধিকারী ও পাপমুক্ততার নিশ্চয়তা বিহীন ব্যক্তিকে ইমাম ও শাসকের পদে বসানোর কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না তথাপি এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত একটি প্রশ্নের জবাব পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না , যদিও বিষয়টির সম্পর্ক অংশতঃ বিচারবুদ্ধির সাথে ও অংশতঃ ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে।
বলা হয় যে , মুসলমানরা যদি তাদের নিজেদের জন্য ইমাম ও শাসক বেছে নেয় এবং তিনি যদি‘
ইলমী দিক থেকে সর্বাগ্রগণ্য না-ও হন এবং পাপমুক্ততার নিশ্চয়তা না থাকলেও দৃশ্যতঃ তিনি পাপাচারী না হন , আর তিনি যদি কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে তাদেরকে শাসন ও পরিচালনা করেন তাহলে তা-ই যথেষ্ট। অতএব , আল্লাহ্ তা‘
আলার পক্ষ থেকে কোনো ইমাম ও শাসক মনোনীত করা অপরিহার্য নয়।
এ যুক্তি এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে , উম্মাতের হেদায়াত ও পরিচালনার ক্ষেত্রে ইমাম বা শাসক কোনো প্রশ্নের বা সমস্যার সম্মুখীন হবার পর কোরআন ও সুন্নাহ্ থেকে তার জবাব বা সমাধান খুঁজে বের করবেন এবং এরপর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব বা উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেবেন - এর পরিবর্তে তাঁর মস্তিষ্কে ইতিমধ্যেই মওজূদ কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের দ্বারা জবাব দেবেন এটাই হওয়া উচিত। অর্থাৎ ইমাম বা শাসকের কাছে জবাব বা সমাধান পূর্ব থেকেই মওজূদ থাকতে হবে। কারণ , ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর কাছে সমাধান খোঁজার মতো যথেষ্ট সময় না-ও থাকতে পারে।
দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) ইন্তেকালের পর কোরআন মজীদ যেভাবে লিপিবদ্ধ আকারে হাতের কাছে ছিলো সুন্নাহ্ কখনোই সেভাবে লিপিবদ্ধ আকারে মওজূদ ছিলো না। সুন্নাহ্ অনেক বিলম্বে এমন সময়ে ও এমন অবস্থায় লিপিবদ্ধ হয়েছে যখন তাতে অনেক মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটেছিলো। এমনকি কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ আকারে মওজূদ থাকলেও কতক ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর কাছ থেকে জানা প্রয়োজন ছিলো। এমতাবস্থায় , ইমাম ও শাসক পদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর কাছ থেকে কোরআন ও সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনকারী ব্যক্তির কোনো বিকল্প ছিলো না।
অবশ্য সতর্কতার নীতির দাবীও এটাই ছিলো। কারণ , আল্লাহ্ তা‘
আলার পক্ষ থেকে নেতা ও শাসক মনোনীত না হয়ে থাকলেও মুসলমানদের জন্য উচিত ছিলো সেই ব্যক্তিকে এ দায়িত্ব অর্পণ করা যার আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হলেও এর‘
সম্ভাবনা’
ছিলো। কারণ , হাদীছে গ্বাদীরে ব্যবহৃত“
মাওলা”
শব্দের উদ্দেশ্য যদি‘
বন্ধু’
হয়ে থাকে তাহলেও অন্য কারো পরিবর্তে হযরত‘
আলী (আঃ)কে এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করায় কোনো সমস্যা ছিলো না। কিন্তু এর উদ্দেশ্য যদি‘
নেতা ও শাসক’
বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে অন্যকে এ দায়িত্ব অর্পণ করা ঠিক হয় নি। আর সতর্কতার নীতির দাবী হচ্ছে দু’
টি পন্থার যেটিতে ঝুঁকি নেই সেটি অনুসরণ করতে হবে।
 0%
0%
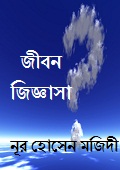 লেখক: নূর হোসেন মজিদী
লেখক: নূর হোসেন মজিদী