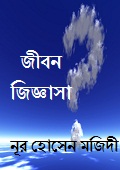ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাবপূর্ব দ্বীনী নেতৃত্ব
হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) - তা তিনি জন্মগ্রহণ করে থাকুন বা না-ই করে থাকুন - আবির্ভূত না হওয়ায় বা আত্মপ্রকাশ না করায় এবং জনসমক্ষে উপস্থিত হয়ে নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব দাবী না করায় তাঁর নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব মেনে নেয়ার বিষয়টি বর্তমানে শিয়া-সুন্নী উভয়ের জন্য প্রায় অভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এমতাবস্থায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে চার খলীফাহ্ ও আহলে বাইতের ইমামগণ - উভয়ের অনুপস্থিতিতে আজকের দিনে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের প্রশ্নটির সমাধান কীভাবে করণীয়।
এ প্রশ্নটি তাত্ত্বিক ছাঁচে ফেলে উপস্থাপন করতে হলে বলতে হবে যে , আজকে সুন্নীদের সামনে প্রশ্ন: হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর অবর্তমানে উম্মাহর পথনির্দেশ , নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের দায়িত্ব ও অধিকার কা’
র ? তেমনি শিয়াদের সামনে প্রশ্ন: হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর অনুপস্থিতিকালে উম্মাহর পথনির্দেশ , নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্বের দায়িত্ব ও অধিকার কা’
র ?এ প্রশ্নের জবাবে সুন্নীদের অনেকের মনে হতে পারে যে , রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর অবর্তমানে উম্মাহর নেতৃত্বের দায়িত্ব চার খলীফাহর তথা চার খলীফাহ্ ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর পর্যায়ক্রমিক উত্তরাধিকারী। আবার কেউবা তাত্ত্বিকভাবে ছ্বাহাবী , তাবে‘
ঈন্ ও তাবে‘
তাবে‘
ঈন্-কে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর পর্যায়ক্রমিক উত্তরাধিকারী বলে মনে করতে পারে। কিন্তু এ ধরনের জবাব উক্ত প্রশ্নের তাত্ত্বিক জবাব হিসেবে গণ্য হতে পারে না। বরং এর জবাব হতে হবে একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ জবাব ; চার খলীফাহকে বাস্তব প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উক্ত জবাবে প্রাপ্তব্য কাঠামোর আওতায় ফেলার চেষ্টা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ছ্বাহাবী , তাবে‘
ঈন্ বা তাবে‘
তাবে‘
ঈনের মতো সুনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রজন্মের ব্যক্তিগণও এ প্রশ্নের জবাব হতে পারেন না। বরং এর জবাব হতে হবে এমন একটি তাত্ত্বিক জবাব যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য হবার উপযোগী - যে কাঠামোতে উক্ত তিনটি প্রজন্ম থেকেও উপযুক্ত নেতৃত্ব পাওয়া যেতে পারে।
এ ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির রায় এই যে , যিনি বা যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (ছ্বাঃ) আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশ সম্বন্ধে তথা ইসলামের সকল দিক-বিভাগ সম্বন্ধে পুরোপুরি অবগত তিনি বা তাঁরাই উম্মাহকে নেতৃত্ব ও পথনির্দেশ দেবেন এবং উম্মাহর শাসনকর্তৃত্ব পরিচালনা করবেন ; এটা একই সাথে তাঁর বা তাঁদের কর্তব্য ও অধিকার দুইই। আর শিয়া মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আত্মগোপনে থাকার যুগে নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের প্রশ্নের জবাবও এটাই।
অবশ্য
,
ইতিপূর্বেও যেমন উল্লেখ করা হয়েছে
,
এ ধরনের ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিবর্গকে উপরোক্ত ধরনের জ্ঞানগত যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি আরো দু
’
টি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে
,
তাঁকে বা তাঁদেরকে চিন্তা
-
চেতনায়
,
জীবন ও আচরণে এবং মানুষকে শিক্ষা ও পথনির্দেশ দানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ভারসাম্যের অধিকারী হতে হবে
;
এ ধরনের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ চরমপন্থী
(
ইফরাতী
- extremist)ওহবেন না
,
শিথিলপন্থী
(
তাফরীতী
- liberal)ওহবেন না
,
বরং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল
(
ছ্বাঃ
)
ও তাঁর আহলে বাইতের ইমামগণ
(
আঃ
)
যে বিষয়ের ওপর যতোটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি বা তাঁরা সে বিষয়ের ওপর ঠিক ততোটুকু গুরুত্ব আরোপ করবেন।
অপর বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে , তাঁকে বা তাঁদেরকে যুগসচেতন হতে হবে ; পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী উম্মাহকে নেতৃত্ব দানের মতো দূরদর্শিতা বা অন্তর্দৃষ্টি (বাছ্বীরাত্)-এর অধিকারী হতে হবে। ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে , নবীর মাধ্যমে পথনির্দেশের প্রয়োজনীয়তা এখানেই নিহিত। নয়তো আল্লাহ্ তা‘
আলা চাইলে ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর পথনির্দেশসমূহ এমনভাবে পাঠাতে পারতেন যে সম্পর্কে কারো মনেই সন্দেহ সৃষ্টি হতো না। কিন্তু তার পরিবর্তে নবী-রাসূলগণের (আঃ) মাধ্যমে পথনির্দেশ পাঠানো হয় এবং তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী লোকদেরকে পরিচালনা করেন।
আমরা রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর জীবনে দেখতে পাই , তিনি মক্কায় তিন বছর গোপনে বাছাই করা লোকদের মধ্যে তাঁর আদর্শ প্রচার করেন এবং পরবর্তী দশ বছর প্রকাশ্যে প্রচারকার্য চালান। এ সময় তিনি কোনোরূপ সংঘাত বা প্রতিরোধের পন্থা অনুসরণ করেন নি ; যুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন , কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করেন নি। এরপর তিনি দেশত্যাগ করে মদীনায় চলে যান। সেখানে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন ও ইয়াহূদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। মদীনার জীবনের দশ বছরে তিনি দ্বীন প্রচারের পাশাপাশি প্রশাসন গড়ে তোলেন এবং কূটনৈতিক তৎপরতাও চালান। এ সময় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠায় তিনি একদিকে যেমন একাধিক বার যুদ্ধ করেন , তেমনি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ বিবেচনায় যুদ্ধ এড়ানোর জন্য , দৃশ্যতঃ অপমানজনক শর্তাবলী সত্ত্বেও তিনি সন্ধি করেন (হুদায়বিয়ায়)। অর্থাৎ ইসলামী নেতৃত্বের জন্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণের যোগ্যতা তথা দূরদর্শিতা একটি অপরিহার্য মৌলিক গুণ।
অতএব , যথাযথ ও পরিপূর্ণ দ্বীনী জ্ঞান , ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা-চেতনা , চরিত্র ও আচরণ এবং দূরদর্শিতা - এই তিনটি গুণের অধিকারী ব্যক্তিই ইসলামী নেতৃত্বের উপযুক্ত - ইসলামী পরিভাষায় যাকে‘
যুগসচেতন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নিষ্ঠাবান মুজতাহিদ’
বলা যেতে পারে। ইসলামী উম্মাহর নেতৃত্ব প্রদান এরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের শুধু অধিকারই নয় , দায়িত্বও বটে। কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এরূপ ব্যক্তিদের মর্যাদার ওপর আলোকসম্পাৎ করা হয়েছে। অন্যদিকে শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল মুসলমানের নিকট অভিন্নভাবে গ্রহণযোগ্য একটি হাদীছে বলা হয়েছে:
العلماء ورثة الانبياء
“
আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।”
বলা বাহুল্য যে , এ হাদীছে‘
আলেম বলতে বর্তমানে প্রচলিত অর্থে প্রথাগত বা প্রতিষ্ঠানিক আলেম বুঝানো হয় নি , বরং এমন ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নবী না হয়েও নবীর গুণাবলী (জ্ঞান , আচরণ ও দূরদর্শিতা)-এর অধিকারী ; তাঁদের কাছে নতুন কোনো ওয়াহী নাযিল হয় না , কিন্তু তাঁরা মওজূদ ওয়াহীর পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। অন্যথায় তাঁদের পক্ষে নবীদের (আঃ) উত্তরাধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। কারণ , নবীদের (আঃ) উত্তরাধিকারী হওয়া মানে নবীদের (আঃ) অবর্তমানে তাঁদের সকল দায়িত্ব পালন করা।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে , এ ধরনের ব্যক্তিত্ব কীভাবে উম্মাহর নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী হবেন এবং উম্মাহর সাথে তাঁর বা তাঁদের সম্পর্ক কেমন হবে ?
বলা বাহুল্য যে , একজন নবীকে যেভাবে বিচারবুদ্ধি দ্বারা চিনে নিতে হয় সেভাবেই নবীর (ও নিষ্পাপ ইমামের) উত্তরাধিকারী যুগসচেতন ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা-চরিত্রের অধিকারী মুজতাহিদকেও বিচারবুদ্ধি দ্বারা চিনে নেয়া অপরিহার্য। বিচারবুদ্ধির আলোকে বিশ্লেষণ করে কারো নবী হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর তাঁকে গ্রহণ ও আশ্রয় করার নামই নবীর প্রতি ঈমান। অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা এ ঈমান হাছ্বিল হয় না। কারণ , অন্ধ বিশ্বাস এমন এক কর্মপদ্ধতি যার আশ্রয় নিলে ঘটনাক্রমে যেমন প্রকৃত নবীকে নবী বলে মেনে নেয়া ও আশ্রয় করা হতে পারে , তেমনি ভণ্ড নবীকেও নবী বলে মেনে নেয়া ও আশ্রয় করা হতে পারে - যার পরিণতি ব্যক্তি ও সমাজের ইহ-পরকালের জন্য , অন্ততঃ পরকালের জন্য , অত্যন্ত মারাত্মক।
একইভাবে কোনো ব্যক্তি প্রকৃতই নবীদের (আঃ) , এবং শিয়া মাযহাবের মতে , নবীদের (আঃ) ও একই সাথে নিষ্পাপ ইমামের (আঃ) , উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতাসম্পন্ন কিনা সে ব্যাপারে বিচারবুদ্ধির আলোকে যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হওয়ার পরেই তাঁকে আশ্রয় করতে হবে এবং তাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশ মেনে চলতে হবে ; প্রয়োজনে তাঁর আদেশে ধন-সম্পদ , স্বজনসম্পর্ক , এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির ওপর নবীর যে অধিকার আছে , নবীর উত্তরাধিকারীরও তদনুরূপ অধিকার আছে।
কাউকে প্রকৃত ওয়ারেছে নবী (নবীর উত্তরাধিকারী) জানার পর তাঁকে গ্রহণ না করা বা তাঁর কথা অমান্য করা এবং নবীকে গ্রহণ না করা ও তাঁর কথা অমান্য করার মধ্যে কার্যতঃ কোনো পার্থক্য নেই। এ কারণে ওয়ারেছে নবীকে অবশ্যই বিচারবুদ্ধি দ্বারা চিহ্নিত করে গ্রহণ করতে হবে। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস ও অন্যের অন্ধ অনুসরণ অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল কর্মনীতি। কারণ , এ ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী ভণ্ড-প্রতারকের খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বলা বাহুল্য যে , এরূপ প্রতারকের খপ্পরে পড়লে ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয়ই , অন্ততঃ পরকাল ধ্বংস হওয়া অনিবার্য।
এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে , ব্যক্তির জন্য নবীর অবর্তমানে নবীর উত্তরাধিকারীর অনুসরণ অপরিহার্য। অতএব , তাকে অবশ্যই উপরোক্ত শর্তাবলী বিশিষ্ট মুজতাহিদের সন্ধান করতে হবে এবং পাওয়া মাত্রই তাঁকে আশ্রয় করতে হবে। মুসলিম সমাজের জন্য এরূপ কোনো না কোনা মুজতাহিদের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে ফরযে কেফায়ী। অর্থাৎ উম্মাহর মধ্যে কমপক্ষে একজন অনুসরণযোগ্য মুজতাহিদ থাকতেই হবে , না থাকলে গোটা উম্মাহ্ই এক অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার কবলে নিক্ষিপ্ত হবে। ব্যক্তি যদি এ ধরনের কোনো অনুসরণযোগ্য মুজতাহিদ খুঁজে না পায় তাহলে তার জন্য স্বয়ং মুজতাহিদ হওয়ার চেষ্টা করা বা সমাজে যাতে কমপক্ষে একজন মুজতাহিদ তৈরী হতে পারেন এ জন্য একটি প্রক্রিয়ার সূচনা করা অপরিহার্য কর্তব্য।
নবীর উত্তরাধিকারিত্ব প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন এই যে , রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে [শিয়া মাযহাব অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আত্মগোপনের পরে] নবীগণের (আঃ) উত্তরাধিকারী অভিন্ন সময়ে একজন হওয়া অপরিহার্য , নাকি একাধিক হতে পারেন ? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে , একজনও হতে পারেন , একাধিক হতেও বাধা নেই।
অতীতে একই সময় বিশ্বের বুকে একাধিক নবী (আঃ) থাকার বিষয়টি একটি প্রমাণিত বিষয়। শুধু এক নবীর সহযোগী অন্য নবীই ছিলেন না , বরং একই সময় বিভিন্ন ভূখণ্ডে স্বতন্ত্রভাবে দায়িত্ব পালনকারী একাধিক নবীর দৃষ্টান্তও রয়েছে । যেমন: হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত লূত্ব (আঃ) , হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত শু‘
আইব (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ) । দ্বিতীয়তঃ পূর্বোক্ত হাদীছে আলেম ও উত্তরাধিকারী উভয় ক্ষেত্রেই বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।
এছাড়াও আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত অনেক হাদীছের তাৎপর্য অনুযায়ী আলেমগণ রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর প্রতিনিধি (নায়েবে নবী)। অন্যদিকে শিয়া মাযহাবের বিভিন্ন হাদীছ অনুযায়ীও হাদীছ বর্ণনাকারীগণ তথা ওলামায়ে কেরাম হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ও নিষ্পাপ ইমামগণের (আঃ) প্রতিনিধি। অন্যদিকে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। দ্বীন প্রচার ও শিক্ষাদান , কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা , যুদ্ধ ও শাসনকার্য ইত্যাদি সব কিছুই ছিলো তাঁদের দায়িত্ব। কখনো একজন প্রতিনিধির ওপর একটি দায়িত্ব অর্পিত থাকতো , কখনো একাধিক বা সবগুলো দায়িত্ব অর্পিত হতো। মোদ্দা কথা , একই সময় তাঁর একাধিক প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও দিকনির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতেন এবং কোনো ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার সম্মুখীন হলে উক্ত শিক্ষা ও দিকনির্দেশের আলোকে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে সমাধানে উপনীত হতেন অথবা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর নিকট এসে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান জেনে নিতেন।
বস্তুতঃ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোথাও প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত কোনো ছ্বাহাবী যখন তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও দিকনির্দেশের আলোকে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে কোনো সমস্যার সমাধানে উপনীত হতেন তা ছিলো এক ধরনের ইজতিহাদ।
হযরত রাসূলে আকরাম
(
ছ্বাঃ
)-
এর জীবদ্দশায় কতক ক্ষেত্রে তাঁর
অবস্থানস্থল থেকে স্থানগত ব্যবধানের কারণে এবং যোগাযোগ যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ হওয়ায় সরাসরি তাঁর নিকট থেকে কোনো প্রশ্নের জবাব জানার সুযোগ না থাকায় তাঁর কতক প্রতিনিধি যেভাবে কোরআন মজীদ ও তাঁর দিকনির্দেশের আলোকে চিন্তা
-
গবেষণা করে কোনো সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন করতেন
,
তাঁর ইন্তেকালের পর কালগত ব্যবধানে অবস্থানকারী মুজতাহিদগণও একই পন্থায়
,
বরং অধিকতর সুবিন্যস্ত
( systematic)পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে
,
সমস্যাবলীর সমাধান উদ্ভাবন করে থাকেন।
প্রকৃত পক্ষে মুজতাহিদের কাজ হচ্ছে এ দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা করা যে , স্বয়ং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর নিকট (এবং শিয়া মতে , সেই সাথে নিষ্পাপ ইমামের কাছে) এ প্রশ্ন করা হলে তাঁর পক্ষ থেকে কী উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো ? অর্থাৎ মুজতাহিদের কাজ নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া সমাধান পেশ করা নয় , বরং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর প্রদত্ত সমাধান চিহ্নিত করা বা তাঁর পক্ষ থেকে দেয়া হতে পারতো এমন সম্ভাব্য সমাধান উদ্ঘাটন করা। আর যেহেতু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় একই সময় তাঁর একাধিক প্রতিনিধি ছিলেন সেহেতু তাঁর ইন্তেকালের পরে একই সময় একাধিক ওয়ারেছে নবী থাকায় কোনোই বাধা নেই।
আমাদের এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে , নবীর প্রতিনিধিত্ব বা উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়টি নবুওয়াতের কর্মগত (ওয়াহী আগমনগত নয়) সম্প্রসারণ ও ধারাবাহিকতা মাত্র। অর্থাৎ হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির যে দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার-মর্যাদা ছিলো , তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর উত্তরাধিকারী (যথাযথ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ)-এর দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার-মর্যাদা তা-ই। অতএব , হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় কোনো ব্যক্তিকে তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে জানার পরে তাঁর প্রতি আনুগত্য ও তাঁকে অমান্য করা যেরূপ স্বয়ং হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য ও তাঁকে অমান্য করার সমার্থক ছিলো , তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর উত্তরাধিকারী যথাযথ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ হিসেবে কারো ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি হবার পর তাঁর আনুগত্য ও তাঁকে অমান্য করা প্রত্যয়ের অধিকারী ঐ ব্যক্তির জন্য অনুরূপভাবে হযরত নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর আনুগত্য ও তাঁকে অমান্য করার সমার্থক বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।
বলা বাহুল্য যে , কোনো ব্যক্তি যদি কারো ব্যাপারেই ওয়ারেছে নবী বলে প্রত্যয়ের অধিকারী হতে না পারে , সে ক্ষেত্রেও সে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না। কারণ , সে ক্ষেত্রে তাকে দুনিয়ার অপর কোনো প্রান্তে গিয়ে হলেও এরূপ ওয়ারেছে নবী খুঁজে পাবার চেষ্টা করতে হবে , অথবা নিজে ওয়ারেছে নবী হবার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টাসাধনা ও অধ্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে অথবা সমাজে যাতে এরূপ কোনো ওয়ারেছে নবী গড়ে উঠতে পারে সে জন্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে বা এরূপ প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকলে তাতে সম্ভব সব রকম সহায়তা প্রদান করতে হবে।
যথাযথ শর্তাবলীর অধিকারী মুজতাহিদ-নেতৃত্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে যখন যে ধরনের সম্পর্ক ও আচরণ নির্ধারণ করে দেবেন তাঁর অনুসারীদের জন্য তখন সে ধরনের সম্পর্ক রক্ষা ও আচরণ করা অপরিহার্য হবে। আর তিনি যদি পরিস্থিতি উপযুক্ত বিবেচনা করে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তাঁর অনুসারীদের জন্য তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং এ জন্য তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী যে কোনো ত্যাগ স্বীকার অপরিহার্য হবে। তিনি কোন্ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টা করবেন পরিস্থিতি বিবেচনায় তিনি নিজেই তা নির্ধারণ করবেন ; এ ব্যাপারে তিনি কোনো ধরাবাঁধা নিয়মের অনুসরণ করতে বাধ্য নন।
একই সময় বিশ্বের বিভিন্ন অংশে একাধিক মুজতাহিদ নেতৃত্ব কর্তৃক একাধিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাধা নেই , আবার তাঁরা যদি প্রয়োজন বা উত্তম মনে করেন তো এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়ও বাধা নেই। অবশ্য কাছাকাছি অবস্থানরত একাধিক মুজতাহিদের পক্ষে ভৌগোলিক কারণে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বিধায় তাঁদের জন্য একটিমাত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যেমন: একই শহরে অবস্থানরত একাধিক মুজতাহিদ-নেতৃত্ব - যাদের অনুসারীরা স্বতন্ত্র এলাকাসমূহে বসবাস করে না , বরং সকল এলাকায় মিশ্রিত অবস্থায় বসবাস করে , তাঁদের প্রত্যেকেই ওয়ারেছে নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকেই নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর ক্ষমতা ও এখ্তিয়ার , রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি এবং তার ক্ষমতার মেয়াদকাল তাঁরা মতৈক্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করে দেবেন। তিনি দেশ শাসনের ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন এবং তিনি শারীরিক , মানসিক , নৈতিক বা রাজনৈতিক যোগ্যতা হারিয়েছেন বলে মনে করলে তাঁরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন। কারণ , তাঁদের প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি এবং নতুন ওয়াহী প্রাপ্তি ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর সকল দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার-মর্যাদা-এখতিয়ারের অধিকারী। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারের একটি অংশ সমঝোতার ভিত্তিতে আমানত স্বরূপ একজনের ওপর অর্পণ করেছেন মাত্র যা তাঁরা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারও রাখেন।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে , কেউ কেউ মনে করেন , কাউকে দ্বীনী নেতা বা দ্বীনী শাসক হিসেবে কবূল করে শপথ গ্রহণ করলে অতঃপর আর তা প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকে না বা তিনি যতোদিন জীবিত থাকবেন ততোদিন পর্যন্ত তাঁর অনুকূলে শপথ গ্রহণকারীদের জন্য তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে নেতারূপে গ্রহণ করা বৈধ হবে না। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ , ওয়ারেছে নবী বা নায়েবে নবী কোনো নবী নন এবং তাঁর গুনাহ্ ও ভুল থেকে বেঁচে থাকা নবীর মতো (শিয়া মাযহাবের মতে , নবী ও ইমামের মতো) নিশ্চিত নয়। বরং শব্দ সহযোগে উল্লেখ করা হোক বা না-ই হোক , এ ধরনের নেতার ওপর নেতৃত্ব অর্পণ ও তাঁর অনুকূলে শপথ গ্রহণ হয় শর্তাধীন এবং যতোক্ষণ তাঁর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল শর্ত বিদ্যমান থাকে ততোক্ষণই তিনি আনুগত্যের উপযুক্ত থাকেন।
দু’
টি কারণে তাঁর ওপর নেতৃত্ব অর্পণ ও তাঁর অনুকূলে আনুগত্য-শপথ শর্তাধীন।
প্রথমতঃ
তাঁকে চিহ্নিত করা হয় শুধু বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করে ; নবীর মতো মু‘
জিযাহ্ তাঁর থাকে না এবং থাকা অপরিহার্যও নয়। তাছাড়া বাহ্যিক মানদণ্ডও তাঁর ও নবীর ক্ষেত্রে হুবহু এক নয়। যেমন: জীবনে কখনো কোনো পাপ না থাকা নবীর জন্য (এবং শিয়া মতে , ইমামের জন্যও) অপরিহার্য। কিন্তু নায়েবে নবী বা ওয়ারেছে নবীর জন্য এ শর্ত এরূপ কঠোর নয়। হতে পারে একজন মুজতাহিদের দ্বারা যৌবনে বা মুজতাহিদ হওয়ার আগে কোনো গুনাহ্ সংঘটিত হওয়ার বিষয় জানা আছে , কিন্তু মুজতাহিদ হবার পরে ও দীর্ঘ বহু বছর যাবত তাঁর মধ্যে অকাট্যভাবে গুনাহ্ বলে বিবেচিত কোনো দোষ দেখা যায় নি। এমতাবস্থায় ব্যক্তি ও সমষ্টি তাঁকে অনুসরণ করতে পারে এবং তাঁর অনুকূলে আনুগত্য-শপথ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর মধ্যে আরো এমন ধরনের দোষ ধরা পড়তে পারে যা আগেও ছিলো , কিন্তু আনুগত্যকারী ব্যক্তি তা লক্ষ্য করে নি , অথবা বিচারবুদ্ধির যে মানদণ্ডে বিচার করে ব্যক্তি বা সমষ্টি তাঁকে আনুগত্যের উপযুক্ত মনে করে তাঁর অনুকূলে শপথ গ্রহণ করেছিলো এখন দেখতে পাচ্ছে যে , সে মানদণ্ড যথেষ্ট ছিলো না এবং প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যক্তি আনুগত্যের উপযুক্ত ছিলেন না।
দ্বিতীয়তঃ
হতে পারে যে , ব্যক্তি বা সমষ্টি যার অনুকূলে আনুগত্য-শপথ গ্রহণ করেছিলো তিনি ঐ সময় যথাযথ শর্তের অধিকারী ছিলেন , কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো শর্ত হারিয়ে ফেলেছেন। আর যেহেতু তিনি নবী নন , এবং শিয়া মতে , নবী বা আল্লাহ্-মনোনীত ইমাম কোনোটাই নন , এ কারণে তিনি নবী বা ইমামের মতো পাপ ও ভুল থেকে খোদায়ী সংরক্ষণের অধিকারী নন , সেহেতু তাঁর যোগ্যতা হারানো অসম্ভব কিছু নয়। এমতাবস্থায় তাঁর প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখা মানে ব্যক্তিদের পরকালীন জীবনকে (এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইহকালীন জীবনকেও) হুমকির মুখে ঠেলে দেয়া।
অবশ্য কারো অনুকূলে আনুগত্য-শপথ গ্রহণ করা ও শপথ প্রত্যাহার করে নেয়া উভয়ই আন্তরিকভাবে (ইখ্লাছ্বের সাথে) যথার্থ মনে করে করতে হবে ; এর পিছনে কোনো পার্থিব স্বার্থ (যেমন: অর্থ , পদ , সম্মান , মর্যাদা বা সুযোগ-সুবিধা লাভ বা পার্থিব ঝুঁকি এড়ানো) থাকলে সে অবশ্যই আল্লাহ্ তা‘
আলার নিকট অপরাধী বা কপটাচারী বলে পরিগণিত হবে , এমনকি তার সিদ্ধান্তটি (গ্রহণের বা বর্জনের) প্রকৃত পক্ষে সঠিক হলেও। আর ব্যক্তি যদি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে সে ক্ষেত্রে সাধ্যানুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রকৃতই যদি সিদ্ধান্তটি ভুল হয় , তাতে পার্থিব ক্ষতি হলেও পরকালীন ক্ষতি থেকে সে আল্লাহ্ তা‘
আলার অনুগ্রহমূলক সুরক্ষার অধিকারী হবে বলে আশা করা যায়।
অন্যদিকে কাউকে নেতৃত্ব অর্পণ বা তাঁর প্রতি আনুগত্য-শপথের বিষয়টি মূলগতভাবেই সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য হতে ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তির কোনো কারণ নেই। কারণ , যেহেতু নবীর উত্তরাধিকারী বা ওয়ারেছ নবী স্বয়ং নবীর মতো নিষ্পাপ বা নির্ভুল হবার নিশ্চয়তার অধিকারী নন , সেহেতু তাঁর প্রতি অন্যদের আজীবনের জন্য আনুগত্য তাঁর মধ্যে অহঙ্কারসহ অন্যবিধ বিচ্যুতি , এমনকি সীমালঙ্ঘনপ্রবণতা তৈরী করতে পারে। অন্যদিকে স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) বিভিন্ন সময় যাদেরকে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন তাঁদের প্রত্যেককেই স্থায়ীভাবে নিয়োগদান করেন নি। অতএব , নীতিগতভাবেই ওয়ারেছে নবী বা নায়েবে নবীর পদমর্যাদা কারো জন্য স্থায়ী হবেই এমন কোনো কথা নেই। বিশেষ করে স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর মনোনয়নের তুলনায় মুসলমানদের নিজেদের মনোনয়ন দুর্বলতর হবার সম্ভাবনা বেশী। তাই নেতৃত্বের বিষয়টি সীমিত সময়ের জন্য ও শর্তাধীন হতে বাধা নেই।
নেতৃত্বের শর্তাধীনতার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে , মুজতাহিদগণ যে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি , তা তাঁর অবর্তমানে তাঁর সকল দায়িত্ব পালনের জন্য। কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্য থেকে যাকে রাজনৈতিক নেতা বা রাষ্ট্রনেতা নির্বাচন করবেন , তাঁকে নির্বাচন করবেন কেবল রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের জন্য অর্থাৎ তাঁদের নেতৃত্বের রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় অংশটি তাঁরা এক ব্যক্তির ওপর অর্পণ করবেন এবং তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেন কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন । এই অর্পণের ফলে তাঁদের নিজেদের উত্তরাধিকারিত্ব ও প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা রহিত হয়ে যাবে না। অতএব , রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বহির্ভূত বিষয়াদিতে যে সব গৌণ ক্ষেত্রে তাঁদের ভিন্ন মত রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকের অনুসারীরা পূর্বের ন্যায়ই নিজ নিজ মুজতাহিদ-নেতার মতের অনুসরণ করবেন। এ সব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে উক্ত নেতার মত বা সংখ্যাগুরুর মত সকলের ওপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না।
এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ জরুরী। তা হচ্ছে , অ-মুজতাহিদগণের জন্য সর্বাবস্থায়ই কোনো না কোনো জীবিত মুজতাহিদের অনুসরণ করা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে কোনো মৃত মুজতাহিদের অনুসরণ করা যথেষ্ট নয়। কারণ , মৃত মুজতাহিদের পক্ষে যেমন নবজাগ্রত যুগজিজ্ঞাসার জবাব দেয়া সম্ভব নয় , তেমনি পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বা ভুল ধরা পড়ার কারণে ইতিপূর্বে প্রদত্ত স্বীয় রায় পরিবর্তন করাও সম্ভব নয়।
একজন মুজতাহিদ যত উঁচু দরের মুজতাহিদই হন না কেন , যেহেতু তিনি নবী নন (শিয়া মতে , নবী বা ইমাম নন) , সেহেতু তাঁর ইজতিহাদে ভুল হতেই পারে এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নিজের কাছে সে ভুল ধরা না-ও পড়তে পারে। দ্বিতীয়তঃ কালগত সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করে মৃত মুজতাহিদের অনুসরণ যদি যথেষ্ট হতো তাহলে ইজতিহাদ ও মুজতাহিদের আদৌ প্রয়োজন হতো না। কারণ , সে ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ্ই যথেষ্ট হতো । কিন্তু যেহেতু স্থানগত ও কালগত ব্যবধানের কারণে কোরআন-হাদীছ থেকে সঠিক তাৎপর্য ও ফয়সালা বের করার জন্য ইজতিহাদ ও মুজতাহিদের প্রয়োজন রয়েছে , সেহেতু মৃত মুজতাহিদের প্রদত্ত রায়ের ভুল সংশোধন ও নবজাগ্রত যুগজিজ্ঞাসার জবাব উদ্ঘাটনের জন্য নতুন মুজতাহিদের প্রয়োজন রয়েছে। তাই যারা মুজতাহিদ নয় তাদের জন্য জীবিত মুজতাহিদের অনুসরণ করা অপরিহার্য ; তারা মৃত মুজতাহিদের ফয়সালা ততোটাই অনুসরণ করবে যতোটা জীবিত মুজতাহিদ অনুমোদন করবেন।
এখানে ইজতিহাদ-বিরোধীদের বক্তব্যের ওপর সংক্ষেপে হলেও আলোকপাত করা অপরিহার্য বলে মনে হয়।
বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে এমন কয়েকটি ধারা-উপধারার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যারা ইজতিহাদকে শুধু অপ্রয়োজনীয় মনে করে না , বরং দ্বীন ও ঈমানের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করে। তাদের মধ্যকার কোনো কোনো দলের মতে , শুধু কোরআনের এবং অন্যদের মতে , কোরআন ও হাদীছের অনুসরণই যথেষ্ট এবং মুজতাহিদের ফয়সালা মেনে চলা মানে আল্লাহ্ তা‘
আলা ও তাঁর রাসূলের (আঃ) সাথে সংশ্লিষ্ট মুজতাহিদগণকে শরীক করা।
তাদের এ ধরনের চরমপন্থী অভিমত মোটেই সঠিক নয়। কোরআন-হাদীছের বর্তমানে ইজতিহাদের প্রয়োজন কেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুজতাহিদের কাজ হচ্ছে কোরআন-হাদীছের সঠিক তাৎপর্য উদ্ধার এবং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ও শিয়া মতে , সেই সাথে নিষ্পাপ ইমামের (আঃ) , তথা এক কথায় মা‘
ছূমের (নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের) তথা বিধানদাতা বা শরীয়তদাতার (আল্লাহর) প্রকৃত ফয়সালা ও সম্ভাব্য ফয়সালা উদ্ঘাটন। [মা‘
ছূমগণের (আঃ) ফয়সালাকে আল্লাহর ফয়সালা গণ্য করার কারণ , মা‘
ছূমগণ নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কোনো কথা বলেন না , বরং আল্লাহ্ তা‘
আলার ওয়াহীর ভিত্তিতে কথা বলেন বা ওয়াহীর সঠক ও নির্ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেন।]
অতএব , এখানে আল্লাহ্ ও রাসূল (ছ্বাঃ)-এর সাথে শরীক করার প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে এ ধরনের মতামতের প্রায়োগিক তাৎপর্য ক্ষেত্রবিশেষে খুবই গুরুতর হতে পারে। কারণ , একই যুক্তির ভিত্তিতে কেউ দাবী করতে পারে (এবং কেউ কেউ করছেও) যে , কোরআনের বর্তমানে হাদীছের প্রয়োজন নেই। কারণ , হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) নিজ থেকে কোনো কথা বলেন নি , বরং তিনি কোরআনের প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্যই আগমন করেন এবং সে দায়িত্বই পালন করে যান। অতএব , হাদীছ নামে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর বাণী , কাজ ও অনুমোদন নামে যা কিছু বলা হয় তার যতোটুকু কোরআনের অনুরূপ তার প্রয়োজন নেই , কারণ , তা তো কোরআনেই রয়েছে। আর এর বাইরে যা কিছু রয়েছে তা তাঁর নামে তৈরী করে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারে যে , হাদীছ মানার অর্থ হচ্ছে কোরআনের সাথে হাদীছকে তথা আল্লাহর সাথে রাসূল (ছ্বাঃ)-কে শরীক করা। কিন্তু আমরা জানি যে , এ ধরনের যুক্তি ঠিক নয়। কারণ , অনেক বিষয়ে কোরআন মজীদে সাধারণ বিধান নাযিল হয়েছে ; বিস্তারিত বা প্রায়োগিক বিধান দেয়া হয় নি ; এ সব ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর কথা , আচরণ ও অনুমোদনই অবশ্য অনুসরণীয় বিধান। যেমন: নামাযের ন্যূনতম শর্তাবলী , রাকা‘
আত-সংখ্যা ও প্রক্রিয়া (তারতীব্) , যাকাতের নেছাব ও হার ইত্যাদি।
একইভাবে কোরআন মজীদের আয়াতের সঠিক তাৎপর্য গ্রহণ ও হাদীছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর বা মা‘
ছূম-এর প্রকৃত ফয়সালা ও সম্ভাব্য ফয়সালা বের করার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন ; মুজতাহিদই হচ্ছেন সেই বিশেষজ্ঞ। অসংখ্য জাল হাদীছ এবং ছ্বাহীহ্ নামে অভিহিত অসংখ্য পরস্পর বিরোধী হাদীছের উপস্থিতিই এ ধরনের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।
এছাড়া , ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে , সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হাদীছ অনুযায়ী আলেমগণ নবী-রাসূলগণের (আঃ) উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি - বিচারবুদ্ধিও যা গ্রহণ করে। এভাবে ইজতিহাদ-বিরোধীরা যখন হাদীছকে যথেষ্ট গণ্য করে ইজতিহাদ ও মুজতাহিদের প্রয়োজনীয়তাকে প্রত্যাখ্যান করছেন , তখন হাদীছই ইজতিহাদ ও মুজতাহিদকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। তাছাড়া স্বয়ং কোরআন মজীদ (সূরা আত্-তাওবাহ্: 122) থেকেও সমাজের জন্য ফক্বীহ্ বা ইসলাম-বিশেষজ্ঞ থাকা ফরযে কেফায়ী বলে প্রমাণিত হয় এবং মুজতাহিদই হচ্ছেন সেই ফক্বীহ্ বা ইসলাম-বিশেষজ্ঞ।
অন্যদিকে , যারা ইজতিহাদের বিরোধিতা করেন ও কোরআন-হাদীছের অনুসরণকে যথেষ্ট বলে দাবী করেন , তাঁরাও কিন্তু প্রকারান্তরে এক ধরনের ইজতিহাদ করে থাকেন এবং এক ধরনের ইজতিহাদ অনুসরণ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যেও পরস্পরবিরোধী হাদীছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গ্রহণ-বর্জন করার জন্য হাদীছ-বিশেষজ্ঞ (মুহাদ্দিছ) রয়েছেন এবং হাদীছ সংকলকগণ (হাদীছের ইমামগণ) নিজেরা হাদীছ পরীক্ষার কতোগুলো নিয়মনীতি‘
উদ্ভাবন করে’
তার ভিত্তিতে হাদীছ বাছাই করে সংকলিত করেন এবং হাদীছকে যথেষ্ট গণ্যকারী ইজতিহাদ-বিরোধীরা সেই সব সংকলনের ওপর নির্ভর করেন।
মুজ্তাহিদগণের ন্যায় হাদীছ-সংকলনসমূহের সংকলকগণও নবী-রাসূল বা মা‘
ছ্বূম ইমাম ছিলেন না এবং ভুলের উর্ধে ছিলেন না। হাদীছ সংকলনের মাধ্যমে ইসলামের যে বিরাট খেদমত তাঁরা করেছেন সে জন্য তাঁদেরকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা সত্ত্বেও এ সত্যটি স্বীকার করতে হবে। এমতাবস্থায় তাঁদের ওপর অন্ধ নির্ভরতা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের (ছ্বাঃ) সাথে শরীক করা না হয় , তাহলে মুজতাহিদের অন্ধ অনুসরণ (অ-মুজতাহিদ সাধারণ মুসলমানের জন্য) আল্লাহ্ ও রাসূলের (ছ্বাঃ) সাথে শরীক করা বলে গণ্য করা হবে কেন ?
বস্তুতঃ হাদীছ বাছাই করার মূলনীতি নির্ধারণ ও তার প্রয়োগও এক ধরনের ইজতিহাদ বৈ নয়। ইজতিহাদের মূলনীতি নির্ধারণ ও তা প্রয়োগ তথা ইজতিহাদ একই ধরনের কাজ , তবে তা অধিকতর বিশেষজ্ঞত্বের সাথে আঞ্জাম দেয়া হয়।
একজন মুজতাহিদ যখন একজন মুহাদ্দিছ কর্তৃক ছ্বাহীহ্ বলে চিহ্নিত কোনো হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেন তখন তার মানে এ নয় যে , তিনি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর (এবং শিয়া মতে , সেই সাথে কোনো নিষ্পাপ ইমামের) কোনো কথা , কাজ বা কাজের অনুমোদনকে প্রত্যাখ্যান করছেন। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে , হাদীছ যাচাই-বাছাই করার এক ব্যাপকতর ও নির্ভুলতর মানদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে , এটা আদৌ ছ্বাহীহ্ হাদীছ নয় অর্থাৎ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) বা যে নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের নামে এটি বর্ণিত হয়েছে তিনি আদৌ এ কথা বলেন নি বা এ কাজ করেন নি বা এরূপ কাজের অনুমোদন দেন নি , অথবা এটি ছিলো স্থান , কাল বা পরিস্থিতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনো বিষয়ের সাথে জড়িত যা উচ্চতর মূলনীতি অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়ে প্রযোজ্য নয় তথা যে বিষয়ের ফয়সালা করা হবে তা দৃশ্যতঃ হাদীছে বর্ণিত বিষয়ের সাথে অভিন্ন হলেও প্রকৃত পক্ষে তা ভিন্ন বিষয় , অতএব , তার ফয়সালাও হবে ভিন্ন। বস্তুতঃ এভাবে তিনি নব-উদ্ভূত বিষয়ে সঠিক ফয়সালা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন।
উদাহরণস্বরূপ , কোরআন মজীদে‘
আঙ্গুরের রস’
(খামর্)-কে হারাম করা হয়েছে। কিন্তু একজন মুজতাহিদ জানেন যে , ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব মুশরিকরা আঙ্গুরের রসকে আগুনে জ্বাল দিয়ে বা রোদে উত্তপ্ত করে তাতে মাদকতার গুণ সৃষ্টি হবার পর তা পান করতো ; আঙ্গুর থেকে রস বের করে তাজা তাজাই তা পান করতো না। তাই মুজতাহিদ মাদকতার গুণবিহীন আঙ্গুরের তাজা রসকে (বর্তমান যুগে যার যথেষ্ট ব্যবহার আছে) কোরআন মজীদে বর্ণিত উক্ত হুকুমের বহির্ভূত ভিন্ন বিষয় বলে গণ্য করেন। একইভাবে , আঙ্গুরের রসে মাদকতা সৃষ্টির পরেও তা জ্বাল দেয়া অব্যাহত রাখলে তা কমে এক চতুর্থাংশের নীচে নেমে সির্কায় পরিণত হলে তাতে আর মাদকতা থাকে না বিধায় মুজতাহিদ এ ঘনীভূত আঙ্গুর-রসকে তৃতীয় একটি বিষয় বলে গণ্য করেন এবং এর প্রতি খামর্-এর হুকুম প্রযোজ্য মনে করেন না। অন্যদিকে ভাত পচানো মদ বা তালের রসের তাড়ির কথা কোরআন মজীদে বা হাদীছে উল্লেখ না থাকলেও মুজতাহিদ অভিন্ন গুণের কারণে খামর্-এর হুকুম এতদুভয়ের প্রতি প্রযোজ্য গণ্য করেন।
 0%
0%
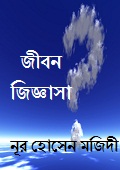 লেখক: নূর হোসেন মজিদী
লেখক: নূর হোসেন মজিদী