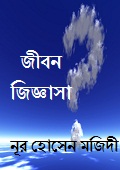ইজতিহাদে মতপার্থক্য ও তার ক্ষেত্র
হাদীছ সংকলনের ও হাদীছ-বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা এবং হাদীছ পরীক্ষার মূলনীতি ও ইজতিহাদের মূলনীতি প্রশ্নে মতপার্থক্য সহ বিভিন্ন কারণে অনেক বিষয়ে বিভিন্ন মুজতাহিদের রায়ে বিভিন্নতা দেখা যায়।
এছাড়া যারা ইজতিহাদের বিরোধী ও শুধু কোরআন-হাদীছের অনুসরণের পক্ষপাতী এবং এ হিসেবে নিজেদেরকে‘
হাদীছপন্থী’
(আহলে হাদীছ) বলে অভিহিত করে থাকে তাদের মধ্যেও একাধিক গোষ্ঠী রয়েছে , যেমন: সুন্নী ধারার হাদীছপন্থীরা“
আহলে হাদীছ”
নামে এবং শিয়া ধারার হাদীছপন্থীরা“
আখবারী”
নামে পরিচিত।
সুন্নী ধারার“
আহলে হাদীছ”
গোষ্ঠীর মধ্যে এমনও অনেকে আছে যারা আহ্কামের ক্ষেত্রে কোরআনকে বাদ দিয়ে শুধু হাদীছকেই যথেষ্ট গণ্য করে এবং কোরআনকে শুধু তেলাওয়াত করে থাকে। কারণ , তাদের কথা , হাদীছ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) কর্তৃক কোরআনের মৌখিক ও কার্যতঃ ব্যাখ্যা। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে সচেতন নয় যে , যা কিছুই রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর নামে বর্ণিত হয়েছে তার সব কিছুই সত্যি সতিই তাঁর থেকে এসেছে এমন কোনো নিশ্চয়তা দেয়ার উপায় নেই ।
এ সব গোষ্ঠীর মধ্যকার মতপার্থক্যের কারণ , ক্ষেত্র ও গুরুত্ব নির্ণয় এবং এ থেকে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের পন্থার ওপর সংক্ষেপে হলেও আলোকপাত করা অপরিহার্য বলে মনে হয়। আমরা ইতিপূর্বে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তাবলী উল্লেখ করেছি। এখানে আরো কতোগুলো বিষয় উল্লেখ করছি।
এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলাম প্রদত্ত বিধিবিধান সমূহের মধ্যকার প্রকৃতিগত পার্থক্যের ওপর আলোকপাত করতে হয়।
ইবাদত সংক্রান্ত বিধিবিধানের কোনো প্রাকৃতিক মানদণ্ড নেই ; এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা‘
আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত বিধিবিধানসমূহই চূড়ান্ত। কারণ , এ সব বিধিবিধানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা‘
আলার প্রতি বান্দাহর আনুগত্য পরীক্ষা করা। এ কারণে , যে সব আদেশ প্রদান করা হয়েছে তার পরিবর্তে যদি ভিন্ন ধরনের কোনো আদেশ দেয়া হতো তাহলে বান্দাহর জন্য তা-ই মেনে চলা অপরিহার্য হতো। তাই এ জাতীয় আদেশের পিছনে কোনো বাস্তব বা পার্থিব কারণ অনুসন্ধান করা অনুচিত। যদিও এ ধরনের কোনো কোনো বিধান পালনের পার্থিব সুফল অনুসন্ধান করলে অনেক সুফল আবিষ্কৃত হতে পারে , কিন্তু এ সব সুফলের লক্ষ্যেই এ আদেশ দেয়া হয়েছে বলে মনে করলে ভুল হবে এবং এ সব সুফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে আদেশ পালন করলে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে না অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তা‘
আলার আদেশ পালন করা হবে না।
কতগুলো বিধিবিধান প্রাকৃতিক মানদণ্ডের ওপর ভিত্তিশীল। যেমন: খাদ্যদ্রব্যের হালাল-হারামের বিষয়টি। মানুষের শরীর , মন , নৈতিকতা ও চরিত্রের মধ্য থেকে একটির ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়বে না এমন কোনো বস্তুকে হারাম করবেন অথবা বিরূপ প্রভাব পড়বে এমন কোনো বস্তুকে হালাল করবেন - এরূপ দুর্বলতা থেকে আল্লাহ্ তা‘
আলা প্রমুক্ত। অতএব , সন্দেহ নেই যে , হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ) পর্যন্ত এ তালিকা অভিন্ন। অবশ্য কখনো কোনো জনগোষ্ঠীর আনুগত্য পরীক্ষা করা বা কোনো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ শুধু ঐ জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো চিরন্তন হালাল বস্তুকে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে হারাম করা হতে পারে , সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী ও মেয়াদের বাইরে যার কোনো কার্যকরিতা থাকে না এবং যে সম্পর্কে জানা থাকে যে , পরীক্ষা বা শাস্তির উদ্দেশ্যেই সংশ্লিষ্ট বস্তুকে হারাম করা হয়েছে।
সামাজিক বিধিবিধান। এ ক্ষেত্রে স্থান-কাল ও পরিস্থিতির পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা‘
আলা কতক সাধারণ মূলনীতি ও কতক গুরুত্বপূর্ণ বিধান প্রদান করেছেন ; অবশিষ্ট বিষয়গুলো হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের এখতিয়ারে এবং প্রচলিত রীতিপ্রথার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন: বিবাহে দেনমোহর ও নাফাক্বাহ্ (ভরণ-পোষণ)-এর বিধান দেয়া হয়েছে , কিন্তু তার পরিমাণ রীতিপ্রথা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থানের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যেমন: কোরআন মজীদে মীরাছ বণ্টনের সুনির্দিষ্ট বিধান দেয়া হয়েছে ও খুমস্ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে , কিন্তু যাকাত ফরয করা হলেও তার নেছ্বাব্ ও হার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় নি , বরং তা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে।
দণ্ডবিধির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কতক ক্ষেত্রে কোরআন মজীদে সুনির্দিষ্ট বিধান দেয়া হয়েছে এবং কতক ক্ষেত্রে বিষয়টি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন: বিবাহিত স্বাধীন নারী-পুরুষের যেনা বা ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান কোরআন মজীদে নেই ,
কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) যে এ শাস্তি কার্যকর করতেন সে ব্যাপারে দ্বিমত নেই।
রাজনৈতিক , কূটনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে কতক স্থায়ী মূলনীতি প্রদান করে বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয় - যা তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারীদের অধিকার।
এবার ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। তা হচ্ছে , আল্লাহ্ তা‘
আলা যে সব মৌলিক দায়িত্ব পালনের জন্য নবী-রাসূলগণকে (আঃ) প্রেরণ করেন তা সংক্ষেপে তিনটি: (1) মানুষের নিকট জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্য সম্পর্কে সঠিক বিষয় তুলে ধরা ও তার প্রচার , (2) আল্লাহ্ তা‘
আলা মানুষের জন্য যে সব কাজ অপরিহার্য কর্তব্য (ফরয) রূপে নির্ধারণ করেছেন ও যে সব কাজ নিষেধ (হারাম) করেছেন তা জানিয়ে দেয়া এবং (3) নবীর দাও‘
আত্ গ্রহণকারীদের নেতৃত্ব দান ও পরিচালনা।
এখানে দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলতে হয় যে , ফরয ও হারাম সম্পর্কে জানানো যেহেতু নবীর মৌলিক দায়িত্ব সেহেতু নবী তাঁর অনুসারীদেরকে সর্বজনীনভাবেই তা অবগত করাবেন ; এ বিষয়ে তিনি তাঁর অল্প সংখ্যক অনুসারীকে জানাবেন তা সম্ভব নয়। অতএব , আমরা এ উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে , চারটি সূত্রে ফরয ও হারাম প্রমাণিত হতে পারে: (1) কোরআন মজীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা , (2) হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা উম্মাহর অভিন্ন আমল (ইজমা‘
), (3) মুতাওয়াতির হাদীছ ও (4)‘
আক্বলের অকাট্য রায়। অর্থাৎ খবরে ওয়াহেদ হাদীছ দ্বারা ফরয বা হারাম প্রমাণিত হয় না। অবশ্য খবরে ওয়াহেদ হাদীছের অন্যবিধ গুরুত্বপূর্ণ বহু ক্ষেত্র রয়েছে , যেমন: জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য সম্বলিত হাদীছ এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট ছোটখাটো বা বিস্তারিত বিধান সংশ্লিষ্ট হাদীছ।
আল্লাহ্ তা‘
আলা যা কিছু ফরয করেছেন তা সম্পাদন না করলে বান্দাহ্ অবশ্যই শাস্তিযোগ্য হবে এবং তিনি যা কিছু হারাম করেছেন সে সব কাজ সম্পাদন করলেও শাস্তিযোগ্য হবে (যদিও অন্যের অধিকার হরণ বা বিনষ্ট বা লঙ্ঘন করা ব্যতীত যে সব অপরাধ করা হয়েছে আন্তরিক অনুতাপ সহ তার পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ্ তা‘
আলা তার শাস্তি মওকুফ করে দেবেন)। এই ফরয ও হারাম ব্যতিরেকে মানব জীবনের বাকী সকল ক্ষেত্রে বান্দাহ্ পুরোপুরি স্বাধীন। অবশ্য এই স্বাধীন ক্ষেত্রের মধ্যে কতক কাজ ফরয না হলেও উত্তম , কল্যাণকর ও আল্লাহ্ তা‘
আলার পসন্দনীয় ; হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) এ ধরনের কাজ সম্পাদন করতেন ও তা করার জন্য অন্যদেরকে উৎসাহিত করতেন এবং যে সব কাজ হারাম না হলেও অপসন্দনীয় ও রুচিবিগর্হিত , রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) তা থেকে বিরত থাকতেন ও তাঁর অপসন্দ প্রকাশ করতেন। এ ধরনের বিষয়ের বেশীর ভাগই খবরে ওয়াহেদ হাদীছে পাওয়া যায়।
এই শেষোক্ত বিষয় সমূহে অর্থাৎ পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় বিষয়সমূহে ক্ষেত্রবিশেষে তথ্যগত মতপার্থক্য রয়েছে এবং ক্ষেত্র-বিশেষে তথ্যগত মতপার্থক্য না থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ তথা হাদীছের ব্যবহারিক দিক নির্ণয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। অর্থাৎ কোনো বিষয়কে কেউ হয়তো ফরয অর্থে গ্রহণ করেছেন , আবার কেউ পসন্দনীয় অর্থে গ্রহণ করছেন। তেমনি কোনো বিষয়কে কেউ হারাম অর্থে গ্রহণ করেছেন , আবার কেউ অপসন্দনীয় অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে এই যে , বিতর্কিত মতামত দ্বারা ফরয বা হারাম নির্ধারিত হয় না। কারণ , আল্লাহ্ তা‘
আলা বা তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল (ছ্বাঃ) কোনো কাজকে ফরয বা হারাম বলে নির্ধারণ করলে তা খবরে ওয়াহেদ হাদীছের মতো খুবই সীমিত সংখ্যক সূত্রের বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না।
কতগুলো মতপার্থক্য ঘটেছে বিস্তারিত বা বাস্তবায়নসংক্রান্ত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অথবা গৌণ বিষয়ে , অথবা একটি বিষয় আদৌ বিধান হিসেবে গণ্য কিনা সে ব্যাপারে। যেমন: দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তে সতেরো রাক্‘
আত্ নামায ফরয হবার ব্যাপারে বিতর্ক নেই , নামাযের পূর্বপ্রস্তুতি ও নামাযের মধ্যকার ফরয কাজগুলো নিয়েও বিতর্ক নেই। কিন্তু সূরা ফাতেহার পরে একটি পুরো সূরা পড়তে হবে , নাকি আংশিক পড়লেই যথেষ্ট হবে - এ ব্যাপারে বিতর্ক আছে। এ বিতর্কই প্রমাণ করে যে , বিষয়টি ফরয সংক্রান্ত নয় , অর্থাৎ পূর্ণ সূরা পড়া অপরিহার্য নয়। কারণ , অপরিহার্য হলে স্বয়ং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর যুগ থেকে এ ব্যাপারে মুসলমানদের ধারণা ও আমল অভিন্ন হতো এবং বিতর্কের সৃষ্টি হতো না। তেমনি নামাযের তাশাহ্হুদ্ , দরূদ ও সালামের বাক্যাবলীতে শব্দগত বিভিন্নতা দেখা যায় - যা প্রমাণ করে যে , এর মূল বিষয়টা যরূরী , তবে এর শব্দাবলীতে বিভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক রাক্‘
আতে সূরা ফাতেহার পূর্বে“
বিসমিল্লাহির্ রাহমানির রাহীম”
পড়তে হবে কিনা সে প্রশ্নের সমাধান‘
আক্বলী দলীলের দ্বারা করতে হবে। তা হচ্ছে , যেহেতু সূরা তাওবাহর শুরুতে“
বিসমিল্লাহ্”
নেই সেহেতু অন্যান্য সূরার শুরুতে যে“
বিসমিল্লাহ্”
রয়েছে তা ঐ সব সূরার (সূরা ফাতেহাহ্ সহ) অংশ , অতএব , তা না পড়লে ঐ সব সূরা পাঠ সম্পূর্ণ হবে না।
নামাযের ভিতরে পঠনীয় তাশাহ্হুদ্ ও দরূদের পাঠে মতপার্থক্য থেকে বুঝা যায় যে , হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন ; এ ব্যাপারে তিনি সব সময় অভিন্ন শব্দাবলী ব্যবহার করলে মতপার্থক্য হতো না। তেমনি নামাযে হাত কী অবস্থায় থাকবে তার সাথে নামাযের আদৌ কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে বলে মনে হয় না। তাই এ ব্যাপারে তিন ধরনের মত ও আমল দেখা যায় , তবে কেউই বিষয়টিকে নামাযের অন্যতম ফরয কাজ বলে গণ্য করেন না বা তাঁদের মতের অন্যথা হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে বলেও মনে করেন না। তা সত্ত্বেও অনেকে বিষয়টি নিয়ে বাড়াবড়ি করে থাকেন যা বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
মতপার্থক্যের কতগুলো বিষয় হচ্ছে সামাজিক , অর্থনৈতিক ও বিচার-ফয়সালা সংক্রান্ত। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বিভিন্ন হাদীছে প্রাপ্ত তথ্যাদির মধ্যকার পার্থক্য থেকে মতপার্থক্য ঘটেছে। যেমন: কোনো কোনো দ্রব্যে যাকাত প্রযোজ্য হওয়া বা না-হওয়া প্রশ্নে মতপার্থক্য। কিন্তু এ জাতীয় শাখাগত বিধান যেহেতু সরাসরি আল্লাহ্ তা‘
আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয় , সেহেতু নিঃসন্দেহে তা হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর এখ্তিয়ারাধীন বিষয় ছিলো। এ কারণে হয়তো তিনি বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্তে পার্থক্য করে থাকবেন। হয়তো তিনি কোনো এক সময় একটি দ্রব্যের ওপর যাকাত আরোপ করে থাকবেন এবং অন্য এক সময় তিনি দ্রব্যটিকে যাকাত-বহির্ভূত রেখে থাকবেন। অথবা হয়তো বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় তিনি একই দ্রব্যের ক্ষেত্রে কারো কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করে থাকবেন এবং কাউকে ঐ বস্তুর জন্য যাকাত প্রদান থেকে রেহাই দিয়ে থাকবেন।
বলা বাহুল্য যে , আর্থ-সামাজিক বিষয়ে স্বীয় এখ্তিয়ারাধীন ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর জন্য বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখ্তিয়ার ছিলো এবং এরূপ ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর উত্তরাধিকারীদের জন্যও বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখ্তিয়ার রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রায়োগিক ব্যাপারে , ইতিপূর্বে খবরে ওয়াহেদ্ হাদীছ গ্রহণের জন্য যে সব শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে তা পূরণ সাপেক্ষে বিভিন্ন হাদীছের মধ্য থেকে যার কাছে যেটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে হয় তিনি সেটির অনুসরণ করলে বা স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী নতুন সিদ্ধান্ত নিলেও অসুবিধা নেই।
আল্লাহ্ তা‘
আলা যেভাবে ধরণীর বুকে তাঁর প্রকৃত প্রতিনিধি নবী-রাসূলগণকে (আঃ) বিধিবিধানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি হাত-পা বেঁধে দেন নি , বরং কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখ্তিয়ার দিয়েছেন , তেমনি তিনি নবী-রাসূলগণের (আঃ) উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধিগণকেও পুরোপুরি হাত-পা বেঁধে দেন নি , যদিও তাঁদের স্বাধীন এখ্তিয়ারের ক্ষেত্র অবশ্যই নবী-রাসূলগণের (আঃ) স্বাধীন এখতিয়ারের ক্ষেত্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত এবং নবী-রাসূলগণের (আঃ) এখ্তিয়ার আল্লাহ্ তা‘
আলার বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ হলেও তাঁদের এখ্তিয়ার একই সাথে সংশ্লিষ্ট নবীর অকাট্য ও শর‘
ঈ বিধান দ্বারাও সীমাবদ্ধ।
কিন্তু নবীর উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি যখন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদির আওতাভুক্ত কোনো বিষয়ে নবীর সিদ্ধান্তটিকে‘
নীতিগত বা শর‘
ঈ সিদ্ধান্ত নয় , বরং সমাজনেতা ও রাষ্ট্রনেতা হিসেবে তাঁর পক্ষ থেকে আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক গৌণ সিদ্ধান্ত’
হিসেবে দেখতে পান - যা বিশেষ স্থান , কাল বা পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত , সে ক্ষেত্রে তিনি যথাযথ মনে করলে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারেন , যদিও নবীর সিদ্ধান্তের হুবহু অনুসরণ ও বাস্তবায়নে কোনো অসুবিধা না হলে তিনি তাকেই অগ্রাধিকার দেবেন।
এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) তাঁর পালকপুত্র হযরত যায়দ্কে (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু এরপরও যায়দ্ (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দিয়েছিলেন। কারণ , হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর এ নিষেধ কোনো শর‘
ঈ নির্দেশ ছিলো না , বরং তাঁর এ নির্দেশ ছিলো যায়দ্ (রাঃ)-এর মুরুব্বী হিসেবে তাঁর কল্যাণকামিতা। যেহেতু আল্লাহ্ তা‘
আলা ত্বালাক্ব দানের অনুমতি দিয়েছেন , অতএব , রাসূলের (ছ্বাঃ) কথা না শুনে স্বীয় স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দেয়ায় যায়দ্-এর কোনো গুনাহ্ হয় নি।
যদিও , কোরআন মজীদের ঘোষণা অনুযায়ী , মুসলমানদের ওপর তাদের নিজেদের চেয়েও রাসূলের (ছ্বাঃ) বেশী অধিকার রয়েছে - এ দৃষ্টিতে বলা যেতে পারে যে , যায়দের পক্ষে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর নিষেধ অমান্য করা ঠিক হয় নি। তবে দেখতে হবে যে , এ নিষেধটি কোন্ পর্যায়ের ; নিঃসন্দেহে এ নিষেধ কোনো দৃঢ় পর্যায়ের নিষেধ ছিলো না , বরং এ ছিলো যায়দ্-দম্পতির কল্যাণকামনা থেকে উদ্ভূত নছ্বীহত্ মাত্র যা মেনে নেয়া বা না নেয়ার বিষয়টি তিনি ব্যক্তি যায়দের (রাঃ) ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।
অন্যদিকে হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) একজন ছ্বাহাবীর প্রতি তাঁর কন্যাকে অপর একজন ছ্বাহাবীর (যিনি ছিলেন নিঃস্ব) সাথে বিবাহ দিতে বললে কন্যার পিতা তাতে রাযী হন নি ; এতেও ঐ ছ্বাহাবী কোনো শর‘
ঈ আদেশ লঙ্ঘন করেন নি। কিন্তু মেনে নেয়া অপরিহার্য না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত কন্যা কেবল হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) সন্তুষ্ট হবেন বিবেচনায় উক্ত নিঃস্ব ছ্বাহাবীকে বিবাহ করেন। তবে মুসলমানদের ওপর তাদের নিজেদের চেয়েও রাসূলের (ছ্বাঃ) যে বেশী অধিকার , রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক-সামষ্টিক ব্যাপারে তা মুসলমানদের জন্য ফরয পর্যায়ভুক্ত , একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নয়।
এ জাতীয় ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয় যে , হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর সকল আদেশ বা কাজই তাঁর উম্মাতের জন্য শর‘
ঈ আদেশ অথবা অপরিহার্যভাবে মেনে চলার পর্যায়ের আদেশ বা অবশ্য অনুসরণীয় কাজ ছিলো না।
এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে , যেহেতু নবী মু’
মিনদের ওপর তাদের নিজেদের চেয়েও বেশী অধিকার রাখেন সেহেতু তিনি উম্মাত্ , রাষ্ট্র , সমাজ ও ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ বিবেচনা করলে তাদের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করার তথা ব্যক্তিগত অধিকারকে সঙ্কুচিত করার অধিকার রাখেন। অর্থাৎ নবী কাউকে হারাম কাজের নির্দেশ দিতে পারেন না (যা আসলে নবীর পক্ষ থেকে ঘটার প্রশ্নই ওঠে না) , কিন্তু তিনি কল্যাণ বা অপরিহার্য বিবেচনা করলে তাদেরকে হালাল থেকে বিরত রাখার অধিকার রাখেন। উদাহরণস্বরূপ , মূলগতভাবে ইসলামী শরী‘
আতে দু’
জন মু’
মিন নর-নারীর মধ্যে বিবাহ অনুমোদিত হলেও নবী ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরের কোনো নর-নারীর সাথে (যদিও তারা মুসলিম) ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন। তবে এটা কোনো স্থায়ী শর‘
ঈ বিধান হবে না , বরং এ হবে সাময়িক রাষ্ট্রীয় বিধান এবং তা কার্যকর রাখা যতোদিন অপরিহার্য বিবেচিত হবে ততোদিন তা কার্যকর থাকবে ; অতঃপর নবী বা তাঁর উত্তরাধিকারী প্রয়োজনবোধে তা তুলে নিতে ও পুনরায় প্রয়োজন হলে তা পুনরায় আরোপ করতে পারেন। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ , সম্পদ জাতীয়করণ বা ভূমি অধিগ্রহণ এ পর্যায়ের কাজ যে ক্ষেত্রে নবীর যেমন স্বাধীন এখ্তিয়ার রয়েছে , তেমনি নবীর উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধিরও স্বাধীন এখ্তিয়ার রয়েছে।
এছাড়া হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর সুন্নাত্ (তাঁর প্রবর্তিত ঐতিহ্য) নিয়েও মতপার্থক্য হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ , মুসলমান পুরুষদের দাড়ি রাখার প্রশ্নে ওলামায়ে ইসলামের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে , কিন্তু দাড়ি ছাঁটা বা ছোট করা প্রশ্নে মতপার্থক্য রয়েছে। অতএব , সন্দেহ নেই যে , দাড়ি রাখাই সুন্নাত্ , সুনির্দিষ্ট মাপের দাড়ি রাখা সুন্নাত্ নয়। কারণ , সুনির্দিষ্ট মাপের দাড়ি রাখা সুন্নাত্ হলে এ বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো না। তেমনি কোরআন মজীদে তাক্ব্ওয়ার পোশাক পরিধান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে , কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ) যে লম্বা ঢোলা জামা পরিধান করতেন , তা কি তাক্ব্ওয়ার পোশাক হিসেবে পরতেন , নাকি আরবদের ঐতিহ্য ও আবহাওয়াগত কারণে পরতেন (যাতে অবশ্য তাক্ব্ওয়ার শর্তও পূরণ হতো) - এ ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু এ ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে সেহেতু আরবদের পোশাকের মতো পোশাক পরিধান করা যে সুন্নাত্ নয় তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ , তা সুন্নাত্ হলে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো না।
এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে , মতপার্থক্যের বিষয়গুলো মৌলিক বা মুখ্য নয়। তাই এ সব ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকা সম্ভব হয়েছে এবং এসব বিষয়ে মতপার্থক্য থাকায় কোনো সমস্যাও নেই। সমস্যা হয় তখনই যখন এ সব বিষয়ের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় অথবা এর ভিত্তিতে ফরয বা হারাম নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়।
অবশ্য ইজতিহাদী মতপার্থক্যের কতগুলো বিষয় ইজতিহাদী নীতিমালা নির্ধারণে দুর্বলতা থেকে উৎসারিত। এ বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে ইজতিহাদের অব্যাহত চর্চা , মতপার্থক্যের বিষয়গুলোতে পারস্পরিক দলীল-প্রমাণকে আবেগমুক্তভাবে বিশ্লেষণ এবং ইজতিহাদী নীতিমালা ও মুজতাহিদের গুণাবলী সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি অপরিহার্য। অর্থাৎ একজন মুজতাহিদের নিকট যখনই কোনো সত্য উদ্ঘাটিত হবে তখনি তা গ্রহণ করে নেয়ার জন্য তাঁর মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। তেমনি একজন মুজতাহিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা সমূহে , বিশেষ করে মানবিক বিজ্ঞান সমূহে যতো বেশী ব্যুৎপত্তির অধিকারী হবেন তাঁর পক্ষে বিভিন্ন সমস্যাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা ও তার সঠিক সমাধান উদ্বাবন করা ততোই সহজতর হবে।
এ কারণে , ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে , একজন মুজতাহিদের জন্য কোরআন নাযিলকালীন ও জাহেলিয়্যাত্ যুগের আরবদের ভাষার ব্যাকরণগত খুটিনাটি বিষয়ের সাথে পরিচিত থাকার পাশাপাশি জ্ঞানতত্ত্ব , তাৎপর্যবিজ্ঞান , ভাষাতত্ত্ব , যুক্তিবিজ্ঞান ও দর্শনে ব্যুৎপত্তির এবং ইসলামের মৌলিক উপস্থাপনা সমূহ (তাওহীদ , আখেরাত্ ও রিসালাত্)কে বিচারবুদ্ধির আলোকে ও কোরআন মজীদের আলোকে পেশ করার যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। এছাড়া তাঁকে পরিবর্তনশীল চলমান জীবন ও জগতের পরিস্থিতি সম্পর্কে সদা অবহিত থাকতে হবে। তাঁকে বিভিন্ন ধারার উছূলে হাদীছ (হাদীছ শাস্ত্রের মূলনীতি) ও দেরায়াতে হাদীছ (হাদীছ পরীক্ষণ শাস্ত্র)-এর মানদণ্ড এবং উছূলে ফিক্বহ্ (ইজতিহাদের মূলনীতি) সম্পর্কে গভীর ধারণার অধিকারী হতে হবে। এভাবে তাঁকে পূর্ববর্তী হাদীছ সংগ্রাহক , হাদীছ বিশেষজ্ঞ ও মুজতাহিদগণের নির্ধারিত উছূলের ভুলত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও সংশোধনের যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। কেবল তখনই তাঁর পক্ষে সকল ব্যাপারে প্রায় নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছা ও মতপার্থক্য নিরসনে অবদান রাখা সম্ভব হবে।
কৃতজ্ঞতা
পুরোপুরি বিচারবুদ্ধির আলোকে জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্য উদ্ঘাটন করে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় এটাই প্রথম। এ পর্যায়ে ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যে পুরোপুরি সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ , বিশেষ করে বিচারবুদ্ধির ভাবাবেগমুক্ত উপস্থাপন অত্র গ্রন্থকারের চোখে পড়ে নি। তবে বিন্যাসে দুর্বলতা , অপূর্ণাঙ্গতা ও ভাবাবেগের সংমিশ্রণ সত্ত্বেও ইতিপূর্বে এ পথে যারা অবদান রেখেছেন তাঁরা বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। বিশেষ করে সূচনাকারীর গুরুত্ব অনেক বেশী। তাঁদের লেখা দ্বারা আমি যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছি। অন্যদিকে আরবী ও ফার্সী ভাষায় এ বিষয়ে প্রচুর সংখ্যক সুবিন্যস্ত , পূর্ণাঙ্গ ও ভাবাবেগমুক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । বিশেষ করে ফার্সী ভাষায় লেখা এতদসংক্রান্ত কতক গ্রন্থ লেখককে বিচারবুদ্ধির সুসংহত প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছে।
বিচারবুদ্ধির দলীল ব্যক্তিবিশেষের সম্পদ নয় , বরং সর্বজনীন সম্পদ এবং যে কেউ তা অধ্যয়ন করার পর তাকে সঠিক হিসেবে দেখতে পায় তখন তা তার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়ে যায়। এ বিষয়টি অত্র গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তা সত্ত্বেও যে সব মনীষীর এ বিষয়ক লেখা অত্র গ্রন্থকারের বিচারবুদ্ধিকে শানিত করেছে এবং অত্র গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে , বিচারবুদ্ধির দলীলকে দুর্বল না করার লক্ষ্যে গ্রন্থমধ্যে তাঁদের নাম তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার না করলেও এবং ভূমিকায় তাঁদের নাম উল্লেখ না করলেও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাকে নিজের জন্য অপরিহার্য গণ্য করছি। তাই এখানে তাঁদের কথা স্মরণ করতে চাই।
এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যার কথা স্মরণ করছি তিনি হলেন আমার দ্বীনী শিক্ষক পিতৃপ্রতীম হযরত মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রঃ)। তাঁর লেখা‘
মহাসত্যের সন্ধানে’
গ্রন্থ এ ব্যাপারে আমার মন-মগযকে যথষ্ট প্রভাবিত করেছে। অতঃপর স্মরণ করছি ইরানের স্বনামখ্যাত ইসলামী মনীষী হযরত আয়াতুল্লাহ্ জা‘
ফার্ সোব্হানী , হযরত আয়াতুল্লাহ্ তাক্বী মেছ্ববাহ্ ইয়ায্দী ও হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন মোহাম্মাদ মোহাম্মাদী রেইশাহরী-কে (আল্লাহ্ তা‘
আলা তাঁদেরকে শুভ প্রতিদান প্রদান করুন)। তাঁদের এতদ্বিষয়ক লেখা আমাকে জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত মহাসত্যকে বিচারবুদ্ধির আলোকে দেখার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে।
এ ছাড়া কতক ক্ষেত্রে হযরত ইমাম খোমেইনী (রঃ) , শহীদ হযরত আয়াতুল্লাহ্ মোরতাযা মোতাহ্হারী (রঃ) ও হযরত আয়াতুল্লাহ্ মোহাম্মাদ তাক্বী জা‘
ফারী (রঃ)-এর কোনো কোনো লেখা আমাকে তাৎপর্যের গভীরে প্রবেশে সহায়তা করেছে। বিশেষ করে হযরত আয়াতুল্লাহ্ মোহাম্মাদ তাক্বী জা‘
ফারী (রঃ) বিষয়বস্তুর এতো গভীরে প্রবেশ করেছেন ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োগকে এমনভাবে দূরতম ও সূক্ষ্মতম দুর্বলতা থেকেও মুক্ত করেছেন যে , তা আমাকে দারুণভাবে বিস্মিত ও অভিভূত করেছে। (আল্লাহ্ তা‘
আলা এ মহান মনীষীদেরকে আলমে বারযাখের বেহেশতে সুখে-শান্তিতে রাখুন এবং শেষ বিচারে অবিনশ্বর জান্নাত্ নছ্বীব্ করুন।)
 0%
0%
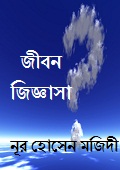 লেখক: নূর হোসেন মজিদী
লেখক: নূর হোসেন মজিদী