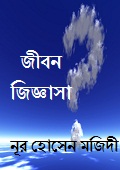বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে অপরিহার্য সত্তার গুণাবলী
মানুষের বিচারবুদ্ধি জীবন ও জগতের অন্তরালে এক অপরিহার্য অস্তিত্বের সন্ধান পায় যা থেকে সমস্ত রকমের সম্ভব-অস্তিত্ব অর্থাৎ বস্তুগত , সূক্ষ্ম ও অবস্তুগত অস্তিত্বসমূহ অস্তিত্ব লাভ করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে , মানুষের বিচারবুদ্ধি কি সে অপরিহার্য অস্তিত্বের সংজ্ঞা প্রদান করতে সক্ষম ? মানুষের পক্ষে কি তাঁর অস্তিত্বের স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব ?
এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে , কোনো কিছু সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের তিনটি অবস্থা হতে পারে: পূর্ণাঙ্গ নির্ভুল জ্ঞান , মোটামুটি কিন্তু ভ্রান্তিমুক্ত জ্ঞান এবং ভ্রান্তিযুক্ত জ্ঞান। জীবন ও জগতের উৎস যে অপরিহার্য অস্তিত্ব তাঁকে পরিপূর্ণ অথচ নির্ভুলভাবে জানা‘
ভিন্নতর তথা নিম্নতর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সম্ভব-অস্তিত্ব’
মানুষের পক্ষে পুরোপুরি অসম্ভব। কোনো মানুষের গড়া একটি চেয়ার বা একটি টেবিল বা একটি ছুরি বা অন্য কোনো জিনিস ঐ মানুষের শারীরিক আকৃতি ও অভ্যন্তরীণ রহস্য , তার আত্মা , মন-মানস ও মেধা-প্রতিভা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হতে সক্ষম - এরূপ দাবী যতোখানি অবাস্তব , মানুষ তার উৎস অপরিহার্য সত্তার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উদঘাটন করতে সক্ষম বলে কেউ দাবী করলে এর চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী অসম্ভব কিছু দাবী করা হবে। তবে বিচারবুদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য সত্তা সম্পর্কে মোটামুটি কিন্তু ভ্রান্তিমুক্ত ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ: একজন মানুষকে পুরোপুরি চেনার বা জানার দাবী করতে হলে তার বাহ্যিক চেহারা-ছুরত চেনা বা জানাই যথেষ্ট নয় , বরং তার শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু , তার মেধা-প্রতিভা , মন-মানস , ঝোঁকপ্রবণতা , আত্মা ও ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা অপরিহার্য। তবে আমরা যখন কাউকে তার চেহারার ভিত্তিতে চেনার দাবী করি তখন তা অসম্পূর্ণ হলেও ভ্রান্তিমুক্ত। কারণ , এর ভিত্তিতে আমরা তাকে শনাক্ত করতে ও তার নিকট উপনীত হতে পারি এবং তার চেহারার নির্ভুল ও নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারি। যদিও এই জানা বা চেনার দ্বারা তাকে পূর্ণরূপে জানার বা তার স্বরূপ উদঘাটনের দাবী করা যাবে না , তবে তার সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হবে এবং আমরা ভুল ব্যক্তির কাছে গিয়ে উপস্থিত হবো না।
বিচারবুদ্ধির পক্ষে জীবন ও জগতের উৎস অপরিহার্য সত্তাকে এভাবে অর্থাৎ মোটামুটি অথচ নির্ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব।
অপরিহার্য সত্তার সংজ্ঞায়নের পূর্বে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সামান্য আলোকপাত করা যরূরী বলে মনে হয়। কারণ , তা অপরিহার্য সত্তার সঠিক সংজ্ঞায়ন ও অনুধাবনে সহায়ক হবে। তা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে অস্তিত্বের প্রকারভেদ ও পর্যায়ভেদ এবং অস্তিত্বের পর্যায়ভেদ প্রশ্নে দার্শনিকদের একটি ভ্রান্তি।
ধর্মানুসারী দার্শনিকগণ
,
বিশেষতঃ মুসলিম দার্শনিকগণ সামগ্রিকভাবে
‘
অস্তিত্ব
’
(وجود
- Existence)-
এর প্রাথমিক বিভাজন নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন
:
অস্তিত্ব এক বিবেচনায় দু
’
ধরনের
:
অপরিহার্য অস্তিত্ব
(واجب الوجود
- Essential Existence)ও সম্ভব অস্তিত্ব
(ممکن الوجود
- Possible Existence)।অন্য এক বিবেচনায়ও অস্তিত্ব দু
’
ধরনের
;
তবে এ বিবেচনা পূর্বোক্ত বিবেচনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ বিবেচনায়
,
যে কোনো অস্তিত্ব হয় অবস্তুগত
(مجرد
- Non-material),নয়তো বস্তুগত
(مادّی
- Material)।এই দ্বিতীয়োক্ত বিবেচনায় তাঁরা আল্লাহ্ তা
‘
আলা
,
ফেরেশতা
,
রূহ্ ইত্যাদিকে অবস্তুগত অস্তিত্ব
(وجود مجرد
- Non-material Existence)এবং বস্তুজগত ও তার সকল উপকরণকে বস্তুগত অস্তিত্ব
(وجود مادّی
- Material Existence)রূপে গণ্য করেছেন। কিন্তু এ বিভাজন মৌলিকভাবেই ত্রুটিপূর্ণ। কারণ
,
এতে আল্লাহ্ তা
‘
আলাকে এবং ফেরেশতা ও নাফস্
-(
আত্মা
)
কে অভিন্ন ধরনের অস্তিত্ব বলে গণ্য করা হয়েছে। যদিও এতে সন্দেহ নেই যে
,
আল্লাহ্ তা
‘
আলা যেমন অবস্তুগত অস্তিত্ব তেমনি ফেরেশতা ও নাফ্স্ ইত্যাদিও অবস্তুগত অস্তিত্ব
,
কিন্তু এর চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই যে
,
আল্লাহ্ তা
‘
আলা হচ্ছেন অপরিহার্য অস্তিত্ব
(واجب الوجود
- Essential Existence), অন্যদিকে ফেরেশতা ও নাফস্ অবস্তুগত হলেও সম্ভব-অস্তিত্ব (ممکن الوجود
- Possible Existence)। এমতাবস্থায় অস্তিত্ব বিভাজনের ক্ষেত্রে কেবল অবস্তুত্বের কারণে অপরিহার্য ও সম্ভব অস্তিত্বকে এক কাতারভুক্ত করা সঙ্গত নয়। তাই আমাদের মতে , অস্তিত্বের বিভাজন হওয়া উচিত এভাবে:
অস্তিত্ব এক বিবেচনায় দু
’
ধরনের
:
অপরিহার্য অস্তিত্ব
(واجب الوجود
- Essential Existence) ও সম্ভব অস্তিত্ব (ممکن الوجود
- Possible Existence)।অপর এক বিবেচনায় অস্তিত্ব দু
ধরনের
:
পরম প্রমুক্ত অস্তিত্ব
(
সম্ভব অস্তিত্বের সকল প্রকার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত অস্তিত্ব
-وجود مجرد
) এবং অ-প্রমুক্ত অস্তিত্ব (وجود غير مجرد
) ।
অতঃপর সম্ভব-অস্তিত্ব বা অ-প্রমুক্ত অস্তিত্ব দু’
ধরনের: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব ও ইন্দ্রিয়াতীত অস্তিত্ব। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব দু’
ধরনের: বস্তুগত অস্তিত্ব ও সূক্ষ্ম অস্তিত্ব এবং ইন্দ্রিয়াতীত অস্তিত্বও দু’
ধরনের: আত্মিক অস্তিত্ব ও অ-আত্মিক অস্তিত্ব। এরপর অস্তিত্বকে নীচের দিকে আরো বিভিন্নভাবে ভাগ করা যেতে পারে। (তবে আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্যে এ বিষয়ের ওপর এতোটুকু আলোকপাতই যথেষ্ট বলে মনে হয়।)
এবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি।
অপরিহার্য সত্তা যেহেতু আমাদের অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ও উচ্চতর অস্তিত্ব সেহেতু কেবল তাঁর গুণবৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমেই তাঁকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। এ সব গুণবৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই এমন কতক ইতিবাচক গুণবৈশিষ্ট্য হতে হবে যা অপরিহার্য সত্তার জন্যে অপরিহার্য অর্থাৎ কোনো সত্তায় এ সব গুণবৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে একটি গুণও যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলেও সে সত্তার পক্ষে অপরিহার্য সত্তা হওয়া সম্ভব নয়। সেই সাথে অপরিহার্য সত্তার জন্যে ঐ সব বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য যা অপরিহার্য সত্তার জন্যে দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা রূপে প্রতিভাত হয়।
এবার আমরা অপরিহার্য সত্তার জন্যে অপরিহার্য ও পরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো।
এক: তিনি অনাদি-অনন্ত ও কালোর্ধ সত্তা
অপরিহার্য সত্তা হচ্ছেন সকল প্রকার সম্ভব-অস্তিত্বের আদি উৎস। সম্ভব-অস্তিত্ব স্বীয় সৃষ্টি , স্থিতি ও ধ্বংসের জন্যে তাঁর ওপরই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উভয়ভাবেই নির্ভরশীল। আর কাল বা সময় হচ্ছে সম্ভব-অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। সম্ভব-অস্তিত্বের শুরু ও শেষ রয়েছে যা থেকে কালের ধারণা ও অনুভূতি সৃষ্টি হয়। কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির আওতাধীন সম্ভব-অস্তিত্বের বিবর্তনধারাবাহিকতার আদিতম উৎস ও কারণ হচ্ছেন অপরিহার্য সত্তা। সুতরাং তিনি কোনো উৎস বা কারণ থেকে উদ্ভূত হতে পারেন না। অন্য কথায় ,‘
কারণ’
ও‘
উৎস’
কথাগুলো তাঁর সত্তার জন্যে আদৌ প্রযোজ্য নয়। অতএব , তাঁর কোনো শুরু থাকতে পারে না , তেমনি তাঁর কোনো শেষও থাকতে পারে না। বরং তিনি‘
শুরু’
ও‘
শেষ’
-এর উর্ধে ;‘
শুরু’
ও‘
শেষ’
কথাগুলো তাঁর জন্যে প্রাসঙ্গিক নয়। অর্থাৎ তিনি অনাদি ও অনন্ত বা কালোর্ধ সত্তা। যেহেতু অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় কালও তাঁরই সৃষ্টি - যদিও তা অবস্তুগত ও মাত্রাগত সৃষ্টি , এবং তিনি কালের গর্ভে অন্য সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন , সেহেতু তাঁর জন্যে কাল প্রাসঙ্গিক নয়।
সৃষ্টিকুলের জন্যে প্রকৃত কাল হচ্ছে দু’
টি: অতীত ও ভবিষ্যত ; বর্তমান কাল হচ্ছে এ দুইয়ের মিলনবিন্দু - অপসৃয়মাণ মুহূর্ত মাত্র। সৃষ্টির এ বৈশিষ্ট্য তার দুর্বলতামাত্র ; সে স্বীয় অতীতকে ধরে রাখতে অক্ষম বিধায় সে স্থিতিহীন। অন্যদিকে তার ভবিষ্যতও অনিশ্চিত এবং তা বর্তমানের ক্রান্তিবিন্দু অতিক্রম করে অতীতের গর্ভে হারিয়ে যায়। তাই অপরিহার্য সত্তার জন্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রযোজ্য হওয়ার ন্যায় দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য। এ কারণে , আমরা যেহেতু কালের আওতাধীন এবং সব কিছুকেই কালের আওতায় চিন্তা করি সেহেতু আমরা যদি অপরিহার্য সত্তা সম্বন্ধে কালকে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি তো কেবল বর্তমান কালকেই প্রাসঙ্গিক গণ্য করতে পারি। অর্থাৎ তিনি কালের উর্ধে এবং কালকে ধারণ করে আছেন ; আমাদের নিকট যা অতীত ও ভবিষ্যৎ তা তাঁর নিকট সদা বর্তমান।
যেহেতু সৃষ্টিকুল কালের আওতাধীন সেহেতু কালোর্ধতার ধারণা সৃষ্টির নিকট গোলকধাঁধার মতো মনে হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিচারবুদ্ধি অপরিহার্য সত্তাকে কালোর্ধ বা অনাদি-অনন্ত বলে গণ্য করতে বাধ্য। অপরিহার্য ও সম্ভব সত্তার মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যের কারণেই সম্ভব-সত্তার দৃষ্টিতে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য প্রতিভাত হলেও অপরিহার্য সত্তার জন্যে অনাদি-অনন্ত হওয়া অপরিহার্য। অন্যথায় তাঁর পক্ষে অপরিহার্য সত্তা হওয়া সম্ভব নয়।
দুই: তিনি অসীম বা স্থানোর্ধ সত্তা
সসীমতা সৃষ্টি বা সম্ভব-সত্তার বৈশিষ্ট্য। তাই অপরিহার্য সত্তাকে অনিবার্যভাবেই তা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অতএব , বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে এই যে , তিনি অসীম , অর্থাৎ তিনি স্থানগত যে কোনো সীমাবদ্ধতার উর্ধে ; স্থানগত কোনো বৈশিষ্ট্যই তাঁর জন্যে প্রযোজ্য নয়। কেননা , সসীমতা বা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে দুর্বলতা ও অপূর্ণতার পরিচায়ক। এমনকি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও যে সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা যত বেশী তাকে তত বেশী দুর্বল এবং যার সীমাবদ্ধতা যত কম তাকে তত কম দুর্বল বলে গণ্য করা হয়। এমতাবস্থায় অপরিহার্য সত্তাকে অবশ্যই এ অপূর্ণতা ও দুর্বলতার উর্ধে থাকতে হবে ; এটাই তাঁর পূর্ণতা-গুণের দাবী।
অপরিহার্য সত্তাকে স্থানের আওতাভুক্ত মনে করা (তা সে স্থানের আওতা যতোই প্রশস্ত হোক না কেন) মানে তাঁকে সসীম গণ্য করা , আর তাঁকে সসীম গণ্য করা মানে তাঁকে স্থানের আওতাভুক্ত গণ্য করা , অথচ তিনি স্থানেরও সৃষ্টিকর্তা। তিনি স্থান ও কাল সৃষ্টি করেছেন এবং স্থান ও কাল রূপ ধারকের গর্ভে অন্য সবকিছুকে , বিশেষতঃ বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করেছেন। এমতাবস্থায় কী করে তিনি স্বীয় সৃষ্ট স্থানের আওতাভুক্ত হতে পারেন ?
বলা বাহুল্য যে , এখানে স্থান মানে শুধু ভূপৃষ্ঠ বা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদির পৃষ্ঠ মাত্র নয় , বরং প্রচলিত অর্থে যা শূন্য বা মহাশূন্য তা-ও স্থানরূপে পরিগণিত। অর্থাৎ যেখানেই কোনো সৃষ্টির পক্ষে স্থানলাভ করা সম্ভব তা-ই স্থান। আর‘
স্থান’
কে যে কোনো অর্থেই গ্রহণ করা হোক না কেন ,‘
স্থান’
মাত্রই অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টি। নিঃসন্দেহে তিনি স্বীয় সৃষ্টির আওতায় সীমাবদ্ধ হতে পারেন না। সৃষ্টি তাঁকে ধারণ করতে পারে - তাঁর সম্পর্কে এটা ধারণাই করা চলে না।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে , বিশ্বলোকের আদি উৎস অপরিহার্য সত্তা তথা সৃষ্টিকর্তা যে অপরিহার্যভাবেই অসীম - বিচারবুদ্ধির এ অনস্বীকার্য রায়কে স্বীকার করে নিয়েও অনেক লোক তাঁকে‘
অসীম হওয়া সত্ত্বেও সসীমরূপে আত্মপ্রকাশকারী’
বলে কল্পনা করতে পসন্দ করেন এবং‘
সীমার মধ্যে অসীম তুমি’
ও‘
সৃষ্টির কল্যাণার্থে’
যুগে যুগে সম্ভব সত্তা বা সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হন (সম্ভবামি যুগে যুগে) ইত্যাদি কাব্যমণ্ডিত ভাষায় স্বীয় দাবী উপস্থাপনের মাধ্যমে বিচারবুদ্ধির রায়ের অনিবার্য উপসংহারকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো , অসীমের বৈশিষ্ট্যই এই যে , তাঁর পক্ষে সসীম হওয়া সম্ভব নয় ; সসীম সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ তো দূরের কথা।
অনেকে এ প্রসঙ্গে ভ্রমাত্মক কূটতর্কের
( fallacy -مغالطة
)আশ্রয় নিয়ে বলার চেষ্টা করেন যে
,
সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছুই নেই
,
অতএব
,
তাঁর পক্ষে সসীমরূপে আত্মপ্রকাশ করাও সম্ভব
;
অন্যথায় তিনি অক্ষম বলে প্রমাণিত হবেন এবং তা তাঁর অপূর্ণতার পরিচায়ক হবে। এ এক স্ববিরোধী উদ্ভট অপযুক্তি। কারণ
,
কারো দুর্বলতা ও অক্ষমতা তখনই প্রমাণিত হয় যখন একটি সম্ভব কাজ করতে সে অসমর্থ হয়
;
বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে যে কাজটি মূলগতভাবেই অসম্ভব তা করতে না পারার কারণে কারো ওপরে অক্ষমতা আরোপ করা যায় না। অসীম সত্তা সৃষ্টিকর্তাকে সসীম সৃষ্টিতে পরিণত হতে হবে
-
এ হচ্ছে সোনার পাথর
-
বাটির মতোই অসম্ভব কিছু দাবী করা
।
একটি বাটি হয় সোনার
হবে
,
নয়তো পাথরের হবে
,
নয়তো সোনা ও পাথরের মিশ্রণের হবে
;
কিন্তু একই সাথে তা খাঁটি সোনারও হবে
,
আবার খাঁটি পাথরেরও হবে
-
এটা তো সম্ভব নয়। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে
,
কোনো না কোনোভাবে খাঁটি সোনার বাটি খাঁটি পাথরের বাটিতে পরিণত হতে সক্ষম তাহলেও মানতে হবে যে
,
যেই মুহূর্তে সোনা পাথরে পরিণত হবে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে আর সোনার বাটির অস্তিত্ব থাকবে না এবং এর বিপরীত ক্ষেত্রেও তা
-
ই। অতএব
,
একই সাথে তা পুরোপুরি সোনার ও পুরোপুরি পাথরের হতে পারে না।
তেমনি যদি ধরে নেয়া হয় যে , অপরিহার্য সত্তা সৃষ্টিকর্তার পক্ষে সম্ভব-সত্তা সসীম সৃষ্টিতে পরিণত হওয়া সম্ভব তাহলে যে মুহূর্তে তিনি সসীম সৃষ্টিরূপ সম্ভব-সত্তায় পরিণত হবেন ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে আর তিনি অসীম অপরিহার্য সত্তা সৃষ্টিকর্তা থাকছেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের সমস্যা হচ্ছে এই যে , যেহেতু সম্ভব-অস্তিত্ব সমূহ কেবল তাদের অস্তিত্বলাভের জন্যেই অপরিহার্য সত্তার ওপর নির্ভরশীল নয় , বরং অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার জন্যেও তাঁর ওপর নির্ভরশীল , সেহেতু অপরিহার্য সত্তা সসীম সৃষ্টির রূপ ধারণ করলে তথা অপরিহার্যতা হারালে সাথে সাথে তার সৃষ্টিনিচয়ও অস্তিত্ব হারাতে বাধ্য ।
বস্তুতঃ অসীমত্ব হচ্ছে পূর্ণতার পরিচায়ক এবং সসীমত্ব হচ্ছে অপূর্ণতার পরিচায়ক। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সসীমের মধ্যে অসীমতা তথা অপূর্ণের মধ্যে পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। কিন্তু এর বিপরীতে অসীমের মধ্যে সসীম হওয়ার তথা পূর্ণের মধ্যে অপূর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকতে পারে না। অভাবহীন অসীম সত্তা কোন্ অভাব পূরণের জন্যে সসীম হতে চাইবেন ? সৃষ্টির কল্যাণের জন্যে ? সৃষ্টির কল্যাণের জন্যে তো তাঁর সৃষ্টির রূপ ধারণ করার প্রয়োজন নেই। তিনি তো সৃষ্টি থেকে দূরে নন , বরং তিনি সৃষ্টিকে ধারণ করে আছেন , অতএব , তিনি চাইলেই সৃষ্টিকে কল্যাণ পৌঁছাতে পারেন। তিনি কি সৃষ্টির সামনে আদর্শ উপস্থাপনের জন্যে সসীম সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হবেন ? তার কোনো প্রয়োজন আছে কি ? তিনি তো চাইলেই তাঁর কোনো সৃষ্টিকে অন্যান্য সৃষ্টির জন্যে আদর্শরূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম। তাহলে তিনি নিজেকেই কেন আদর্শরূপে উপস্থাপন করবেন ? যদি যুক্তির খাতিরে তা সম্ভব বলে ধরে নেই তথাপি তা হবে উদ্দেশ্যের বিপরীত। কারণ , স্রষ্টা কখনো সৃষ্টির জন্যে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারেন না। কারণ , স্রষ্টার পক্ষে যা সম্ভব ও সহজ সৃষ্টির পক্ষে তা সম্ভব ও সহজ নয়। এ ক্ষেত্রে বরং বিপরীত ফল পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সৃষ্টির এটাই মনে হতে বাধ্য যে , তিনি তো স্রষ্টা ; তাঁর পক্ষে যা সম্ভব আমাদের পক্ষে কি তা সম্ভব ? অতএব , যে ক্ষেত্রে তার পক্ষে স্রষ্টাকে অনুসরণ করা সম্ভব সে ক্ষেত্রেও অনুসরণীয় সত্তা সৃষ্টি না হয়ে স্রষ্টা হওয়ায় সে হতাশায় আক্রান্ত হয়ে তাঁকে অনুসরণে অক্ষম হয়ে পড়বে অথবা , ক্ষেত্রবিশেষে , সে স্বেচ্ছায় এটাকে বাহানা হিসেবে গ্রহণ করবে।
অতএব , বিচারবুদ্ধি এ উপসংহারে উপনীত হতে বাধ্য যে , অপরিহার্য সত্তা কোনো স্থানবিশেষে অবস্থান , অধিষ্ঠান , অবতরণ বা অবতাররূপে জন্মগ্রহণ জনিত সসীমতার উর্ধে।
তিন: তিনি নিরাকার
অপরিহার্য সত্তা নিরাকার হতে বাধ্য। কারণ , আকার হচ্ছে সম্ভব সত্তার , বিশেষতঃ বস্তুগত সত্তার বৈশিষ্ট্য এবং সসীমতার পরিচায়ক। বরং আকারের জন্য সীমাবদ্ধতাই দায়ী। অন্যভাবে বলা যায় যে , আকারবিশিষ্ট হওয়া সসীমতার চেয়েও অধিকতর দুর্বলতার পরিচায়ক। অতএব , অসীম সত্তার কোনো আকার থাকা সম্ভব নয়। বরং তিনি আকারবিশিষ্ট হওয়ার ন্যায় দুর্বলতার উর্ধে। এ কারণে তিনি আকার ধারণ করার বা আকার ধারণের ইচ্ছাপোষণেরও উর্ধে। কারণ , অসীম সত্তা আকার ধারণ করতে পারেন না ; আকার ধারণ করতে হলে তাঁকে অবশ্যই সসীম হতে হবে। আর অসীমত্ব পূর্ণতার ও সসীমত্ব অপূর্ণতার পরিচায়ক।
বলা বাহুল্য যে , পরম পূর্ণতার অধিকারী অপরিহার্য সত্তার কোনো অপূর্ণতা বা অভাব থাকতে পারে না যা পূরণের জন্যে তাঁকে আকার ধারণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কেউ সৃষ্টির কল্যাণ বা শিক্ষার প্রসঙ্গ তুলতে পারেন। তবে তা যে , ভ্রান্ত তা ওপরে অপরিহার্য সত্তার অসীমত্ব সংক্রান্ত আলোচনায়ই প্রমাণিত হয়েছে।
অপরিহার্য সত্তার অনিবার্যভাবেই নিরাকার হওয়া থেকে এ-ও প্রমাণিত হয় যে , তাঁকে কোনোভাবেই দেখা সম্ভব নয় ; না ইহকালে , না পরকালে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে আত্মিকভাবে দেখার কথা বলা হয় যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে আত্মিকভাবে দর্শনের মানে তাঁর অস্তিত্ব এমন অকাট্যভাবে উপলব্ধিকরণ যাতে কোনোভাবেই বিন্দুমাত্র সংশয় প্রবেশের সুযোগ নেই ; এর সাথে চাক্ষুষ দর্শনের কোনো সম্পর্ক নেই। ভীতি ও প্রশান্তির ন্যায় মানসিক অবস্থা এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রায় অবস্তুগত অস্তিত্বের ন্যায় পার্থিব জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি মোটামুটি বুঝা যেতে পারে , যদিও অপরিহার্য অস্তিত্বের আত্মিক উপলব্ধি অনুধাবনের জন্যে এ সব অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত দুর্বল ও অপূর্ণ দৃষ্টান্ত।
চার: তিনি অবিভাজ্য ও অযৌগিক সত্তা
অপরিহার্য সত্তার জন্যে সকল বিবেচনায়ই এক ও একক হওয়া অপরিহার্য । অর্থাৎ তিনি অনিবার্যভাবেই অবিভাজ্য ও অযৌগিক সত্তা। কেননা , যৌগিকতা হচ্ছে সম্ভব-সত্তা বা সৃষ্ট-সত্তার , বিশেষতঃ বস্তুগত সত্তার বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের যে কোনো সত্তা বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত , তা সে অংশসমূহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই হোক (যেমন: মানুষের রয়েছে) অথবা প্রাথমিক মৌলিক উপাদানই হোক (যেমন: একটি পরমাণু ইলেকট্রন , প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত)। আর যে কোনো অবস্থায়ই একটি যৌগিক সত্তার অস্তিত্ব তার উপাদানসমূহের ওপর নির্ভরশীল। এ সব উপাদান বিভাজিত বা বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে ঐ সত্তার বিনাশ বা বিলুপ্তি ঘটে। অতএব , সন্দেহ নেই যে , বিভাজ্যতা বা যৌগিকতা সম্ভব-সত্তা বা সৃষ্টির দুর্বলতাবাচক বৈশিষ্ট্য। তাই অপরিহার্য সত্তার জন্য অবশ্যই এহেন দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য। অর্থাৎ তিনি কোনোভাবেই কোনো যৌগিক উপাদানের সমন্বিত সমষ্টি নন। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে ,‘
উপাদান’
মাত্রই সম্ভব-সত্তারই বৈশিষ্ট্য। অতএব , অপরিহার্য সত্তার জন্যে উপাদানের ধারণা প্রযোজ্য হতে পারে না , তা বিভিন্ন উপাদানই হোক বা অভিন্ন উপাদানই হোক।
অপরিহার্য সত্তা শুধু যৌগিকতার বস্তুগত ধারণা থেকেই মুক্ত নন
,
বরং যৌগিকতার অবস্তুগত ধারণা থেকেও মুক্ত। যৌগিকতার অবস্তুগত বা বিচারবুদ্ধিগত ধারণাসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একই সত্তায় বিভিন্ন গুণের সমাহার। যেহেতু কোনো সৃষ্টির মধ্যে সম্ভাব্য গুণসমূহের সবগুলো বা কয়েকটি থাকতেও পারে বা না
-
ও থাকতে পারে। এমতাবস্থায় প্রথমত
:
ঐ সৃষ্টি থেকে তার গুণকে বা গুণসমূহকে আলাদা করে দেখা যায়
,
আবার তার বিভিন্ন গুণকেও পরস্পর আলাদা করে দেখা যায়। যেমন
:
একটি সদ্যজাত শিশু কোনো গুণের অধিকারী নয়
,
কিন্তু পরে সে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন গুণের অধিকারী হয়। এমতাবস্থায় সে জ্ঞান
,
শক্তি
,
সাহস
,
ধৈর্য ইত্যাদি গুণাবলীর যে কোনোটির অধিকারী হতে পারে
,
আবার না
-
ও হতে পারে। অতএব
,
মানুষ ও তার গুণাবলী এক নয় এবং তার গুণসমূহও পরস্পর অভিন্ন নয়। এমতাবস্থায় মানুষের মূল সত্তা
(
অবস্তুগত সত্তা
-
নাফ্স্ বা অহং
/
self)
একটি যৌগিক সত্তা যা অবস্তুগত বিধায় এর যৌগিকতা বিচারবুদ্ধিগত যৌগিকতা
(ترکيب عقلی
- abstract combination)।অপরিহার্য সত্তার জন্যে এ ধরনের যৌগিকতারও উর্ধে থাকা অপরিহার্য। কারণ
,
এ ধরনের যৌগিকতাও দুর্বলতার পরিচায়ক তথা সম্ভব
-
সত্তার বৈশিষ্ট্য। অতএব
,
অপরিহার্য সত্তার গুণাবলী তাঁর সত্তা থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়
,
তেমনি সে সব গুণাবলী পরস্পরও পৃথক নয়। বরং একদিকে যেমন তাঁর সকল গুণ প্রকৃত পক্ষে এক অভিন্ন গুণ
,
তেমনি তাঁর গুণ ও তাঁর সত্তা অভিন্ন। অন্য কথায়
,
তাঁর সত্তাই তাঁর গুণাবলী।
বিচারবুদ্ধিগত যৌগিকতার আরেকটি ধারণা হচ্ছে কোনো সত্তায় কোনো গুণের মাত্রাগত কম-বেশীর ধারণা । যেমন: কোনো মানুষের মধ্যে শক্তি , সাহস , জ্ঞান , ধৈর্য ইত্যাদি গুণ কম থাকতে পারে এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে , তেমনি বেশী থেকে তা ক্রমান্বয়ে কমে যেতে পারে। এভাবে একই সত্তায় কোনো গুণের বিভিন্ন মাত্রা ধারণা করা যেতে পারে যার ফলে বিচারবুদ্ধি একটি গুণকে বস্তুগত অর্থে না হলেও মাত্রাগত অর্থে বিভিন্ন ইউনিটে বা পরিমাণে বিভক্ত করতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি গুণই কতক মাত্রাগত এককের সমষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। অপরিহার্য সত্তার গুণাবলী যেহেতু অর্জিতও নয় , প্রাপ্তও নয় , বরং তাঁর সত্তার সাথে অভিন্ন তথা তাঁর চিরবিদ্যমান সত্তাই তাঁর গুণ , সেহেতু তাঁর গুণাবলীতে এ ধরনের মাত্রাগত এককের বিচারবুদ্ধিগত যৌগিকতাও ধারণা করা যেতে পারে না। বরং যৌগিকতার যত রকমের ধারণা করা যেতে পারে তিনি তার সবগুলো ধারণারই উর্ধে।
একই কারণে তাঁর সত্তা সব রকমের গতি , পরিবর্তন , বিবর্তন বা পূর্ণতাভিমুখিতারও উর্ধে। কেননা যা অযৌগ একক তাতে পরিবর্তন সম্ভব নয় , যা অসীম একক তাতে গতি সম্ভব নয় এবং যা পরম পূর্ণতার অধিকারী তার জন্যে পূর্ণতা-অভিমুখে অগ্রগামিতার প্রশ্নও উঠতে পারে না।
অপরিহার্য সত্তার সত্তা ও গুণাবলীর অভিন্নতার বিষয়টি অনেকের নিকট দুর্বোধ্য বলে মনে হতে পারে , তবে সৃষ্টিজগত থেকে প্রাপ্ত উদাহরণ থেকেই এ দুর্বোধ্যতা দূরীভূত হতে পারে। যেমন: আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় পাঁচটি গুণের পরিচায়ক ; আমাদের দর্শনশক্তি , শ্রবণশক্তি , আঘ্রাণশক্তি , আস্বাদনশক্তি ও স্পর্শনশক্তি এ ইন্দ্রিয়নিচয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তাই আমরা একটি ইন্দ্রিয় হারিয়ে ফেললে এ সব শক্তি বা গুণের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট শক্তি বা গুণটি হারিয়ে ফেলি। কিন্তু আসলে আমরা এ সব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে বিচারবুদ্ধির বস্তুগত যন্ত্ররূপ মস্তিষ্কে প্রেরণ করি। কিন্তু কোনো কোনো প্রাণী তার একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মানুষের একাধিক ইন্দ্রিয়ের কাজ পুরো মাত্রায় সম্পাদন করে থাকে। যেমন: কেঁচোর শরীর একই সাথে দর্শন , শ্রবণ ও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করে। অন্যদিকে সাপ তার জিভ দিয়ে শুধু স্বাদগ্রহণের কাজই করে না , শ্রবণের কাজও করে থাকে। অতএব , এমন কোনো সৃষ্টি থাকাও বিচিত্র নয় যার একটিমাত্র ইন্দ্রিয় আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দায়িত্ব হুবহু ও নিখুঁতভাবে পালন করে। এমতাবস্থায় এমন কোনো সৃষ্টি থাকাও অসম্ভব নয় যার গোটা শরীরই পঞ্চেন্দ্রিয় (যেমন: কেঁচোর গোটা শরীরই শ্রবণ , দর্শন ও স্পর্শনেন্দ্রিয়) অর্থাৎ তার সত্তা ও ইন্দ্রিয়নিচয় অভিন্ন।
এটা অবশ্য অপরিহার্য সত্তার সত্তা ও গুণাবলীর অভিন্নতা অনুধাবনের জন্যে একটি খুবই দুর্বল উপমা। কিন্তু এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে , অপরিহার্য সত্তার জন্যে তাঁর সত্তা ও গুণাবলী অভিন্ন হওয়া সম্ভব। আর যেহেতু সত্তা ও গুণাবলী অভিন্ন না হওয়া এবং পৃথক হওয়া দুর্বলতার পরিচায়ক সেহেতু অপরিহার্য সত্তার সত্তা ও গুণাবলী অভিন্ন হওয়া অপরিহার্য।
পাঁচ: তিনি অস্তিত্বদান-ক্ষমতার অধিকারী
যেহেতু সম্ভব-অস্তিত্বসমূহের অস্তিত্বলাভের আদিতম কারণ হচ্ছেন অপরিহার্য সত্তা এবং তিনি ব্যতীত সম্ভব-অস্তিত্বের জন্যে দ্বিতীয় কোনো আদি উৎস বা আদি কারণ চিন্তা করা সম্ভব নয় , সেহেতু অপরিহার্য সত্তার জন্যে সৃষ্টি করার গুণ বা ক্ষমতা তথা অস্তিত্বপ্রদান-ক্ষমতার অধিকারী হওয়া অপরিহার্য। এ ধরনের গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী না হলে তিনি সম্ভব-অস্তিত্বকে অস্তিত্বদান করতে পারতেন না। তবে অপরিহার্য অস্তিত্ব সম্ভব-অস্তিত্বের জন্যে শুধু আদি কারণই নন , বরং বর্তমান কারণও বটে। অর্থাৎ সম্ভব-অস্তিত্বের সৃষ্টিই শুধু নয় , বরং স্থিতিও অপরিহার্য সত্তার ওপর নির্ভরশীল।
বলা বাহুল্য যে , আমরা সৃষ্টিলোকের বিভিন্ন উপকরণের তথা বিভিন্ন সৃষ্টির অস্তিত্বলাভের পিছনে বিভিন্ন কারণ লক্ষ্য করি , তবে এ সব কারণও আদি কারণ বা অপরিহার্য সত্তা থেকে উৎসারিত। সৃষ্টিলোকে বিদ্যমান আমাদের প্রত্যক্ষকৃত কারণসমূহ ও আদি কারণ অপরিহার্য সত্তার মধ্যকার বৈশিষ্ট্যগত অন্যতম পার্থক্য এই যে , কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব-অস্তিত্বের অস্তিত্বলাভের‘
পূর্ণ কারণের’
অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহের মধ্য থেকে কোনো উপাদানের বিলুপ্তির পরেও সে কারণের ফলশ্রুতি ঐ সম্ভব-অস্তিত্বটি টিকে থাকে। যেমন: একটি গাছের অস্তিত্বলাভের জন্যে বীজ , বীজের প্রাণসম্ভাবনা , উপযুক্ত মাটি ও আবহাওয়া এবং বীজবপনকারীর অস্তিত্ব অপরিহার্য। বীজ বপন করার পর বীজবপনকারীর ও চারাগাছের জন্মের পর বীজের বিলুপ্তি বা বিনাশ ঘটলেও গাছ টিকে থাকতে পারে। অর্থাৎ গাছটির অস্তিত্বলাভের জন্যে বীজ ও বীজবপনকারীর অস্তিত্ব অপরিহার্য হলেও তার টিকে থাকার জন্যে এ দুই উপাদানের টিকে থাকা অপরিহার্য নয়। কিন্তু গাছটির জন্ম ও স্থিতির সকল কারণ বা উপাদানই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরিহার্য সত্তা থেকে অস্তিত্বলাভ করেছে। ফলে গাছটি তার জন্মের কারণসমূহের মধ্য থেকে যে ক’
টির বা যেটির ওপরই টিকে থাকুক না কেন , কার্যতঃ সে সকল কারণের আদি কারণ অপরিহার্য সত্তার ওপর নির্ভর করেই টিকে আছে।
বস্তুতঃ গোটা সৃষ্টিলোকের অস্তিত্বদানকারী সত্তার জন্যে কতগুলো গুণের অধিকারী থাকা অপরিহার্য এবং এ কারণে আদি কারণ বা অপরিহার্য সত্তা অবশ্যই তার অধিকারী। এ সব গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে , সম্ভব-অস্তিত্ব তথা সৃষ্টিলোকের মধ্যে যে সব পূর্ণতাবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অবশ্যই তাঁর মধ্যে থাকতে হবে। যেহেতু তিনি নিজে ছাড়া আর কোনো আদি উৎস নেই সেহেতু কোনো পূর্ণতাবাচক গুণের অধিকারী তিনি নিজে না হলে তাঁর সৃষ্টিকে সে গুণ প্রদান করতে পারেন না। অবশ্য তিনি এ সব গুণের পরিপূর্ণ ও পূর্ণ মাত্রায় অধিকারী , কিন্তু সৃষ্টি এ সব গুণের বা এ সবের মধ্য থেকে একটি বা কয়েকটি গুণের অপূর্ণ অধিকারী। তাই তারা ঐ সব গুণে পূর্ণতা অর্জনের প্রয়াসী বা প্রত্যাশী। তবে এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ শারীরিক বা বস্তুগত বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণতাবাচক গুণ বলে গণ্য করা ঠিক হবে না। কারণ , শরীর ও বস্তুর অধিকারী হওয়া সীমাবদ্ধতাবাচক তথা অক্ষমতা ও অপূর্ণতা বাচক বৈশিষ্ট্য , সক্ষমতা ও পূর্ণতা বাচক বৈশিষ্ট্য নয়। তাই অপরিহার্য সত্তার জন্যে কোনোরূপ শারীরিক বা বস্তুগত‘
পূর্ণতা’
অচিন্ত্যনীয়।
অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিক্ষমতার আরেকটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে , তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের সূচনা করেন। কারণ , নিজের সৃষ্ট নয় এমন মওজূদ উপায়-উপাদানের দ্বারা সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব-অস্তিত্বসমূহের মধ্যকার সৃজনীশক্তির অধিকারী প্রজাতি-সমূহের বৈশিষ্ট্য। যেহেতু সমস্ত সম্ভব-অস্তিত্বের আদিতম কারণ হচ্ছেন অপরিহার্য সত্তা সেহেতু তাঁর দ্বারা সৃষ্টিকর্মের সূচনাকালে কোনোরূপ সৃষ্টি-উপাদান মওজূদ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব , নিঃসন্দেহে তিনি অনস্তিত্ব থেকে সম্ভব-অস্তিত্বের সৃষ্টির সূচনা করেন এবং এ কারণে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মই মূলগতভাবে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বদান।
অবশ্য তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি স্বাধীন অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কিত তাঁর ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তের মধ্যে সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং স্থান-কাল সবই শামিল থাকে। তিনি চাইলে কোনো কিছুকে মুহূর্তের মধ্যে সরাসরি সৃষ্টি করতে পারেন অর্থাৎ সরাসরি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বদান করতে পারেন , আবার চাইলে প্রাথমিক উপাদান ও প্রাকৃতিক বিধিবিধান সৃষ্টি করে এতদুভয়ের সমন্বয়ে বিশেষ স্থান ও কালে কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করতে পারেন।
বিচারবুদ্ধির পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে যে , এ সৃষ্টিজগতে প্রাকৃতিক বিধিবিধান কার্যকর রয়েছে এবং সে বিধিবিধানের অধীনে বিদ্যমান সৃষ্টিনিচয় পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন সৃষ্টির উদ্ভব হচ্ছে। অতএব , সন্দেহ নেই যে , তিনি প্রাকৃতিক বিধিবিধান ও মৌলিক উপাদান সৃষ্টির মাধ্যমে একটি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চালু করেছেন। অন্যদিকে সীমাহীন সৃজনক্ষমতার অধিকারী অপরিহার্য সত্তা একবার আদি সৃষ্টি-উপাদান ও প্রাকৃতিক বিধিবিধান সৃষ্টির মাধ্যমে একটি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সূচনা করে গোটা সৃষ্টিকর্মকে স্বয়ংক্রিয় বা যান্ত্রিক করে দিয়েছেন এবং তাঁর সৃষ্টিক্ষমতাকে আর ব্যবহার করছেন না , অন্য কথায় , সৃষ্টিকার্য থেকে অবসর নিয়েছেন - তাঁর সম্পর্কে এমনটা চিন্তাও করা যায় না। বরং এটাই স্বাভাবিক যে , সীমাহীন সৃজনক্ষমতার অধিকারী সত্তা প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রতিও দৃষ্টি রাখছেন এবং প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপও করছেন , অন্যদিকে তিনি অনবরত নব নব মৌলিক সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনও অব্যাহত রেখেছেন যদিও আমরা সে সম্পর্কে অবহিত নই।
অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিগুণের বা সৃষ্টিক্ষমতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে , যেহেতু তিনি সৃষ্টির আদিতম কারণ এবং যে কোনো সৃষ্টির সকল কারণের মূল কারণ , সেহেতু যে কোনো সৃষ্টির স্থিতিও পুরোপুরিভাবে তাঁর ওপরই নির্ভরশীল।
এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ না করলে নয়। তা হচ্ছে , অপরিহার্য সত্তার সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হওয়ার মানে এ নয় যে , সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন তাঁর জন্যে অপরিহার্য হবে। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করতে বাধ্য নন। কারণ , সৃষ্টি করতে তিনি বাধ্য হলে সংশ্লিষ্ট সৃষ্টিকেও তাঁর পাশাপাশি অপরিহার্য সত্তায় পরিণত হতে হয় , আর তা একেবারেই অসম্ভব। বরং তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হওয়া মানে তিনি চাইলেই সৃষ্টি করতে পারেন , তবে সৃষ্টি করা তাঁর জন্যে অপরিহার্য নয়। অবশ্য তিনি এরূপ ক্ষমতার অধিকারী বিধায় এটাই স্বাভাবিক যে , তিনি সৃষ্টি করার জন্যে ইচ্ছা করবেন এবং তদনুযায়ী সৃষ্টি করবেন , আর প্রকৃত পক্ষেও তিনি ইচ্ছা করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন।
এখানে একটি দার্শনিক বিতর্ক দেখা দিতে পারে। তা হচ্ছে , অপরিহার্য সত্তা তো পরম পূর্ণতার অধিকারী ; এমতাবস্থায় তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা করা ও তা সম্পাদন করার কারণ কী ? সৃজনক্ষমতা থাকলেই সৃষ্টি করতে হবে - এটা তো অপরিহার্য নয়! তিনি যখন সকল প্রকার অভাব ও প্রয়োজনের উর্ধে তখন তিনি সৃষ্টি করলেন কেন ? বলা হতে পারে: যেহেতু তিনি সৃষ্টি করেছেন সেহেতু এর কারণ হয়তো এই যে , হয় তাঁর মধ্যে কোনো অভাববোধ আছে যা পূরণের জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন , নয়তো তাঁর সৃষ্টিগুণ এমন যে , সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন তার অনিবার্য দাবী , অতএব , তাঁর জন্যে সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন না করা সম্ভব ছিল না।
এ কথার জবাব হচ্ছে এই যে , অপরিহার্য সত্তা ইতিবাচক সংখ্যা ও নেতিবাচক সংখ্যার মাঝামাঝি কোনো নিরপেক্ষ সংখ্যা তথা শূন্যের সাথে তুলনীয় নন। বরং অনস্তিত্ব ও অস্তিত্ব যথাক্রমে শূন্য ও ইতিবাচক সংখ্যার সাথে তুলনীয়। যেহেতু অপরিহার্য সত্তা অনিবার্যভাবেই আছেন এবং অস্তিত্বমাত্রই ইতিবাচক , সেহেতু অপরিহার্য সত্তা ইতিবাচক। তাই তাঁর নিজের জন্যে সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও এবং তিনি আদৌ কোনো সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন না করার স্বাধীনতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনভাবেই তাঁর এ গুণের ইতিবাচক বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তিনি সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা করেছেন এবং এ সৃষ্টিলোককে সৃজন করেছেন ও পত্যক্ষ-পরোক্ষ উভয়ভাবে সৃষ্টিকর্ম অব্যাহত রেখেছেন। একই কারণে তিনি সৃষ্টিকুলের প্রয়োজনে যা কিছুকে চান স্থিতি বিধানের ইচ্ছা করছেন এবং স্থিতি প্রদান করছেন।
ছয় : তিনি চিরজীবী
যে সত্তা প্রকৃত সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ পূর্ব থেকে বিদ্যমান কোনো উপাদান ছাড়াই সৃষ্টি করতে সক্ষম সে সত্তা কখনোই নিষ্প্রাণ বা যান্ত্রিক সত্তা হতে পারেন না। কারণ
,
সৃষ্টিক্ষমতা একমাত্র প্রাণশীল সত্তারই বৈশিষ্ট্য। অবশ্য বর্তমানে এমন ধরনের যন্ত্র তৈরী করাও সম্ভব হয়েছে যা কোনো প্রাণশীল পরিচালক ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে এবং সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম। কিন্তু যেহেতু যন্ত্রটি প্রাণশীল সত্তা কর্তৃক তৈরী এবং প্রাণশীল সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত কর্মসূচী
( programme)-
এর বদৌলতেই সে তার সৃজনশীলতার প্রমাণ রাখতে পারছে সেহেতু তার এ সৃজনক্ষমতা মূলত
:
তার নির্মাতারই সৃজনক্ষমতার বহি
:প্রকাশ মাত্র।
বস্তুতঃ জীবন বা প্রাণশীলতা একটি পূর্ণতাবাচক গুণ নিষ্প্রাণ সত্তা যা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। এ কারণে কোন নিষ্প্রাণ সত্তার পক্ষে কোনো প্রাণশীল সত্তা সৃষ্টি করা তো দূরের কথা
,
প্রকৃত অর্থে অন্য কোন নিষ্প্রাণ সত্তা সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়। সুতরাং যিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন এবং বিশেষ করে কতক সৃষ্টিকে প্রাণময় করে সৃষ্টি করেছেন নিঃসন্দেহে তিনি প্রাণময় সত্তা।
অবশ্য কতক সৃষ্টিরও প্রাণ আছে
,
কিন্তু স্রষ্টার প্রাণময়তা ও সৃষ্টির প্রাণশীলতা পরস্পর তুলনীয় নয়
,
বরং উভয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তা হচ্ছে
,
প্রাণশীল সৃষ্টিসত্তার প্রাণের সূচনা ও সমাপ্তি আছে যা তার কালগত সীমাবদ্ধতার অনিবার্য দাবী। কিন্তু অপরিহার্য সত্তা যেহেতু কালগত সীমাবদ্ধতার উর্ধে সেহেতু তিনি চিরজীবী ও চিরস্থায়ী। তেমনি আমাদের অভিজ্ঞতার আওতাধীন প্রাণশীল সৃষ্টিপ্রজাতির ক্ষেত্রে আমরা যা দেখতে পাই তা হচ্ছে
,
এরূপ সৃষ্টি দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত এবং তার দেহ
,
প্রাণ
,
চেতনা ও ব্যক্তিসত্তা
(نفس
- self)-
এর অস্তিত্ব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও অভি
ন্ন নয়
,
বরং পরস্পর স্বতন্ত্র। বিশেষ করে তার দেহ তার সীমাবদ্ধতার তথা অপূর্ণতা ও দুর্বলতার পরিচায়ক। তেমনি প্রাণ
,
চেতনা ও ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য ও মাত্রাগত প্রাবল্য
-
দুর্বলতাও তার অপূর্ণতা ও দুর্বলতার পরিচায়ক।
অপরিহার্য সত্তার প্রাণময়তা অনিবার্যভাবেই এ ধরনের দুর্বলতার উর্ধে। অর্থাৎ একদিকে যেমন
তিনি দেহের অধিকারী হবার উর্ধে , তেমনি তাঁর প্রাণ ও চেতনা এবং তাঁর সত্তা বা ব্যক্তিসত্তা অভিন্ন । যেহেতু অপরিহার্য অস্তিত্বের সত্তা ও গুণাবলী একটি অভিন্ন , একক ও অবিভাজ্য অস্তিত্ব সেহেতু তাঁর অন্যতম গুণ প্রাণময়তাও তাঁর সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাই‘
তিনি জীবিত বা চিরজীবী’
না বলে‘
তিনিই জীবন’
বলাই শ্রেয়তর।
সাত : তিনি চিরজ্ঞানময়
অপরিহার্য সত্তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর চির জ্ঞানময়তা। অর্থাৎ জ্ঞান তাঁর সত্তার সাথে অভিন্ন ।
এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে যে , যখন তিনি কিছুই সৃষ্টি করেন নি তখন তিনি কিসের জ্ঞান রাখতেন ? অতএব , তিনি কীভাবে চির জ্ঞানময় হতে পারেন ?
এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে , অপরিহার্য সত্তার অস্তিত্বের স্বরূপ সৃষ্টিকুলের জন্যে এমন এক রহস্যলোক যাকে জানা তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে তিনি স্বয়ং স্বীয় সত্তার স্বরূপ ও গুণাবলী সম্বন্ধে সদা অবগত। অতএব , তিনি সদা জ্ঞানময়। যেহেতু তিনি স্বীয় সত্তার স্বরূপ ও গুণাবলী সম্পর্কে সদা জ্ঞানময় সেহেতু তিনি স্বীয় সৃষ্টিক্ষমতা এবং সম্ভাব্য সৃষ্টি ও সকল সম্ভব-সৃষ্টি সম্পর্কেও সদা অবগত। যেহেতু তিনি কালোর্ধ সত্তা সেহেতু তাঁর সৃষ্টিপরিকল্পনা ও সৃষ্টির সম্ভাব্য গতিবিধি তাঁর নিকট সদা বর্তমান , তাই তাঁর তা জানা না থাকার প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য তাঁর জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করা সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বলা বাহুল্য যে , তাঁর জ্ঞান ও তাঁর সত্তা অভিন্ন।
আট : তিনি সর্বশক্তিমান
শক্তি নিঃসন্দেহে একটি পূর্ণতাবাচক বৈশিষ্ট্য। অবশ্য শক্তি মানে শারীরিক বা বস্তুগত শক্তি গণ্য করলে তা শক্তি বটে তবে খুবই সীমিত ও দুর্বল শক্তি। শুধু তা-ই নয় , বরং বস্তুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ , হাতিয়ার ও অন্যান্য উপকরণের মধ্য দিয়ে প্রাণী প্রজাতির অবস্থাগত সীমিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাত্র যা অপরিহার্য সত্তার জন্যে দুর্বলতারূপে পরিগণিত হতে বাধ্য। বরং অপরিহার্য সত্তার শক্তি মানে কোনো কিছু করতে চাইলে বা বাস্তবায়ন করতে চাইলে তা করার সীমাহীন ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। কারণ , এরূপ সক্ষমতা না থাকলে জ্ঞান ও সৃজনশীলতা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে স্বীয় ইচ্ছার বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না। কিন্তু যেহেতু অপরিহার্য সত্তার যা ইচ্ছা তা-ই করার ক্ষমতা রয়েছে সেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান। তবে সৃজনশীলতা ও সর্বশক্তিমানতার মধ্যে পার্থক্য এই যে , সর্বশক্তিমানতা-গুণের অধিকারী সত্তা শুধু সৃষ্টি ও স্থিতিদান ক্ষমতারই অধিকারী নন , বরং ধ্বংসক্ষমতারও অধিকারী। তবে এ ক্ষেত্রেও তাঁর গুণ তাঁর সত্তার সাথে অভিন্ন ।
নয় : তিনি ইচ্ছাশক্তির অধিকারী
সৃজনী-সম্ভাবনা ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকাই সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের জন্যে যথেষ্ট নয় , বরং এ জন্য ইচ্ছাও থাকা চাই। যেহেতু সৃষ্টিলোক আছে সেহেতু নিঃসন্দেহে তা অপরিহার্য সত্তার ইচ্ছার প্রতিফলন। অতএব , তিনি যে ইচ্ছাশক্তির অধিকারী তা বলাই বাহুল্য । অবশ্য ইচ্ছাশক্তি এমন একটি গুণ যার মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার ভাবধারা নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ যিনি এ গুণের অধিকারী তিনি কোনো কিছু ইচ্ছা করতেও পারেন , না-ও করতে পারেন। এ-ও বলা বাহুল্য যে , অপরিহার্য সত্তার ক্ষেত্রে তাঁর সত্তা ও ইচ্ছাশক্তি অভিন্ন।
আমাদের এ আলোচনার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে , অপরিহার্য সত্তা হচ্ছেন অনাদি-অনন্ত (কালোর্ধ) , অসীম (স্থানোর্ধ) , নিরাকার , অবিভাজ্য ও অযৌগ একক সত্তা ; তিনি চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী , সদাজ্ঞানময় , সর্বশক্তিমান , সৃজনীসম্ভাবনাময় ও ইচ্ছাময়। অন্য কথায় , তিনিই জীবন , তিনিই স্থায়িত্ব , তিনিই জ্ঞান , তিনিই শক্তি , তিনিই সৃজনী সম্ভাবনা , তিনিই ইচ্ছাশক্তি যিনি স্থান-কালের উর্ধে নিরাকার পরমপ্রমুক্ত একক সত্তা।
 0%
0%
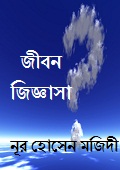 লেখক: নূর হোসেন মজিদী
লেখক: নূর হোসেন মজিদী