আরবী ভাষার প্রকাশক্ষমতার দৃষ্টান্ত
এবার আমরা আরবী ভাষার বাক্যগঠন বৈচিত্র্যের প্রতি দৃষ্টি দেবো যা কথক বা লেখককে তার বাঞ্ছিত ভাব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য সহকারে প্রকাশ করতে সহায়তা করে।
এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে , আরবী ভাষায় বাক্যের ভিতরে ভূমিকা ভেদে ক্রিয়া ও বিশেষ্য-বিশেষণের শেষ বর্ণের স্বরচিহ্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে বাক্যের তাৎপর্যে পরিবর্তন ঘটানো হয়। এ ক্ষেত্রে স্বরচিহ্নের ভূমিকাকে রাফ্‘
(رَفع
), নাছ্বব্ (نَصب
) , জায্ম্ (جَزم
) ও জার্র্ (جَرّ
) বলা হয়। এর মধ্যে প্রথম দু’
টি ক্রিয়া ও বিশেষ্য-বিশেষণ উভয় ক্ষেত্রে , তৃতীয়টি শুধু ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এবং চতুর্থটি শুধু বিশেষ্য-বিশেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
কর্তা ও কর্মভেদে এগুলোর বিবিধ ব্যবহার নিয়ে আলোচনা এখানে খুব বেশী যরূরী নয়। তবে জার্র্ (جَرّ
) সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ ছাড়া আরবী ভাষার প্রকাশক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণা হবে খুবই অসম্পূর্ণ ও অগভীর। কারণ জার্র্ (جَرّ
) হচ্ছে এমন একটি ব্যাকরণিক নিয়ম আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় যার ব্যবহার নেই। জার্র্-এর দ্বারা আরবী ভাষায় এমনভাবে সংক্ষেপে ভাব প্রকাশ করা হয় যে জন্য অন্যান্য ভাষায় বাক্যে অতিরিক্ত শব্দ যোগ করতে হয়। স্মর্তব্য , অভিন্ন ভাব দুর্বোধ্যতা ছাড়াই অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারা যে কোনো ভাষা বা বক্তা বা লেখকের কৃতিত্ব বা গৌরব বলে পরিগণিত হয়ে থাকে।
এখানে বাংলা ও ইংরেজী অর্থ সহ আরবী ভাষায় জার্র্-এর ব্যবহার সহ সংক্ষেপে ভাব প্রকাশের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো :
رَأيتُ زيداً
(
রাআইতু যাইদান্
) -
আমি যায়েদকে দেখলাম।
I saw Zayd.এ বাক্যে আরবীতে ২ শব্দ
,
বাংলায় ৩ শব্দ ও ইংরেজীতে ৩ শব্দ।
مَرَرتُ بِزَيدٍ
(
মারারতু বিযাইদিন্
) -
আমি যায়েদকে অতিক্রম করে গেলাম
;
আমি যায়েদের পাশ ঘেঁষে গেলাম।
I passed accross Zayd.জারর নিয়মের এ আরবী বাক্যে শব্দসংখ্যা ২টি
,
বাংলা বাক্যে ৫টি এবং ইংরেজী বাক্যে ৪টি।
এবারجحد
ক্রিয়াপদ যোগে গঠিত বাক্যের উদাহরণ :
لَم يَضرِب زَيدٌ عَلياً / لَمَّا يَضرِب زَيدٌ عَلياً
(
লাম্ ইয়াযরিব্ যাইদুন্
‘
আলীয়্যান্
/
লাম্মা ইয়াযরিব্ যাইদুন্
‘
আলীয়্যান্
) -
এ উভয় বাক্যেরই মানে হচ্ছে
:
যায়েদ
‘
এখনো
’
আলীকে মারে নি
- Still Zayd has not beaten Ali.এখানে লক্ষ্য করার বিষয়
,
উভয় আরবী বাক্যেই শব্দসংখ্যা ৪টি
,
বাংলায় ৫টি এবং ইংরেজীতে ৬টি।
কিন্তু উপরোক্ত আরবী বাক্যে বতিক্রমধর্মী যে তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা হচ্ছে , যায়েদ এখনো আলীকে মারে নি বটে , কিন্তু পরে মারতে পারে। তবে প্রথম বাক্যে এ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে যে , যায়েদ পরে আলীকে মারতেও পারে , না-ও মারতে পারে। অন্যদিকে দ্বিতীয় বাক্যে এ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে , যায়েদ পরে আলীকে মারবে - এ সম্ভাবনাই বেশী।
উপরোক্ত উভয় বাক্য কর্তা-কর্ম অগ্র-পশ্চাত করে এভাবেও বলা যেতে পারে :لَم يَضرِب عَلياً زَيدٌ / لَمَّا يَضرِب عَلياً زَيدٌ
(লাম্ ইয়াযরিব্‘
আলীআন্ যাইদুন্ / লাম্মা ইয়াযরিব্‘
আলীআন্ যাইদুন্) সে ক্ষেত্রে প্রথম বাক্যে এ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে যে , আলীকে এখনো যায়েদ মারে নি , তবে অন্য কেউ মেরে থাকতে পারে। আর দ্বিতীয় বাক্যে এ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে যে , আলীকে এখনো যায়েদ মারে নি , তবে পরে মারবে।
কিন্তু আরবী ভাষায় কর্তা-কর্ম অগ্র-পশ্চাত করেও ভাব প্রকাশে বিরাট পরিবর্তন করা হয়। যেমন :ضرب زَيدٌ عَلياً
(যারাবা যাইদুন্ আলীয়্যান্) না বলেضرب عَلياً زَيدٌ
(যারাবা আলীয়্যান্ যাইদুন্) বলা যেতে পারে। এ উভয় বাক্যের অর্থই“
যায়েদ আলীকে মেরেছে।”
কিন্তু পার্থক্য এখানে যে , প্রথম বাক্যে বক্তা কর্তার ওপর এবং দ্বিতীয় বাক্যে কর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছেন।
ব্যাকরণে আলাদাভাবে আলোচনা করা না হলেও বাংলা ভাষায় কোনো কোনো অঞ্চলের গ্রামের লোকদের মধ্যে তাৎপর্যের ভিন্নতা বুঝানোর জন্য এভাবে কর্তা-কর্ম অগ্র-পশ্চাত করার প্রচলন রয়েছে। যেমন : আমি ভাত খাই (সাধারণ তথ্য/ সংবাদ)। কিন্তু অনেক সময় বলা হয় : আমি খাই ভাত। এর মানে : আমি (প্রধান খাদ্য হিসেবে) অন্য কিছু বা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট খাবার খাই না। যেমন বলা হয় : আমি খাই ভাত , সে খায় রুটি। ইংরেজী ভাষায়ও এ ধরনের প্রচলন কিছুটা থাকলেও তা ব্যাকরণে স্বতন্ত্র গুরুত্ব না পাওয়ায় এর ব্যবহার খুবই কম।
অন্যদিকে আরবী ভাষায় সাধারণ বাক্য ক্রিয়াপদ দ্বারা শুরু করার নিয়ম থাকলেও কর্তা বা কর্ম দ্বারাও শুরু করা যয়। সে ক্ষেত্রে তাৎপর্যে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। যেমন : কোনো বাক্য ক্রিয়াপদ দ্বারা শুরু না করে কর্তা বা কর্ম দ্বারা শুরু করলে এবং ক্রিয়াপদটিকে তার পরে স্থান দিলে (যেমন :زَيدٌ ضرب عَلياً
বাعَلياً ضرب زَيدٌ
) তাৎপর্যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে , তা হচ্ছে , এ ক্ষেত্রে ক্রিয়ার তুলনায় কর্তা বা কর্মকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়।
তেমনি সামান্য ওপরেجحد
ক্রিয়াপদের উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত বাক্য দু’
টি কর্তা-কর্ম অগ্র-পশ্চাত করে এভাবেও বলা যেতে পারে :لَم يَضرِب عَلياً زَيدٌ / لَمَّا يَضرِب عَلياً زَيدٌ
(লাম্ ইয়াযরিব্‘
আলীয়্যান্ যাইদুন্/ লাম্মা ইয়াযরিব্‘
আলীয়্যান্ যাইদুন্) সে ক্ষেত্রে কর্তার তুলনায় কর্মের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়াও প্রথম বাক্যে এ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে যে , আলীকে এখনো যায়েদ মারে নি , তবে অন্য কেউ মেরে থাকতে পারে। আর দ্বিতীয় বাক্যে এ তাৎপর্যও নিহিত রয়েছে যে , আলীকে এখনো যায়েদ মারে নি , তবে পরে মারবে।
বাংলা ভাষায় এ ধরনের বাক্যরীতির সাধারণ প্রচলন না থাকলেও অন্ততঃ অংশতঃ হলেও এ ধরনের ভাব প্রকাশের জন্যে কর্তা
-
কর্ম অগ্র
-
পশ্চাত করে বাক্য গঠনের মতো প্রশস্ততা রয়েছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় অতিরিক্ত শব্দ যোগ না করে বা কর্তৃবাচ্য বাক্যকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত না করে তা প্রকাশের সুযোগ নেই। কারণ
,
যদি বলি যে
,
Still Ali has not beaten Zayd..তাহলে এর অর্থই উল্টে যাবে। আর যদি বলি যে
,
Still Ali has not been beaten by Zayd.তাহলে বাক্যটি শুধু কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যেই রূপান্তরিত হবে না
,
বরং তার শব্দসংখ্যা বেড়ে ৮টিতে দাঁড়াবে। এই একটি বিষয়ের ওপরে আরো দীর্ঘ আলোচনা করা যেতে পারে।
অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবী ভাষায় কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ভাষার সাথে আরবী ভাষায় এর ব্যবহারের পার্থক্য এখানে যে , আরবী ভাষায় কর্মবাচ্যের ব্যবহারের পিছনে সাধারণতঃ বক্তার উদ্দেশ্য থাকে কর্তাকে গুরুত্ব না দেয়া ; কেবল কর্মকে গুরুত্ব দেয়া। এ কারণে কর্মবাচ্যে সাধারণতঃ কর্তাকে আদৌ উল্লেখ করা হয় না। যেমন :ضُرِبَ علیٌّ
(যুরিবা‘
আলীয়্যুন্)- আলী প্রহৃত হলো (কার দ্বারা প্রহৃত হলো তা বলার জন্যে বক্তার কোনো আগ্রহ নেই)।
আরবী ভাষায় বাক্য গঠনের ধরনের আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক :
نَشَرَ زَيدٌ کِتاباً
(৩ শব্দ)। যায়েদ একটি বই প্রকাশ করলো (৫ শব্দ)। Zayd published a book (৪ শব্দ)।نُشِرَ کِتابٌ
(২ শব্দ)। একটি বই প্রকাশিত হলো (৪ শব্দ)। A book is published (৪ শব্দ)।الکِتابُ مَنشورٌ
(২ শব্দ)। বইটি প্রকাশিত (২ শব্দ)। The book is published (৪ শব্দ)।
আরবী বাক্য প্রকরণেحال
(হাাল্- অবস্থা) একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা অন্য ভাষায় অনুপস্থিত না থাকলেও পরিবর্তিত ভাবপ্রকাশের জন্য আরবী ভাষায় এর যে ব্যবহার তা অন্যান্য ভাষায় দেখা যায় না এবং এ কারণেই অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণে এটি আলাদা বিষয় হিসেবে আলোচিত হতে দেখা যায় না।
حال
মানে হচ্ছে একটি ক্রিয়া কী অবস্থায় সংঘটিত হচ্ছে। এ অবস্থাটা কর্তা , কর্ম উভয়েরই হতে পারে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক :
جاء رجول راكب
- (যাআ রাজূলুন্ রাাকেব্ - একজন অশ্বারোহী লোক এলো।) এখানেراكب
হচ্ছেصفت
- বিশেষণ।
جاء رجول راكباً
- (যাআ রাজূলুন্ রাাকেবান্ - অশ্বারূঢ় অবস্থার অধিকারী একজন লোক এলো।) এখানেراكباً
হচ্ছেصفت
- বিশেষণ।
جاء الرجول الراكب
- (যাআর্ রাজূলুর্ রাাকেব্ - অশ্বারোহী লোকটি এলো।) এখানেالراكب
হচ্ছেصفت
- বিশেষণ।
جاء الرجول راكباً
- (যাআর্ রাজূলু রাাকেবান্ - লোকটি অশ্বারূঢ় অবস্থায় এলো।) এখানেراكباً
হচ্ছেحال
- অবস্থা।
এ বিষয়ে আরো অনেক আলোচনা করা যেতে পারে। আরবী ভাষার বিস্ময়করভাবে ব্যাপক ও সুগভীর ভাব প্রকাশ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভের জন্য মোটামুটি এতোটুকুই যথেষ্ট বলে মনে হয়।
কোরআন মজীদের প্রকাশক্ষমতার মু‘
জিযাহ্
আরবী ভাষায় একটি বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে :خير الکلام ما قلَّ دلَّ
-“
(ভাষা-সাহিত্যের মানগত বিচারে) সর্বোত্তম কথা হলো যা সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যবহ।”
এটা যে কোনো ভাষায়ই সর্বজনস্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে যে কোনো ভাষায় রচনাপ্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। রচনা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সকল প্রতিযোগীই রচনা তৈরী করে। এ ক্ষেত্রে রচনা বিচারের বেলায় যে বিষয়গুলো দেখা হয় তা হচ্ছে : (১) বিষয়বস্তুর জন্য উপযোগী সর্বোত্তম শব্দাবলী নির্বাচন , (২) স্বল্পতম আয়তন , (৩) গভীরতম , ব্যাপকতম ও সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশ , (৪) গতিশীলতা তথা প্রাঞ্জলতা বজায় রেখে উন্নততম রচনাশৈলী ব্যবহার ও (৫) বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল আলঙ্কারিকতা।
কোরআন মজীদ তার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার বিচারে খুবই সংক্ষিপ্ত একটি গ্রন্থ , অথচ সীমাহীন তাৎপর্যের অধিকারী। কারণ , শব্দচয়ন , শব্দপ্রয়োগ ও বাকরীতির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে অবলম্বিত এক বিস্ময়কর রচনাকৌশলের আশ্রয়ে এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে‘
আক্বাএদ্ , আহ্কাম , আইন-কানুন , নৈতিকতা , দর্শন , ভবিষ্যদ্বাণী , উপদেশ , প্রার্থনা , ইতিহাস , রাজনীতি , অর্থনীতি , সমাজবিজ্ঞান , সমাজতত্ত্ব , মনস্তত্ত্ব , যুদ্ধ , সন্ধি , প্রকৃতিবিজ্ঞান , বস্তুবিজ্ঞান ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। অতএব , উপরোক্ত মানদণ্ডের বিচারে কোরআন মজীদ হচ্ছে পূর্ণতম ভাব প্রকাশের চরমতম নিদর্শন।
বস্তুতঃ আরবী ভাষা ভাব প্রকাশের বিচারে প্রায় সীমাহীন সম্ভাবনার অধিকারী। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে মানুষের ভাষা‘
সীমাহীন’
সম্ভাবনার অধিকারী হতে পারে না , কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে তা সীমাহীনই বটে। কারণ , কোনো মানুষের পক্ষেই আরবী ভাষার সকল সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করে একই কথা বা রচনায় সূক্ষ্মতম তাৎপর্য প্রকাশ , স্বল্পতম শব্দের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও উন্নততম সাহিত্যিক সৌন্দর্য - এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই বজায় রাখা সম্ভব নয় , বিশেষ করে বিষয়বস্তু যদি নিরেট সাহিত্য বা ইতিহাস না হয় , বরং জ্ঞানমূলক হয়।
সুদক্ষ বাগ্মী বক্তা বা সুসাহিত্যিক লেখক অনেক সময় অনেক পরিশ্রম করে উপযুক্ততম শব্দাবলী ও উন্নততম বাক্যরীতি ব্যবহার করে কথা বা রচনা পেশ করার পর , এ ভাষার এই প্রায় সীমাহীন প্রকাশ সম্ভাবনার কারণে দেখা যায় , পরবর্তীতে অন্যদের পর্যালোচনায় ধরা পড়ে যে , তা আরো উন্নত হতে পারতো। এমতাবস্থায় কোনো মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাপ্রশাখা নিয়ে কথা বলতে চাইলে - কোরআন মজীদে যেরূপ বলা হয়েছে - তার পক্ষে সংক্ষিপ্ততা , প্রাঞ্জলতা , সহজবোধ্যতা ও সাহিত্যিক আলঙ্কারিকতা বজায় রেখে কোনো গ্রন্থ রচনা করা পুরোপুরি অসম্ভব ব্যাপার। কারণ , মানবিক প্রতিভার পক্ষে এ ধরনের গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে একদিক বজায় রাখতে গেলে আরেক দিক বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কিন্তু কোরআন মজীদে এর সব দিকই বজায় রাখা হয়েছে। তাই কোরআন মজীদের চ্যালেঞ্জের সামনে সকল যুগের সকল অমুসলিম পণ্ডিত , ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক সম্মিলিতভাবে মোকাবিলার সুযোগ পেয়েও ব্যর্থতার কলঙ্ক বহন করতে বাধ্য হয়েছেন। সৃষ্টিলোকের ধ্বংস পর্যন্ত এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না।
 2%
2%
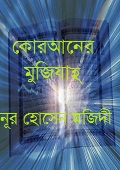 লেখক: নূর হোসেন মজিদী
লেখক: নূর হোসেন মজিদী





