কোরআন মজীদে সৃষ্টিরহস্য
কোরআন মজীদের বহু আয়াতে সৃষ্টি , প্রাকৃতিক জগত , নভোমণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্রাদি এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক বিধিবিধান সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। কোরআন মজীদ এমন এক যুগে এ সব সত্য ও রহস্য উন্মোচন করে দেয় যে যুগে একমাত্র খোদায়ী ওয়াহী ছাড়া এ সব সত্য ও রহস্যে উপনীত হবার মতো অন্য কোনো পন্থা কারো কাছেই বর্তমান ছিলো না।
অবশ্য সে যুগে গ্রীসে এবং আরো কোনো কোনো জায়গায় অত্যন্ত মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিজ্ঞানী ছিলেন যারা সৃষ্টিলোকের রহস্যাবলীর অংশবিশেষ সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং নিখুঁত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির কিছু কিছু উদ্ঘাটন করেছিলেন। কিন্তু তৎকালে আরব উপদ্বীপ এ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছিলো , বরং এ জাতীয় বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যন্ত ওয়াকেফহাল ছিলো না।
কিন্তু কোরআন মজীদ যে সব বৈজ্ঞানিক তথ্যের রহস্য উন্মোচন করেছে তার অংশবিশেষ এবং কোরআন মজীদের অধিকাংশ জ্ঞানমূলক বিষয়াদি - যা এখন থেকে চৌদ্দশ’
বছর আগে মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয় , তা এতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং এমনই নিখুঁত ও সূক্ষ্ম যে , তৎকালীন গ্রীস ও অন্যান্য দেশের জ্ঞানী-গুণী-বিজ্ঞানীগণ পর্যন্ত সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাবার পর এবং বিজ্ঞানের প্রসার ও অগ্রগতির সাথে সাথে এ সব রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে।
এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে , কোরআন মজীদ তার বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত সমূহে একদিকে যেমন হুবহু বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি তুলে ধরেছে , অন্যদিকে তৎকালীন মানুষের গ্রহণ ও অনুধাবন ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রেখে বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেছে। কিন্তু যে সব বিষয় তৎকালীন মানুষের অনুধাবনশক্তির বহির্ভূত ছিলো সে সব বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার পরিবর্তে মোটামুটিভাবে তুলে ধরাটাই যথোপযোগী ছিলো এবং মোটামুটি আভাসদানই যথেষ্ট ছিলো - যার পরিপূর্ণ উদ্ঘাটন ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরবর্তীতে বিভিন্ন শতাব্দীতে আগত বিজ্ঞানীদের ওপর ন্যস্ত করাই সঙ্গত ছিলো। কোরআন মজীদ তা-ই করেছে এবং পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি , উন্নততর ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ইত্যাদির ফলে কোরআন মজীদের উপস্থাপিত এ সব বৈজ্ঞানিক তথ্য বিস্তারিত রূপ লাভ করেছে।
এখন আমরা সৃষ্টিরহস্য , বিশ্বব্যবস্থাপনা ও সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াত সমূহের অংশবিশেষ তুলে ধরবো।
সুনির্দিষ্ট ও পরিমিত উপাদানে সৃষ্টি
কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :
)
و انبتنا فيها من کل شيء موزون(
“
আমি তাতে (ধরণীর বুকে) প্রতিটি জিনিসকে যথাযথ পরিমিতি ও ভারসাম্য সহকারে উদ্ভূত করিয়েছি।”
(সূরাহ্ আল্-হিজর : ১৯)
সৃষ্টিলোকের গুরুত্বপূর্ণ রহস্যাবলীর অন্যতম হচ্ছে যথাযথ পরিমিতি ও বিভিন্ন উপাদানের যথোপযোগী অনুপাতের যৌগিকতা সহকারে সব কিছুর সৃষ্টি। অত্র আয়াতে এরই আভাস দেয়া হয়েছে।
এখানে উল্লেখ্য যে , আলোচ্য আয়াতেরانبتنا
(উদ্গত করিয়েছি) দৃষ্টে মুফাসসিরগণ সাধারণতঃ এ আয়াতটিকে কেবল উদ্ভিদরাজি সম্পর্কিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আয়াতের কর্মপদکل شيء
(প্রতিটি জিনিস)-এর প্রতি দৃষ্টি দিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে , এ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় কেবল উদ্ভিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় , বরং প্রাণীকুলও এর আওতাভুক্ত যার প্রতিটি প্রজাতিকে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট উপাদানের সুনির্দিষ্ট অনুপাতের যৌগের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে , বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ক্রোমোজম ও জিনের যে পার্থক্য রয়েছে যান্ত্রিক অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় প্রাকৃতিক পন্থায় তাতে পরিবর্তন ঘটা ও এক প্রজাতির অন্য প্রজাতিতে পরিণত হওয়া সম্ভব নয় (কৃত্রিম হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সম্ভব হলে হতেও পারে) - যা বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিকে পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিয়েছে।
অবশ্য এতে সন্দেহ নেই যে , এ আয়াতের বক্তব্যের অন্যতম প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে উদ্ভিদরাজি। ধরণীর বুকে যে সব উদ্ভিদের উদ্গম ঘটে এবং উদ্ভিদ থেকে যে পুষ্পরাজি প্রস্ফূটিত হয় , তার প্রতিটিই সুনির্ধারিত উপাদানসমষ্টির সমন্বয়ে এবং বিশেষ পরিমিতির ভিত্তিতে সৃষ্ট। সম্প্রতি উদ্ভিদবিজ্ঞানেও প্রমাণিত হয়েছে যে , প্রতিটি ধরনের উদ্ভিদই সুনির্দিষ্ট অংশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত এবং তা সুনির্দিষ্ট উপাদানসমষ্টির পরিমিত ও নির্ধারিত অনুপাত সমন্বয়ে গঠিত যার ফলে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছোট-বড় হলেও তা ঐ উদ্ভিদের সংজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হয় না এবং অন্য উদ্ভিদে পরিণত হয় না।
কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ বা উপাদানের অনুপাতের ব্যবধান এমনই সূক্ষ্ম যে , এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এখনো তা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না।
বায়ুবাহিত পরাগায়ণ
খোদায়ী ওয়াহী যে সব বিস্ময়কর সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে আভাস দিয়েছে তার মধ্যে উদ্ভিদজগতের পরাগায়ণ অন্যতম। বায়ুর সাহায্যে অসংখ্য গাছপালা , লতাপাতা ও তৃণ-আগাছার পরাগায়ণ সম্পাদিত হয় এবং এর ফলেই উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি সম্ভব হয় ; ফুল , ফল ও নব নব উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।
এখানে লক্ষণীয় যে , যদিও পাখী ও বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গের দ্বারাও পরাগায়ণ ঘটে থাকে , কিন্তু তা সমগ্র উদ্ভিদ জগতের মোট পরাগায়ণের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আরো লক্ষণীয় যে , আল্লাহ্ তা‘
আলা সৃষ্টিপ্রকৃতিতে বায়ুবাহিত পরাগায়ণের ব্যবস্থা না রাখলে কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারের বর্তমান যুগে ফল-ফসল ফলানো সম্ভব হতো না অথবা কীটনাশক বর্জন করতে হতো , ফলে ফল-ফসল হলেও আনুপাতিক হারে কম হতো।
আল্লাহ্ তা‘
আলা এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে এরশাদ করেন :
)
و ارسلنا الرياح لواقح(
.
“
আর আমি পরাগায়ণ সম্পাদনকারী বায়ু পাঠিয়েছি।”
(সূরাহ্ আল্-হিজর : ২২)
যেহেতু অতীতে বায়ুর মাধ্যমে উদ্ভিদের পরাগায়ণের বিষয়টি মানুষের জানা ছিলো না , তাই প্রাচীন কালের মুফাসসিরগণ অভিধানেتلقيح
শব্দের (যার অভিন্ন মূল থেকেلواقح
শব্দটি উৎসারিত) অন্যতম অর্থحمل
(বহন) দৃষ্টে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন :“
আমি বায়ু পাঠিয়েছি যাতে তা মেঘমালাকে বহন করে।”
বা“
আমি বায়ু পাঠিয়েছি যা মেঘমালার মধ্যে বৃষ্টিকে বহন করে।”
এছাড়া অনেকে উক্ত আয়াতের অনুবাদ করেছেন :“
আমি গর্ভবতী বায়ু প্রেরণ করেছি।”
এবংالرياح لواقح
-এর অর্থ করেছেন‘
মেঘকে গর্ভে ধারণকারী বায়ু’
।
কিন্তু কোরআন মজীদের এ আয়াতের যে এরূপ অর্থ করা হয়েছে তা এর সঠিক অর্থ বলে মনে হয় না। কারণ , বহন করে নেয়া বলতে যা বুঝায় সে অর্থে বায়ু মেঘকে বহন করে না , বরং বায়ু মেঘকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত করে মাত্র।
এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে , পাখী বা পাতা , তুলা , ঘুড়ি ইত্যাদিকে বায়ু যেভাবে বহন করে মেঘকে সেভাবে বহন করে না। কারণ , মেঘ কোনো কঠিন পদার্থ নয় , বরং মেঘ হচ্ছে বিরাট ঘনক্ষেত্র জুড়ে জলীয় বাস্পের অবস্থান (যা বায়ুরই ন্যায় গ্যাসীয় অবস্থার অধিকারী এবং যাতে বায়ু মিশ্রিত থাকে) , তবে দূর থেকে দৃষ্টি প্রতিহত করায় তা দেখতে ঘন কঠিন পদার্থের মতো মনো হয়। কিন্তু কার্যতঃ বায়ু মেঘকে বহন করে না , বরং মেঘ নামে অভিহিত‘
বায়ু ও জলীয় বাস্পের সংমিশ্রণ’
বায়ুপ্রবাহের ফলে বায়ুরই অংশ হিসেবে গতিশীল ও স্থানান্তরিত হয়।
বস্তুতঃ এ আয়াত আমাদেরকে এক উঁচু স্তরের বৈজ্ঞানিক সত্যের দিকে পরিচালিত করে যা পর্যবেক্ষণে অতীতের জ্ঞানী-মনীষীগণ অক্ষম ছিলেন। এ সত্যটি হচ্ছে এই যে , প্রাণীজগতের ন্যায় গাছপালা-লতাপাতারও গর্ভসঞ্চারের অর্থাৎ নারী ও পুরুষ - এ দুই উপাদানের একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে ; এছাড়া ফল উৎপাদিত হয় না ও বংশবৃদ্ধি ঘটে না।
উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই গর্ভসঞ্চার বা দুই বিপরীত উপাদানের একত্রিত হওয়ার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই বায়ুর দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে , যেমন : ডালিম , কমলা , তুলা , বিভিন্ন ধরনের ডাল ইত্যাদি। এগুলোর পরাগায়ণ বায়ুর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে পুরুষ জাতীয় পরাগরেণু বায়ুর সাহায্যে ফুলের গর্ভকেশরে পৌঁছার ফলে ফুলের গর্ভসঞ্চার ঘটে এবং ফল উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট বৃক্ষের বা উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া এগিয়ে যায়।
জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি
কোরআন মজীদ তার বৈজ্ঞানিক সত্য উদঘাটনকারী আয়াত সমূহে অপর যে একটি সত্য তুলে ধরেছে তা হচ্ছে , জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি তথা প্রজাতিসমূহের নারী ও পুরুষ রূপে সৃষ্টি এবং তাদের উভয়ের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি কেবল প্রাণীকুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় , বরং উদ্ভিদও এ প্রাকৃতিক বিধানের আওতাভুক্ত। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :
)
و من کل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين(
“
আর প্রতিটি ফল-ফসলের ক্ষেত্রে তিনি দুইয়ে দুইয়ে জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন।”
(সূরাহ্ আর্-রা‘
দ্ : ৩)
)
سبحان الذی حلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون(.
“
পরম প্রমুক্ত সেই সত্তা যিনি ধরণীর বক্ষে যা কিছু উদ্গত হয় সে সব কিছুকে , স্বয়ং তাদেরকে (মানুষকে) এবং এমন অনেক কিছুকে যাদের সম্পর্কে তারা জ্ঞান রাখে না , সে সবের প্রতিটিকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।”
(সূরাহ্ ইয়া-সীন্ : ৩৬)
এখানে স্মর্তব্য যে , কোরআন নাযিলের যুগে উদ্ভিদকুলের মধ্যে মাত্র হাতে গণা কয়েকটি উদ্ভিদ প্রজাতি ব্যতীত - যেগুলোর পুরুষ গাছ ও নারী গাছ আলাদা - অন্যান্য উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে নারী ও পুরুষ উপাদানের বিষয়টি কারো জানা ছিলো না যা আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে বর্তমানে এটা সকলেরই জানা যে , যে সব উদ্ভিদের স্বতন্ত্র নারী গাছ ও পুরুষ গাছ নেই সে সব উদ্ভিদে হয় একই গাছে নারী ফুল ও পুরুষ ফুল - দুই ধরনের ফুল ধরে , অথবা একই ফুলে গর্ভকেশর ও পুংকেশর হয়ে থাকে। এমনকি ডুমুরে - দৃশ্যতঃ যা ফুল ছাড়া সরাসরি ফল হিসেবেই বের হয় , তাতেও গর্ভকেশর ও পুংকেশর আছে বলে অতি সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হয়েছে। ডুমুর যখন বের হয় প্রকৃত পক্ষে তা-ই ফুল এবং এর পশ্চাদদেশে গর্ভকেশর ও পুংকেশর থাকে ; এক ধরনের পিঁপড়ার দ্বারা এর পরাগায়ণ হয় এবং এর ফলে তা ফলে পরিণত হয় ; এ পরাগায়ণ না ঘটলে বের হওয়া ডুমুর ঝরে পড়ে যায়।
পৃথিবীর গতিশীলতা
কোরআন মজীদ তার বৈজ্ঞানিক সত্য উপস্থাপনকারী আয়াত সমূহে অপর যে একটি সত্য তুলে ধরেছে তা হচ্ছে পৃথিবীর গতিশীলতা। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :
)
الذی جعل لکم الارض مهداً(
.
“
(তিনিই আল্লাহ্) যিনি এ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য দোলনা বানিয়ে দিয়েছেন।”
(সূরাহ্ ত্বা-হা : ৫৩)
লক্ষ্য করার বিষয় , এ আয়াতে কীভাবে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকরূপে পৃথিবীর গতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা কোরআন নাযিলের বহু শতাব্দী পরে মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। এ আয়াতে পৃথিবীকে শিশুর দোলনার সাথে তুলনা করা হয়েছে যার শান্ত ও সুশৃঙ্খল গতিশীলতার ফলে দুগ্ধপোষ্য শিশু আরাম অনুভব করে ঘুমিয়ে পড়ে।
পৃথিবীও মানুষের জন্য দোলনাস্বরূপ। কারণ , এর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবী তার অধিবাসীদের আরামের জায়গা হয়েছে। ঠিক যেভাবে দোলনার গতির ফলে শিশু আরাম ও বিশ্রাম লাভ করে ঠিক সেভাবেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ফলে এ পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য পরিবৃদ্ধি ও আরাম-আয়েশের জায়গায় পরিণত হয়েছে।
এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে , কোরআন মজীদে যে সব ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে একই বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা ভিন্ন ভিন্ন উপমা ব্যবহার করা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। এরূপ ক্ষেত্রে দু’
টি শব্দের বা দু’
টি উপমার মধ্যে যদি তাৎপর্যে আংশিক মিল ও আংশিক অমিল থাকে - যুক্তিবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকেعموم و خصوص من بعض
(অংশতঃ সাধারণ ও বিশেষ) বলা হয় - সে ক্ষেত্রে একটি শব্দের বা উপমার পরিবর্তে অন্য শব্দ বা উপমা ব্যবহারের উদ্দেশ্য হয় তাৎপর্যের‘
বিশেষ’
অংশটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।
এ কারণেই কোরআন মজীদে কোথাও বলা হয়েছে যে , আল্লাহ্ পৃথিবীকেبساط
(নে‘
আমতপূর্ণ বিস্তৃত জায়গা) বানিয়ে দিয়েছেন (সূরাহ্ আন্-নূহ্ : ১৯) , কোথাও বলা হয়েছে ,قرار
(বাসোপযোগী) বানিয়ে দিয়েছেন (সূরাহ্ আল্-মু’
মিন : ৬৪) , কোথাও বলা হয়েছে ,فراش
(বিছানা) বানিয়ে দিয়েছেন (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ : ২২) , আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছেمهد
(দোলনা)। এ থেকে সুস্পষ্ট যে , এখানে পৃথিবীর গতিশীলতা বুঝানোই লক্ষ্য।
যেহেতু পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি না থাকলে তার এক পিঠ হতো সর্বাবস্থায় আক্ষরিক অর্থেই আগুনের মতো গরম এবং এক পিঠ হতো অনেক বেশী ঠাণ্ডা ; কেবল দুই অংশের মধ্যবর্তী একটি বলয়রূপ অংশে তাপমাত্রা কম হতো এবং তাতেও ঋতুবৈচিত্র হতো না। শুধু তা-ই নয় , সব সময়ই দ্রুত গতিতে গরম অংশের বায়ু উর্ধাকাশে উঠে ঠাণ্ডা অংশের দিকে ছুটে যেতো এবং ঠাণ্ডা অংশের হাওয়া ভূমি ছুঁয়ে গরম অংশের দিকে ছুটে যেতো। ফলে পৃথিবী বাসোপযোগী হতো না। কেবল আহ্নিক গতির কারণেই তা বাসোপযোগী হয়েছে এবং বার্ষিক গতির ফলে শুধু ঋতুবৈচিত্রই সৃষ্টি হয় নি , বরং গোটা পৃথিবীই বাসোপযোগী হয়েছে। আর এখানে পৃথিবীর গতিশীলতা বুঝানো উদ্দেশ্য না হয়ে আরামদায়ক বাসস্থান বুঝানো উদ্দেশ্য হলেفراش
(বিছানা) বলাই যথেষ্ট হতো।
উপরোক্ত আয়াতে (সূরাহ্ ত্বা-হা : ৫৩) পৃথিবীর গতি সম্পর্কে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয় নি। কারণ , এ আয়াত এমন এক যুগে নাযিল্ হয়েছে যে যুগের সমস্ত মানুষের , এমনকি জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞানীগণের পর্যন্ত ধারণা ছিলো যে , পৃথিবী স্থির ও গতিহীন। সে যুগের সকল মানুষের নিকটই পৃথিবীর স্থিরতা একটি অকাট্য বিষয়রূপে পরিগণিত ছিলো।
হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)-এর হিজরতের দশ শতাব্দী পরে নক্ষত্র বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এ দীর্ঘ বদ্ধমূল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং পৃথিবীর দু’
টি গতি - আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি প্রমাণ করেন ও তা ঘোষণা করেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই এ ঘোষণার জন্য তিনি অপমান , লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হন। শুধু তা-ই নয় , এ অপরাধে (!) তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এতো বড় বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এহেন পরিস্থিতির কারণেই - খৃস্টধর্মের যাজকদের দ্বারা ধর্মীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও অপরিহার্য রূপে পরিগণিত গতানুগতিক ধারণা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারাদির সাথে সাংঘর্ষিক হবার কারণে - ইউরোপের জ্ঞানী , মনীষী , বিজ্ঞানী ও আবিষ্কর্তাগণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও জনকল্যাণমূলক অন্য বহু আবিষ্কার-উদ্ভাবনকে প্রাণের ভয়ে গোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।
পশ্চিম গোলার্ধের ভূখণ্ড
কোরআন মজীদ দীর্ঘ চৌদ্দশ’
বছর পূর্বে যার রহস্য উন্মোচন করেছে এবং মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে যা আবিষ্কৃত হয়েছে এরূপ একটি বিষয় হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের যে পার্শ্বে তৎকালীন বিশ্বের মানুষ অবস্থান করতো - অর্থাৎ এশিয়া , ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ নিয়ে গঠিত মহাভূখণ্ড - তার অপর পার্শ্বে আরেকটি মহাভূখণ্ডের অবস্থান। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদ এরশাদ করেছে :
)
رب المشرقين و رب المغربين(
“
তিনি (আল্লাহ্ তা‘
আলা) দুই মাশরেক্ব্ ও দুই মাগ্বরেবের প্রভু।”
(সূরাহ্ আর্-রাহমাান্ : ১৭)
এ আয়াতটি দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী যাবত সমস্ত মুফাসসিরে কোরআনকে মশগূল রেখেছিলো ; এ আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁরা স্থিরনিশ্চিত ও অভিন্ন মতে উপনীত হতে পারছিলেন না। মুফাসসিরগণের অনেকে বলেছেন , এ আয়াতে বর্ণিত‘
দুই মাশরেক্ব্’
(مشرقين
) ও‘
দুই মাগ্বরে’
(مغربين
)-এর তাৎপর্য হচ্ছে সূর্যের মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেব্ (পূর্ব ও পশ্চিম বা উদয় ও অস্তের জায়গা) এবং চন্দ্রের মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেব্ (পূর্ব ও পশ্চিম বা উদয় ও অস্তের জায়গা)। আবার অনেকে বলেছেন , দুই মাশরেক্ব্ ও দুই মাগ্বরেবের মানে হচ্ছে সূর্যের শীতকালীন উদয়াস্তের জায়গা ও গ্রীস্মকালীন উদয়াস্তের জায়গা। কিন্তু এ সব অভিমত যে ঠিক নয় তা সুস্পষ্ট। কারণ , সাধারণভাবে আমরা যখন উদয়াস্তের‘
দিক’
কে পূর্ব ও পশ্চিম বলি তখন পূর্ব ও পশ্চিমের ধারণায় পূর্ব ও পশ্চিমের দিগন্তের দুই সুপ্রশস্ত অংশকে বুঝায় এবং সূর্য ও চন্দ্রের উদয়াস্ত এর মধ্যেই ঘটে থাকে। অন্যদিকে আমরা যদি উদয়াস্তের‘
সুনির্দিষ্ট স্থান’
কে ( Spot) বুঝাতে চাই তো সে ক্ষেত্রে উদায়াস্তের স্থানের সংখ্যা অনেক , কারণ , প্রতিদিনই সূর্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদয় হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্ত যায় ; চন্দ্রের ক্ষেত্রেও তা-ই। এভাবে উদয়-দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সূর্যের অন্ততঃ ১৮২টি বা ১৮৩টি উদয়স্থান আছে এবং অনুরূপভাবে অন্ততঃ সমসংখ্যক অস্তগমনস্থান আছে ; চন্দ্রের ক্ষেত্রেও তা-ই।
সুতরাং উক্ত আয়াতের শাব্দিক তাৎপর্য থেকে যে ধারণা পাওয়া যায় আয়াতটিতে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতটি তৎকালে জ্ঞাত মহাভূখণ্ড ছাড়াও অপর একটি মহাভূখণ্ডের অস্তিত্ব সম্পর্কে আভাস দিচ্ছে - যা এ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে অবস্থিত। ফলে পৃথিবীর এ পৃষ্ঠে অবস্থিত আমাদের মহাভূখণ্ডে যখন সূর্যোদয় তখন সেখানে সূর্যাস্ত এবং এখানে যখন সূর্যাস্ত তখন সেখানে সূর্যোদয়। ফলে এ পৃথিবীতে দু’
টি মাশরেক্ব্ (সূর্যোদয়ের দিক) ও দু’
টি মাগ্বরেব্ (সূর্যাস্তের দিক) দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।
কোরআন মজীদের আরো একটি আয়াতে এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। তা হচ্ছে :
)
يا ليت بينی و بينک بعد المشرقين. فبئس القرين(
.
“
হায়! তোমার ও আমার মাঝে যদি দুই মাশরেক্বের ব্যবধান থাকতো! কেমন নিকৃষ্ট সঙ্গীই না তুমি!”
(সূরাহ্ আয্-যুখরূফ্ : ৩৮)
এ আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে , এ ধরণীবক্ষে দুই মাশরেক্বের মধ্যকার ব্যবধান হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যবধান। অতএব , ইতিপূর্বে উল্লিখিত আয়াতে দুই মাশরেক্ব্ মানে চন্দ্র ও সূর্যের উদয়স্থল এবং দুই মাগ্বরেব্ মানে চন্দ্র ও সূর্যের অস্তগমনস্থল হতে পারে না , তেমনি তা গ্রীস্মকালের উদয়স্থল ও শীতকালের উদয়স্থলও হতে পারে না ; দ্বিতীয়োক্ত আয়াতের লক্ষ্যের সাথে এ দু’
টি তাৎপর্যের একটিও খাপ খায় না।
সুতরাং এখানে দুই মাশরেক্ব্ ও দুই মাগ্বরেব্ মানে দুই মহাভূখণ্ডের মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেব্ বলে মেনে নিতে আমরা বাধ্য। কারণ , আমাদের এ মহাভূখণ্ডের মাশরেক্ব্ (সূর্যোদয়স্থল - পূর্ব দিগন্তের প্রশস্ত স্থান) ও পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠস্থ মহাভূখণ্ডের মাশরেক্বের ব্যবধান এ ভূপৃষ্ঠে দীর্ঘতম ব্যবধান। আর অপর মহাভূখণ্ডের মাশরেক্ব্ মানে আমাদের মাগ্বরেব্। অতএব , এ আয়াত থেকে অপর একটি মহাভূখণ্ডের অস্তিত্বের আভাস-এর তাৎপর্য গ্রহণ করলেই সঠিক অর্থ গ্রহণ করা হবে।
অতএব , যে সব আয়াতে‘
মাশরেক্ব্’
ও‘
মাগ্বরেব্’
শব্দদ্বয় একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে , সে সব আয়াতে শব্দ দু’
টি এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে , যেমন :لله المشرق و المغرب
(পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকই আল্লাহর।) - যেখানে সাধারণ অর্থে পূর্ব দিক ও পশ্চিম দিক বুঝানো হয়েছে। আর যে সব আয়াতে শব্দ দু’
টি দ্বিবচনে ব্যবহৃত হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে তা ভিন্নতর এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ; এ সব ক্ষেত্রে অপর এক মহাভূখণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর যে সব ক্ষেত্রে শব্দ দু’
টি বহু বচনে ব্যবহৃত হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে তা তৃতীয় এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে , তা হচ্ছে , বিভিন্ন দেশ , শহর ও ভূখণ্ডের অবস্থানভেদের কারণে প্রতিটি জায়গার যে মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেব্ রয়েছে তা-ই। এই শেষোক্ত প্রসঙ্গে আমরা এর পরেই আলোচনা করছি।
এখানে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের অনুধাবনের সুবিধার্থে উল্লেখ করা ভালো মনে করছি যে , আরবী ভাষায় ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার স্থান ও কালের বেশ কয়েকটি শব্দ-প্যাটার্ন (وزن
) আছে , এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাশরিক্ব্ , মাগ্বরিব্ , মাসজিদ্ , মাজলিস্ ইত্যাদি। সে হিসেবে‘
মাশরিক্ব্’
ও মাগ্বরিব্’
(যার পরিবর্তিত বাংলা উচ্চারণ‘
মাশরেক্ব্’
ও‘
মাগ্বরেব্’
)-এর মানে হচ্ছে যথাক্রমে :‘
সূর্যোদয়ের স্থান/ সময়’
ও‘
সূর্যাস্তের স্থান/ সময়’
।
তবে আরবী ভাষায় প্রচলিত অর্থে (প্রত্যেক ভাষায়ই যেভাবে কিছু শব্দ নতুন অর্থ পরিগ্রহণ করে থাকে ও সে অর্থে প্রচলিত হয়ে থাকে) মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেব্-এর আরো দু’
টি করে প্রচলিত অর্থ রয়েছে। তা হচ্ছে ,‘
মাশরেক্ব্’
মানে পূর্ব দিক (সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে সূর্যোদয় সোজা পূর্ব দিকে না হলেও) ও প্রাচ্য ভূখণ্ড এবং‘
মাগ্বরেব’
মানে পশ্চিম দিক (সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে সূর্যাস্ত সোজা পশ্চিম দিকে না হলেও) ও পশ্চিমা ভূখণ্ড। এ কারণেই মরক্কোকে‘
মাগ্বরেব্’
নামকরণ করা হয় আরব উপদ্বীপ থেকে পশ্চিমের দেশ হিসেবে। তেমনি একই কারণে , পশ্চিম গোলার্ধ আবিষ্কৃত হওয়ার পর তাকেও আরবী ভাষায়‘
মাগ্বরেব্’
(পাশ্চাত্য) বলা হয়।
এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত আয়াত থেকে‘
মাশরেক্ব্ ও‘
মাগ্বরেব্’
-এর মানে যথাক্রমে‘
প্রাচ্য’
ও‘
পাশ্চাত্য’
গ্রহণ করা হলে‘
মাশরেক্বাইন্’
ও‘
মাগ্বরেবাইন্’
-এর মানে দাঁড়ায়‘
দুই প্রাচ্য’
ও‘
দুই পাশ্চাত্য’
। সে ক্ষেত্রে‘
দুই প্রাচ্য’
মানে দাঁড়ায় প্রাচ্য মহাভূখণ্ডের প্রাকৃতিকভাবে বিভক্ত দুই ভূখণ্ড অর্থাৎ‘
এশিয়া-ইউরোপ’
ও‘
আফ্রিকা’
এবং‘
দুই পাশ্চাত্য’
মানে দাঁড়ায় পাশ্চাত্য মহাভূখণ্ডের প্রাকৃতিকভাবে বিভক্ত দুই ভূখণ্ড অর্থাৎ‘
উত্তর আমেরিকা’
ও‘
দক্ষিণ আমেরিকা’
। তবে দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে‘
মাশরেক্বাইন্’
মানে‘
দুই মহাভূখণ্ডের সূর্যোদয়ের দিক’
এবং‘
মাগ্বরেবাইন্’
মানে দুই মহাভূখণ্ডের সূর্যাস্তের দিক।
পৃথিবীর গোলাকৃতি
কোরআন মজীদ প্রাকৃতিক জগতের অপর যে একটি রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করেছে তা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের বক্রতা তথা গোলাকৃতি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘
আলা এরশাদ করেন :
)
و اورثنا القوم الذين کانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها(
.
“
দুর্বল হয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে আমি ধরণীর মাশরেক্ব্ সমূহের ও মাগ্বরেব্ সমূহের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি।”
(সূরাহ্ আল্-আ‘
রাাফ্ : ১৩৭)
)
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ(
.
“
তিনি (আল্লাহ্ তা‘
আলা) আসমান সমূহ ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রভু , আর তিনি মাশরেক্ব্ সমূহেরও প্রভু।”
(সূরাহ্ আছ্-ছ্বাফ্ফাত্ : ৫)
)
فلا اقسم برب المشارق و المغارب و انا لقادرون(
“
(তারা যা বলছে) তা কক্ষনোই নয় , শপথ মাশরেক্ব্ সমূহের ও মাগ্বরেব্ সমূহের প্রভুর , আমি অবশ্যই সক্ষম।”
(সূরাহ্ আল্-মা‘
আারেজ্ : ৪০)
উল্লিখিত আয়াত সমূহ একদিকে যেমন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ও স্থান সমূহের বহুত্বের কথা প্রকাশ করছে , তেমনি ভূপৃষ্ঠের বক্রতার প্রতিও ইঙ্গিত করছে। কারণ , কেবল ভূপৃষ্ঠের বক্র অবস্থাতেই এটা সম্ভব যে , ভূপৃষ্ঠের কোনো এক অংশে যখন সূর্যোদয় তখন অপর এক অংশে সূর্যাস্ত এবং এভাবেই বহু মাশরেক্ব্ ও বহু মাগ্বরেব্ অস্তিত্ব লাভ করে এবং এতে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় সংঘটিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ বক্র না হলে বহু মাগ্বরেব্ ও বহু মাশরেক্ব্-এর কোনো মানে হয় না।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে , ইমাম ক্বুরত্বুুবী এবং আরো অনেক মুফাসসির‘
মাশরেক্ব্ সমূহ’
ও‘
মাগ্বরেব্ সমূহ’
-এর অর্থ করেছেন : বছরের বিভিন্ন দিনের মধ্যকার পার্থক্য জনিত কারণে মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেবের (সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান ও কালের) পার্থক্য। এভাবে তাঁরা মাশরেক্ব্ ও মাগ্বরেবের বহুত্ব নির্দেশ করেছেন।
কিন্তু এ ব্যাখ্যা উক্ত আয়াতের বাহ্যিক তাৎপর্যের সাথে সঙ্গতিশীল নয় , অতএব , তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ , বছরের বিভিন্ন দিনের ক্ষেত্রে যে কোনো পর পর দুই দিনে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান ও সময়ের ব্যবধান এতো স্থূল নয় যে , তা সাধারণ মানুষের কাছে ধরা পড়বে - যা আল্লাহ্ তা‘
আলার শপথের বিষয়ে পরিণত হতে পারে। অতএব , এ ক্ষেত্রে‘
মাশরেক্ব্ সমূহ’
ও‘
মাগ্বরেব্ সমূহ’
-এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর গতি ও ভূপৃষ্ঠের বক্রতাজনিত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দ্রাঘিমাংশে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান ও কাল সমূহ - পরস্পর থেকে যার ব্যবধান সব সময়ই অত্যন্ত সুস্পষ্ট।
অতএব , এটা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে , এ জাতীয় আয়াত সমূহে ভূপৃষ্ঠের বক্রতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং হযরত রাসূলে আকরাম্ (ছ্বাঃ)-এর পবিত্র আহলে বাইতের (‘
আঃ) ধারাবাহিকতায় আগত মা‘
ছ্বূম্ ইমামগণের বিভিন্ন বক্তৃতা-ভাষণ , হাদীছ ও দো‘
আয় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ সব থেকে এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি :
(১) হযরত ইমাম জা‘
ফর ছাদেক (‘
আ্ঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে , তিনি এরশাদ করেছেন :“
একবার আমার এক সফরে এক ব্যক্তি আমার সাথে সফর করে। সে সব সময়ই রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হবার পর মাগ্বরেবের নামায আদায় করতো এবং ছ্বুবহে ছ্বাদেক্ব্ হবার বেশ পূর্বে শেষ রাতের আঁধারে ফজরের নামায আদায় করতো। কিন্তু আমি তার বিপরীতে অর্থাৎ মাগ্বরেবের নামায সূর্যোস্তের পর পরই এবং ফজরের নামায ছ্বুব্হে ছ্বাদেক্ব্ হবার পর আদায় করতাম। লোকটি আমাকে বললো :“
আপনিও আমার ন্যায় আমল করুন , কারণ , আমাদের দ্রাঘিমারেখায় যখন সূর্যোদয় ঘটে তার বেশ আগেই অন্যদের দ্রাঘিমারেখায় সূর্যোদয় হয়ে থাকে , অন্যদিকে আমাদের দ্রাঘিমারেখায় যখন সূর্য অস্ত যায় তখনো অন্যদের দ্রাঘিমারেখায় সূর্য আকাশে বিদ্যমান।”
আমি তাকে বললাম যে , সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত প্রশ্নে প্রত্যেক জাতি ও জনগোষ্ঠীকেই স্ব স্ব দ্রাঘিমা রেখার অনুসরণ করতে হবে এবং তদনুসারেই স্ব স্ব দ্বীনী কর্তব্য পালন করতে হবে , অন্যদের দ্রাঘিমারেখা অনুসারে নয়।”
(وسائل الشيعة- ١/٢٣٧- باب ١١٦
.)
(২) হযরত ইমাম জা‘
ফর ছাদেক (রহ্ঃ) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে , তিনি এরশাদ করেছেন :“
তোমাকে স্বীয় দ্রাঘিমার (বা দিগন্তের) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অনুসরণ করতে হবে।”
(৩) হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (‘
আঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে , তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্ তা‘
আলার দরবারে যে দো‘
আ করতেন তাতে বলতেন :“
আল্লাহ্ তা‘
আলা দিন ও রাত্রির প্রতিটির জন্যই সীমারেখা ও পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার প্রত্যেকটিকে তিনি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন এমন অবস্থায় যে , অপরটিকেও এটির মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন।”
(صحيفة سجادية
)
হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (‘
আঃ) তাঁর এ চমৎকার সাহিত্যসমৃদ্ধ উক্তির মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের বক্রতাকে - যার কারণে দিন রাতের মধ্যে ও রাত দিনের মধ্যে প্রবেশ করছে - তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়টি তৎকালীন মানুষের অনুধাবনক্ষমতার উর্ধে ছিলো বিধায় তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম আভাসের মাধ্যমে ও সমুন্নত সাহিত্যমণ্ডিত ভাষায় এমনভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন যে , প্রকৃত সত্যটিও তুলে ধরা হলো অথচ ঐ যুগের মানুষের দৃষ্টিতে বিষয়টি সামঞ্জস্যহীন বলে পরিগণিত হয় নি।
কেউ হয়তো ধারণা করতে পারে যে , এ কথার পিছনে হযরত ইমামের (‘
আঃ) উদ্দেশ্য ছিলো এটা বুঝানো যে , দিন ও রাত ছোট-বড় হয় ; পৃথিবীর বক্রতা বা গোলাকার অবস্থা বুঝানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ , হযরত ইমাম যদি দিন-রাত্রির ছোট-বড় হওয়ার বিষয়টি বুঝাতে চাইতেন - যা সবাইই লক্ষ্য করে থাকে , তাহলে তাঁর এতদসংক্রান্ত বক্তব্যের প্রথম অংশটিই যথেষ্ট ছিলো যেখানে তিনি বলেছেন :“
আল্লাহ্ তা‘
আলা দিন ও রাত্রির প্রতিটির জন্যই সীমারেখা ও পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার প্রত্যেকটিকে তিনি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন।”
এরপর আর একথা বলার প্রয়োজন হতো না যে ,“
এমন অবস্থায় যে , অপরটিকেও এটির মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন।”
কারণ , বাহ্যতঃ দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যটিরই পুনরাবৃত্তি। তাই আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে , দ্বিতীয় বাক্যটি - আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী যা প্রথম বাক্যের ক্রিয়াটি কী অবস্থায় সংঘটিত হচ্ছে তা-ই বুঝাচ্ছে - উল্লেখের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে , দিন যখন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে ঠিক সে সময়ই রাত দিনের মধ্যে প্রবেশ করে।
অতএব , হযরত ইমামের (‘
আঃ) দো‘
আর অন্তর্ভুক্ত এ বাক্যটি থেকে ভূপৃষ্ঠের বক্রতা তথা গোলাকার অবস্থা প্রমাণিত হয়। কারণ , কেবল ভূপৃষ্ঠের গোলাকার অবস্থায়ই একই সময় দিন ও রাত্রির পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর। অর্থাৎ পৃথিবীর এক পৃষ্ঠে যখন দিন , অপর পৃষ্ঠে তখন রাত্রি ; ফলতঃ এক পৃষ্ঠে যখন দিনের আলো রাতের আঁধারে হারিয়ে যাচ্ছে , ঠিক তখনই অপর পৃষ্ঠে রাতের আঁধার দিনের আলোয় দূরীভূত হচ্ছে। হযরত ইমামের (‘
আঃ) বক্তব্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যথায় তাঁর বক্তব্যের শেষোক্ত বাক্যটি বাহুল্য হয়ে দাঁড়ায়। আর হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ্ঃ)-এর মতো ব্যক্তির বক্তব্যে বাহুল্য থাকার প্রশ্নই ওঠে না।
কোরআন মজীদের অপর এক আয়াতেও পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার আভাস দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :تولج الليل فی النهار و توليج النهار فی الليل
-“
তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান ও দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান।”
(সূরাহ্ আালে‘
ইমরাান্ : ২৭) বস্তুতঃ এখানেليل
(রাত্রি) ওنهار
(দিন) উভয়ের পূর্বেال
যোগ হওয়ায় বিভিন্ন দিন-রাত্রি না বুঝিয়ে স্বয়ং‘
দিন’
ও‘
রাত্রি’
নামক ধারণা দু’
টিকে বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘
আলা সর্বাবস্থায় দিনকে রাতের মধ্যে ও রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান। এর মানে হচ্ছে একটিই দিন ও একটিই রাত পরস্পরের পিছনে এগিয়ে যাচ্ছে এবং পরস্পরকে গ্রাস করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এটা কেবল তখনি সম্ভব হয় যখন তা একটি গোলাকার বস্তুর ওপর দিয়ে একে অপরের পিছনে এগিয়ে যেতে থাকে।
এ হচ্ছে কোরআন মজীদের অলৌকিকতার বিভিন্ন দিকের অংশবিশেষ মাত্র। গ্রন্থের আয়তন সীমিত রাখার লক্ষ্যে আমরা শুধু এতোটুকু উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করছি। কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত আলোচনাই কোরআন মজীদের খোদায়ী ওয়াহী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট । এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে , কোরআন মজীদ আল্লাহ্ তা‘
আলার পক্ষ থেকে রচিত হয়েছে এবং কোনো অসাধারণ মানবিক প্রতিভার পক্ষেই এরূপ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। এ গ্রন্থ মানবিক প্রতিভার উর্ধে।
 2%
2%
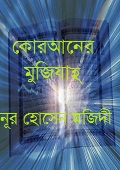 লেখক: নূর হোসেন মজিদী
লেখক: নূর হোসেন মজিদী





