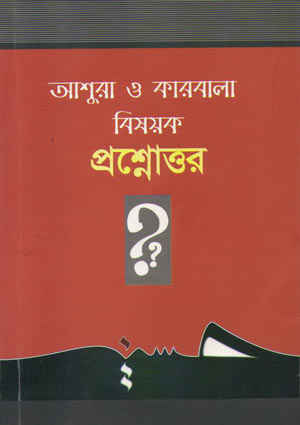ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আন্দোলন কি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ছিল ?
25 নং প্রশ্ন : ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আন্দোলন কি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ছিল ? ইসলামের দৃষ্টিতে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা জায়েয ?
উত্তর : আশুরার দিন ওমর ইবনে সাদের সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকে ওমর ইবনে হাজ্জাজ নামে এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলে :
یا اهل الکوفه ! الزموا طاعتکم و جماعتکم و لا ترتابوا فی قتل من مرق من الدین و خالف الامام
‘
হে কুফাবাসী! (আমার) আনুগত্যের ক্ষেত্রে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ থাক এবং যারা ধর্ম থেকে বেরিয়ে গেছে ও তোমাদের নেতার বিরোধিতা করেছে তাদের সাথে যুদ্ধে কোনরূপ সন্দেহে পতিত হয়ো না ।’
এ বক্তব্যে ইমাম হোসাইন (আ.)-কে মুসলমানদের ইমামের সাথে বাইআত ভঙ্গকারী এবং একজন বিদ্রোহী বলে পরিচিত করানো হয়েছে । দুঃখজনকভাবে এ ধরনের চিন্তাধারা এখনো বিদ্যমান । ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলন যে যালেম ও স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই । আমাদের জানা থাকা উচিত যে ,ইসলামের দৃষ্টিতে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা শর্তহীনভাবে নিষিদ্ধ কোন বিষয় নয় যদিও কোন কোন মতাদর্শ এবং ইসলামী মাযহাব জনগণের এরূপ অধিকারকে অস্বীকার করে ।
প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের অধিকারের সাথে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং শাসকের আনুগত্যের অপরিহার্যতার কারণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে যা রাজনৈতিক দর্শনের সবচেয়ে মৌলিক একটি বিষয় । যদি আমরা কোন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বৈধতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই সর্বপ্রথম আমাদেরকে আমরা কেন কোন শাসকের আনুগত্য করব তা নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে । আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে ,শাসকের আনুগত্যের বিষয়টি কি সবসময় শর্তহীন ? এ ক্ষেত্রে কি কোনরূপ বিরোধিতার অনুমতি নেই ? নাকি বিরোধিতা করা যাবে ? যদি করা যায় তবে তার শর্তগুলো কী কী ? আমরা এখন এ প্রশ্নগুলোর উত্তর গণতন্ত্র এবং ঐশী অধিকারের মতবাদের মধ্যে খুঁজব ।
1. গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে বিদ্রোহ করার অধিকার
পশ্চিমা বিশ্ব সামাজিক চুক্তি (SOCIAL CONTACT
) ও জনগণের সন্তুষ্টিকে সরকারের বৈধতার ভিত্তি মনে করে । সরকারের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের নিরাপত্তা দান ,এর পরিবর্তে জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের আনুগত্য করা । এ দৃষ্টি থেকে সরকারের দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন ও শাসন প্রতিষ্ঠা করা । এ নীতির ভিত্তিতে শাসন কর্তৃত্বের বৈধতার ভিত্তি হলো ওকালত বা প্রতিনিধিত্ব যা জনগণ সরকারের হাতে অর্পণ করে । হবজের মতে ,এ দায়িত্ব ও প্রতিনিধিত্ব জনগণ তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দিয়ে থাকে । কিন্তু জন লকের মতে ,জনগণ তাদের প্রাকৃতিক অধিকার (NATURAL RIGHTS
) রক্ষার জন্য তা করে থাকে । রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদের পক্ষের কেউ কেউ যেমন হবজ (HOBS
) জনগণের সরকারের বিরোধিতা করা ও অবাধ্যতার অধিকার আছে বলে মনে করেন না । আবার কেউ কেউ এ অধিকার শুধু একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর জন্য বৈধ মনে করেন ,প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নয় । যেমনভাবে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা হয়েছে : সরকার তার ন্যায়গত ক্ষমতাকে শাসিত জনগণের সমর্থন থেকে লাভ করে থাকে যা তারা স্বেচ্ছায় তার হাতে অর্পণ করে । আমরা বিশ্বাস করি যে ,সরকার-তা যে কোন পদ্ধতিরই হোক ,যদি এ লক্ষ্যকে হুমকির সম্মুখীন করে তাহলে জনগণের অধিকার রয়েছে ঐ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত অথবা পরিবর্তন করার এবং সে স্থানে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করার ।
জন লক যদিও মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষার পক্ষে এবং সরকারের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহের অধিকারের বিষয় উপস্থাপন করেছেন ;কিন্তু তাঁর বক্তব্য তেমন স্পষ্ট নয় । তিনি তাঁর নগর সরকার বিষয়ক প্রবন্ধে বলেন :‘
যে আইন সকল মানব প্রণীত আইনের ওপর প্রাধান্য রাখে তা হলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার-যা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট-জনগণের জন্য সংরক্ষিত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবীর বিচারের সময় আসবে (অর্থাৎ বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত) ততক্ষণ ঐশী ফয়সালার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে ।
কিন্তু এই অবস্থায়ও সমাজের অধিবাসীদের ক্ষুদ্র বা একাংশের দৃষ্টিতে যে সরকার বা শাসক সঠিকভাবে জনগণের অধিকার রক্ষা করছে না তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার রাখে না । যদিও এ অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ক্ষেত্রে আছে ।
তাই গণতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থকদের অনেকেই বিদ্রোহ করার অধিকারকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বৈধ বলে মনে করে না ,তাদের মতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিদ্রোহের বিষয়টি উপেক্ষা করা উচিত । কারণ ,গণতন্ত্র সংখ্যালঘু দলের জন্য মত প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদের অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে ।
ফলে স্বতন্ত্রভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে কারো প্রতিবাদের অধিকার নেই ।
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিদ্রোহের অবৈধতার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়েছে ,যেমন-
এক : যদিও সরকার ও রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে প্রাথমিক যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার ভিত্তিতে জনগণ সরকারকে তাদের শাসনের দায়িত্বভার অর্পণ করেছে ,কিন্তু যখন ব্যক্তি দেখছে যে ,বর্তমান অবস্থা তার সার্বিক কল্যাণ অর্জনের পথকে হুমকির মুখে ফেলছে তখন সে কেন তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না ? কেন এই অবস্থায় সে তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে পারবে না ?
দুই : সংখ্যাগুরু শাসকগোষ্ঠী অন্যদের অধিকারকে লঙ্ঘন করে-এ ধারণাটি সবসময় অগ্রাহ্য করা যায় না । কারণ ,গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীও যে ঔপনিবেশিক দমন নিপীড়ন চালায় এবং কখনও কখনও ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে মানুষের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই তা প্রমাণ করে । ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ,সাধারণ ইচ্ছার (এবহবৎধষ রিষষ) প্রতিফলনের নামে অনেক সময় ব্যক্তি-ইচ্ছা ,ব্যক্তিস্বার্থ ও স্বৈরাচার বাস্তবায়িত হয়ে থাকে অর্থাৎ সাধারণ ইচ্ছা স্বৈরাচারী শাসনে পরিণত হতে পারে ।
তিন : গণতন্ত্রে যে সংখ্যালঘুদের জন্য যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়েছে তা কে নির্ণয় করবে ? আর গণতন্ত্রের অধীনে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে কি না তা-ই বা কে বিচার করবে ? তাই এতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংখ্যালঘুদের প্রতিবাদের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা হয়েছে-এ দাবি যদি সংখ্যালঘুদের দ্বারা সমর্থিত না হয় ,যে কোন কর্তৃপক্ষই তা নির্ণয় করুক ,বাস্তবে অধিকার হরণ করা হয়েছে দাবি উঠলে তাদের দাবির সমাধান কে করবে ? ফ্রান্টেস নিউম্যানের ভাষায় :‘
গণতন্ত্রের পক্ষপাতিরা বিদ্রোহের অধিকারের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের বিষয়ে কোন উপায় ও পথই দেখান নি ।’
চার : যেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনের ভিত্তি হলো অধিকাংশের সমর্থন ,চাওয়া ও সন্তুষ্টি ,সেহেতু কেউই সাধারণ ইচ্ছার বিপরীতে কোন কিছুকে আইন বা মূল্যবোধ বা অধিকার হিসেবে দাবি করতে পারে না এবং তার ভিত্তিতে প্রতিবাদ জানাতে পারে না । তাই এ পদ্ধতিতে বিদ্রোহের কোন সুযোগ নেই ।
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশের স্বৈরাচার নৈরাজ্যের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে ।
তবে বাস্তবে অবস্থা এর থেকেও শোচনীয় । কারণ ,সংখ্যালঘু দল ভোটে তুলনামূলক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর শাসন পরিচালনা করে । ফলে নতুন করে নৈরাজ্যবাদের দাবিকে সোচ্চার করে ।
2.‘
ঐশী অধিকার’
মতবাদ অনুযায়ী বিদ্রোহ করার অধিকার
এ মতবাদে সরকারের বৈধতার ভিত্তি হচ্ছে ঐশী অনুমোদন থাকা যা আল্লাহর সর্বভৌমত্ব থেকে উৎসারিত । এ মতবাদ দীঘদিন ধরে চালু আছে এবং ইতিহাসের পরিক্রমায় বিভিন্নরূপ সমস্যা তাতে দৃষ্টিগোচর হয়েছে । প্রাচীন প্রাচ্যদেশীয় সম্রাটগণ ,মিশরীয় ফিরআউন বংশীয় সম্রাটগণ এবং অন্য শাসকগণ নিজেদেরকে‘
খোদা’
মনে করত । কিছু কিছু মতবাদ রাজা-বাদশাহদের ক্ষমতার উৎস খোদায়ী বলে মনে করত অর্থাৎ তাদের নেতৃত্বের উৎস হলেন স্বয়ং স্রষ্টা । মধ্য যুগের খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করত যে ,শাসকদের ক্ষমতার উৎস হলেন খোদা । প্রাচ্যের দেশগুলোতে এ চিন্তাধারা ছিল যে ,শাসকরা (সুলতানরা) হচ্ছেন আল্লাহর আরশের ছায়া যা আল্লাহর সাথে তাঁদের এক ধরনের সম্পর্কের পরিচয় বহন করে ।
এ মতবাদে বিদ্রোহ করার অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম মতভেদ রয়েছে ।
বাইবেলের তেরতম অধ্যায়ের প্রথমে এসেছে :‘
সবাই যেন শাসকদের হুকুম মেনে চলে ,কেননা ,সকল শক্তিই খোদা থেকে সৃষ্টি এবং সকল শাসনকর্তাকেই তিনি নিয়োগ করেছেন । অতএব ,যে কেউ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে সে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছে এবং নিজেকে আল্লাহের আযাবের দিকে ঠেলে দিয়েছে ।’
খ্রিস্টান ধর্মজাযক সেন্ট টমাস এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন যে ,‘
কোন ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে ,স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে অথবা তাকে হত্যা করবে । যদিও সেই ব্যক্তির (বিদ্রোহী) পেছনে জনগণের সমর্থন ও মদদ থাকে ।’
অতীতের পাশ্চাত্য রাজনৈতিক বিধিমালায় এই বাণী ছিল যে ,শাসকেরা আল্লাহর ইচ্ছায় ক্ষমতা হাতে নিয়েছে । এ জন্য অবশ্যই তার আনুগত্য করতে হবে এবং তাকে মেনে নিতে হবে ,যদিও সে অত্যাচারী হয় ,এছাড়া আর কোন উপায় নেই ।
আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিভঙ্গি
অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের নিরঙ্কুশ আনুগত্যের মতবাদ সমর্থন ও গ্রহণযোগ্যতা পায় নি । অধিকাংশ ইসলামী মাযহাব যালেম-অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জায়েয মনে করে । যদিও ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা বিস্তারের ভয় আন্দোলন জায়েয হওয়ার ফতোয়ার জন্য এক ধরনের প্রতিবন্ধক ।
যদিও কোন কোন ব্যক্তি ,যেমন ইমাম আবু হানিফা জায়েযের ফতোয়া দেওয়া ছাড়াও নিজেই অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাকে সমর্থন দিয়েছেন ।
এর বিপরীতে কতিপয় মাযহাব ,যেমন হাম্বালী মাযহাব বৈধ শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাকে স্পষ্টভাবে ইসলামের সীমা লঙ্ঘন মনে করে এটাকে নিষেধ করেছে । দুঃখজনকভাবে এ মত অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসার লাভ করেছে । কেননা ,
প্রথমত ,রাসূল (সা.)-এর কিছুসংখ্যক হাদীসের বাহ্যিক অর্থ তাদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে । যেমন-‘
তাদের (শাসকদের) কথা শ্রবণ কর ও তাদের আনুগত্য কর । নিশ্চয় তারা যা করবে তার দায়িত্ব তাদের এবং তোমরা যা করবে তার দায়িত্ব তোমাদের ।’
দ্বিতীয়ত ,অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের মতবাদ পোষণকারীদের সাথে শাসকদের সুসম্পর্ক ছিল ।
তৃতীয়ত ,বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতা তাদের মধ্যে লোপ পেয়েছিল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারার সমর্থক দলসমূহ ,যেমন মুতাযিলা মতবাদ দুর্বল হয়ে ছিটকে গিয়েছিল । ইবনে আকিল মুতাযিলি বলেন :‘
আমাদের অনুসারীরা অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাকে ওয়াজিব মনে করে । আশআরী মতবাদের অনুসারীদের-যেমন আবু হামেদ গাজ্জালীর-এ ধরনের বিদ্রোহে বিশ্বাস নেই ।’
দুঃখজনকভাবে এ ধরনের চিন্তা আহলে সুন্নাতের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে যার ফলে বর্তমান সময়ে আরব দেশসমূহে কিছু কিছু সরকারবিরোধী গোষ্ঠী ও আন্দোলনকারী দল-যারা ধর্মের প্রতি অনুগত তারা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন যে ,সরকারের বিরুদ্ধে তাদের এ আন্দোলন শরিয়তবিরোধী কাজ বলে গণ্য হয় কিনা ।
শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি
প্রতিবাদ ,বিদ্রোহ ,অবাধ্যতা-এ বিষয়গুলো সরকারের বৈধতার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে বিদ্রোহের বৈধতার বিষয়টি‘
বৈধ সরকার ও অবৈধ সরকার’
শিরোনামে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব ।
যালেম ও অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ : যেহেতু শিয়াদের আকিদা আনুযায়ী ইমামদের যুগে ইমামত ও নেতৃত্বের শর্ত হচ্ছে নিষ্পাপত্ব ,সেহেতু নিষ্পাপ ইমাম ছাড়া অন্য কোন শাসক ,এমনকি ন্যায়পরায়ণ হলেও জবর-দখলকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং শাসন কাজে তার হস্তক্ষেপ অবৈধ । ইমামদের অনুপস্থিতিতে যদি কোন শাসক বর্তমান ইমামের সম্মতিক্রমে নির্বাচিত না হয়ে থাকে তাহলে তা জবর-দখল হিসেবে গণ্য হবে । কেননা ,এ ধরনের অনুমতি কেবল ন্যায়পরায়ণ ফকীহদের দেওয়া হয়েছে । অন্য কারো জন্য এ ধরনের অনুমতি দেওয়া হয়নি । সেহেতু যে সরকার সকল শর্তের অধিকারী ফকীহর তত্ত্বাবধানে নেই সে সরকার হচ্ছে জবর-দখলকারী ও তাগুতী সরকার ।
শরিয়তের বৈধতা ছাড়া কোন শাসকের জনগণকে শাসন করার অধিকার নেই এবং জনগণের জন্য আবশ্যক নয় ঐ সরকারের আইন মেনে চলা । অবশ্য এ ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থায় ও সাধারণ অবস্থায় অত্যাচারী সরকারের (ও শাসন কর্তৃপক্ষের) বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । কারণ ,যদিও প্রথম ক্ষেত্রে সরকার বৈধ নয় ,কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশেষ পরিস্থিতির কারণে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ নিশ্চিত হয় অথবা অধিকতর অকল্যাণকে প্রতিরোধ করা যায় । এক্ষেত্রে শাসকের আনুগত্যের বিষয়টি সরকার বৈধ হওয়ার ওপর নির্ভর করে না ;বরং এ আনুগত্য জরুরি অবস্থায় দ্বিতীয় পর্যায়ের (বিশেষ অবস্থায় উদ্ভূত) বিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে যা সাধারণ ও প্রকৃত বিধান নয় । উদাহরণস্বরূপ ,শিয়া ফকীহ্গণ জবর-দখলকারী সরকারের সাথে সহযোগিতাকে হারাম মনে করেন । কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলমী দেশসমূহে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ শর্তাধীনে জবর-দখলকারী সরকারের সাথে সহযোগিতা এবং তাদের অনুসরণকে প্রয়োজনীয় মনে করেন । প্রথমত ,এটা স্বাভাবিক যে ,এ রকম বিষয়ে জবর-দখলকারী সরকারের অনুসরণের অর্থ এই নয় যে ,তাকে শরিয়তের বৈধতা দেওয়া । দ্বিতীয়ত ,এ রকম অসহায় অবস্থায় ইসলামী সমাজের স্বার্থের জন্য তা প্রয়োজন ছিল । এ ধরনের মতাদর্শের পেছনে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি রয়েছে । যেমনভাবে অষ্টম ইমাম রেযা (আ.)-কে এক ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত বক্ষীর হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন :‘
যদি ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে ,তবে যুদ্ধ সরকারের শক্তি বৃদ্ধির জন্য নয় ;বরং ইসলামী দেশ ও সমাজ রক্ষার জন্য । যদি ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্মান ও মৌলিক কোন বিষয় হুমকির সম্মুখীন হয় তবে ইসলামী সমাজের কারণেই (ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে) যুদ্ধ করবে-শাসকের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য নয় ।’
বিদ্রোহের পর্যায়সমূহ
ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জবর-দখলকারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পর্যায় রয়েছে ।
প্রথমত ,অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান : জবর-দখলকারী শাসককে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান এবং তার নির্দেশ পালন ও বাইআত থেকে বিরত থাকাই ছিল নিষ্পাপ ইমামদের পথ । যেমন ইমাম আলী (আ.) ও হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.) জীবিত থাকা অবস্থায় খলিফার বাইআত করা থেকে বিরত থেকেছেন ।
ইমাম হোসাইনও ইয়াযীদের বাইআত অস্বীকার করে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে বলেন :‘
কখনই ইয়াযীদের কাছে বাইআত করব না । কেননা ,আমার ভাই হাসানের পরে ঐ খেলাফত আমার ।’
কখন কখন যদিও বাইআত জায়েয নয় ,কিন্তু বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে এ হুকুম পরিবর্তন হয় । উদাহরণস্বরূপ ,ইমাম আলী (আ.) ইসলাম ধর্মকে রক্ষা এবং শক্তিশালী করার জন্য খলিফাদের বাহ্যিক সমর্থন ও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন । তাই তিনি বলেন :‘
আমি এ বিষয়ে ভীত ছিলাম যে ,যদি ইসলাম ও তার অনুসারীদের সাহায্য না করি তাতে ইসলামে ফাটল অথবা উত্তপ্ত অবস্থার (উত্তেজনার) সৃষ্টি হবে যার কষ্ট আমার নিকট তোমাদের ওপর (ন্যায়ের) শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা হারানোর কষ্ট হতে অধিক ।’
কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.)-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি হচ্ছে যে ,ইয়াযীদের হাতে বাইআতের অর্থ হচ্ছে তার যুলুম ,অত্যাচার ,পাপাচার ও অবাধ্যতাকে বৈধতা দান । কারণ ,ইয়াযীদ প্রকাশ্যে ঐ সকল অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করত । ধর্মকে খেলা মনে করত । যার ফলে ইসলাম ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল । ইমাম হোসাইন (আ.) চরম প্রতিকূল অবস্থা ও চাপের মুখেও ফাসেক শাসকের হাতে বাইআত করেননি । ইমাম হোসাইন (আ.) পরিষ্কারভাবে তাঁর বাইআত হতে বিরত থাকার কারণ সম্পর্কে বলেন :‘
নিশ্চয় সুন্নাতকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং বিদআতকে জীবিত করা হয়েছে ।’
দ্বিতীয়ত ,আন্দোলন ও প্রতিরোধ : অবৈধ শাসকের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা যা মৌখিকভাবে বলার মাধ্যমে শুরু হবে এবং অত্যাচারী শাসক ও সরকারকে বিতারিত না করা পর্যন্ত তা চলবে । এ ক্ষেত্রে আন্দোলন ও বিদ্রোহের বিশেষ গুরুত্ব ও ভূমিকা রয়েছে । ইসলাম ধর্মে বিদআত চালুর অভিযোগে ওসমানের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিদ্রোহ করে যা মুসলমানদের সর্বপ্রথম বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা ছিল । অন্য উদাহরণ হচ্ছে ,অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলন । ইমাম সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালনের জন্য ইয়াযীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন । ইমাম হোসাইন (আ.) অত্যাচারী শাসকের বিরোধিতা করাকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত ওয়াজিব দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করেছেন । তিনি আলেমসমাজ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে এ কারণে তিরস্কার করেছেন যে ,কেন অত্যাচারীদের সাথে হাত মিলিয়েছে এবং নীরবে বসে আছে ।
তিনি বলেন :‘
তারা কেন মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে অত্যাচারীদের হাত শক্তিশালী করেছে যাতে তারা (অত্যাচারী গোষ্ঠী) তাদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করতে পারে । আর দুর্বলদেরকে হাতের মুঠোয় আনতে এবং অসহায়দেরকে দমন করতে পারে । আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করে শাসনক্ষমতাকে নিজের খেয়াল-খুশি মতো পরিচালনা করতে পারে ।’
ইমাম হোসাইন (আ.) বনু উমাইয়ার শাসনকে অবৈধ প্রমাণ করা এবং বৈধ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে সাহায্য ও তাঁর অনুসরণ এবং মুসলিম সমাজের সঠিক ইমাম ও পথপ্রদর্শনকারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করে বলেন :‘
আমার সত্তার শপথ ,ইমাম তিনি ব্যতীত কেউ নন যিনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করেন ,ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করেন ,সত্যের
অনুগত ও অনুসারী হন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন ।’
হুর ইবনে ইয়াযীদ রিয়াহীর সৈন্য বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইয়াযীদের শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আবশ্যকতা বর্ণনা করে বলেন :‘
এ জাতির ক্ষমতাধররা শয়তানের আনুগত্যকে অপরিহার্য জ্ঞান করেছে ,করুণাময়ের (আল্লাহর) আনুগত্যকে ত্যাগ করেছে । প্রকাশ্যে তাঁর বিধানকে লঙ্ঘন করেছে ও তাঁর নির্ধারিত আইন ও বিধিকে অকার্যকর করেছে । বাইতুল মাল ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে আত্মসাৎ করেছে ,আল্লাহর বৈধ বিষয়কে হারাম এবং তার নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ ঘোষণা করেছে । এ অবস্থায় আমি এরূপ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকারপ্রাপ্ত ।’
বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
শিয়াদের বিশ্বাস হচ্ছে ,বৈধ সরকার ও শাসনব্যবস্থা ইমামদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইমামের অনুপস্থিতিতে ইমামের অনুমতি ও প্রত্যয়ন প্রয়োজন যা সকল শর্তের অধিকারী ফকীহদের দেওয়া হয়েছে । এটা স্পষ্ট যে ,ইমামত ও তাঁদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ নয় । কেননা ,তাঁরা হচ্ছেন নিষ্পাপ ,তাঁদের থেকে ভুল ,পথভ্রষ্টতা ও পাপাচারের কোন সম্ভাবনা নেই । এ দিক থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাঁদের অবাধ্যতা অবশ্যই যুলুমের শামিল হবে এবং তা মোকাবিলা করতে হবে । আল্লামা হিল্লি এ সম্পর্কে বলেন :‘
যে কেউ ন্যায়পরায়ণ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে তার সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব ।’
কিন্তু কথা হচ্ছে ,ইমামদের অনুপস্থিতিতে (গাইবাত) বেলায়াতে ফকীহর শাসন কীভাবে গ্রহণযোগ্য হয় ?
যেমনভাবে আমরা জানি যে ,আল্লাহর দৃষ্টিতে ঐ সকল শাসকের আনুগত্য করা বৈধ যে ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুমতি আছে ,এর বাহিরে কখনই আনুগত্য বৈধ নয় । এই দিক থেকে শরিয়তের বাহিরে ও নিরঙ্কুশভাবে কোন শাসকের আনুগত্য গ্রহণযোগ্য নয় । স্রষ্টার (আল্লাহর) নির্দেশ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টির (বান্দার) আনুগত্য করা যাবে না বা আনুগত্য বৈধ নয় ।
ইমামদের নিষ্পাপত্বের কারণে তাঁরা কখনই শরিয়তবিরোধী কাজ ও নির্দেশ দেবেন না ,তাই বিদ্রোহের কোন প্রয়োজনই নেই ।
কিন্তু ইমামদের পক্ষ হতে নিযুক্ত শাসকের ক্ষেত্রে আনুগত্য শুধু ধর্মীয় বিধি-বিধান ও সামাজিক বিষয়াদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ । যেমন ইমাম আলী (আ.) মালিক আশতারকে নিয়োগ দেওয়ার পর মিশরের জনগণের প্রতি মালিকের প্রশংসা এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানানোর পর বলেন :‘
যতক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যের পথে চলবে তার আনুগত্য করবে ।’
হযরত আলী (আ.) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বসরার শাসক হিসেবে নিয়োগ দানের সময় জনগণকে বলেন :‘
যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মেনে চলবে ততক্ষণ তার আনুগত্য করবে আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিদআতের সৃষ্টি করে অথবা সত্য থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে আমাকে খবর দেবে যাতে তাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করতে পারি ।’
শাসকের কর্মকাণ্ডের সঠিকতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কেবল ঐ সকল ব্যক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে যাদের ইসলামী অধিকার ও শরিয়তের বিধি-বিধানের ওপর বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান রয়েছে । অন্যদিকে চলমান সময়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে ।
এছাড়াও শাসকের পথভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতির বিভিন্ন কারণ রয়েছে ,যেমন খোদাভীতির অভাব ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে দূরে সরে যাওয়া ,ইসলামের বিধি-বিধানের সঠিক ব্যাখ্যা না জানা ,সমসাময়িক বিশ্বকে বিশ্লেষণে ব্যর্থতা ,সামাজিক কোন প্রেক্ষাপট বুঝতে না পারা ইত্যাদি ।
এ জন্য এ দুই বিষয়ে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে । কেননা ,খোদাভীতি ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে দূরে সরে যাওয়া কখনই গ্রহণযোগ্য নয় । এরূপ ক্ষেত্রে শাসক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবে ও শাসনের বৈধতা হারিয়ে ফেলবে । কিন্তু সামাজিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে যদি ভুল করা বা বিষয়কে সঠিকভাবে বিশ্লেষণে ব্যর্থ হওয়া বা কোন ঘটনার পরিণতি কী হতে পারে তা নির্ণয় করতে না পারা-এরূপ ঘটনা তার (শাসক) ক্ষেত্রে খুব কম ঘটে তবে তা উপেক্ষণীয় । তেমনি নিজের মতকে প্রাধান্য দান এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি শাসক ফকীহ থেকে কদাচিৎ দেখা যায় এবং পুনঃপুনঃ না ঘটে তবে তা বুদ্ধিবৃত্তি ও শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ও উপেক্ষা করার মতো । কারণ ,এধরনের অনিচ্ছাকৃত ভুল পৃথিবীর সকল শাসনেই কম-বেশি ছিল । যেমন শহীদ বাকের সাদর এ ক্ষেত্রে বলেন :‘
যদি কোন মুজতাহিদ তাঁর সর্বসাধারণ কর্তৃত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের সার্বিক বিষয়ে কোন হুকুম (নির্দেশ জারি) করেন ,যদিও সে বিষয়ে তিনি ভুল করেছেন বলে কেউ নিশ্চিত হয় ,তদুপরি কারো জন্য বৈধ নয় যে ,সে ঐ সেই শাসকের হুকুমকে এড়িয়ে নিজের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করবে ।’
কিন্তু শাসক যদি একের পর এক ভুল করতে থাকে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলি বুঝতে অক্ষম হয় এবং নেতৃত্বের সঠিক কর্মকৌশল জানা না থাকে তাহলে উত্তম হচ্ছে এ পদের জন্য যে যোগ্য তাকে নেতা হিসেবে নিয়োগ করা ।
প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
বিভিন্ন প্রকার বিদ্রোহের মধ্যে একটি হলো ইসলামী শাসনের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা । শহীদ বেহেশতী এ সম্পর্কে বলেন :‘
প্রশাসন যদি চলমান বিভিন্ন ইসলামবিরোধী দলের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নেয় তাহলে জনগণ ও বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের উচিত দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের কাছে বিভিন্নভাবে দাবি জানানো যে ,তাঁরা যেন সঠিকভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন । যদি তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন না করেন এবং ইসলামবিরোধী তৎপরতা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নৈতিকতার জন্য হুমকিস্বরূপ হয় তাহলে ইসলামী দলসমূহ সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার কাছ থেকে ফতোয়া (তাদের করণীয় নির্দেশ) চাইবে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে । আর এভাবে তারা একদিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করল ,অন্যদিকে রাষ্ট্রে কোন বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হলো না ।
হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) বিভিন্ন কর্মকর্তাদের নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলার ক্ষেত্রে জনগণের জন্য প্রতিবাদের পথকে উন্মুক্ত রেখেছিলেন এবং তাঁর রাজনৈতিক ও ঐশী অসিয়তনামায় বলেন :‘
শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম বলে গণ্য যে কোন বিষয় এবং ইরানী জাতি এবং এই ইসলামী প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্য ও সম্মানের পরিপন্থী সকল কাজ কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা সকলেরই দায়িত্ব । বিপ্লবী জনগণ এবং যুবকরা যদি ঐ রূপ কোন বিষয় দেখেন তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদ জানাবেন । আর যদি তাঁরা গুরুত্ব না দেন (সংশোধিত না হন) তখন বিপ্লবী জনগণ এবং যুবকরাই তা মোকাবেলা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন ।’
আশুরা এবং ধর্ম ও রাজনীতির সংযোগ
26 নং প্রশ্ন : ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলন ও আশুরার সংস্কৃতি কি সেক্যুলার বিশ্বাসকে (ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর পৃথক) বাতিল প্রমাণ করে ?
উত্তর : কিছুসংখ্যক ব্যক্তি‘
ধর্ম রাজনীতি থেকে পৃথক’
-এটাকে প্রমাণ করার জন্য এ রকম বলে থাকেন যে ,ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলন শতভাগ গণতান্ত্রিক ছিল এবং জনগণের দাবির কারণে তা ঘটেছে । এর দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে ,ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলনের সাথে খোদায়ী নেতৃত্বের কোন সম্পর্ক নেই ।
ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কুফার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ প্রথমে মদীনা থেকে মক্কা ,অতঃপর সেখান থেকে কারবালা গমনের কারণ ছিল জনগণের লিখিত ও মৌখিক দাওয়াত । কুফার গোত্রপতি ও জনগণের উদ্দেশ্য ছিল উমাইয়াদের যুলুম ও অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ এবং শাসনক্ষমতা লাভ করা । জনগণের পক্ষ থেকে ইমামকে আহ্বান ছিল শতভাগ গণতান্ত্রিক । যুদ্ধ ,শাহাদাত অর্থাৎ ইমাম হুসাইন এবং তাঁর সঙ্গীসাথিদের আন্দোলন ও বিপ্লব এক প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ ছাড়াও ইসলাম ও তাঁর পরিবারের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষামূলক পদক্ষেপ ছিল । যা এ বাস্তবতার প্রতি নির্দেশ করে যে ,ইসলাম ও ইমাম হোসাইনের দৃষ্টিতে খেলাফত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইয়াযীদ ও অন্যান্য খলিফার জন্য নয় । এমনকি ইমাম হোসাইন (আ.) এবং আল্লাহও এর অধিকারী নন ;বরং এ ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ অর্থাৎ রাষ্টীয় ক্ষমতা হলো জনগণের এবং তারা নিজেদের নির্বাচনের মাধ্যমে এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে ।
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইমাম হোসাইনের বাণী ও ইতিহাসের বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করলে এটাই স্পষ্ট হয় যে ,ইমামের রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল খোদায়ী ও ঐশী উদ্দেশ্যে যা সেক্যুলারদের আকিদাকে বাতিল করে দেয় । ইমাম হোসাইনের আন্দোলন কোন্ ধরনের শাসনের ভিত্তিতে ছিল ,এ বিষয়ে জানার জন্য প্রথমে প্রয়োজন হচ্ছে খোদায়ী শাসন ও ধর্ম নিরপেক্ষ শাসনের পার্থক্য জানা । কেননা ,এ দুই ধরনের শাসনের মূল দর্শন ,লক্ষ্য ,শাসনের বৈধতার ধরন এবং শাসকের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে মূল পার্থক্য রয়েছে । তাই ইমাম হোসাইন (আ.)-এর দৃষ্টিতে উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করব ।
এক. শাসনের লক্ষ্য ও দর্শন
ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর শাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ঊর্ধ্বের এক বিষয় বলে উপস্থাপন করেছেন । অর্থাৎ তিনি জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ,জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়কে তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেননি ।
তিনি কুফাবাসীর দাওয়াত ও বাইআতের বিষয় আলোচিত হওয়ার পূর্বেই মদীনা ত্যাগ করার সময় তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ইসলামী সমাজের সংস্কার সাধন ,ধর্মীয় দায়িত্ব পালন ও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ বলে ঘোষণা করেন ।
انّا خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدّی ارید ان ءامر بالمعروف و انهی عن المنکر
‘
আমি বের হয়েছি কেবল আমার নানার উম্মতকে সংশোধন করার জন্য । আমি চাই ,সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে ।’
ইমামের এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে ,যদিও তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে ,তাঁর পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না এবং কুফাবাসীরা তাদের বাইআত ভঙ্গ করবে তবুও তিনি তাঁর আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান নি । কেননা ,তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে জীবিত করা । নেতৃত্ব ও শাসনক্ষমতা ছিল পরবর্তী পর্যায়ে ।
ইমাম হোসাইন (আ.) মুয়াবিয়ার জীবনের শেষ পর্যায়ে হজের মৌসুমে মিনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন । সেখানে শত শত জনতা এবং সে সময়ের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । তিনি তাঁর শাসনক্ষমতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে এভাবে বর্ণনা করেন-‘
হে আল্লাহ! আপনি জানেন ,আমি যা করছি তা ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতার জন্য নয় । আমি এর মাধ্যমে পার্থিব সম্পদ লাভ করতে চাই না । আমি কেবল চাই আপনার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং আপনার জমিনে সংস্কার সাধন করতে ,যাদের ওপর যুলুম করা হয়েছে তাদেরকে মুক্তি ও নিরাপত্তা দান করতে । আর সকল ফরয ,সুন্নাত ও ঐশী বিধি-বিধানকে বাস্তবায়িত করতে ।’
(তুহাফুল উকুল ,পৃ. 243)
তিনি তাঁর এ বক্তব্যের পর না ক্ষমতা দখল ও জনগণের ওপর কর্তৃত্ব লাভের কথা বলেছেন ,আর না কোন পার্থিব সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন । তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে এভাবে বর্ণনা করেন-
1. আল্লাহর দ্বীনের নিশানাকে স্পষ্ট করা ।
2. পৃথিবীতে সংস্কার করা ।
3. অসহায় মানুষের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ।
4. আল্লাহর সুন্নাত ,বিধান ও ওয়াজিবসমূহের আমল করা ।
ইমাম হোসাইন (আ.) মক্কা থেকে কুফার পথে ফারাযদাকের সাথে কথোপকথনের সময় বলেন :‘
হে ফারাযদাক! এ জাতি (বনু উমাইয়্যা) শয়তানের আনুগত্যকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করেছে ,পরম করুণাময়ের আনুগত্যকে ত্যাগ করেছে । তারা পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি এবং আল্লাহর বিধি-বিধানকে বাতিল প্রতিপন্ন করেছে । মদপান করছে এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে । এ অবস্থায় আমি হলাম সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর দ্বীনে সাহায্য করার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত । তাঁর শরিয়তকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা এবং তাঁর পথে জিহাদের দায়িত্ব আমার ওপরই ন্যস্ত যাতে আল্লাহর বাণী সমুন্নত ও উচ্চকিত হয় ।’
এই অংশে ইমাম হোসাইন উমাইয়াদেরকে সত্যিকার অর্থে সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । কারণ ,তাদের চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে শাসনক্ষমতা থেকে দূরে রাখা । ইসলামী সমাজে সর্বপ্রথম তারাই এই চিন্তার বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় । ইমাম হোসাইন (আ.) এদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা এবং আল্লাহের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করাকে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে মনে করেন । তিনি হুকুমতের মূল দর্শন“
کلمة الله هي العلیا
”
-‘
আল্লাহর বাণীকে (বিধান) সমুন্নত ও উচ্চকিত করা’
বলে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন । এটা স্পষ্ট যে ,পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন ইসলামই হচ্ছে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা দানকারী ।
দুই. শাসনক্ষমতার খোদায়ী বৈধতা (আল্লাহ প্রদত্ত বৈধ শাসন)
ইমাম হোসাইন (আ.)-এর বক্তব্য এটাই প্রমাণ করে যে ,সরকারের বৈধতা কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট হবে । শরিয়তের দৃষ্টিতে ঐ শাসনই বৈধ যেখানে ফকীহরা (ইমামদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হন । এ ক্ষেত্রে জনগণের রায় ও বাইআতের কোন প্রভাব এতে নেই ,যদিও তা ক্ষমতায় আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ । বিষয়টি তেমন নয় যেমনটি কিছু কিছু অজ্ঞ ,পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত এবং স্যেকুলার শাসনের সমর্থকরা মনে করে । তারা এমনকি নিষ্পাপ ইমামদের উপস্থিতির যুগেও শাসনের ঐশী বৈধতা থাকার অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করে ।
মদীনার গভর্নর যখন ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কাছ থেকে ইয়াযীদের জন্য বাইআত চেয়েছিল তখন ইমাম বলেন :
‘
হে শাসক (ওয়ালীদ ইবনে ওকবা)! আমরা হলাম নবুওয়াতের গৃহের সদস্য ,রেসালাতের খনি ,ঐ গৃহের অধিবাসী যেখানে ফেরেশতাদের আনাগোনা ছিল এবং আল্লাহর রহমত নাযিলের স্থান । আল্লাহ আমাদের (বংশের রাসূলের নবুওয়াত) দ্বারাই শুরু করেছেন এবং আমাদের (বংশের ইমাম মাহদীর শাসন) দ্বারাই শেষ করবেন । ইয়াযীদ মদ্যপায়ী ,পাপাচারী ,এমন সম্মানিত ব্যক্তিদের হত্যাকারী যাদের হত্যা নিষিদ্ধ ,সে প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত হয় । তাই আমার মতো ব্যক্তি ইয়াযীদের মতো ব্যক্তির হাতে বাইআত করতে পারে না ।’
এ বাক্যের দ্বারা ইমাম হোসাইন (আ.) সমাজের ওপর নিজ শাসনের বৈধতার দলিল পেশ করেন এবং ইয়াযীদের শাসনকে অবৈধ ও খোদাবিরোধী বলে ইঙ্গিত করেন । সমাজের শাসক হওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ঐশী দলিল ইয়াযীদের নেই ;বরং আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে তার বাইআত বৈধ না হওয়ার দলিল আছে ।
মুসলমানদের অধিকাংশই ইয়াযীদের হাতে বাইআত করা সত্ত্বেও ইমাম হোসাইন (আ.) ইয়াযীদের কাছে বাইআত না করা এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা এটাই প্রমাণ করে যে ,ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও শাসকের জন্য খোদায়ী বৈধতার প্রয়োজন-যা স্যেকুলার মতবাদকে বাতিল করে দেয় । যদি ইমাম হোসাইন (আ.) আন্দোলন না করতেন তাহলেও শুধু ইয়াযীদের বাইআত থেকে দূরে থাকাই এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল । অনেক বর্ণনাতেই ইমাম হোসাইন তাঁর ও অন্য ইমামদের নেতৃত্ব দানের অধিকার যে খোদাপ্রদত্ত অর্থাৎ তাঁরা যে ঐশীভাবে শাসনের বৈধতা লাভ করেছেন তার উল্লেখ করেছেন । তাই তিনি বলেন :
ان مجاری الامور و الاحکام علی یدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه
‘
শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয় ও ধর্মীয় বিধি বিধান বাস্তায়নের দায়িত্ব আল্লাহওয়ালা আলেমদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে যারা তাঁর হালাল ও হারামের রক্ষক ও এ বিষয়ে বিশ্বষ Íতার অধিকারী ।’
রেওয়ায়াতে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে ,জনগণের ওপর শাসন করার অধিকার শুধু হালাল-হারামের ওপর বিশেষজ্ঞ ও দ্বীনের তত্ত্বাবধায়ক ও আমানতদার আলেমগণের-যাঁদের মধ্যে নিষ্পাপ ইমামগণ শীর্ষস্থানীয় ।
যখন ইবনে যুবাইর ইমাম হোসাইন (আ.)-কে ইয়াযীদের হাতে বাইআত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তখন ইমাম না-বোধক উত্তর দিয়ে বলেন :
انی لا ابایع له ابدا لان الامر انّا کان لی من بعدی اخی الحسن
যার মর্ম হলো এমন-আমি কখনই তার (ইয়াযীদের) হাতে বাইআত করব না । কেননা ,আমার ভাই (ইমাম) হাসানের (শাহাদতের) পর খেলাফতের বৈধ অধিকারী হচ্ছি আমি ।
তেমনিভাবে ইমাম বসরার জনগণের উদ্দেশে লিখিত চিঠিতে বলেন :‘
আমরা হচ্ছি রাসূল (সা.)-এর বংশধর এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী । তাঁর (রাসূলের) প্রতিনিধিত্বের জন্য আমরা হচ্ছি সবার চেয়ে যোগ্য । অন্যরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে । আমরা ঐক্যের স্বার্থে তা মেনে নিয়েছি । এটা ঐ অবস্থায় ছিল যখন জানতাম যারা শাসনকর্তৃত্ব দখল করে নিয়েছে এ বিষয়ে আমরাই তাদের চেয়ে উত্তম ও যোগ্য ।’
এছাড়াও কুফার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে তিনি লিখেছিলেন :‘
আল্লাহর রাসূলের সাথে (আত্মীয়তা ও আধ্যাত্মিক) নৈকট্যের কারণে এ পদের জন্য আমিই সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখি ।’
তিন. ইসলামী শাসকের শর্তসমূহ
ইমাম হোসাইন (আ.)-এর দৃষ্টিতে শাসন-কর্তৃত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা যা মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য দান করবে এবং তার বৈধতা কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হবে । তাই এটা স্পষ্ট যে ,ঐ শাসককে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে:
1. খোদায়ী বিধি-বিধান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা : খলিফাদের সাথে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর বিরোধিতার এটি ছিল অন্যতম মূল কারণ । ইমাম এক বক্তব্যে দ্বিতীয় খলিফাকে লক্ষ্য করে বলেন:
صرت الحاکم علیهم بکتاب نزل فیهم لا تعرف معجمه ولا تدری تاویله الاّ سماع الاذان
‘
তুমি ঐ কিতাবের দোহাই দিয়ে তাদের শাসক হয়েছ যা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবারের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তুমি তাঁর বাণীসমূহ শুধু কানেই শুনেছ ,কিন্তু তার প্রকৃত ও অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে অবহিত নও ।’
ইমাম হোসাইন (আ.) মিনায় উপস্থিত বিশিষ্ট ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উদ্দেশে বলেন :‘
শাসনক্ষমতা সেই ধর্মীয় ব্যক্তিদের হাতে থাকবে যারা আল্লাহর হালাল ও হারাম বিধানের আমানতদার ও রক্ষক । ইমামতের যুগে আহলে বাইতের ইমামরাই হচ্ছেন এ পদের অধিকারী ।’
2. কোরআন ও সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা : এ সম্পর্কে ইমাম হোসাইন (আ.) কুফার জনগণের উদ্দেশে লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেন :
فلعمری ما الامام الاّ العامل بالکتاب و الآخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه علی ذات الله
‘
আমার সত্তার শপথ ,উম্মাহর ইমাম ও নেতা কেবল আল্লাহর কিতাবের ওপর আমলকারী ,ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী ,সত্যের প্রচারক ও আল্লাহর জন্য নিজের প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক ।’
এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ,শাসকের শর্ত হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আমল ,ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা এবং নিজেকে আল্লাহর পথে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত ও উৎসর্গ করা ।
3. ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা : ইমাম হোসাইন (আ.)-এর দৃষ্টিতে ইসলামী শাসকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা । যেমনিভাবে কুফাবাসীর উদ্দেশে লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেন :‘
والآخذ بالقسط
’
অর্থাৎ ন্যায় ও সুবিচারকারী এবং আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি এ বিষয়টিকে উমাইয়া শাসকদের অবৈধতার কারণ হিসেবে অভিহিত করেন ।
তাই ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলন ও আশুরার সংস্কৃতির মূল শিক্ষা হচ্ছে ,ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন গভীর ও দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে তা স্পষ্ট করা । তাঁর দৃষ্টিতে কোন সরকারের বৈধতা ,শাসক হওয়ার শর্তসমূহ ,শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ,কার্যকারিতা ,কর্মসূচি সবকিছুই ইসলামী বিধিবিধান ও শিক্ষার ভিত্তিতে হতে হবে ,আর তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই জনগণের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য নিশ্চিত হবে ।
ইবনে যিয়াদকে গুপ্তহত্যা না করা
27 নং প্রশ্ন : ইবনে যিয়াদকে হত্যা করার সুযোগ পেয়েও কেন হযরত মুসলিম তা থেকে বিরত হন ?
উত্তর : মহান আল্লাহ ও নিষ্পাপ পবিত্র আহলে বাইত যুলুম-অত্যাচার এবং ধোঁকাবাজি দ্বারা শত্রুর ওপর জয়লাভ করাকে নিন্দা করেছেন ।
যেমন হযরত আলী (আ.)-এর খেলাফতের সময় কোন এক যুদ্ধে শত্রুরা জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল ,এক ব্যক্তি পরামর্শ দিল যে ,জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হোক । হযরত আলী (আ.) এ ধরনের যুলুম থেকে বিরত থাকার জন্য বলেন :‘
لا اطلب النصر با لجور
’
‘
আমি অন্যায় পথে (যুলুমের সাহায্যে) বিজয়ী হতে চাই না ।’
হযরত মুসলিমও ইসলাম ও আহলে বাইত (আ.)-এর শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন । তাই যখন হানি ইবনে উরওয়া ও শারিক ইবনে আওয়ার অসুস্থ হন তখন কথা ছিল ইবনে যিয়াদ তাঁদেরকে দেখতে আসবে । শারিক হযরত মুসলিমকে বলেন :‘
যখন সে আসবে তখন তাকে হত্যা করবে । অতঃপর তার প্রাসাদ দখল করবে!’
কিন্তু হানি ইবনে উরওয়া এর বিরোধিতা করেন । ইবনে যিয়াদ এসে কিছুক্ষণ কথা বলার পর চলে যায় । তখন শারিক হযরত মুসলিমকে এই প্রশ্নটিই করেন । তিনি বলেন :“
দু’
টি কারণে ইবনে যিয়াদকে হত্যা করিনি । প্রথমত ,এ কাজে হানি ইবনে উরওয়ার অনুমতি না থাকা । কেননা ,তিনি বলেছিলেন :‘
আমি চাই না তার রক্ত আমার বাড়িতে ঝরবে ।’
দ্বিতীয়ত ,রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে ,‘
ان الایمان قید الفتک و لا یفتک المومن
’
‘
ঈমান আকস্মিক হামলা ও গুপ্তহত্যার প্রতিবন্ধক এবং মুমিন গুপ্তহত্যা করে না ।”
হানি ইবনে উরওয়া বলেন :‘
হ্যাঁ ,যদি তাকে হত্যা করতে তাহলে একজন ফাসেক ,কাফের ও ধোঁকাবাজকে হত্যা করতে । কিন্তু আমি রাজি হইনি এবং পছন্দ করিনি যে ,তার রক্ত আমার বাড়িতে ঝরুক ।’
গুপ্তহত্যা শরিয়তবিরোধী কাজ
28 নং প্রশ্ন : মুসলিম ইবনে আকিলের ঘটনার প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তির কি অধিকার আছে ইসলামী সমাজে কাউকে হত্যা করবে বা কাউকে হত্যার নির্দেশ দেবে ? অথবা বিচারকের হুকুম ছাড়াই সরাসরি কাউকে হত্যা করবে ?
উত্তর : ইসলাম এমন এক ধর্ম যা সকল মানুষের (মুসলমান ,অমুসলমান ,বিদেশি ,ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী) জীবন ও সম্মান রক্ষা করাকে ইসলামী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব বলে মনে করে । মানুষের জীবন রক্ষা করাকে ইসলাম ধর্মে এমনভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে ,একজন নিষ্পাপ মানুষের জীবন রক্ষা করাকে সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করার সমান বলে অভিহিত করেছে ।
তাই মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার হচ্ছে এক ঐশীদান । ইসলামী শরিয়তে বর্ণিত হয়েছে : ফাসেক ,সীমাহীন পাপাচারী ,ধর্মত্যাগী ,নিরীহ মানুষের হত্যাকারী ও ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ছাড়া কাউকে হত্যা করা যাবে না । কিন্তু কিছু কিছু যালেম-অত্যাচারী ও আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি খোদা প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নিজেকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ;কিসাসের (হত্যার কারণে মৃত্যুদণ্ড) মতো শাস্তিকে নিজের জন্য ডেকে আনে । যদিও এ সকল বিষয় কেবল ইসলামী শাসনের অধীনে ন্যায়পরায়ণ বিচারকের দ্বারা শরিয়তের বিধান অনুযায়ী বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব । কিন্তু কাউকে গুপ্তহত্যা করা বৈধ কিনা-এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাবের জন্য‘
গুপ্তহত্যা’
শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জানা প্রয়োজন । ডেভিড অরভিন শোয়ার্টজ তাঁর লিখিত‘
আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামী আইন’
প্রবন্ধে লিখেছেন :‘
এ বিষয়টিকে সঠিকভাবে জানার জন্য পাশ্চাত্যের দেওয়া আইনি সংজ্ঞার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় । পশ্চিমাদের এ বিষয়টিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার জন্য প্রথমেই উচিত গবেষণা করা যে ,ইসলাম এ সম্পর্কে কী বলেছে অর্থাৎ শরিয়ত কীভাবে সন্ত্রাস ও সহিংসতাকে ব্যাখ্যা করেছে এবং কীভাবে তার জবাব দিয়েছে ।
1. পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস
পাশ্চাত্যের অভিধানগুলোতে সন্ত্রাস হচ্ছে এমন এক ত্রাস সৃষ্টিকারী সহিংস আচরণ যা একজন অথবা একদল ব্যক্তি কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ ও ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় । অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ত্রাস ও সহিংসতামূলক কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নেওয়াই হলো সন্ত্রাসবাদ ।
পশ্চিমাদের সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় অনেক অস্পষ্টতা বয়েছে । প্রত্যেক দেশ তাদের নিজস্ব স্বার্থ অনুযায়ী সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করেছে ,আর এ জন্যই এতে মতভেদ দেখা দিয়েছে । উদাহরণস্বরূপ ,যে সকল দল গোপনে তাদের অধিকার ও ভাগ্য নির্ধারণের জন্য যে সহিংসতামূলক পদক্ষেপ নেয় সেটা কি সন্ত্রাসের শামিল হবে ?
ফিলিস্তিনবাসীরা-যাদের ভূমি যায়নবাদী ইসরাইল কর্তৃক জবর-দখল হয়েছে এবং তারা তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে ,এই অবস্থায় তারা যে ইসরাইলীদের মোকাবিলা করছে এতে কি তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করছে এবং তারা কি অত্যাচারী ইসরাইলের কাছে আত্মসমর্পণ করবে ? এ ধরনের সহিংসতামূলক আচরণের উৎস সম্পর্কে অত্যাচারী ইসরাইল কিংবা অন্তত ঐ সকল সরকার যারা অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনী জনগণকে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তারা কী জানে ?
2. ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস
ইসলামের দৃষ্টিতে এ শব্দের অর্থ হচ্ছে কাউকে অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে হত্যা করা । ইসলামী ফিকাহ্শাস্ত্রের দৃষ্টিতে বলা যায় :
1. নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হারাম তা যে কোন দলের বা ধর্মের বা যে কোন স্থানেরই হোক না কেন । বর্তমান ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী 2001 সালের 11 সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হামলাকে ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেন । তিনি নির্বিচারে নিরীহ মানুষ হত্যা-হোক সে মুসলমান অথবা খ্রিস্টান বা অন্য কোন ধর্ম ও মতে বিশ্বাসী ,যে কোন স্থানেই হোক অথবা যে কোন অস্ত্রের মাধ্যমেই হোক-তা অ্যাটম বোমা বা দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ,জীবাণু অস্ত্র বা রাসায়নিক অস্ত্র অথবা যাত্রীবাহী ও জঙ্গি বিমানের মাধ্যমে এবং যে কোন প্রতিষ্ঠান ,রাষ্ট্র বা ক্ষমতাবান ব্যক্তির (প্রভাবশালী ব্যক্তিদের) দ্বারাই সংঘটিত হোক ,তা যে হারাম ও নিষিদ্ধ তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলেন : এরূপ হত্যাকাণ্ড জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি ,লেবাননের কানআ এবং সাবরা ও শাতিলা ,ফিলিস্তিনের দাইর ইয়াসিন অথবা বসনিয়া ও কসোভা ,ইরাক ,নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটন-যেখানেই ঘটুক তাতে কোন পার্থক্য নেই (অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই তা অন্যায় ও নিন্দনীয়) । এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে :‘
الایمان قید الفتک
’
অথবা‘
الفتک
الاسلام قید ’
ইসলাম গুপ্তহত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে । যদি ধরে নিই যে ,এ হাদীস সত্য ,তবে এটা শুধু এ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । যদিও সর্বসাধারণভাবে বর্ণিত এ হাদীসটির বিধান অন্য হাদীসের দ্বারা-যা পরবর্তীকালে আসবে-সীমাবদ্ধ হবে ।
2. যে সকল ব্যক্তি হত্যাযোগ্য অপরাধ করেছে এবং যাদের রক্তকে মূল্যহীন ঘোষণা করা হয়েছে সে সকল লোককে হত্যা করা ওয়াজিব । সম্ভবত তাদের অপরাধ মুসলমানদের ও ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা (যেমন কাফের র্হাবী বা যুদ্ধরত কাফের) অথবা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ,যেমন রাসূল (সা.) ও ইমামদের গালিগালাজ ও কুৎসা রটনা করা বা তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়া অথবা অত্যাচারী ও তাগুত সরকারকে সহযোগিতা করা-যদি তাদের হাতে অনেক মুসলমানের রক্ত ঝরে ।
এটা ইতিহাসের স্পষ্ট উদাহরণ যে ,রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান সৈন্যবাহিনী মক্কা শহরে প্রবেশের পূর্বেই সেনাপতিদের সকলকে ডেকে বললেন ,‘
আমি চাই কোন রক্ত ঝরানো ছাড়াই মক্কা জয় করতে ,তাই যে সকল লোক বাধা সৃষ্টি করবে তাদের ব্যতীত অন্যান্য লোককে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে । কিন্তু দশ জন বিশেষ অপরাধীকে যেখানেই পাবে ,এমনকি যদি তারা কাবা ঘরের পর্দাও ধরে থাকে তবুও তাদের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবে ।’
ঐ দশ জন হচ্ছে আকরামা ইবনে আবু জাহল ,হুব্বার ইবনে আসওয়াদ ,আবদুল্লাহ ইবনে সাদ আবিহ সারাহ্ ,মুকাইশ ছাবাবে লেইছি ,হুয়াইরেছ ইবনে নুফাইল ,আবদুল্লাহ ইবনে খাতল ,সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ,ওয়াহশী ইবনে র্হাব (হযরত হামযার হত্যাকারী) ,আবদুল্লাহ ইবনে আল-যুবাইর এবং হারেস ইবনে তালাতালাহ এবং চার জন মহিলা । এর মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা এবং দু’
জন গায়িকা যারা রাসূল (সা.)-কে তিরস্কার করে বিভিন্ন কুৎসিত গান গাইত ;এই সকল ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের আপরাধের সাথে জড়িত ও চক্রান্তকারী ছিল । রাসূল (সা.) তাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করেন ।
যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এ কাজের বাস্তবায়নের পদ্ধতি :
প্রথমত ,মূলত এ নির্দেশটি লুক্কায়িত ও গোপনীয় কোন বিষয় নয় । যখন মুসলমানদের সর্বোচ্চ নেতা নির্ণয় করবেন যে ,কোন ব্যক্তি বা দল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করছে বা ইসলামের নির্দিষ্ট কোন শাস্তি থেকে পলায়ন করছে বা ইসলামী শাসনের গণ্ডির মধ্যে নেই সে ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রকাশ্যে এ ধরনের নির্দেশ জারি করবেন । যেমনভাবে রাসূল (সা.) সেনাপতিদের মাধ্যমে সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন উল্লিখিত ব্যক্তিদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে ।
তাই যেমন মুসলমান সৈন্যবাহিনী জানত কোন্ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে ,অনুরূপ কাফেররাও জানত কোন্ ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ জারি করা হয়েছে ।
এ বিষয়টির অর্থ এই নয় যে ,ইসলামী শাসন জনগণকে তাদের নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করে বরং প্রাথমিক নীতি হচ্ছে সমস্ত জনগণের জান ,মাল ,সম্মান ও অন্যান্য অধিকার রক্ষা করা ফরয-তা যে কোন দল ,মাযহাব বা বিশ্বাসের লোক হোক না কেন ,যদি না সে কোন বিশ্বাসঘাতকতামূলক ও মারাত্মক অপরাধ করে । এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়েছে ।
হযরত ইমাম খোমেইনী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সালমান রুশদীর ব্যাপারে এ নির্দেশ জারি করেছিলেন এবং তিনি বলেন :‘
বিশ্বের সকল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানকে জানাচ্ছি যে ,‘
স্যাটানিক ভার্সেস’
বইয়ের-যা ইসলাম ,কোরআন এবং রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে লেখা এবং প্রকাশ করা হয়েছে-লেখক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে । বিশ্বের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানদের প্রতি আমার আবেদন যেখানেই তাকে পাবেন সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবেন যাতে আর কেউ ইসলামের অবমাননার সাহস না পায় । যদি কেউ এ পথে নিহত হন তিনি শহীদ হিসেবে গণ্য হবেন । যদি কেউ তাকে হাতের কাছে পায় ,কিন্তু তাকে হত্যা করার মতো শক্তি নেই ,তাহলে জনগণের কাছে তাকে যেন পরিচয় করে দেন যাতে সে তার নিকৃষ্ট আমলের প্রতিদান পায় ।’
যেমনভাবে বর্তমান রাহ্বার সহিংসতার বৈধতা ও অবৈধতার আলোচনায় স্পষ্টভাবে বলেন ,ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের হত্যার নির্দেশ ইসলামে আছে । কিন্তু যখনই কোন ইসলামী শাসক এ ধরনের পদক্ষেপ নেবে প্রকাশ্যে জনগণের মাঝে তা ঘোষণা করবে যাতে কোন বিষয় লুক্কায়িত না থাকে (যাতে গোপন হত্যা বলে বিবেচিত না হয় এবং এধরনের অপরাধীরা সতর্ক হয়ে যায় ও এরূপ কর্মের দুঃসাহস না দেখায়) ।
দ্বিতীয়ত ,যে সকল ক্ষেত্রে শাস্তির জন্য বেত্রাঘাত অথবা আহত করার প্রয়োজন আছে সেসব ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে (তবে নবী ও ইমামদের গালিগালাজ ও অবমাননাকারীদের ক্ষেত্রে এরূপ অনুমোদনের প্রয়োজন নেই) :
ক. এ বিষয়টি অবশ্যই ইসলামের বিজ্ঞ ও যুগসচেতন নেতার (অর্থাৎ নবী ,ইমামগণ এবং বর্তমানে গাইবাতের যুগে যোগ্য ফকীহ্ ও মুজতাহিদগণ) অনুমতিক্রমে হতে হবে ।
খ. যখন ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত ও এর মূল ক্ষমতা ন্যায়পরায়ণ ও বিজ্ঞ ফকীহর হাতে ন্যস্ত থাকবে তখন সরকারই এ ব্যবস্থা হাতে নেবে । কিন্তু যখন ইসলামী শাসন না থাকবে এবং রাষ্ট্র ওয়ালিয়ে ফকীহ্ দ্বারা পরিচালিত না হবে সে ক্ষেত্রে যে কোন একজন বিশিষ্ট ফকীহ মুজতাহিদের নির্দেশে তা হতে হবে ।
গ. এ ধরনের অনুমতি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির ওপর অর্পণ করা যেতে পারে । যেমন ইরানী বিপ্লবের সময় সাবেক তাগুত সরকারকে উৎখাত করার আন্দোলনের অনুমতি হযরত ইমাম খোমেইনী একদল আলেমের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন যাঁরা তাঁর অনুপস্থিতিতে এ কাজটি করেছেন । তিনি তাঁর বিরল প্রতিভা ও গভীর ফিকাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে ধর্মীয় ব্যুৎপত্তির অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে উপযুক্তদের মনোনীত করেছিলেন ।
তৃতীয়ত ,রাসূল (সা.) ,ইমামগণ এবং হযরত ফাতেমা (আ.)-কে গালিগালাজ করার শাস্তির বিধান আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে ।
মূলকথা হচ্ছে ,ইসলাম নিরপরাধ মানুষ হত্যার বিরোধী ,তা যে ভাবেই হোক না কেন-সন্ত্রাস বা অন্য কোন নামে অথবা রাজনৈতিক ও মাযহাবগত উদ্দেশ্যে এবং খ্রিস্টান বা ইহুদি বা মুসলমান যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন এবং তা বিশ্বের যে কোন স্থানেই হোক না কেন ;বরং এ কাজ হচ্ছে অপরাধ ;যে এ কাজ করবে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে ।
ইসলামী বিপ্লবের পূর্বে যে সকল হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তা ছিল দুই ধরনের:
ক. যে সকল হত্যাকাণ্ড এমন একদল বিপ্লবী ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়েছে যারা ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গী ও শরিয়তের বিধি-বিধানের প্রতি অনুগত ছিল এবং কোন মারজায়ে তাকলীদ বা উপযুক্ত সার্বিক যোগ্যতার অধিকারী মুজতাহিদের সাথে তাদের সম্পর্ক (অনুমোদন) ছিল।
এ ধরনের হত্যার পেছনে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের মুজতাহিদের ফতোয়া ছিল । কারণ ,চরম অনাচারী ও অপরাধী হিসেবে কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে হত্যা করা ওয়াজিব ছিল । সুতরাং শরিয়তের বিধান এরূপ হত্যাকে সমর্থন করেছে । কেননা ,সকল শর্তের অধিকারী মুজতাহিদের ফতোয়া ইসলামের বিধান অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য দলিল ।
খ. যে সকল হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘটেছে যার পেছনে শরিয়তের কোন বৈধতা বা মুজতাহিদের কোন ফতোয়া ছিল না । যেমন মুজাহিদিনে খাল্ক ও কম্যুনিস্টদের দ্বারা যে সকল হত্যাকাণ্ড ঘটেছে । তাদের ঐ সকল কাজের পেছনে শরীয়তের কোন বৈধতা ছিল না । তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এটা কখনই গ্রহণযোগ্য নয় ।
আশুরা ও ইরানের ইসলামী বিপ্লব
29 নং প্রশ্ন : কোন দলিলের ভিত্তিতে দাবি করেন যে ,ইরানের ইসলামী বিপ্লব ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলন ও শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত ? এ বিপ্লবের সফলতার পেছনে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলনের কি প্রভাব ছিল ?
উত্তর : ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সফলতার কারণ নিয়ে অনেক চিন্তাবিদ ও গবেষকই মতামত দিয়েছেন । তাঁদের মতে এ বিপ্লবের সফলতার মূল কারণ হচ্ছে
শিয়া মাযহাব ।
ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং নব-আধুনিকতাবাদের ( POST MODERNISM ) অন্যতম প্রবক্তা মিশেল ফুকো ইরানে ইসলামী বিপ্লবের কারণসমূহ পর্যালোচনা করতে গিয়ে এ বিপ্লবকে রাজনৈতিক আধ্যাত্মিক প্রবণতা দ্বারা উৎসারিত বলেছেন । তাঁর দৃষ্টিতে এ বিপ্লবের মাধ্যমে ইরানীরা তাদের অভ্যন্তরে এক ধরনের পরিবর্তনের চেষ্টায় ছিল । তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি , সমাজ , রাজনীতি এবং মানুষের চিন্তাতে এক ধরনের মৌলিক পরিবর্তন আনা । তারা এ সংস্কারের পদ্ধতি হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করেছে । ইসলাম তাদের জন্য এক দিকে ব্যক্তি-সমস্যার সমাধান ছিল অন্য দিকে সামাজিক ত্রুটি ও অসুস্থতার প্রতিকারক ।
আসেফ হোসেন তাঁর‘
ইসলামী ইরান : বিপ্লব ও প্রতি বিপ্লব’
গ্রন্থে লিখেছেন ,এ বিপ্লবকে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এর আদর্শগত উপাদান ,ইসলামবিরোধী পক্ষসমূহের ভূমিকা ,বৈধতার দিক ,শিক্ষাসমূহ ,বিশেষত নেতৃত্বের বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে ।
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. হামিদ আলগার তাঁর ইসলামী বিপ্লবের ভিত্তিসমূহ বইয়ে তিনটি উপাদানকে (শিয়া মাযহাব ,ইমাম খোমেইনীর নেতৃত্ব এবং ইসলামকে একটি আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন) এ বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন ।
অন্যদিকে ইসলামী বিপ্লব প্রতিষ্ঠা ও তা বাস্তব রূপ লাভের প্রক্রিয়ায় যে সকল রাজনৈতিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে ,আন্দোলনের নেতারা তাঁদের বক্তব্য ,বিপ্লবী ঘোষণা এবং স্লোগানে যা বলেছেন সেগুলো এটাই প্রমাণ করে যে ,এ বিপ্লবের মূল উপাদান হচ্ছে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলন ও শিক্ষা ।
আশুরার শিক্ষাসমূহ নিম্নরূপ :
1. শাহাদাতের সংস্কৃতি ।
2. বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার শিক্ষা ।
3. তাগুতের সাথে সংঘাত ও তাগুতকে নিশ্চিহ্ন করা ।
4. মহান আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জন এবং মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা ।
5. যুলুম ও অত্যাচারের প্রতিরোধ এবং সরকারের কর্মকাণ্ডকে সার্বক্ষণিক নজরে রাখা ও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের শিক্ষা ।
এই শিক্ষাসমূহ ইরানী ইসলামী বিপ্লব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং বিপ্লবকে রক্ষা করাও এই শিক্ষাসমূহের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ।
এখন বিস্তারিত তথ্যের জন্য আলোচনাকে কয়েক ভাগে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব ।
এক : ইসলামী বিপ্লবের উৎপত্তিতে আশুরা সংস্কৃতির প্রভাব
1. বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা ও উদ্দেশ্যের ওপর প্রভাব
ইসলামী বিপ্লব প্রতিষ্ঠার পেছনে ইরানের জনগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল যুলুম ,অত্যাচার ,স্বৈরতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের মূলোৎপাটন এবং ঐশী ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ও ইসলামী বিধি - বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং বহিঃশক্তির ওপর নির্ভরশীল হওয়া থেকে দূরে থাকা ও তাদেরকে বিতারিত করা - যা ইমাম হোসাইনের আন্দোলনেরও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল । তাই তিনি বলেন ,
انّا خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی
‘
আমি আমার নানার উম্মতকে সংশোধনের জন্য বের হয়েছি । আমি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে চাই এবং আমি আমার নানা ও পিতা আলী ইবনে আবি তালিবের পথে চলতে চাই ।’
ইয়াযীদ যেমন ফাসেক ,অত্যাচারী ও পাপাচারী ছিল ,পাহলভী বংশও ঠিক তেমনি ছিল । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ,রেযা শাহ ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার লক্ষ্যে ফারসি সালকে হিজরি থেকে পাহলভী সালে রূপান্তরিত করেছিল । ইমাম খোমেইনী (র.) ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আশুরার প্রভাব সম্পর্কে বলেন ,‘
ইমাম হোসাইন (আ.) আমাদের শিখিয়েছেন যে ,অন্যায় ,অত্যাচার ও যালেম শাসকদের বিরুদ্ধে আমাদের কী করতে হবে ।’
কিছু কিছু আলেম বিশ্বাস করেন যে ,ইমাম হোসাইন (আ.)-এর মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা । ইমাম খোমেইনী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন :‘
ইমাম হোসাইন (আ.)-এর জীবনের লক্ষ্য এবং ইমাম মাহদী (আ.) এবং সকল নবীর জীবনের লক্ষ্য একই ছিল । হযরত
আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী রাসূল (সা.) পর্যন্ত সকলেরই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারী শাসকের মোকাবিলা করা এবং ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা ।’
2. বিপ্লবের নেতার ওপর ইমাম হোসাইনের আন্দোলনের প্রভাব
ইমাম হোসাইন (আ.)-এর নেতৃত্ব এবং তাঁর সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ইমাম খোমেইনীর মতো নেতা ও বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে । ইরানী জনগণ ইমাম হোসাইন (আ.)-এর সাহসিকতা ,বীরত্ব ,দৃঢ়তা ,আপোসহীনতা এবং বিপ্লবী মনোভাবকে ইমাম খোমেইনী (রহ)-এর ব্যক্তিত্বে দেখতে পেয়েছিলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের একজন শাসকের যে সকল বৈশিষ্ট্য ইমাম হোসাইন (আ.) বর্ণনা করেছিলেন তার সবই তাঁর মধ্যে তারা পেয়েছিল । বিপ্লবীদের স্লোগান-‘
খোমেইনী ,খোমেইনী ,তুমি হোসাইনের উত্তরাধিকারী’
-এ কথাই প্রমাণ করে ।
3. সংগ্রামের পদ্ধতির ওপর আশুরার আন্দোলনের প্রভাব
বস্তুবাদী চিন্তাধারার মতে ,খালি হাতে অল্পসংখ্যক লোকের জন্য কখনই অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয় । কিন্তু ইরানী জনগণ ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়ে ইমাম হোসাইন (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের আত্মত্যাগের ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল । যখন ইরানী যুবকরা‘
আল্লাহু আকবার’
স্লোগান দিয়ে ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রসজ্জিত অত্যাচারী শাহ বাহিনীর মোকাবিলা করছিল তখন ইমাম খোমেইনী বলেন :‘
অল্প সংখ্যক লোককে কিভাবে স্বৈরাচারী শাসনের মোকাবিলা করতে হয় তা ইমাম হোসাইন (আ.) এ জাতিকে শিখিয়েছেন ।’
4. শোক পালনের স্থান ও দিনসমূহের প্রভাব
ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শোক পালনের দিন ও তাঁর জন্য শোকানুষ্ঠান পালনের স্থানসমূহ বিশেষ করে মসজিদ ,ইমামবাড়ি ও তাঁবুসমূহ বিপ্লবের কার্যক্রম পরিচালনা এবং জনগণকে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী পাহলভী শাসন সম্পর্কে অবহিত করার সর্বোত্তম কেন্দ্র ও মাধ্যম ছিল ।
তাদেরকে বিভিন্ন বিক্ষোভ মিছিলের জন্য একত্র করা ও ইমাম খোমেনীর বিপ্লবী বাণী তাদের কাছে পৌছানোর জন্য এ দিনগুলোকে বেছে নেয়া হত এবং এ দিনগুলোর স্মরণের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হত । বিশেষ করে মুহররম ও সফর এই দুই মাস বিপ্লব শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল বিশেষ করে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর স্মরণে তাসুয়া (নয় মুহররম) ও আশুরা (দশ মুহররম) ও দিন আয়োজিত সমাবেশগুলো অত্যাচারী শাহানশাহী রাজবংশের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল । সে সময় সাভাক (ইরানের নৃশংস গোয়েন্দা) বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা তাদের পর্যালোচনায় বলেছিল ,‘
যদি আমরা এই মুহররম ও সফর মাসকে অতিক্রম করতে পারি (বিপ্লবীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারি) তাহলে পাহলভী বংশ টিকে যাবে ।’
কিন্তু আমরা সকলেই দেখেছি যে ,1399 হিজরি সালে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের চল্লিশ দিন পালনের পর 2500 বছরের শাহানশাহী রাজবংশ এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হয় ।
দুই. ইরানী ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ে আশুরা সংস্কৃতির প্রভাব
এ বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে ,এর মূল ভিত্তি রচিত হয়েছিল ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শোক পালনের সময় এবং তা ছিল আশুরা আন্দোলনেরই শিক্ষা ।
1. 15ই খোরদাদের আন্দোলনটিও-যেটাকে বিপ্লবের সূচনা মনে করা হয়-আশুরার বিকাল বেলায় (13ই খোরদাদ ,1342 ফারসি সাল) ইমাম খোমেইনীর দৃঢ় কণ্ঠের বক্তব্যের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল । তিনি 15ই খোরদাদের আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন :‘
এ মহান জাতি আশুরা আন্দোলনের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে 15ই খোরদাদ এক গণ-বিস্ফোরণমুখী আন্দোলন করেছে । যদি আশুরার উদ্দীপনা ও বিপ্লবী মনোভাব জনগণের মধ্যে না থাকত তাহলে এ ধরনের আন্দোলন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া সফল করা সম্ভব হতো কি না নিশ্চিত করে বলা যায় না ।’
2. বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে 17ই শাহরিভার (ফারসি মাস)-যা আশুরার শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে । 17ই শাহরিভার আশুরার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে । শুহাদা চত্বর কারবালার প্রান্তরে এবং আমাদের শহীদরা কারবালার শহীদে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এ জাতির বিরোধিতাকারী ও তাদের সমর্থকরা ইয়াযীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ।
3. 1357 সালের 21শে বাহ্মান (10 ফেব্রুয়ারি ,1979) ইমাম খোমেইনীর ঐতিহাসিক ঘোষণা সামরিক বাহিনীর ভিত্তিকে ভেঙে দিয়েছিল ,যাদের পরিকল্পনা ছিল বিপ্লবের মূল নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করা এবং বিপ্লবকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলা ;বাস্তবে যা আশুরার কালজয়ী বিপ্লবের বিজয় হিসেবে অভিহিত হয়েছে ।
জনগণ বর্তমান যুগের হোসাইনের নির্দেশে রাস্তায় নেমেছিল ও শাহ্ বাহিনীর সকল চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল । এ সম্পর্কে ইমাম খোমেইনী (রহ) বলেন :‘
যদি ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলন না থাকত তাহলে আজকে আমরা বিজয় লাভ করতে পারতাম না । এক কথায় আমাদের বিপ্লব বিজয়ের মূল কারণ হচ্ছে ইমাম হোসাইন (আ.)-এর (আজাদারি) শোক অনুষ্ঠান পালন এবং এ অনুষ্ঠানসমূহই ইসলামকে প্রচার করেছে ও টিকিয়ে রেখেছে ।
তিন. ইসলামী বিপ্লব রক্ষায় আশুরা শিক্ষার প্রভাব
আশুরার শিক্ষা ও সংস্কৃতি শুধু বিপ্লব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রই প্রস্তুত করেনি ;বরং বিভিন্ন পর্যায়ে বিপ্লবকে রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।
ইসলামী বিপ্লব যে আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যদি তা রক্ষা করতে চায় তাহলে সেটাকে কারবালার শিক্ষা ও আদর্শের তথা আত্মত্যাগী মনোভাব ,স্বাধীনতার চেতনা ,আত্মসম্মানবোধ ,যুলুম ও অত্যাচারের প্রতিরোধ ,ইসলামী বিধি-বিধান লঙ্ঘনের বিরোধিতা ইত্যাদির ওপর দৃঢ় থাকতে হবে ।
রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ,যেমন পররাষ্ট্র নীতি ,অভ্যন্তরীণ ও স্বরাষ্ট্র নীতি ,অর্থনীতি ,সামাজিক ,রাজনৈতিক ,সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যেন ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আন্দোলনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভূত হয় ।
যদি ইসলামী বিপ্লব শত্রুদের সকল চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়ে সফলতায় পৌঁছে থাকে ,আট বছরের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে আমেরিকা ,সোভিয়েত ইউনিয়ন ,ফ্রান্স ,ইসরাইল ,ব্রিটেনসহ সকল পরাশক্তি ও বিশ্বের শক্তিধর দেশসমূহের সরাসরি সাহায্যপ্রাপ্ত সাদ্দামকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়ে থাকে ,ইসলামের শত্রুদের হুমকিকে ভ্রুকুটি দেখিয়ে বিপ্লবের অস্তিত্বকে দৃঢ়তর করে থাকে ,সাম্রাজ্যবাদীদের অপপ্রচারের মোকাবেলায় নিজেদের শক্তিশালী অবস্থানকে তুলে ধরে থাকে ,অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ,সামরিক অভ্যুত্থান কোন কিছুই বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ফাটল ধরাতে ব্যর্থ হয়ে থাকে ,এসবের পেছনে একটিই কারণ ,আর তা হলো আশুরার শিক্ষা এ জাতির মধ্যে পুরোদমে জাগ্রত ছিল ।
তাই এ পাহাড় টলায়মানকারী ষড়যন্ত্রগুলো এ জাতির অগ্রযাত্রায় বিন্দুমাত্র বিঘড়ব ঘটাতে পারেনি ।
এ সম্পর্কে ইমাম খোমেইনী বলেন :‘
মুহররমকে জীবিত রাখ । কেননা ,আমরা যা কিছু পেয়েছি এই মুহররম থেকেই পেয়েছি । যদি আমরা ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের গভীর তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই আজও সমগ্র বিশ্বে তার প্রভাব রয়েছে । যদি এ সকল আজাদারি ,শোক ও মাতম অনুষ্ঠান ,ওয়াজ-মাহফিল না থাকত আমরা জয়লাভ করতে পারতাম না । সকলেই ইমাম হোসাইন (আ.)-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে আন্দোলন করেছিল । ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় ইরানী যোদ্ধাদের (আত্মোৎসর্গী ভূমিকা ,চেতনামূলক বক্তব্যমালা ,শাহাদাতপূর্ব অন্তিম বাণী ,নামায ,কোরআন পাঠ ,দোয়া ও নফল ইবাদতের) যে চিত্রগুলো তখন ধারণ করা হয়েছে সেগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে ,তারা ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আদর্শে কীভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল ও তাঁর ভালোবাসায় যুদ্ধ ক্ষেত্রকে উষ্ণ রেখেছিল ।
তিনি অন্যত্র বলেন :‘
ইমাম হোসাইন (আ.)-এর আত্মত্যাগ ইসলামকে জীবিত রেখেছে... জেনে রাখ ,যদি তোমরা বিপ্লবকে রক্ষা করতে চাও তাহলে ইমাম হোসাইনের আন্দোলনকে রক্ষা কর ।
 0%
0%
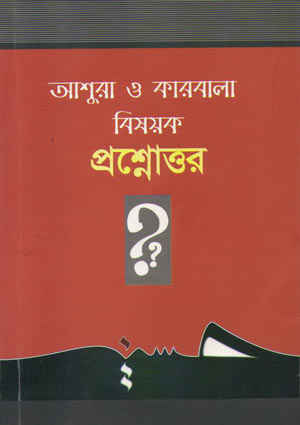 লেখক: লেখকবৃন্দ
লেখক: লেখকবৃন্দ