মানব -বিবর্তনের কাহিনী
মানবজাতির উৎস -
এটিই বিবর্তনবাদ ভক্তদের সর্বাধিক উত্থাপিত আলোচনার বিষয়। ডারউইনের সমর্থকগণ এই বলে দাবী করেন যে ,
এখনকার মানবজাতি কিছু গরিলা বা শিম্পাঞ্জী জাতীয় প্রাণী থেকে বিকশিত হয়েছে। কথিত এই বিবর্তন প্রক্রিয়া ৪৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল বলে দাবী করা হয় ;
আরো দাবী করা হয় যে ,
বিবর্তন প্রক্রিয়ার সময় এখনকার মানবজাতি তার ও তার পূর্বপুরুষদের মাঝামাঝি কোন
“
অন্তর্বর্তীকালীন রূপে
”
বিদ্যমান ছিল। সম্পূর্ণ কাল্পনিক এই রূপরেখা থেকে চারটি মৌলিক শ্রেণীর একটি তালিকা তৈরী করা যায় :
১ । অষ্টোলোপিথেকাস
২ । হোমো হেবিলিস
৩ । হোমো ইরেকটাস
৪ । হোমো সেপিয়েনস
বিবর্তনবাদীগণ তথাকথিত মানবজাতির পূর্বপুরুষের নাম রেখেছেন“
অষ্ট্রেলো পিথেকাস”
অর্থাৎ“
দক্ষিন আফ্রিকান বানর”
। প্রকৃতপক্ষে , এই জীবগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বানর বৈ কিছু নয়। ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে দুজন জগৎ বিখ্যাত এনাটমিষ্ট , লর্ড সলী যুকারম্যান এবং অধ্যাপক চার্লস অক্সনার্ড বিভিন্ন অষ্টোলোপিথেকাসের নমুনার উপর গবেষণা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে , এগুলো সাধারণ এক প্রকার গরিলা শ্রেণীর ; এরা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে আর মানবজাতির সাথে এদের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি।
বিবর্তনবাদীরা মানব বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়কে“
হোমো”
বা“
মানুষ”
নামে শ্রেণীকরণ করেছেন। তাদের দাবী অনুসারে হোমো শ্রেণীর জীবগুলো অষ্ট্রেলোপিথেকাসের চেয়ে উন্নতর পর্যায়ের। বিবর্তনবাদীরা এই প্রাণীগুলোর বিভিন্ন ধরণের জীবাশ্ম নিয়ে এদের নির্দিষ্ট বিন্যাসে সাজিয়ে এক অলীক বিবর্তন বিন্যাস বা পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। এই বিভিন্ন শ্রেণীগুলোর মাঝে বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বা এদের মাঝে বিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন প্রমাণ কখনো দাড় করানো যায়নি ; তাই এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বিংশ শতাব্দীতে বিবর্তন মতবাদের একজন অগ্রবর্তী সমর্থক আর্নস্ট মায়ার তার দীর্ঘ বিতর্ক নামক বইটিতে লিখেছেন যে ,“
হোমো সেপিয়েনস পর্যন্ত অগ্রসর চেইনটি হঠাৎ হারিয়ে গেছে।”
বিবর্তনবাদীগণ বিভিন্ন্ প্রজাতির মাঝে যোগসূত্র স্থাপনকারী এই চেইনটির রূপরেখা টেনেছেন এভাবেঃ অষ্ট্রেলোপিথেকাস > হোমো হেবিলিস > হোমো ইরেকটাস > হোমো সেপিয়েনস। এ চেইনটি থেকে বিবর্তনবাদীগণ দেখাতে চান যে ,এই প্রজাতিগুলোর প্রত্যেকে একে অপরের আদি পুরুষ। অবশ্য বিবর্তনবাদীদের সাম্প্রতিক কালের প্রাপ্ত তথ্য হতে এটা পকাশিত হয়েছে যে , অষ্ট্রেলোপিথেকাস , হোমো হেবিলিস আর হোমো ইরেকটাস পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে বিদ্যমান ছিল ।
তদুপরি , হোমো ইরেকটাস নামে শ্রেণীকৃত মানুষের একটি নির্দিষ্ট অংশ এখনও আধুনিক কাল পর্যন্ত বসবাস করে আসছে। হোমো সেপিয়েনস নিনদারথেলেনসিস ও হোমো সেপিয়েনস (আধুনিক মানুষ) একই সঙ্গে একই অঞ্চলে বসবাস করছিল ।
এ অবস্থা সুস্পষ্টভাবেই , প্রজাতিগুলোর একজন আরেকজনের উত্তরসূরী-এ দাবীটি দূর্বল করে দেয়। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জীবাশ্মবিদ , ষ্টীফেন জে গুল্ড , নিজে একজন বিবর্তনবাদী হয়েও বিবর্তন থিওরীর এই অচলাবস্থার ব্যাখ্যা করেছেন :
আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ধাপ কি হতে পারে যদি তিনটি হোমিনিড বংশানুক্রম (এ.আফ্রিক্যানাস , বিশাল অষ্ট্রেলোপিথেসিনস , আর এইচ. হেবিলিস) একই সঙ্গে বর্তমান থাকে আর স্পষ্টভাবে কেউই একজন আরেকজন থেকে জন্ম নেয়নি ? অধিকন্তু , পৃথিবীতে থাকাকালীন অবস্থায় এই তিনটি হোমিনিডের কেউই বিবর্তনের কোন প্রবণতাই দেখায়নি ।
সংক্ষেপে বললে , মানব বিবর্তনের গল্পটি চালু রাখতে“
অর্ধেক বানর , অর্ধেক মানুষ”
এমনতর প্রাণীর বিভিন্ন ছবি এঁকে তা প্রচার মাধ্যম ও কোর্স বইতে হাযির করা হয় ; খোলাখুলি বলতে গেলে এগুলো নিছকই প্রচারণার মাধ্যমে করা হয়-যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিবিহীন একটি গল্প ছাড়া আর কিছুই নহে ।
ইংল্যান্ডের সবচেয়ে প্রখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীদের মাঝে অন্যতম একজন লর্ড সলী যুকারম্যান এই বিষয়টির উপর বছরের পর বছর গবেষনা চালিয়েছেন , বিশেষ করে অষ্ট্রেলোপিথেকাসের উপর ১৫ বছর ধরে কাজ করার পর নিজে একজন বিবর্তনবাদী হয়েও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ,“
সত্যি বলতে কি , বানর সদৃশ প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত কোন বংশ তালিকার অস্তিত্ব নেই ।”
যুকারম্যান একটি আকর্ষণীয়“
বিজ্ঞানের পরিসরও”
তৈরী করেছিলেন। তার মতে যা সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক তা থেকে শুরু করে যা সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক সে পর্যন্ত বিস্তৃত এই পরিসরটি তিনি গঠন করেন। এই পরিসরের প্রথম সারিতে থাকে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো অর্থাৎ রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান - যেগুলো কিনা বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ডাটা ফিল্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর পর আসে জীব সম্প র্কিত বিজ্ঞান এবং তারপর সমাজ বিজ্ঞান। এই পরিসরের একদম শেষের দিকে আসে সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক বলে ধারণা করা হয় যে অংশগুলোকে , যেগুলো হলো :“
অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধি”
যেমন টেলিপ্যাথি ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং পরিশেষে আসে“
মানব বিবর্তন”
। যুকারম্যান তার যুক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :
আমরা তখন ঠিক বস্তুনিষ্ঠ সত্যের তালিকা থেকে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধি কিংবা মানুষের ফসিলের ইতিহাসের ব্যাখ্যার মতো অনুমান নির্ভর জীব বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর দিকে সরে যাই , যেখানে একজন বিশ্বাসী [বিবর্তনবাদী] লোকের কাছে সবকিছুই সম্ভব বলে বিবেচিত হয়-আর যেখানে [বিবর্তনে] অতি ভক্তরা কখনো কখনো একই সময়ে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন ব্যাপারও বিশ্বাস করতে সক্ষম হয় ।
মানবজাতির বিবর্তনের গল্প গুটিকয়েক অন্ধ বিবর্তনবাদ ভক্ত ব্যক্তি কর্তৃক মাটি খুঁড়ে তুলে আনা ফসিলের পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যাই দিয়েছে শুধু , কোন সফলতা খুঁজে পায়নি ।
মানব বিবর্তনকে সমর্থন করার জন্য কোন ফসিল নেই। উল্টো ফসিল রেকর্ড প্রদর্শন করছে যে , বানর ও মানুষের মাঝে একটি দুস্তর-বাধা রয়েছে। এই সত্যটির সম্মুখীন হয়ে বিবর্তনবাদীরা নির্দিষ্ট কিছু চিত্র আর মডেলের উপর তাদের আশা রাখেন। ফসিলের উপর তারা মুখাবরণ পরিয়ে দেন এলোপাতারিভাবে। আর অর্ধ -বানর আর অর্ধমানুষের মুখাবয়ব জোড়া লাগান।
চক্ষু ও কর্ণের টেকনোলজী
চোখ ও কানের অসাধারণ উপলব্ধি ক্ষমতা হলো আরেকটি বিষয়-যা সম্পর্কে বিবর্তন থিওরী নিরুত্তর থেকে যায় ।
চক্ষু সম্পর্কিত বিষয়ে যাওয়ার আগে চলুন ,“
আমরা কি প্রক্রিয়ায় দেখতে পারি ?”
-এই প্রশ্নটির একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করি। কোন একটি বস্তু হতে আগত আলোক রশ্মি চোখের রেটিনার ( অক্ষি গোলকের সর্ব পিছনের স্তর ) উপর গিয়ে ঠিক উল্টোভাবে পতিত হয়। এখানে পতিত আলোক রশ্মিগুলো কিছু কোষের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তরিত -হয় এবং পরে তারা“
দৃষ্টির কেন্দ্র”
নামে মস্তিস্কের পশ্চাৎদিকের একটি ছোট এলাকায় গিয়ে পৌচ্ছে। মস্তিস্কের -কেন্দ্রে এই ইলেকট্রিক সিগন্যাল গুলো বিভিন্ন ধারাবাহিক পরিবর্তনের পর একটি ইমেজ বা প্রতিবিম্ব হিসেবে গৃহীত হয়। চলুন , এই টেকনিক্যাল পটভূমি সম্পর্কে আমরা কিছু চিন্তা ভাবনা করে দেখি।
মস্তিষ্ক আলো থেকে সম্পূর্ণ রূপে সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। তার মানে হলো যে , মস্তিস্কের -ভিতর ভাগটা ঘন অন্ধকার আর যে জায়গাটিতে মস্তিষ্ক থাকে সেখানে আলোক পৌছে না।“
দর্শনের কেন্দ্র”
নামক স্থানটি একটি ঘন অন্ধকার জায়গা যেখানে কখনো আলো পৌছে না ; এমনকি এটি আপনার জানা সমস্ত জায়গা সমূহের মাঝে সবচেয়ে অন্ধকার জায়গাও হতে পারে। যাই হোক , আপনি এই ঘন কালো অন্ধকারের মাঝেই একটি উজ্জ্বল আলোকিত জগৎ দেখতে পান।
চোখে তৈরী ইমেজ এত তীক্ষ্ম ও পরিষ্কার যে এমনকি বিংশ শতাব্দীর টেকনোলজিও তা অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ , আপনি আপনার বইটির দিকে তাকান , যে হাতগুলো দিয়ে বইটি ধরে আছেন সেগুলোর দিকেও তাকান , তারপর আপনার মাথা উঠিয়ে আপনার চার পাশে লক্ষ্য করুন। আপনি কি কখনো অন্য কোথাও এটির মতো এমন তীক্ষ্ম ও স্বচ্ছ ইমেজ দেখেছেন ? এমনকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেলিভিশন নির্মাতাদের তৈরী সবচেয়ে প্রাগ্রসর টেলিভিশন পর্দাও আপনার জন্য এমনতর তীক্ষ্ম ইমেজ তৈরী করতে পারে না। এটি হলো ত্রিমাত্রিক , রঙ্গিন আর অত্যন্ত স্পষ্ট ইমেজ। একশ বছরেরও বেশী সময় ধরে এমনতর স্বচ্ছতা অর্জন করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়র । কারখানা , বড় বড় জায়গা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে , অনেক গবেষনা করা হয়েছে , এই উদ্দেশ্যে বহু পরিকল্পনা ও ডিজাইন করা হয়েছে। আবার টি ভি পর্দা এবং আপনার হাতে ধরা বইটির দিকে তাকান। তীক্ষ্মতা ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আপনি বিরাট এক পার্থক্য খুঁজে পাবেন। অধিকন্তু , টেলিভিশন পর্দা আপনাকে দ্বিমাত্রিক ছবি প্রদর্শন করে , যেখানে আপনার চোখ দিয়ে গভীরতাসহ একটি ত্রিমাত্রিক ছবি আপনি দেখতে পান।
বহু বছর ধরে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার একটি ত্রিমাত্রিক টেলিভিশন তৈরীর আর চোখের সমান দর্শন গুণ অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। হ্যাঁ
,
তারা ত্রিমাত্রিক একটি টেলিভিশন সিস্টেম আবিষ্কার করেছেন বটে ;
তবে তা একটি কৃত্রিম ত্রিমাত্রা মাত্র। পশ্চাৎপটটি অধিকতর ঘোলাটে ,
পুরোভূমিটি একটি পেপার
সেটিং এর মতো দেখা যায়। চোখের ন্যায় স্বচ্ছ
আর পরিষ্কার ছবি তৈরী করা কখনো সম্ভব হয়ে উঠেনি। ক্যামেরা ও টেলিভিশন উভয় ক্ষেত্রেই ইমেজ কোয়ালিটি হ্রাস পেয়েছে।
যে পদ্ধতিটি এই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছবি তৈরী করে তা হঠাৎ করেই গঠিত হয়েছে বলে বিবর্তনবাদীগণ দাবী করেন। এখন যদি কেউ আপনাকে বলেন যে আপনার কক্ষের টেলিভিশনটি আকস্মিক সম্ভাবনার একটি ফলাফল , এর সমস্ত পরমাণুগুলো হঠাৎ করেই এক সঙ্গে আসতে লাগল আর ইমেজ তৈরী করার এই যন্ত্রটি তৈরী করল , আপনি কি ভাববেন ? হাজারো লোক যা পারে না , তা কিভাবে পরমাণুগুলো সম্পন্ন করতে পারে ?
যে যন্ত্র চোখের তৈরী ছবির তুলনায় সাদামাটা সেকেলে ছবি তেরী করে তা যদি যুগপৎ সম্ভাবনায় তৈরী না হতে পারে তাহলে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে , চোখ এবং চোখ দ্বারা দৃষ্ট ছবি হঠাৎ করেই সৃষ্টি হতে পারতো না। কানের বেলায়ও একই পরিস্থিতি খাটে। বহিঃকর্ণ অরিকলের মাধ্যমে শব্দ গ্রহন করে তা মধ্যকর্ণের দিকে পরিচালিত করে ; মধ্যকর্ণ শব্দ কম্পনকে আরো তীব্রতর করে অন্তঃকর্ণে প্রেরণ করে ; অন্তঃকর্ণ এই শব্দ কম্পনগুলোকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিণত করে মস্তিস্কে পাঠায়। ঠিক চোখের মতোই মস্তিস্কের -শ্রবণ কেন্দ্রে শ্রবণ কাজটি সম্পন্ন হয়।
চোখের পরিস্থিতিটি কানের বেলায়ও সত্য। অর্থাৎ ব্রেইন যেমন শব্দ থেকে সংরক্ষিত , ঠিক তেমনি করে আলো থেকেও সংরক্ষিত : কোন প্রকার শব্দকে তা ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। সুতরাং বহির্জগৎ যতোই কোলাহলপূর্ণ হোক না কেন , মস্তিস্কের -ভেতরভাগে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করে। তথাপি তীক্ষ্মতম শব্দগুলো মস্তিস্কের -ভেতরেই উপলব্ধি করা হয় । শব্দ থেকে সংরক্ষিত আপনার এই মস্তিস্কে আপনি শুনতে পান অর্কেষ্ট্রার ঐকতান আর জনবহুল জায়গার সমস্ত শব্দই আপনার মস্তিস্ক শ্রবণ করে। অবশ্য যদি ঠিক সেই মুহূর্তে কোন সঠিক যন্ত্র দিয়ে আপনার মস্তিস্কের -শব্দ মাত্রা মেপে দেখা হতো তবে দেখা যেতো যে ঐ এলাকায় পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে।
ঠিক চিত্রকল্পের বেলায় যেমনটি হয়েছে , তেমনি মূল শব্দের ন্যায় যথাযথ শব্দের উৎপাদন আর পুণরুৎপাদনের চেষ্টায় দশক দশকের সাধনা ব্যয় করা হয়েছে। এ সমস্ত প্রচেষ্টারই ফলাফল হলো-সাউন্ড রেকর্ডার , হাই ফাই আর শব্দের অর্থ বুঝার সিস্টেম। সমস্ত টেকনোলজীর প্রয়োগ ,আর এই প্রচেষ্টায় সহস্র সহস্র ইঞ্জিনিয়ার আর এক্সপার্টগণ কাজ চালিয়ে যাওয়া সত্বেও মানুষের-কান দিয়ে শ্রুত শব্দের সমান তীক্ষ্মতা ও স্পষ্টতাসম্পন্ন শব্দ তৈরী করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। মিউজিক ইনডাষ্ট্রিতে সবচেয়ে বৃহৎ কোম্পানিগুলোর তৈরী সবচেয়ে উঁচু মানের গুণসম্পন্ন হাইফাইগুলোর কথা ভাবুন । এমনকি এই যন্ত্রগুলোয় যখন শব্দ রেকর্ড করা হয় তখন শব্দের কিছু গুণ হারিয়ে যায় ; কিংবা যখন আপনি হাইফাই টি অন করেন , তখন মিউজিক শুরু হওয়ার আগে হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পাবেন। যাই হোক , মানব দেহের টেকনোলজীর মাধ্যমে উৎপন্ন শব্দগুলো অত্যন্ত তীক্ষ্ম আর পরিষ্কার। মানুষের কান কখনো শব্দ শোনার সময় হাইফাই এর মতো হিস্ হিস্ শব্দ কিংবা আবহতড়িৎ জনিত পট্ পট্ শব্দ শোনে না ; মানুষের কান শব্দটি স্বাভাবিকভাবে যেমন ঠিক তেমনিরূপে শুনে থাকে , ঠিক তেমনি তীক্ষ্ম আর স্বচ্ছ । মানুষের জন্ম লগ্ন হতে এটা এমনিভাবেই হয়ে আসছে ।
এ পর্যন্ত , সেন্সরি ডাটা উপলব্ধির ব্যাপারে মানুষের কান ও চোখ যেমন সুবেদী (সুক্ষ্ম পরিবর্তন ধরতে সক্ষম) আর সফল , মানুষ তেমনতর কোন দৃষ্টি সম্বন্ধীয় কিংবা কোন রেকর্ডিং যন্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়নি।
যাই হোক , দর্শন আর শ্রবণের ব্যাপারে সমস্ত কিছুর বাইরেও এক বিরাট সত্য নিহিত রয়েছে ।
যে চেতনাটি দর্শন ও শ্রবণ করে থাকে-সেটি কার ?
মস্তিস্কের ভেতর কে মোহময় পৃথিবী দর্শন করে , কে শোনে ঐকতান আর পাখির কিচির মিচির , আর কেইবা গোলাপের সুবাস নেয় ?
মানুষের চোখ , কান আর নাক থেকে আগত উত্তেজনা বা উদ্দীপনা ভ্রমন করে বৈদ্যুতিক রাসায়নিক স্নায়বীয় তারণা হিসেবে মস্তিস্কে গিয়ে পৌছে । কিভাবে মস্তিস্কে এই ইমেজগুলো তৈরী হয় এ সম্পর্কে বহুবিধ বর্ণনা আপনি বায়োলজী , ফিজিওলজি আর বায়োকেমিষ্ট্রি বইতে খুঁজে পাবেন। কিন্তু আপনি কখনও এ বিষয়টি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য খুঁজে পাবেন না : কে সেই জন যে মস্তিস্কে এই বৈদ্যুতিক রাসায়নিক স্নায়বীয় উত্তেজনাগুলোকে ছবি , শব্দ , ঘ্রাণ কিংবা স্নায়বীয় ঘটনা হিসেবে উপলব্ধি করে থাকে ? মস্তিস্কের ভেতরে একটি চেতনা থাকে , যে চোখ , কান , নাকের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই সমস্ত জিনিস উপলব্ধি করে থাকে। এই চেতনাটি আসলে কার ? কোন সন্দেহ নেই যে , এটি মস্তিস্ক গঠনকারী নার্ভ বা স্নায়ু , চর্বি স্তর কিংবা স্নায়ু কোষের নয়। এ কারণেই ডারউইন সমর্থক বস্তুবাদীগণ - যারা সবকিছু বস্তু দিয়ে তৈরী বলে বিশ্বাস করেন , তারা কখনও এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারেন না ।
এই সচেতনতাবোধটি আসলে আত্মা বা স্পিরিটের-যাকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। ছবি দেখার জন্য আত্মাটির চোখ লাগেনা কিংবা শব্দ শুনতে কানের দরকার পড়ে না। উপরন্ত , চিন্তা ভাবনা করতে তার কোন মস্তিস্কের -দরকার হয় না।
যিনিই এই স্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক সত্যটি পড়বেন , তারই উচিত হবে আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করা , তাঁকেই ভয় করা , আর তারঁই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। তিনিই মস্তিস্কের -মাত্র কয়েক ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের আলকাতরা কালো জায়গটিতে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ড কে ত্রিমাত্রিক , বর্ণিল , ছায়াময় আর আলোকোজ্জ্বল রূপে সংকুচিত ও ছোট করে আনেন ।
বস্তুবাদী বিশ্বাস
এতক্ষণ আমরা যে তথ্য উপস্থাপন করেছি , তা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে , বিবর্তন থিওরী এমনি একটি দাবী , যার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের পাওয়া তথ্যের স্পষ্টভাবেই কোন সাদৃশ্য নেই। প্রাণীর উৎপত্তি সম্পর্কে থিওরীটির দাবী বিজ্ঞানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ , এর প্রস্তাবিত বিবর্তনের পদ্ধতিগুলোর বিবর্তন ঘটানোর কোন ক্ষমতাই নেই , আর ফসিলগুলো প্রমাণ করছে যে , মতবাদটির জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্বর্তীকালীন আকার বা গঠনের কোন প্রাণী কখনও বিদ্যমান ছিল না ; তাই বিবর্তন থিওরীকে অবৈজ্ঞানিক ডাটা বলে পরিত্যাগ করাই বাস্তব । এমনভাবে তা করা উচিত যেমনভাবে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বব্রহ্মান্ডের মডেলটি বিজ্ঞানের আলোচ্য সূচী হতে বাদ দেয়া হয়েছে ।
কিন্তু
তবুও বিজ্ঞানের আলোচ্যসূচীতে বিবর্তন মতবাদকে সাগ্রহেই বহাল রাখা হচ্ছে। কিছু কিছু লোক এমনকি থিওরীটির সমালোচনা গুলোকে
“
বিজ্ঞানের প্রতি আক্রমন
”
হিসাবে উপস্থাপনার প্রয়াস চালায় । কিন্তু
কেন ?
কারণটি হলো , বিবর্তন মতবাদ একই সূত্রে গাঁথা (একই মতালম্বী) কিছু লোকের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় অন্ধ বিশ্বাস। এরা অন্ধভাবে বস্তুবাদ দর্শনের অনুরক্ত , আর তারা ডারউইনবাদকে এজন্য সমর্থন করে কেননা এটাই একমাত্র বস্তুবাদী ব্যাখ্যা যা প্রকৃতিতে ব্যবহারের জন্য সহজেই পেশ করা যায়।
যথেষ্ট কৌতুহলের ব্যাপার যে , তারা আবার সময়ে সময়ে এ সত্যটি স্বীকারও করে থাকে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একজন প্রখ্যাত জীন তত্ত্ববিদ , খোলাখুলি বিবর্তনবাদী হিসেবে পরিচিত , রিচার্ড সি লিওনটিন স্বীকার করেছেন যে তিনি“
সর্বাগ্রে একজন বস্তুবাদী এবং তারপর একজন বিজ্ঞানী”
। তিনি বলেন :
এটা এমন নয় যে , বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর বস্তুবাদ ব্যাখ্যা গ্রহনে কোন ভাবে বাধ্য করেছে , বরং , উল্টো , পার্থিব জিনিসের প্রতি আমাদের নিজেদের প্রধান মোহ থাকার কারণে আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার সরঞ্জাম ও কিছু ধারণার সেট তৈরী করতে বাধ্য হয়েছি যেগুলো বস্তুগত ব্যাখ্যা প্রদান করে , তা যতোই হোক অন্তর্জ্ঞানের পরিপন্থী কিংবা যতোই ধাঁধাঁ লাগানো হোক তা অদিক্ষীতদের জন্য-তাতে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। অধিকন্তু বস্তুবাদই আসল ও সবকিছ , তাই আমরা আমাদের দোরগোড়ায় স্বর্গীয় পদচারণা মেনে নিতে পারি না।”
এই সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলো এটাই প্রমাণ করে যে , শুধুমাত্র বস্তুবাদ দর্শনে আসক্ত থাকার কারণেই ডারউইনবাদ নামক এক ধরণের অন্ধ বিশ্বাসকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। এই বিশ্বাসটি এটাই বলতে চায় যে ,“
বস্তু ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই”
। তাই এই মতবাদে তর্ক করে বলা হয় যে ,“
জড় ও অচেতন বস্তু থেকেই প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছে”
।
পাখি , মাছ , জিরাফ , বাঘ , পোকামাকড় , বৃক্ষ , ফুল , তিমি ও মানবজাতি-এ ধরণের মিলিয়ন মিলিয়ন প্রজাতিসমূহ জড় পদার্থ থেকে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া -প্রতিক্রিয়া , যেমন বৃষ্টিধারা ,বজ্রপাত ইত্যারি ফলস্বরূপ জন্ম নিয়েছে-এটাই জোর দিয়ে প্রচার করে যাচ্ছে মতবাদটি। এটা যুক্তি ও বিজ্ঞান উভয়ের পরিপন্থি এক ধরণের অনুশাসন। তথাপি , ডারউইনবাদীগণ এ মতবাদটি সমর্থন করেই যাচ্ছে যেন তাদের“
দোরগোড়ায় স্বর্গীয় পদচারনা মেনে নিতে”
না হয়।
যারা বস্তুবাদে পক্ষপাত নিয়ে প্রাণের উৎপত্তি বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত না করবেন তারাই এই পরিষ্কার সত্যটুকু দেখতে পারবেন : সকল জীব একজন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কর্ম , যিনি সর্বশক্তিমান , সর্বজ্ঞানী এবং সবজান্তা। এই স্রষ্টাই হলেন আল্লাহ-যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থাথেকে বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করেছেন
,
এর ডিজাইন করেছেন অত্যন্ত নিখুঁতরূপে আর সকল জীবের আকার দিয়েছেন।
তারা বলল : আপনি পবিত্র। আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত জ্ঞানময় , প্রজ্ঞাময়।
চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল্লাহ সোবহানাল্লাহু তাআলা মানবজাতির পথচালিকা স্বরূপ কোরআন প্রেরণ করেছিলেন। এ স্বর্গীয় গ্রন্থখানা দৃঢ়ভাবে সমর্থন আর অনুসরণ করে মানবজাতি যেন সঠিক পথে পরিচালিত হয় এ আহ্বান করেছিলেন তিনি। নাযিল হওয়ার দিন থেকে শুরু করে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এ স্বর্গীয় আর সর্বশেষ বইখানা মানবজাতির জন্য একমাত্র পথচালিকা হিসেবে থেকে যাবে।
পবিত্র কোরআনের অসমকক্ষ আর অতুলনীয় রচনাশৈলী এবং এর মাঝে বিদ্যমান প্রকৃষ্ট , গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে এটি মহান আল্লাহ তাআলার বাণী। এ ছাড়াও কোরআনের এমন বহু অলৌকিক বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে এটি পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলারই নাযিলকৃত গ্রন্থ।
এ সমস্ত গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যাদির একটি হলো
অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক যথার্থতা বা সত্যতা আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছিল -
যেগুলো কিনা আমরা সেদিন বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিমালা দিয়ে আবিষ্কার বা সন্ধান করতে সক্ষম হয়েছি। -
অবশ্যই কোরআন কোন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নয়। কিন্তু
এরপরও বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু বিষয়াদি এ গ্রন্থটিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রূপে ও সারগর্ভ হিসেবে বর্ণিত রয়েছে -
যেগুলো বিংশ শতাব্দীর টেকনোলজী বা প্রযুক্তির মাধ্যমে কেবল সেদিন মানব জাতির সমক্ষে উন্মোচিত হয়েছে। কোরআন যখন নাযিল হয় ,
সে সময় এ বিষয়গুলো ছিল অজানা ,
এটি আরো প্রমাণ করে যে কোরআন আল্লাহর বাণী।
 10%
10%
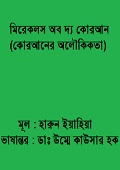 লেখক: হারুন ইয়াহিয়া
লেখক: হারুন ইয়াহিয়া





