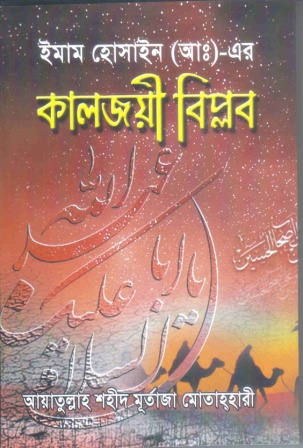আলেম সমাজের দৃষ্টিতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ
ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনে‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের’
উপস্থিতি এই আন্দোলনকে যেমন একটা মহান আদর্শে পরিণত করেছে ঠিক তেমনিভাবে এ আন্দোলন,‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
কে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলেছে। ইসলামের এই রোকন ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনকে শুধু ইসলামী বিপ্লবের শীর্ষেই আসন দান করেনি,বরং যুগ যুগ ধরে বিপ্লবী মুসলমানদের জন্যে অনুকরণীয় আদর্শে রুপান্তরিত করেছে। তেমনিভাবে হোসাইনী আন্দোলনও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে ইসলামের মূল ভিত্তি গুলোর প্রথম সারিতে স্থান করে দিয়েছে।
এখানে হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে,এটা কীভাবে সম্ভব? ইমাম হোসাইন (আ.) আবার ইসলামের কোনো রোকন বা ভিত্তিকে গুরুত্ববহ কিংবা গুরুত্বহীন করে দিতে পারেন নাকি?
উত্তরে বলতে হয় যে উপরোক্ত বক্তব্যে আমরা এ রকম কিছু বলতে চাইনি। কেননা ইসলামের কোন রোকন বা ভিত্তিকে গুরুত্ববহ কিংবা গুরুত্বহীন করার কাজ ইমাম হোসাইনের (আ.) নয়-স্বয়ং রাসূলুল্লাহরও (সা.) নয়। এটা একমাত্র আল্লাহর কাজ। মহান আল্লাহ তার দীনকে যে সব ভিত্তি র উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেগুলোর প্রত্যেকটির একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় গুরুত্ব ও মূল্য রয়েছে এবং এ গুরুত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে। বরং উপরের বক্তব্যে যেটা বলতে চেয়েছি তা হলঃ হোসাইনী আন্দোলনের পর আলেম সমাজ তথা সমগ্র মুসলিম সমাজই‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা এবং এর সঠিক গুরুত্ব নিরূপণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ব্যাপারটা আরও একটু ব্যাখ্যা করলে ভাল হবে। প্রতিটি জিনিসের দুটো অবস্থান রয়েছেঃ
এক
: ঐ বস্তুর সত্বাগত বা প্রকৃত অবস্থান।
দুই
: পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থান।
মনে করুন একটি শহরে কয়েক জন ডাক্তার আছে। এদর মধ্যে সবাই কিন্তু একমানের নয়। কেউ হয়তো সত্যিই দক্ষ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারর। আবার কেউ হয়তো এখনো এ পেশায় একবারে নতুন এবং কাচা। ডাক্তারদের মধ্যকার এই গুণ ও মানগত পার্থক্য একমাত্র ডাক্তাররাই বুঝতে পারেন। সাধারণ মানুষের কাছে এই গুণ ও মান তেমন বিচার্য়যর বিষয় নয় এবং তা নির্ণয় করাও তাদের পক্ষে সহজ কাজ নয়। তাদের চোখে সবাই ডাক্তার,সবাই সমান। কখনো কখনো দেখা যায়,শুধু যে ডাক্তারের প্রচারের জোর যত বেশী,যার কথা জনগণের কানে বেশী বেজেছে,সত্যিকার অর্থে সে যদি একজন তৃতীয় শ্রেণীর ডাক্তারও হয় তবু জনগণ তাকেই বড় ডাক্তার বলে মনে করে। অথচ হয়তো কত প্রথম শ্রেণীর দক্ষ ডাক্তার রয়েছেন যাদের প্রচারের জোর নেই। জনগণের কাছে তারা একান্তই অবহেলিত।
এ উদাহরণে আমরা দেখতে পেলাম যে,একজন ডাক্তার সত্যিকার অর্থেই একজন অভিজ্ঞ এবং ঝানু ডাক্তার হয়েও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়ে তিনি অবহেলিত এবং অপরিচিত ডাক্তার হিসেবে পরিগণিত হলেন।
ইসলামেও তেমনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রোকন রয়েছে। ইসলামে নামায,রোযা,হজ্ব,যাকাত ইত্যাদি রোকনগুলোর মত‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি । কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে,নামায রোযা আর হজ্ব এগুলো নিয়ে মুসলমানরা মশগুল হয়ে পড়েছে। ক্রমে ক্রমে ইসলামের অন্য ভিত্তি গুলো একবারে ভুলেই গিয়েছে। অথচ নামায কিংবা রোযার মত‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
-এর গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। একমাত্র বিজ্ঞ ব্যাক্তিরাই বুঝতে পারেন যে,ইসলামের এই ভিত্তি গুলোর প্রতিটিই কত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমরা যে বললাম,ইমাম হোসাইন (আ.)‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নহী আনীল মুনকার’
কে উন্নীত করেছেন -একথার অর্থ হলো ইমাম ইসলামের এই ভিত্তিকে ইসলামী বিশ্বে উন্নীত করেছেন,খোদ ইসলামে নয়। খোদ ইসলামের কোনো কিছু যোগ-বিয়োগ করার কাজ একমাত্র আল্লাহর।
মহান আল্লাহ দীন ইসলামের প্রতিটি ভিত্তি কে নির্দিষ্ট মাত্রায় গুরুত্ব ও দিয়েই প্রেরণ করেছেন। কিন্তু মুসলিম সমাজ কি ইসলামের এই ভিত্তিগুলোর প্রত্যেকটির যে প্রকৃত মূল্য আল্লাহ দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই মূল্যায়ন করে? হয়তো ঐরকম নাও করতে পারে। শুধু তাই নয়। কখনো কখনো হয়তো যেমন আছে তার উল্টোটাই ধরে নেয়। ইসলামে যে ভিত্তি প্রথম শ্রেণীর মূল্যবহ তাকে হয়তো তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলতে পারে আর তৃতীয় শ্রেণীর কোনো ভিত্তি কে প্রথম শ্রেণীতে নিয়ে আসতে পারে।
ইসলামের ভিত্তি গুলো যদি উল্টো পাল্টা হয়ে যায়,তবে ইসলাম তখন উপহাসের পাত্রে পরিণত হবে। শ্রেষ্ঠধর্মের মর্যাদা হারাবে। যেমন ধরুন চুল এবং দাঁড়ি আচড়ানো সুন্নত। কিন্তু এটা যদি‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
-এর চেয়ে বেশী গুরুত্ব ও মূল্য লাভ করে তাহলে এটাও ইসলামের নামে একটি বিচ্যুতির কারণ। সামান্য চুল ও দাঁড়ি আচড়ানোর গুরুত্ব‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
-এর মতো ইসলামের একটা ভিত্তির চেয়ে কোন ক্রমেই বেশী হতে পারে না।
মুসলমানদের কাছে‘
আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনীল মুনকার’
বিভিন্ন আঙ্গিকে মূল্যায়িত হয়েছে। এ ব্যাপারে আলেম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এক আলোচনা করা যাক। যদিও আলেম সমাজ এই ভিত্তিটির শিরোনামে এ সম্পর্কে কোনো পর্যালোচনা করেননি। তবে তাদের পর্যালোচনায় এই ভিত্তিটি স্থান পেয়েছে এবং এ থেকে এ ভিত্তিটির মূল্য সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুধাবন করা যায়। ইসলামের একটি মূলনীতি রাসূলুল্লাহর (সা.) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যার উপর নির্ভর করে সবাই নিজ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন। হাদীসটি হলোঃ
اذا اجتمعت حرمتان ترکت الصغری للکبری
‘‘
যদি দুটো পরস্পর বিরোধী হারাম একই সাথে উপস্থিত হয়,তাহলে বড়টা পালন করার জন্যে ছোটটা পরিত্যাজ্য ।’’
এ বক্তব্যের বহু উদাহরণ রয়েছে। তবে সচরাচর যে উদাহরণটি পেশ করা হয় তাহলো জবরদখলকৃত জমিতে প্রবেশ করা হারাম। এখন যদি দেখেন যে,এরকম একটা জমির পুকুরে একটা লোক ডুবে যাচ্ছে তাহলে আপনি কি করবেন? এ জমিতে ঢোকা যেমন হারাম তেমনি প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে না যাওয়াও হারাম। আপনি তখন এ জমিতে ঢ়ুকে (যা হারাম) ঐ লোকটার প্রাণ বাঁচাবেন আর নয়তো এখানে ঢোকা যাবে না বলে চুপ করে দাড়িয়ে দাড়িয়ে লোকটির মৃত্যুরবরণ উপভোগ করবেন? এখানে আপনি কি করবেন? জমিতে ঢোকা কিংবা তার প্রাণ না বাচানো দুটোইতো হারাম কাজ?
এখানে আপনার করণীয় হবে জমিতে ঢুকে লোকটার প্রাণ বাঁচানো। জবরদখলকৃত জিনিষে পা মাড়ানোর অপরাধের চেয়ে একটা প্রাণ বাচানো অনেক মূল্যবান। তাই এ মুহুর্তে যদি আপনি ঐ জমিতে প্রবেশ করেন তাহলে আপনার কোনো পাপ তো হবেই না,উপরন্তু আপনি সওয়াবের অধিকারী হবেন।
‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
-এর ক্ষেত্রে ও ইসলামের এই নীতি প্রযোজ্য । আমরা যে‘
আমর বিল মারুফ কিংবা নাহী আনীল মুনকার’
করবো-এ ক্ষেত্রে কতদুর পর্যন্ত এগুতে পারবো? কখনো কখনো‘
আমর বিল মারুফ কিংবা নাহী আনীল মুনকার’
করলে আমাদের জানমালের,মান-সন্মানের ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা থাকে না-এ রকম ক্ষেত্রে সবাই রাজী। আর কেউ যদি এ ও না করে তাহলে সে নিতান্ত অলসতার পরিচয় দেবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে,কাউকে সৎকাজের আদেশ করলে কিংবা অসৎকাজ থেকে বাধা দিলে নিজের জানমাল ও মান-ইজ্জতের হানি হতে পারে তাহলে এ ক্ষেত্রে করণীয় কি? এরূপ অবস্থায়ও কি‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
করা যাবে?
যদি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দিলে আমার নিজের প্রাণহানির পাশাপাশি আমার পরিবার-পরিজনদেরকে বন্দী করা হয়,প্রিয় সন্তান এবং সহযোগীদেরকে হত্যা করা হয় তাহলেও কি তা করা যাবে?
এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আলেম সমাজ ভিন্ন ভিন্ন মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকে মনে করেন,‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের’
সীমানা ততদুর পর্যন্ত যতক্ষণ না জানমাল,ইজ্জত-সম্মান হুমকির মুখে পড়ে। এই মত প্রকৃতপক্ষে‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
কে তার প্রকৃত অবস্থান থেকে নামিয়ে এনেছে। তারা বলে যে যদি‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারে’
জানমালের প্রশ্ন একই সাথে আসে তাহলে‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারকে’
পরিত্যাগ করে তোমরা জানমালের হেফাযত কর,তোমাদের ইজ্জত বাঁচাও।
অবশ্য তাদের বক্তব্য বেঠিক নয়। কেননা,মুমিনের জানমাল এবং ইজ্জতের মূল্য আছে। বিনা কারণে আপনার শরীরে একটা ছোট জখম করারও অধিকার আপনার নেই। আর প্রাণের জন্যে হুমকি সৃষ্টি করা তো আদৌ উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং কোরআন বলছেঃ
)
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ(
‘‘
তোমরা নিজের হাতে নিজদিগকে ধ্বংস করো না।’’
(
বাকারা
-
195
)
কেউ যদি ঋণের ভারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে,যদি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে,পৃথিবীর সব কিছুই যদি তার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে তবুও তার আত্মহত্যা করার কোনো অধিকার নেই। এটি ঠিক তেমনি হবে যে,সে সজ্ঞানে আরেকজনকে হত্যা করলো। কোরআন এর পরিণতি সম্পর্কে বলছেঃ
)
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا(
‘‘
কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু’
মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম।’’
(
নিসা
:
94
)
অনেকে মনে করেন যে,নিজের জীবন নিজের হাতে,নিজের মাল নিজেরই। অতএব যা ইচ্ছা করা যায়,এ ধারণা পুরোপুরি ভুল। কারও মাল সবার আগে সমাজের,তারপর তার নিজের। তিনি কেবল তা ব্যাবহার করতে পারেন। কিন্তু তা অপচয় করা বা ধ্বংস করার অধিকার তার নেই। ইসলাম কাউকে এ ধরনের অধিকার দেয়নি।
আমাদের আলোচনা এ বিষয়ে নয়। প্রশ্ন হলো‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারে’
র মূল্য কতটুকু ?‘
আমর বিল মারুফের কিংবা নাহী আনীল মুনকার’
-এর সম্মান কি জানমালের সম্মানের চেয়েও অধিক নয়?
দুঃখজনক হলেও বলতে হয় যে,অনেকে এমন কি কোনো কোনো নামী-দামী‘
আলেম যাদের কাছ থেকে এ ধরনের মত আশা করা যায় না তারাও বলেছেন যে,‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
-এর পিরিধ প্রাণহানি ও মানহানির সীমা পর্যন্ত । তাদের মতে,আমর বিল মারুফের কিংবা নাহী আনীল মুনকারের জীবনের মূল্যের চেয়েও কম,ধন-সম্পদ এবং মান-ইজ্জতের চেয়েও কম। বস্তুতঃ তারা‘
আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনীল মুনকারকে’
এ ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে নীচে নামিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অন্যরা বলেন যে,‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
-এর মূল্য এ সবের অনেক উর্দ্ধে । অবশ্য জায়গা বিশেষ। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে কি জন্যে আপনি তাকে বাধা দিচ্ছেন বা কোন কাজে তাকে আদেশ দিচ্ছেন। ধরুন,কলার খোসা রাস্তায় ফেলা উচিত নয়। তখন আপনি ঐ লোককে এ কাজ করতে নিষেধ করবেন। কিন্তু যদি আপনার গালি খাওয়ার কিংবা একটা অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনি কি নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে তাকে কলার খোসা রাস্তায় ফেলতে নিষেধ করতে যাবেন? না,দরকার নেই।
কিন্তু কোন কোন পরিস্থিতিতে ইসলাম জানমালের চেয়ে‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
কে বেশী মূল্য দিয়েছে। যেমন,আপনার চোখের সামনে কোরআন অপমানের সম্মুখীন,দুশমনদের সমস্ত প্রচেষ্টা কোরআনের আলাকে নিভিয়ে দেয়ার জন্যে ই চালানো হচ্ছে । কিংবা মুসলমানদের ঐক্যকে ভেঙ্গে-বিভেদের সৃষ্টি করছে কিংবা আদল বা ন্যায়পরায়ণতার বিরুপ্তি ঘটিয়ে অত্যাচার ও অনাচারের প্রচলন করা হচ্ছে আর ওদিকে কোরআন বলছেঃ
)
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا(
‘‘
তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তকরে ধরো এবং পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করো না।’’
(
আল ইমরান
:
103
)
আরেকটি জায়গায় বলছেঃ
)
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(
‘‘
নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রমাণাদি সহকারে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতির মানদন্ড যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।’’
(
হাদীদঃ 25
)
রাসূলুল্লাহ (সা:) বলছেন :
الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم
‘‘
কাফেরের হাতেও দেশ টিকে থাকতে পারে কিন্তু যে রাজ্যে জুলুম অত্যাচার চলে তা কখনই টিকে থাকে না।’’
আর কেউ নিজের চোখে জুলুম হতে দেখেছন,নিজের চোখে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে দেখেছন,কোরআনের অবমাননা ও তা বিপদাপন্ন হতে দেখেছন তারপরও কি বলবেন যে,আমার জানের দাম,মালের দাম,ইজ্জতের দাম এর চেয়েও বেশী,‘
আমর বিল মারুফ’
করতে গেলে কিংবা‘
নাহী আনীল মুনকার’
করতে গেলে আমার মানহানির সম্ভাবনা আছে?
কাজেই‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
এসব ক্ষেত্রে কোনো সীমানা মানে না। কোনো জিনিস,কোনো মুল্যবান সম্পদ এ সময়‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের’
সমকক্ষ হতে পারে না। এই নীতি‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
-এর মৌলিক গুরুত্বের উপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
এখানে এসে আমরা এখন উপলি করতে পারি যে,ইমাম হোসাইন (আ.)‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
কে কতদূর উন্নীত করেছেন। ঠিক যেভাবে‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
ও ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনকে উন্নীত ও চিরঞ্জীব করেছে। কেননা ইমাম হোসাইন (আ.) প্রমাণ করেছেন যে,জায়গা বিশেষে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের জন্যে জানমাল উৎসর্গ করতে হয়। সেদিন অনেকেই ইমামের এই আন্দোলনকে সঠিক ও উপযুক্ত পদক্ষেপ বলে মেনে নিতে পারেনি। অবশ্য তাদের চিন্তার মান অনুযায়ী তাদের এই আপত্তি করাটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ইমাম হোসাইনের (আ.) চিন্তার মান এসবের অনেক উর্দ্ধে ছিল। অন্যেরা বলছিল যে,ইমাম যদি ইয়াযিদের বিরোধিতায় নামেন পরিণতিতে ইমাম জানমাল হারাবেন। ইমাম (আ.) নিজেই আশুরার দিনের অবস্থা দেখে ইবনে আব্বাসকে বলেন :
لله درّ ابن عبّاس ینظر من ستر رقیق
‘
সাবাস! তুমি ভালই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারো।’
কারণ,ইমাম যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হন তখন ইবনে আব্বাস বলেছিলেনঃ‘
আমার দৃঢ় বিশ্বাস,কুফাবাসীরা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে,অনেকেই সেদিন এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। কিন্তু ইমাম জবাবে বলেছিলেন :
لا یخفی علیّ الامر
‘
তোমরা যা বলছো তা আমার অজ্ঞাত নয়,আমিও তা জানি।’
মূলতঃ ইমাম হোসাইন (আ.) বিশ্বকে বোঝালেন যে,‘
আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনীল মুনকারের’
জন্যে জীবনও দেয়া যায়,ধন-সম্পদ সবকিছু উৎসর্গ করা যায়। ইসলামের এই ভিত্তিটির জন্যে পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো ব্যাক্তি কি ইমাম হোসাইনের (আ.) ন্যায় আত্মত্যাগ করতে পেরেছে? ইমাম হোসাইনের (আ.) আন্দোলনের অর্থ হয় যে,‘
আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনীল মুনকারের’
মূল্য এত বেশী যে তার জন্যে এ ধরনের আত্মত্যাগও করা যায়।
ইমাম হোসাইনের (আ.) বিপ্লবের পর একথা বলার আর কোনো অবকাশ থাকে না যে,‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
কেবল মান-প্রাণহানির সীমা পর্যন্ত সম্ভব।
তবে হ্যাঁ,ফ্যাসাদের সম্ভাবনা থাকলে অন্য কথা। অনেক সময় দেখা যায় যে,আমরা ইসলামের স্বার্থে আমর বিল মারুফ করবো কিংবা নাহী আনীল মুনকার করবো বটে;কিন্তু এর চেয়ে বেশী ক্ষতি ইসলামকে আক্রান্ত করার সম্ভাবনা আছে। যেমন ধরুন যে,‘
আমর বিল মারুফ কিংবা নাহী আনীল মুনকার’
করতে গিয়ে একজন মুসলমানকে ইসলামের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাবাপন্ন করে তুললাম এবং সে ইসলামকে বর্জন করলো-তাহলে এখানে ইসলামের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হলো। সুতরাং এখানে‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
প্রয়োজন নেই। অবশ্যএ ক্ষতি ইসলামের উপর অর্পিত হয় বলেই। কেননা,এ ক্ষতি যদি ব্যাক্তিগত কোনো ক্ষতি হতো তাহলে কিন্তু‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারই সম্পন্ন করতে হতো। কারণ ইমাম হোসাইন (আ.) তা নিজে করে দেখিয়েছেন। ইমাম দেখিয়েছেন যে,তিনি এই ভিত্তিতেই আন্দোলন করেছেন কিংবা কমপক্ষে তার আন্দোলনের একটা অন্যতম কারণ ছিল এটিই। মোয়াবিয়ার আমলেই ইমামের (আ.) তৎপরতা থেকে বুঝা যেত যে,তিনি আসন্ন বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহর (সা.) সাহাবীদেরকে তিনি মিনায় সমবেত করে তাদের সাথে আলোচনা করলেন,তৎকালীন দুরবস্থা তুলে ধরলেন,সত্য পথের নির্দেশনা দিলেন। তারপর বললেন এখন এর সংস্কার করার দায়িত্ব আপনাদেরই।‘
তুহাফুল উকুল’
গ্রন্থে বর্ণিত ইমাম হোসাইনের (আ.) এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বক্তব্য ইমামের চিন্তাধারা কেমন ছিল তা স্পষ্ট তুলে ধরে। মোয়াবিয়ার শেষ বয়সে ইমাম হোসাইন (আ.) এক চিঠিতে তাকে বিভিন্ন ভাষায় অভিযোগ করে লিখেন :‘
হে মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান! আল্লাহর কসম করে বলছি যে,আমি যে এ মুহুর্তে তোমার সাথে যুদ্ধে নামছি না এ জন্যে আল্লাহর কাছে জবাবিদিহ করতে হয় কিনা,সেই ভয় করছি।’
অর্থাৎ তিনি বলতে চান,জেনে রাখ আজ যদি হোসাইন চুপ করে থাকে তার অর্থ এই নয় যে,আজীবন চুপ করেই থাকবে বা কোনো দিন বিদ্রোহ করবে না। বরং একটি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকা মাত্র । যে সময় বিদ্রোহ করলে সর্বাধিক ফলপ্রদ হয় এবং তার লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত হয় সে সময়েই তিনি বিদ্রোহ করবেন। যেদিন ইমাম মক্কা ছেড়ে আসেন সেদিন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার কাছে লেখা অসিয়তনামায় তিনি এ বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি লিখেন :
انّی ما خرجت اشرا و لا مفسدا و لا ظالما و انّما خرجت لطلب الاصلاح فی أمّة جدّی، أرید ان امر بالمعروف و انهی عن المنکر.
‘‘
আমি কোনো ধন-সম্পদ বা ক্ষমতার লোভে কিংবা কোনো গোলযোগ সৃষ্টির জন্যে বিদ্রোহ করছি না,আমি শুধু আমার নানার উম্মতের মধ্যে সংস্কার করতে চাই,আমি‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
করতে চাই এবং আমার নানা যে পথে চলেছেন আমিও সেই পথে চলতে চাই।’’
(
দ্রঃ মাকতালু খারাযমীঃ 1
/
188
)
ইমাম হোসাইন (আ.) দীর্ঘ পথ চলার সময় একাধিকবার তার এই লক্ষ্যকে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেন। বিশেষ করে এ সময়গুলোতে তিনি বাইয়াত প্রসঙ্গেরও যেমন কোনো উল্লেখ করেননি তেমনি দাওয়াত প্রসঙ্গেরও কোনো উল্লেখ করেননি। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল পথিমধ্যে তিনি যতই কুফা সম্পর্কে ভয়ানক ও হতাশা ব্যঞ্জক খবর শুনছিলেন ততই তার বক্তব্য জ্বালাময়ী হয়ে উঠছিল। সম্ভবতঃ ইমামের দূত মুসলিম ইবনে আকীলের শহীদ হবার সংবাদ শুনেই ইমাম এই বিখ্যাত খোতবা প্রদান করেনঃ
ایّها الناس، إنّ الدنیا قد ادبرت و اذنت بوداع، و انّ الاخرة قد اقبلت و اشرفت بصلاح
‘
হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবী আমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে,আমাকে বিদায় জানাচ্ছে । পরকাল আমাকে সাদরে বরণ করছে,উপযুক্ত মর্যাদা দিচ্ছে ।’’
الا ترون ان الحق لا یعمل به، و ان الباطل لا ینتهی عنه؟ لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقاً
‘‘
তোমরা কি দেখতে পাচ্ছনা যে সত্য অনুসারে আমল করা হচ্ছে না,তোমরা কি দেখতে পাও না যে আল্লাহর বিধানসমূহকে পদদলিত করা হচ্ছে ? দেখতে পাওনা যে চারদিকে ফেতনা-ফ্যাসাদে ছেয়ে গেছে অথচ কেউ এর প্রতিবাদ করছে না?’’
لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا
‘‘
এ অবস্থায় একজন মুমিনের উচিত নিজের জীবন উৎসর্গ করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা। যদি জীবন উৎসর্গ করতে হয় তাহলে এটাই তার উপযুক্ত সময়।’’
(
দ্রঃ তুহফাল উকুলঃ 245
)
অর্থাৎ‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
এতই মূল্যবান। পথিমধ্যে উচ্চারিত অন্য আরেকটি খোতবায় ইমাম সার্বিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ
.انّی لا اری الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا برما
‘‘
হে লোকসকল! আমি এই পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণকে কল্যাণ ও মর্যাদাকর ছাড়া আর কিছুই মনে করি না।’’
অর্থাৎ একে আমি সত্যের জন্যে শহীদ হওয়া মনে করি। এ থেকে বোঝা যায় যে‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
করতে গিয়ে নিহত হলে সে শহীদের মর্যাদার অধিকারী হবে। .
و الحیاة مع الظالمین الابرما
‘‘
আর জালেমদের সাথে বেঁচে থাকাকে আমি নিন্দাকর অপমান মনে করি। আমার আত্মা এমন আত্মা নয় যে,জালেমদের সাথে আপোষ করে বেঁচে থাকতে পারবে।’’
ইমাম এর চেয়ে আরো বড় কথা বলেন যখন অবস্থা শতভাগ প্রতিকূল হয়ে ওঠে। কাফেলা যখন ইরাকের সীমানায় পৌঁছায় তখন হুর ইবনে ইয়াযিদ আর-রিয়াহীর এক বিশাল বাহিনীর বাধার সম্মুখীন হন। হুর এক হাজার সৈন্যযোগে ইমামের কাফেলাকে বন্দী করে কুফায় নিয়ে যাবার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। তাবারীর মতো বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকগণ ঐ মুহুর্তে ইমামের সেই বিখ্যাত খোৎবার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম ঐ খোতবায় রাসূলুল্লাহর (সা.) উদ্ধৃতি দিয়ে‘
আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’
প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন :
ایها الناس من رآی سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناکثا لعهد الله مستأثرا لفیء الله، معتدیا لحدود الله، فلم یغیّر علیه بقول و لا فعل کان حقا علی الله یدخله مدخله، الا و انّ هولاء القوم قد احلّوا حرام الله و حرّموا حلاله، و استأثروا فیء الله.
(তিনি দুটো পরিপূর্ণ সূত্রের সাহায্য নেন। প্রসিদ্ধ নিয়মানুযায়ী তিনি প্রথমে একটা সাধারণ সূত্রের উল্লেখ করেন)‘‘
হে লোকসকল! রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ‘
যদি কেউ কোনো অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী সরকারকে দেখে যে হালালকে হারাম করে,হারামকে হালাল করে,বায়তুলমালকে নিজের ব্যাক্তিগত খাতে খরচ করে,আল্লাহর বিধি-বিধানকে পদদলিত করে,মুসলমানের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করে না,এরপরও যদি সে নিশ্চুপ বসে থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে ঐ জালেমদের সাথে একই শাস্তি প্রদান করবেন।
و
انّ
هولاء
القوم
..
আজকে যারা (বনি উমাইয়ারা) হুকুমত করছে তারা কি ঐসব জালেম ও স্বৈরাচারীদের মতন নয়? দেখতে পাও না যে তারা হালালকে হারাম করেছে আর হারামকে হালাল? তারা কি আল্লাহর বিধানকে পদদলিত করেনি? বায়তুলমালের অর্থকে তারা কি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেনি? আত্মসাৎ করেনি? তাই এরপরও যারা নীরবতা অবলম্বন করবে তারাও ইয়াযিদদের মতোই বলে সাব্যস্ত হবে।’’
এবার তিনি নিজের প্রসঙ্গে বলেন :
و انا احقّ من غیر
‘‘
আর আমার নানার এই আদেশ পালন করতে অন্যদের চেয়ে আমিই বেশী যোগ্য,আমারই দায়িত্ব অধিক ।’’
(
দ্রঃ তারিখে তাবারীঃ 4
/
304
)
কোনো মানুষ যখন ইমাম হোসাইনের (আ.) এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত হয় তখন বলে যে,এ ধরনের ব্যক্তিই তো চির ভাস্বর হয়ে থাকার অধিকার রাখেন। তিনিই তো চিরঞ্জীব থাকার যোগ্য । কেননা হোসাইন নিজের জন্যে ছিলেন না। তিনি নিজেকে মানুষ ও মানবতার জন্যে উৎসর্গ করেছেন। একত্ববাদ,ন্যায়পরায়ণতা এবং মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। আর এ কারণেই সব মানুষই তাকে ভালবাসে,তাকে শ্রদ্ধা করে। যখন কোনো মানুষ এমন একজনকে দেখে যার নিজের জন্যে কিছুই নেই,মান-সম্মান,মর্যাদা,মানবতা যা আছে তা সবই অন্যের জন্যে -তখন সে নিজেকে ঐ ব্যক্তির সাথে একাত্ম করে নেয়।
হুর ইমাম হোসাইনের (আ.) সাথে সাক্ষাতে ইমামকে কুফায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে ইমাম এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি কখনো অপমানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাননি। মনুষ্যত্বের মাহত্ম্য ও মর্যাদাকেই তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছেন। তিনি বললেনঃ আমি যাব না। শেষ পর্যন্ত আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে,তিনি এমন এক রাস্তায় যাবেন যে রাস্তা কুফারও নয়,মদীনারও নয়। অবেশেষ তিনি মহররম মাসের দুই তারিখে কারবালা ভূখন্ডে এসে পৌঁছুলেন। প্রায় 72 জন সঙ্গী-সাথীসহ সেখানে তাঁবু গাড়লেন। ওদিকে হুরের বাহিনীও কিছুদূরে তাঁবু গাড়লো। কুফার গভর্ণরের দূতরা অনবরত যাওয়া-আসা শুরু করলো। পরের দিনগুলোতে শত্রুদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো এবং নতুন নতুন বাহিনী এসে উপস্থিত হল। এক হাজার,পাঁচ হাজার এভাবে 6 তারিখের দিনের বেলা ত্রিশ হাজারে পৌঁছলো।
কুফার গভর্ণর ইবনে যিয়াদ এই বিশাল বাহিনীর দায়িত্ব ভার ইবনে সা’
দের হাতেই সোপর্দ করলো। ইবনে যিয়াদের ধারণা ছিল ইবনে সা’
দই তাকে হুকুমত এবং ইমারত লাভে সফল করবে। মোদ্দকথা ইবনে যিয়াদ এমন একজনকে নির্বাচিত করলো যাকে দেখে মুসলমানরা মনে করে যে,(নাউযুবিল্লাহ) ইবনে সা’
দ অতীতের মতোই যারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে তাদের সাথে যুদ্ধে নেমেছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ইবনে সা’
দ কাফেরদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়ে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল। অবশ্য ইবনে যিয়াদ যে ইবনে সা’
দকে ব্যাবহার করতে চাচ্ছে একথা ইবনে সাদ ধরে ফেলেছিল। তাই সে ইবনে যিয়াদের কাছে গিয়ে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলো। কিন্তু ইবনে যিয়াদও ইবনে সা’
দের দুর্বলতা কোথায় তা ভাল মতো জানতো। তাই আগেই একটা ডিক্রীপত্রে ইবনে সা’
দের জন্যে গুরগান ও রেই প্রদেশের গভর্ণর পদে নিযুক্তিরকথা লিখে রেখেছিল। এ কারণে ইবনে সা’
দ যখন দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানাতে আসে তখন ইবনে যিয়াদ বলেঃ ঠিক আছে,তাহলে মনে হে এই ডিক্রীপত্রটা এখন অন্য জনের নামে লিখতে হয়! ইবনে সা’
দ এবার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দ্বন্দে ভুগতে লাগলো। কারণ এ ধরনের একটা গভর্ণরের পদ তার বহু দিনের খায়েশ। ইবনে সা’
দ বললো,আমাকে একটু অবসর দাও,একটু ভেবে নেই। ইবনে সা’
দ যার সাথেই আলোচনা করলো সবাই তাকে নিন্দাবাদ করে বললো যে,তুমি নবীর সন্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইবনে সা’
দের কামনার প্রবৃত্তি বিজয়ী হলো এবং ইবনে যিয়াদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিল। ইবনে সা’
দ কারবালায় এসে প্রচেষ্টা করলো খোদা ও খোরমা দুটোই পেতে। সে যে কোনোভাবে ইমামকে একটা আপোষে রাজী করতে প্রচেষ্টা চালালো যাতে অন্ততঃপক্ষে নবীর সন্তানকে হত্যা করার দায় থেকে সে বাচতে পারে। তারপরে যাহোক দেখা যাবে। ইমাম হোসাইনের (আ.) সাথে এরপর তার দু’
-তিনটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হল। ঐতিহাসিক তাবারী লিখেছেন যে,যেহেতু এই বৈঠকগুলো কেবল দু’
জনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল-তাই কি আলোচনা হয়েছিল তা সবিস্তারে উদ্ধার করা যায়নি। কি যেটুকু ইবনে সাদ পরে ফাঁস করে তা থেকে বোঝা যায় যে,এমন কি কিছু মিথ্যা প্রলোভনের আশ্রয় নিয়ে ইবনে যিয়াদ ইমামকে আপোষে টানার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায়। ইবনে সা’
দের সর্বশেষ চিঠি যখন ইবনে যিয়াদের হাতে পৌঁছলো তখন কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ ও তার পাশে বসে ছিল। এ চিঠি পড়ে ইবনে যিয়াদ বললো যে হয়তো ব্যাপারটির শান্তিপূর্ণ সামাধান সম্ভব। কিন্তু তার চারপাশের ইবলিসী দালালদের মধ্যে থেকে শিমার ইবনে যিল জুউশান বলে উঠলোঃ
‘‘
হে আমীর! তুমি একটা অমার্জনীয় ভুল করতে যাচ্ছ । ইমাম হোসাইন (আ.) এ মুহুর্তে তোমার হাতের মুঠোয়। এখান থেকে যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে পরে তাকে আর নাগালে আনা সহজ হবে না। এ দেশে হযরত আলী (আ.)-এর অনুসারী কম নেই। তারা কেবল কুফায় নয়। তুমি কি বুঝবে না যে,আশপাশ থেকে ইমাম হোসাইনের (আ.) অনুসারীরা তার সাথে যোগ দেব? আর যদি সত্যিই ইমাম হোসাইনের (আ.) অনুসারীরা তার সাথে যোগ দেয় তাহলে তোমার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। ইতিহাসে আছে যে,একথা শুনে ইবনে যিয়াদের যেন টনক নড়ে উঠলো। বললোঃ হ্যাঁ ঠিকই তো। এরপর সে ইবনে সা’
দের চিঠির জন্যে তাকে অভিসম্পাত করে বললো,ইবনে সা’
দ যে আমাকে প্রায় ঠকিয়ে দিয়েছিল। এরপর সে ইবনে সা’
দকে লিখে পাঠালো,আমি তোমাকে পাঠিয়েছি আমার হুকুম পালন করবার জন্যে,আমাকে তুমি পিতার মতো উপদেশ লিখে পাঠাবে এ জন্যে তো নয়! তুমি একজন সেনা প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছো,শৃঙ্খলা মেনে চলো আর কোনো টু’
শব্দ ছাড়াই আমার আদেশ পালন করো। যদি এ কাজ না পারো তাহলে বলো,আমি অন্য আরেকজনকে নিয়োগ করবো। ইবনে যিয়াদ শিমারের মাধ্যমে এই চিঠিতে একটা আদশনামা লিখে বললো,ইবনে সা’
দ যদি হোসাইনের (আ.) সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে শিমার (শিমার) এই আদেশনামার জোরে তার শিরচ্ছেদ করবে। তারপর সেনা প্রধানের দায়িত্ব তোমার হাতেই থাকবে।
লিখিত আছে যে 9 মহররমের বিকালে ইবনে সা’
দের হাতে এ চিঠি পৌঁছায়। শিমার চিঠিটি ইবনে সা’
দকে দিল। শিমারের আশা ছিল যে,ইবনে সা’
দ বলে উঠবে,না! আমি নবীর সন্তানকে হত্যা করতে পারবো না।
তাহলেই শিমার ঐ গোপন আদেশনামার জোরে তার শিরচ্ছেদ করে সে নিজেই সেনাপতি হতে পারবে। কিন্তু ইবনে সা’
দ শিমারের মিথ্যা আক্ষেপের অবসান ঘটিয়ে বলে উঠলোঃ আমার ধারণা ছিল যে,আমার চিঠি পড়ে ইবনে যিয়াদের হুশ আসবে। কিন্তু তুমি তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তা হতে দাওনি।
শিমার বললঃ আমি ওসব কিছু বুঝি না। শুধু শুনতে চাই যে,শেষ পর্যন্ত তুমি যুদ্ধ করতে রাজী আছা কিনা। ইবনে সা’
দ এবার বললোঃ অবশ্যই করবো। এমন যুদ্ধ করবো যাতে হাত-পা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে আকাশে নিক্ষিপ্ত হবে।
শিমার বললঃ ঠিক আছে। তাহলে এখন আমার দায়িত্ব কি?
ইবনে সা’
দ জানতো যে ইবনে যিয়াদের কাছে শিমারের ভালই কদর রয়েছে। তাই শিমারকে বললোঃ তুমি হবে পদাতিক বাহিনীর কমান্ডার।
9 মহররমের ঐ চিঠিতে কড়া আদেশ লেখা ছিল। ইবনে যিয়াদ লিখেছিল : আমার চিঠি পৌঁছানোর সাথে সাথেই ইমাম হোসাইনকে (আ.) জোর অবরোধের মধ্যে ফেলবে। ইমাম হোসাইনকে (আ.) হয় আত্মসমর্পণ করতে হবে নতুবা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। এর বাইরে তৃতীয় কোনো পথ নেই। ইবনে সা’
দ এই আদেশ পেয়ে ইমামের তাবুগুলোর চারপাশে সেনা মোতায়েন করে জোর অবরোধ সৃষ্টি করলো। ইমাম হোসাইন (আ.) তাদের এ ধরনের চাল-চলন দেখে হযরত আব্বাসকে যুহাইর ইবনে কাইন এবং হাবিব ইবনে মাযাহিরের সাথে পাঠিয়ে কি খবর জেনে আসতে বললেন। হযরত আব্বাস,নতুন কোন সংবাদ আছে কি?
ইবনে সা’
দ বললোঃ হ্যাঁ,ইবনে যিয়াদ আদেশ পাঠিয়েছে যে,ইমাম হোসাইনকে (আ.) হয় আত্মসমর্পণ করতে হবে আর নয়তো যুদ্ধের পথ বেছে নিতে হবে।
হযরত আব্বাস বললেনঃ আমি নিজের পক্ষ থেকে তো কোনো জবাব দিতে পারি না। ঠিক আছে,আমি ইমামের বক্তব্য জেনে এসে তোমাদেরকে বলছি।
হযরত আব্বাস ইমাম হোসাইনের (আ.) কাছে ফিরে এসে ব্যাপারটা জানালেন।
ইমাম জবাবে বললেনঃ আমরা আত্মসমর্পণ করি না। যুদ্ধই আমরা করবো শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত । তবে ওদেরকে গিয়ে শুধু একটা কথাই বলো,শুধু একটা অনুরোধ করো যে,কাল সকাল পর্যন্ত আমাদের সময় দেয়া হোক। অনেকে হয়তো বলতে পারে যে,ইমাম হোসাইন (আ.) বেঁচে থাকতে খুবই ভালবাসতেন। তাই ঐ এক রাতকে জীবনের জন্যে গনীমত হিসাবে পেলেন। কিন্তু ইমাম নিজেই বলছেনঃ‘‘
স্বয়ং আল্লাহ জানেন আমি এই অবসরটুকু কি জন্যে চেয়েছি। আমার মন-প্রাণ শেষবারের মতো একবার আল্লাহর সাথে অনুনয়-বিনয় করতে চায়। শেষবারের মত নামায পড়তে,দোয়া ও মোনাজাত করতে এবং কোরআন তেলাওয়াত করতে চায়। এই রাতটাকে জীবনের শেষ রাত হিসাবে আমি আল্লাহর ইবাদত করতে চাই।’’
হযরত আব্বাস ফিরে এসে ইবনে সা’
দকে ইমামের মতামত জানালেন এবং ইমামের অনুরোধ ও বললেন। তারা অনেকেই ইমামের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে চাইলো। কিন্তু অনেকে এর প্রতিবাদ করে বললো যে-তোমরা সত্যিই বেশরম। যখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধ হতো তখন তারা যদি এরকম প্রস্তাব দিত তাহলে তা গ্রহণ করা হতো। আর নবীর সন্তান শেষবারের মতো আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে একটা রাত অবসর চেয়েছে,তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করছো! এভাবে তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত ইবনে সা’
দ,সৈন্যদের মধ্যে ঐক্য রক্ষারস্বার্থে ইবনে যিয়াদের আদেশকে কিছুটা উপেক্ষা করে বললোঃ ঠিক আছে,কাল সকালে!
ইমাম হোসাইন (আ.) এই আশুরার রাতে গভীর ইবাদেত নিমগ্ন হন। এক আধ্যাত্মিক,জ্যোতির্ময় এবং ঐশী পরিবেশে তিনি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হন। যারা এই রাতকে ইমাম হোসাইনের (আ.) মে’
রাজের রাত বলে আখ্যায়িত করেছেন তারা সত্যিই যথার্থ কথাই বলেছেন। আশুরার রাতে ইমাম সব সঙ্গী-সাথীদেরকে ডেকে বললেনঃ হে আমার সহযোগীরা,হে আমার পরিজনরা! আমি আমার সহযোগী এবং আমার পরিজনদের চেয়ে উত্তম কোনো সহযোগী এবং পরিজন খুঁজে পাইনি। তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ । তবে সবাই শোনো,ওরা কিন্তু কেবল আমাকেই চায়। আমাকে ছাড়া আর কারো সাথে ওদের কোনো কাজ নেই। তোমরা যদি আমার হাতে বাইয়াত করে থাকো তাহলে আমি সে বাইয়াত তুলে নিলাম,তোমরা সবাই এখন স্বাধীন। তোমাদের মধ্যে যে চলে যেতে চায় সে এখন অনায়াসেই চলে যেতে পারে। আর পারলে আমার পরিজনদের একজনকে হাত ধরে নিয়ে যাও! ইমামের মুখের দিকে চেয়ে অনেকে বিগিলত হতে পারে এ কারণে ইমাম এবার আলো নিভিয়ে দিয়ে বললেনঃ তোমরা এই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে যেতে পার। কেউ তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।
ইমামের একথা শুনে সবাই এক সাথে বলে উঠলোঃ হে ইমাম,একি কথা আপনি আমাদেরকে বলছেন? আমরা আপনাকে একা রেখে চলে যাব? আমাদের সামা একটা প্রাণের চেয়ে বেশী কিছু নেই যা দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারি! আল্লাহ যদি আমাদেরকে পর পর এক হাজারটা জীবন দান করতেন এবং এক হাজার বার আমরা আপনার রাস্তায় কোরবানী হতে পারতাম এবং জীবিত হয়ে পুনঃ পুনঃ আপনার জন্যে কোরবানী হতে পারতাম! এই সামান্য একটা প্রাণ তো আপনার রাস্তায় খুবই নগণ্য । আমাদের এই নগণ্য জীবন আপনার রাস্তায় কোরবানী হবার যোগ্য নয়। বলা হয়েছেঃ
بدأهم بذلك اخوه ابو الفضل العبّاس
‘‘
সর্ব প্রথম যিনি একথা বলেছিলেন তিনি হলেন ইমামের বীর ভাই হযরত আবুল ফযল আল-আব্বাস।’’
ইমাম তাদেরকে এই চুড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখে আরো কিছু নতুন সত্যের পর্দা খুলে দিলেন। তিনি বললেনঃ এখন আমি হাকিকতকে তোমাদের সামনে বলতে চাই। সবাই জেনে রাখ যে,আগামীকাল আমরা সবাই শহীদ হবো।
আমাদের মধ্যে কেউই বেঁচে থাকবে না। সবাই বলে উঠলোঃ আল্লাহকে লাখো শোকর যে,এ ধরনের একটা শাহাদাতের মর্যাদা আমাদেরকে দান করেছেন। যখন ইমাম হোসাইন (আ.) শাহাদাতের এই সুসংবাদ ঘোষণা করলেন তখন 13 বছরের একটা বালকও এই মজলিসে বসেছিলেন। তিনি ছিলেন ইমাম হাসানের পুত্র কাসেম। তিনি খুবই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন,ইমাম যে শাহাদাতের কথা বললেন তা বোধহয় কেবল বড়দের ভাগ্যেই আছে। আমি হয়তো এর শামিল হতে পারবো না। 13 বছরের বালক,এ ধরনের চিন্তা করাই স্বাভাবিক। তিনি গভীর চিন্তা করতে করতে এক সময় মাথা তুলে বললেনঃ
یا عمّا، و انا فیمن یقتل؟
‘‘
হে চাচাজান,আমিও আগামীকালের শহীদদের মধ্যে আছি?
ইমাম হোসাইন (আ.) একটা দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। তারপর বললেনঃ হে প্রিয় কাসেম ! আমি আগে তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি,তার জবাব দাও। তারপর তোমার প্রশ্নের জবাব দেব।
হযরত কাসেম বললেনঃ চাচাজী আপনার প্রশ্ন কি?
ইমাম জিজ্ঞেস করলেনঃ বলতো দেখি মৃত্যুস্বাদ তোমার কাছে কেমন লাগবে?
হযরত কাসেম বললেনঃ
احلی من العسل
‘‘
চাচাজী! মধুর চেয়েও মিষ্টি’’
অর্থাৎ আমি যে জিজ্ঞেস করলাম শহীদদের মধ্যে আমি আছি কিনা তার কারণ হলো যে,ভয় পাচ্ছিলাম আমি এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হই কিনা।
ইমাম বললেনঃ হ্যাঁ,কাল তুমিও শহীদ হবে।
এ ছিল সত্যের অনুসারী ইমাম হোসাইনের (আ.) সাহায্য কারীদের আত্মার একটা স্বরূপ । আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ইমাম হোসাইনের (আ.) সহযোগীদের এ অসামান্য বীরত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।
 0%
0%
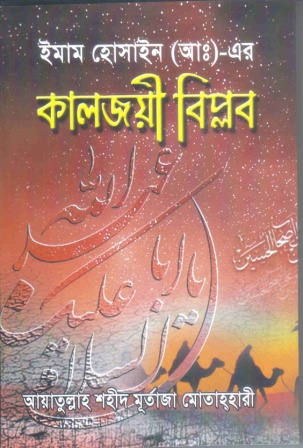 লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী
লেখক: শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী