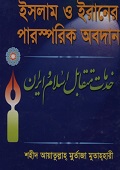মাযদাকী ধর্ম
অন্য যে ধর্মটি সাসানী আমলের শেষাংশে উৎপত্তি লাভ করেছিল ও যার বিপুল সংখ্যক অনুসারীও ছিল তা হলো মাযদাকী। মাযদাকী ধর্মকে মনী ধর্ম হতে উদ্ভূত মনে করা হয়। এ ধর্মের প্রবর্তক মাযদাক সাসানী শাসক আনুশিরওয়ানের পিতা কাবাদের শাসনামলে নিজেকে এ ধর্মের প্রবক্তা বলে ঘোষণা করেন। কাবাদ প্রথম দিকে মাযদার প্রতি ভালবাসা অথবা এ ধর্মে বিশ্বাসের কারণে অথবা যারথুষ্ট্র পুরোহিত ও সম্ভ্রান্তদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে তাঁকে সমর্থন জানান। এতে মাযদাকের কর্মতৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর পুত্র আনুশিরওয়ানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অথবা আনুশিরওয়ান শাসন ক্ষমতা লাভের পর মাযদাকীদের গণহত্যার নির্দেশ দেন। মাযদাকীদের ওপর গণহত্যা পরিচালনায় এ ধর্মাবলম্বীরা আত্মগোপন করে।
মাযদাকীরা ইসলামী শাসনামলের দু’
বা তিন শতাব্দী পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল এবং এ সময়ে ইসলাম ও খেলাফতের বিরুদ্ধে যে সকল ইরানী বিদ্রোহ করেছিল মাযদাকীরা তার নেতৃত্বে ছিল। এ কারণেই যারথুষ্ট্রগণ তাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে মুসলমানদের সহযোগিতা করে।
কথিত আছে মাযদাকী ধর্মের প্রবক্তা মূলত যারদুশ্ত নামের এক ব্যক্তি যিনি ইরানের সিরাজের ফাসার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে মনী ধর্মের একটি স্বতন্ত্র ফির্কার দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতেন। তাঁর এ আহ্বান রোম হতে শুরু হয়। পরে তিনি ইরানে ফিরে এসে তাঁর এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। রোমে তিনি‘
বুন্দেস’
নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ক্রিস্টেন সেন উপরোক্ত বিষয়টি বর্ণনার পর উল্লেখ করেছেন ,
‘
সুতরাং মাযদাকী ধর্ম বুন্দেসের প্রচারিত‘
সত্য দীন’
। মনী ধর্মের এ ব্যক্তির নতুন ধর্মমত প্রচারের জন্য ইরানে আগমন হতে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে ,তিনি ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন। যদিও‘
বুন্দেস’
শব্দটি ফার্সী ভাষায় নাম হিসেবে নেই তদুপরি এটি তিনি নিজের উপাধি হিসেবে গ্রহণ করেন। ইসলামী গ্রন্থগুলোতে দু’
টি উৎস হতে মাযদাকী ধর্মের বিষয়ে আলেচনা এসেছে। এর একটি হলো‘
আল ফেহেরেসত’
যেখানে মাযদাকী ধর্মের প্রবক্তা মাযদাকের কিছু পূর্বের এক ব্যক্তি বলে উল্লিখিত হয়েছে ;ইসলামী গ্রন্থসমূহের অপর উৎস‘
খুযায়ে নমাগ’
গ্রন্থে তাঁর নামের সঙ্গে‘
যারদুশত’
শব্দটি জুড়ে দেয়া আছে এবং এখান হতেই যারদুশত ফির্কার সৃষ্টি হয়েছে... সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায়‘
বুন্দেস’
ও‘
যারদুশত’
এক ব্যক্তি ছিলেন এবং এ ধর্মের প্রবক্তার প্রকৃত নাম‘
যারদুশত’
যেটি যারথুষ্ট্র ধর্মের প্রবক্তার সমনাম অর্থাৎ মাযদা ইয়াসনা যারথুষ্ট্র ধর্মের প্রবক্তা ও নবী এবং মাযদাকী ধর্মের প্রবক্তা উভয়ের নামই ছিল‘
যারদুশত’
। সুতরাং আমাদের আলোচিত ধর্মটি মনী ধর্মেরই একটি ফির্কা যার উৎপত্তি মাযদাকের দু’
শতাব্দী পূর্বেই রোমে‘
বুন্দেসে’
র হাতে ঘটেছিল এবং তিনি ইরানের ফাসার অধিবাসী খুরেগনের পুত্র‘
যারদুশত’
ছিলেন।... আরবী গ্রন্থসমূহ হতে জানা যায় ফাসার যারদুশতের আহ্বান শুধুই তত্ত্বগত ছিল। কিন্তু মাযদাক এ ধর্মের একজন সাধারণ প্রতিনিধি ও প্রচারক হিসেবে (তাবারীর মতে) ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় ধীরে ধীরে প্রবক্তার স্থান দখল করেন ও তাঁর জীবদ্দশায়ই এ ধর্মকে মাযদাকী বলে প্রচার চালান। ফলে পরবর্তীতে সাধারণ মানুষ ধারণা করেছে এ ধর্মের প্রকৃত উদ্গাতা ছিলেন মাযদাক।”
মাযদাকী ধর্মের স্বরূপ ,ফাসায়ী যারদুশতের আবির্ভাবের কারণ ও মাযদাক সম্পর্কে প্রচুর কথা রয়েছে। মাযদাক নিঃসন্দেহে মনীর ন্যায় দ্বিত্ববাদী ছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ দু’
য়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করব। এ ধর্মের আচার-নীতি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব ও সংসার বিরাগের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,“
...মনী ধর্মের ন্যায় এ ফির্কারও মৌল নীতি হলো মানুষ যেন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ কমায় এবং যা কিছুই এ আকর্ষণের সৃষ্টি করে তার সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল করে ও দূরে থাকে। এ কারণেই পশুর মাংস ভক্ষণ মাযদাকীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং তারা বিশেষ নীতির মধ্যে খাদ্য গ্রহণ করত ও কঠোর সাধনায় রত হত । ...শাহরেস্তানী বর্ণনা করেছেন মাযদাক অন্ধকার হতে মুক্তির জন্য আত্মহত্যার নির্দেশ দিতেন। অবশ্য সম্ভাবনা রয়েছে আত্মহত্যা বলতে প্রবৃত্তিকে হত্যা বুঝানো হয়েছে যা আত্মার মুক্তির পথের অন্তরায় । মাযদাক মানুষকে ঈর্ষা ,প্রতিহিংসা ,দ্বন্দ্ব ও হত্যা হতে নিষেধ করতেন। তাঁর মতে যেহেতু মানুষের মধ্যে হিংসা ও দ্বন্দ্বের মূল কারণ অসাম্য সেহেতু বিশ্ব হতে অসাম্যকে বিনাশ করতে হবে। তবেই মানুষের মধ্যে হিংসা ও দ্বিমূখিতার অবসান ঘটবে। মনী ধর্মের মনোনীত প্রতিনিধিগণ বিবাহ করতে পারবেন না ,একদিনের আহার ও এক বছরের প্রয়োজনীয় পোশাকের অধিক রাখতে পারবেন না। যেহেতু মাযদাকীরাও মনীদের ন্যায় সংসার বিরাগ ও কঠোর সাধনায় বিশ্বাসী ছিল তাই ধারণা করা যায় তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের জন্যও এরূপ বিধান ছিল। তবে মাযদাকীদের নেতৃবর্গ বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ মানুষ বস্তুগত আনন্দ উপভোগ যেমন সম্পদ ,তার পছন্দনীয় নারী প্রভৃতি হতে বিরত থাকতে পারে না ;বরং তারা স্বাধীনভাবে এগুলো উপভোগ করতে প্রত্যাশী ,তাই ধর্মযাজকগণ তাঁদের বিশ্বাসকে এভাবে বর্ণনা করেন:“
খোদা জীবন যাপনের সকল উপকরণ পৃথিবীতে দিয়েছেন যাতে করে সকল মানুষ সমভাবে তা হতে ব্যবহার করতে পারে। কেউ যেন অপর হতে অধিক গ্রহণ না করে। অসাম্যের কারণেই মানুষের মধ্যে এ প্রবণতা জন্ম নিয়েছে যে ,তার ভ্রাতার সম্পদ অপহরণ করে নিজেকে পরিতৃপ্ত করবে। তাই কেউ অন্যের চেয়ে অধিক সম্পদ ও নারীর অধিকারী হতে পারবে না। তাই সম্পদশীলদের নিকট থেকে নিয়ে দরিদ্রদের দিতে হবে যাতে করে পুনরায় পৃথিবীতে সাম্য স্থাপিত হয়।”
অবশ্য স্বয়ং মাযদাক এবং এ ধর্মের উদ্ভাবনের পেছনে কি বিষয় তাঁকে উদ্দীপিত করেছে সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিছু জানা যায় না। মাযদাকের পরিচিতি বিশেষত তাঁর সাম্যবাদী চিন্তার কারণে । ক্রিস্টেন সেন মাযদাকের এরূপ চিন্তার মূলে মানবপ্রেম ও নৈতিক অনুভূতি বলে মনে করেন।
মাযদাকের এরূপ চিন্তার কারণ ও উদ্দেশ্য যাই হোক যে বিষয়টি ঐতিহাসিক পর্যালোচনার দাবি রাখে তা হলো তৎকালীন ইরানী সমাজ সাম্যবাদী ধারণা গ্রহণের জন্য কিরূপ উপযোগী ছিল। ক্রিস্টেন সেন তাঁর গ্রন্থের‘
মাযদাকী আন্দোলন’
অধ্যায়ে তৎকালীন শ্রেণীবিভক্ত ইরান সমাজ কিভাবে মাযদাকী চিন্তাধারার প্রসারের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তার আশ্চর্য বিবরণ দিয়েছেন। আমরা ইরানের তৎকালীন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এরূপ চিন্তার প্রসারের কারণ হয়েছিল।
সাঈদ নাফিসী সাসানী আমলের ইরান সমাজে বিবাহ ,তালাক ,উত্তরাধিকার ও নারীর অবস্থানের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন ,“
বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য ও জনসমষ্টির বিশাল অংশের সম্পদের অধিকারবঞ্চিত হওয়ার কারণে ইরান সমাজে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণেই সাসানী আমলের ইরান সমাজ ঐক্যবদ্ধ ছিল না এবং সাধারণ মানুষদের বিরাট অংশ বঞ্চিত ও অসন্তুষ্ট ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে দু’
টি বিপ্লবী ধারার জন্ম হয়। যে দু’
ধারারই লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে তার খোদাপ্রদত্ত অধিকার দান করা। 240 খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ সাসানী শাসনামলের চৌদ্দতম বছরে সাসানী সম্রাট প্রথম শাপুরের সিংহাসনে আরোহণের দিন মনী বঞ্চিত শ্রেণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে তাঁর ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন ও ঘোষনা দেন। এর ঠিক পঞ্চাশ বছর পর ফার্সের ফাসার যারদুশত নতুন আরেকটি ধর্মের উদ্ভব ঘটান যদিও তাঁর ধর্মে সাম্যবাদের বিষয়টি কতটা উপস্থাপিত হয়েছিল তা জানা যায় না। কারণ তিনি এ ধর্ম তেমনভাবে প্রচার করতে পারেননি। তবে এর প্রায় দু’
শ বছর পর বমদাদের পুর মাযদাক তাঁর প্রণীত মৌলনীতিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন। অবশেষে সাম্য ও মুক্তির বাণী নিয়ে ইসলামের আগমন ঘটলে সমাজের অধিকারবঞ্চিত মানুষ তাদের অধিকার অর্জন করে ও সাসানী আমলের বৈষম্যের অবসান ঘটে।”
মাযদাকী ধর্ম বঞ্চিত শ্রেণীর পক্ষে থাকায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করে। ক্রিস্টেন সেন বলেন ,
“
মাযদাকী ধর্ম সমাজের সুবিধাবঞ্চিত নিম্ন শ্রেণীর মাঝে উদ্ভব হয়ে এক রাজনৈতিক বিপ্লবী ধারার জন্ম দেয় ,কিন্তু ধর্মীয় ভিত্তি পাওয়ায় উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও এ ধর্মের অনুসারী ছিল। ধীরে ধীরে মাযদাকীরা শক্তি লাভ করে ধর্মযাজক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায় এবং একজন ধর্মযাজককে তাদের প্রধান মনোনীত করে।”
ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে ,মাযদাক ও তাঁর অনুসারীরা কাবাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর অন্যতম পুত্র কাউসকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালায় ও কাবাদের ঈপ্সিত উত্তরাধিকারী পুত্র আনুশিরওয়ানকে বঞ্চিত করার উদ্যোগ নেয়। এর ফলেই আনুশিরওয়ান তাদের সমূলে ধ্বংসের পরিকল্পনা করেন।
ক্রিস্টেন সেন বলেছেন ,
“
শাসকশ্রেণী তাদের দীর্ঘ দিনের সফল অভিজ্ঞতাকে এ ক্ষেত্রে কাজে লাগায়। তারা ধর্মযাজকদের বিভিন্ন গ্রুপকে দাওয়াত করে। অন্যান্য ধর্মযাজকদের প্রধানদের সঙ্গে মাযদাকী ধর্মীয় গুরুদেরও আহ্বান করা হয়। মাযদাকী পুরোহিতদের এক বৃহৎ অংশ সরকারীভাবে আয়োজিত এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত হলেন। স্বয়ং সম্রাট কাবাদ (কাওয়ায) অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন। এদিকে সম্রাটপুত্র খসরু আনুশিরওয়ান সম্রাটের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে মাযদাকী ও কাউসের ষড়যন্ত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় রত ছিলেন যাতে করে এ অনুষ্ঠান মাযদাকীদের ওপর ভয়ঙ্কর এক হামলার মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে। যা হোক বিতর্ক শুরু হলে বেশ কিছু প্রশিক্ষিত ধর্মযাজক ময়দানে আসলেন...। দু’
জন প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টান ধর্মযাজক গুলুনাযেস ও বাযানেস যারথুষ্ট্র পুরোহিতদের সঙ্গী হিসেবে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাযানেস সম্রাট কাবাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কারণ তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে বেশ দক্ষ ছিলেন। বিতর্কের শেষ পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই মাযদাকীরা পরাস্ত হলেন। এমতাবস্থায় মাযদাকীদের পেছনে অবস্থানকারী প্রহরীরা অস্ত্র হাতে মাযদাকীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রধান বিতর্ককারী (সম্ভবত স্বয়ং মাযদাক ছিলেন) নিহত হলেন। কতজন মাযদাকী এ আক্রমণে নিহত হন তা সঠিক জানা যায়নি। আরব ও ইরানী ঐতিহাসিকগণ যে সংখ্যাসমূহের উল্লেখ করেছেন তার কোন সঠিক ভিত্তি নেই। তবে মনে হয় মাযদাকীদের প্রধান ধর্মযাজকদের সকলেই এতে নিহত হয়েছিলেন। এ ঘটনার পর মাযদাকীদের সকলকে হত্যার নির্দেশ জারী হলো। মাযদাকীরা যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল ও শত্রুর বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হয়ে ধ্বংসের মুখে পতিত হলো। তাদের সম্পদ ও গ্রন্থসমূহ পুড়িয়ে দেয়া হলো... তখন হতে মাযদাকীরা গোপনে কর্মতৎপরতা চালানো শুরু করে এবং সাসানী আমলের পরবর্তীতে ইসলামের আবির্ভাবের পরও তারা অনেকবার আত্মপ্রকাশ করেছে।”
বাহ্যিকভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ ও সহিংসতার মাধ্যমে মাযদাকী ধর্ম অবদমিত হয়েছিল ,কিন্তু বাস্তবে তারা ছাইচাপা আগুনের ন্যায় অপ্রকাশ্য ছিল। নিঃসন্দেহে ইসলাম আবির্ভূত না হলে মাযদাকী ধর্ম তার সাম্যবাদী চেতনা নিয়ে পুনরুত্থিত হতো। কেননা যে সকল কারণে এ ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল ও মানুষ এর প্রতি আশ্চর্যজনকভাবে ঝুঁকে পড়ছিল সে কারণসমূহ বর্তমান ছিল। মাযদাকী ধর্ম দীনের মৌল বিশ্বাস ,বিশ্ব ,মানুষ ও সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণার বিষয়ে যারথুষ্ট্র ধর্ম হতে কোন বিষয়ে কমতি রাখত না ;বরং হয়তো কিছুটা উচ্চ পর্যায়ে ছিল। তাই অন্যান্য ধর্ম হতে তাদের আকর্ষণ কম ছিল না। সামাজিক শিক্ষার বিষয়ে তাদের অবস্থান ছিল যারথুষ্ট্র ধর্মের বিপরীতে। কারণ যারথুষ্ট্রগণ শক্তিমান ও ক্ষমতাশীলদের পক্ষে ছিল। আর মাযদাকীরা সাধারণ নিপীড়িত মানুষের পক্ষে ছিল।
শক্তি প্রয়োগ ও দমন-নিপীড়নের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে মাযদাকী ধর্মের বিলুপ্তির মূল কারণ ছিল ইসলাম। ইসলাম একত্ববাদী ধর্ম হিসেবে খোদা ,সৃষ্টি ,মানুষ ও জীবন সম্পর্কে এক বিশেষ মৌলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থিত হয় ,মাযদাকী ধর্ম কোনক্রমেই তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। ইসলাম তার সামাজিক প্রশিক্ষণের ধারায় ন্যায়নীতি ,সাম্য ,মানুষ হিসেবে সকল শ্রেণী ,বর্ণ ও জাতির অভিন্নতার ধারণা উপস্থাপন করে যার মধ্যে মাযদাকীদের ন্যায় কোন বাড়াবাড়ি ছিল না। বস্তুত ইসলাম চিন্তাগত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে মাযদাকীদের অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল। তাই ইরানের সাধারণ মানুষ মাযদাকী ধর্মে প্রবেশ না করে তাওহীদ ও ন্যায়নীতির প্রতি আহ্বানকারী ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় খলীফাগণ তাঁদের শাসনামলে পারস্য ও রোমের শাসকবর্গের নীতি অবলম্বন করলে ইরানে দ্বিতীয়বারের মত মাযদাকী চিন্তার প্রসারের সুযোগ আসলেও ইরানের মানুষদের সচেতনতা সে সুযোগ দেয়নি। কারণ তারা জানত খলীফাদের আচরণের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তাই ইসলামকে এই খলীফাদের হাত হতে মুক্তি দিতে হবে।
তাই আমরা লক্ষ্য করি উমাইয়্যা শাসনের শেষ দিকে 129 হিজরীতে মারভের সেফিযানজ হতে কালো পোশাকধারীরা যে আন্দোলন শুরু করে তাতে তারা তাদের পতাকায় কোরআনের যে আয়াতটি খোদিত করে তা নিম্নরূপ :
)
أذِنَ للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا و إنَّ الله على نصرهم لقدير(
“
যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হলো তাদের যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।”
এ আন্দোলনের প্রথম দিন ছিল ঈদুল ফিতর। এদিন আন্দোলনের প্রধান নেতা আবু মুসলিম খোরাসানীর নির্দেশে অন্যতম নেতা সুলাইমান ইবনে কাসির ঈদের খুতবা পড়েন ও উমাইয়্যা খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তৎকালীন সময়ে ইরানীদের মধ্যে মাযদাকী ধর্মের প্রতি আকর্ষণ থাকলে তা প্রকাশের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ছিল এটি। কিন্তু আমরা ইতিহাসে লক্ষ্য করি ইরানীদের ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সব সময় ইসলামের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল ;মাযদাকী বা অন্য কোন চিন্তার ওপর নয়।
মাযদাকীরাও মনুয়ীদের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে ,যারথুষ্ট্রদের ন্যায় সংখ্যালঘু হিসেবেও টিকে থাকতে পারে নি। এর কারণ মনী ধর্মের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি ,মুসলমানরা মাযদাকীদের ঐশী ধর্ম বা আহলে কিতাব মনে করত না ;বরং মনীদের ন্যায় তাদেরও ধর্মহীন মনে করত। এ কারণেই তারা যারথুষ্ট্রদের ন্যায় সংখ্যালঘু হিসেবেও অবশিষ্ট থাকে নি। অবশ্য একদিকে মাযদাকীদের কঠোর নৈতিক সাধনা ও প্রচেষ্টার বাড়াবাড়ি ,অন্যদিকে সামাজিক ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ সাম্যবাদী ধারণা এ দু’
টি বিষয়ও তাদের নিশ্চি
হ্ন হওয়ার কারণ ঘটিয়েছিল।
 0%
0%
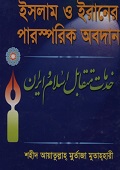 লেখক: শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী
লেখক: শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী