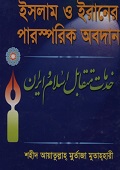ইসলামের প্রতি ইরানের অবদান
অবদানের সর্বজনীনতা ও ব্যাপকতা
আলোচনার এ অংশে ইরান ও ইরানীরা ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতায় যে অবদান রেখেছেন তা উল্লেখ করব। দ্বিতীয়াংশের প্রথমে আমরা বলেছি একটি ধর্মের প্রতি কোন জাতির অবদানকে এভাবে দেখা হয় যে ,সে তার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক শক্তি ,তার চিন্তা ,সৃষ্টিশীলতা ,দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কিভাবে এ দীনের সেবায় নিয়োজিত করেছে এবং তার এ কর্মে কতটা আন্তরিক ও বিশুদ্ধ নিয়্যতের পরিচয় দিয়েছে।
ইরানীরা অন্য সব জাতি অপেক্ষা নিজ শক্তিসমূহকে ইসলামের সেবায় অধিকতর উত্তমরূপে নিয়োজিত করেছে এবং অন্য সকল হতে এ ক্ষেত্রে অধিকতর আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছে। কোন জাতিই এ দু’
ক্ষেত্রে ইরানীদের সঙ্গে তুল্য নয় ,এমনকি যে আরব জাতির মাঝে ইসলাম প্রথম প্রকাশিত হয়েছে তারাও নয়। এ আলোচনায় এ দু’
টি বিষয়কে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য ,বিশেষত দ্বিতীয় বিষয়টি।
ইসলামের সেবায় ইরানীদের অবদান সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয় ,কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি কমই লক্ষ্য করা হয়েছে। ইরানীরা ইসলামের সেবায় মৌলিক ভূমিকা রেখেছে এবং গভীর ভালবাসা ও পূর্ণ ঈমান ব্যতীত এরূপ মৌলিকত্বের সৃষ্টি সম্ভব নয়। বাস্তবে ইসলামই ইরানীদের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগরিত করেছে এবং তাদের মধ্যে নতুন আত্মার জন্ম দিয়ে উদ্দীপিত করেছে। যদি তা না হয় ,অর্থাৎ ইসলামের কারণে তাদের মধ্যে এরূপ উদ্দীপনা যদি সৃষ্টি না হয়ে থাকে তবে প্রশ্ন দেখা দেয় কেন ইরানীরা প্রথম (হিজরী) শতাব্দীতে তাদের পূর্ববর্তীদের ধর্মের পথে এই সাহস প্রদর্শন ঘটাতে সক্ষম হয়নি ?
যেহেতু ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম সেহেতু মানব জীবনের সকল দিকের ওপরই প্রভাব রয়েছে। ইরানীদের অবদানও তাই ইসলামের সকল দিক ও অঙ্গনে বিস্তৃত। আমরা এ বিষয়ে আমাদের সুযোগ ও জ্ঞানের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন দিক ও বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করব।
প্রথম যে অবদানের কথা আমরা উল্লেখ করব তা হলো ইরানীদের প্রাচীন সভ্যতা নতুন ইসলামী সভ্যতায় কি ভূমিকা রেখেছে। এই প্রাচীন সভ্যতা নবীন ও মর্যাদাপূর্ণ ইসলামী সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যদিও এ আলোচনা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় (ইসলামে ইরানীদের আন্তরিক ও সততাপূর্ণ ভূমিকা) বহির্ভূত তদুপরি যেহেতু নবীন এক বিকাশমান সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতা হতে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগতভাবেই অনেক কিছু নিয়ে থাকে এবং ইরানীদের অবদানের বিষয়টিও এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই বিষয়টি উল্লেখ ব্যতীত এ আলোচনা অসম্পূর্ণ মনে করছি।
তা ছাড়াও বইটির নাম যেহেতু‘
ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান’
সেহেতু ইরান সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপনে আমরা সাধারণভাবে ইরানী মুসলমানদের অবদানের বাইরের বিষয়ও উপস্থাপনে অনেকটা বাধ্য। কারণ এ পর্যায়ে পাঠকগণ স্বাভাবিকভাবেই এ সম্পর্কেও জানতে চাইবেন।
ইসলামে ইরানী মুসলমানদের অবদানের আলোচনার শেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা যে ভূমিকা রেখেছে তার দিকে আমরা আলোকপাত করব। যেমন ইসলামের প্রচার ও প্রসার ,অন্য জাতিসমূহের নিকট এর আহ্বান ও উপস্থাপন ,শিক্ষা ও সংস্কৃতি ,শিল্প-বিজ্ঞান ,সামরিক ,যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি। প্রথমেই নবীন ইসলামী সভ্যতায় প্রাচীন ইরানী সভ্যতার অবদান নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করছি।
ইরানী সভ্যতা
ইরানী সভ্যতার স্বরূপ ও এর মূল্যবোধসমূহের যথার্থতা যাচাই এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়। তাই হাখামানেশীয় যুগ হতে সাসানী আমল পর্যন্ত এ সভ্যতায় যে রূপান্তর ঘটেছে তার আলোচনাতে আমরা প্রবেশ করতে চাই না। কারণ প্রথমত এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের ন্যায় মত দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত এ বিষয়গুলো আমাদের আলোচনা বহির্ভূত বিষয়। আমরা এখানে বিশেষজ্ঞদের সমর্থিত প্রামাণ্য ইতিহাস ও তাদের মতামতের ওপর নির্ভর করে আলোচনা শুরু করব। সুতরাং এ বিষয়ে যা কিছুই বলব তা বিভিন্ন ব্যক্তি হতে উদ্ধৃতি মাত্র। এ ক্ষেত্রে দু’
টি বিষয় প্রমাণিত ও অকাট্য হিসেবে স্বীকৃত।
এক ,ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও ইরান এক দীর্ঘ ও উজ্জ্বল সভ্যতার ধারক ছিল। এ সভ্যতা বেশ প্রাচীন।
দুই ,ইরানে ইসলামের প্রবেশের পরবর্তীকালে ইসলামী সভ্যতা এ সভ্যতা হতে উপকৃত হয়েছে।
পি.জে. দুমানাশের বর্ণনায় রয়েছে ,“
ইরানীরা এক বর্ণাঢ্য ও প্রশিক্ষিত সভ্যতা ইসলামের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং ইসলামও ইরানীদের দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল।”
ইরান যে বর্ণাঢ্য ও প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী ছিল যদিও তা ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন নেই তদুপরি এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অর্থহীন হবে না।
ড. রেজা যাদেহ্ শাফাক তাঁর‘
মধ্যপ্রাচ্য-বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ইরান’
গ্রন্থে ব্রেমস্টেডের‘
প্রাচীন সভ্যতার দিনকাল’
গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে হাখামানেশী আমলের সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন ,“
একদিকে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হতে সিন্ধু নদ পর্যন্ত ,অন্যদিকে ভারত মহাসাগর হতে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত প্রসারিত ইরানী ভূখণ্ডের রাজকার্য পরিচালনা সহজ কাজ নয়। ইতোপূর্বে কোন শাসক এত বড় সম্রাজ্যের গুরুদায়িত্বে ছিলেন না যা সাইরাসের রাজত্বকালে শুরু হয় এবং দরভীশের রাজত্বকাল পর্যন্ত (585-525 খ্রিষ্টপূর্ব) বিদ্যমান ছিল। এরূপ বৃহৎ পরিসরে রাজ্য শাসন ও পরিচালনার নমুনা তৎকালীন সময়েই প্রথমবারের মত স্থাপিত হয়- যাকে মধ্য এশিয়ায় ,এমনকি সমগ্র বিশ্ব সভ্যতায় প্রথম উদাহরণ বলা যেতে পারে এবং এটি মানব ইতিহাসের লক্ষণীয় পর্যায়সমূহের একটি বলে পরিগণিত... ।”
একই গ্রন্থে হাখামানেশী আমলের নৌশক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে ,‘
দরভীশের পুত্র খাশাইয়ারশার আমলে ভূমধ্যসাগরে ইরানের কয়েকশ’
রণতরী ছিল এবং তারা সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবাহিনীর অধিকারী ছিল।
ঐ গ্রন্থে বলা হয়েছে ,‘
দরভীশের শাসনামলে একজন প্রসিদ্ধ মিশরীয় আলেম ইরানীদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। দরভীশ তাঁকে মিশরে একটি চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপনের দায়িত্ব প্রদান করেন...।”
সাসানী আমলের প্রত্নতত্ত্ব শিল্প সম্পর্কে লিখা হয়েছে :
“
ইরানী প্রত্নতত্ত্ব শিল্পের ইতিহাসে সাসানী আমলের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দালান নির্মাণ শিল্প ঐ সময়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। এখনও তৎকালীন সময়ের দালান ,প্রাসাদ ,উপাসনালয় ,সাঁকো ও নির্মিত বাঁধের ধ্বংসাবশেষ হতে এগুলোর উচ্চ শৈল্পিক কারুকার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ফার্স প্রদেশের ফিরুযাবাদ ,শাপুর ও সুরুস্তান এবং মাদায়েন (তিসফুন) ও কাসরে শিরিনের প্রাসাদসমূহ সাসানী আমলের প্রসিদ্ধ প্রত্মতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নমুনা।”
জাহেয তাঁর‘
আল মাহাসেন ওয়াল আয্দাদ’
গ্রন্থে দাবি করেছেন ,“
সাসানী আমলের ইরান অন্য সব কিছুর চেয়ে স্থাপত্য অর্থাৎ দালান নির্মাণ শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিত। তৎকালীন শিলালিপি হতে এ বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়। তখন তারা বইয়ের প্রতি তেমন গুরুত্ব দিত না। কিন্তু ইসলামী শাসনামলে দালান ও গ্রন্থ দু’
য়ের প্রতিই দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।”
উইল ডুরান্ট তাঁর‘
তারিখে তামাদ্দুন’
গ্রন্থে (ফার্সী অনুবাদের দশম খণ্ডে) সাসানী শাসনামল ও সভ্যতার বিষয়াবলী নিয়ে ষাট পৃষ্ঠা আলোচনা করেছেন। এ আমলের জ্ঞান চর্চা সম্পর্কে তিনি বলেছেন ,“
আশকানীদের শাসনামলে ইউরোপীয় ইরান ও ভারতবর্ষে প্রচলিত পাহলভী ভাষা সাসানী আমলেও প্রচলিত ছিল। ঐ সময়ের প্রচলিত শব্দের মধ্যে শুধু ছয় লক্ষ শব্দ এখন অবশিষ্ট রয়েছে যার সবগুলোই ধর্ম সম্পর্কিত। তৎকালীন সাহিত্য অত্যন্ত ব্যাপক হলেও যেহেতু এর সংরক্ষক ও বর্ণনাকারী যারথুষ্ট্র পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছিলেন সেহেতু তাঁরা অধর্মীয় চিহ্নসমূহ (ধর্মবহির্ভূত শব্দসমূহ) ব্যবহার হতে বিরত থাকতেন। ফলে তা দিন দিন বিলুপ্ত হতে থাকে। সাসানীরা সাহিত্য ও দর্শনের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক ছিলেন। খসরু আনুশিরওয়ান এ বিষয়ে অন্যদের হতে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর নির্দেশেই আফলাতুন (প্লেটো) ও অ্যারিস্টটলের চিন্তাদর্শন পাহলভী ভাষায় অনূদিত হয় এবং তা জান্দি শাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হতো।”
আমরা অবগত যে জান্দী শাপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরানী খ্রিষ্টানরা এটি পরিচালনা করত এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে এটি প্রসিদ্ধ ছিল। ইসলামী শাসনামলে ও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল। আব্বাসীয় আমলের কয়েকজন প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান চিকিৎসক ,যেমন বাখতীশু ,ইবনে মাসুইয়া ও অন্যান্যরা এ বিশ্ববিদ্যালয় হতেই শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে যখন বাগদাদ বিশ্বের জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল তখন জান্দী শাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড স্তিমিত হতে লাগল ও সময়ের পরিক্রমায় বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।
উইল ডুরান্ট সাসানী আমলের শিল্পকলা সম্পর্কে বলেছেন ,‘
সাসানী আমলের শাপুর ,ক্বাবাদ ও খসরুদের সম্পদ ও প্রতিপত্তির চিহ্ন হিসেবে তৎকালীন শিল্পকলা ব্যতীত কিছুই বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। তবে মহান সম্রাট দরভীশের শাসনকালের রাজধানী পার্সপুলিস হতে শাহ আব্বাস সাফাভীর স্থাপিত ইসফাহান পর্যন্ত ইরানী শিল্পকলার স্থিতিস্থাপকতা ও বিবর্তন আমাদের আশ্চর্যান্বিত করে।”
তৎকালীন সময়ের বুনটশিল্প সম্পর্কে তিনি বলেছেন ,
“
সাসানী আমলের বুনট শিল্প ,চিত্রকর্ম ,ভাস্কর্য ,মৃৎশিল্প প্রভৃতি সৌন্দর্য বর্ধিত ও অলংকারমূলক শিল্প সমন্বিত ছিল। মসৃণ রেশমী কাপড় ,সূক্ষ্ম সূচীকর্মযুক্ত‘
দিবা’
ও‘
দামেস্কী’
সিল্ক ,টেবিল ক্লথ ও চেয়ারের আবরণ ,ছাদ ও বারান্দার বর্ধিত অংশ ,বিছানার চাদর ও কার্পেট প্রভৃতিতে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে অভিজ্ঞতার পরশ দিয়ে হলুদ ,সবুজ ও নীল রং দিয়ে নকশা অংকিত হতো।”
মৃৎ শিল্প সম্পর্কে বলেছেন ,“
সাসানী আমলের প্রতিদিনের ব্যবহৃত কিছু মাটি ও চীনামাটির পাত্র ব্যতীত বর্তমানে কিছু অবশিষ্ট নেই। মৃৎশিল্প হাখামানেশী আমলে অগ্রগতি লাভ করেছিল এবং সাসানী আমলেও তা অব্যাহত ছিল ও আরব শাসনামলে তা পূর্ণতায় পৌঁছায়।”
উইল ডুরান্ট দাবি করেছেন ,আশকানী শাসনামলের চার শতাব্দীর স্থবিরতা ও অধঃপতনের পর সাসানী আমলে শিল্পকলা ইরানে পুনরুজ্জীবন লাভ করে। যদি সে সময়কার অবশিষ্ট স্থাপত্য ও শিল্পকলাকে যাচাই করি তাহলে দেখব পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বে তা হাখামানেশী আমলের শিল্প বিশেষত্বের সঙ্গে একেবারেই তুলনীয় নয়। তেমনি সৃজনশীলতা ,সূক্ষ্মকারুকার্য এবং রুচির দিক হতে তা ইসলাম পরবর্তী ইরানী শিল্পেরও সমকক্ষ নয়।
উইল ডুরান্ট ঐ অধ্যায়ের উপসংহারে বলেছেন ,“
তবে সামানী শিল্পকলার বিভিন্ন অবয়ব ও চিত্ররূপের প্রভাব পূর্বে ভারতবর্ষ ,তুর্কিস্তান ও চীনে এবং পশ্চিমে সিরিয়া ,এশিয়া মাইনর ,
কনস্টান্টিনোপল ,বলকান ,মিশর ও স্পেনে ব্যাপকভাবে পড়েছিল। এ শিল্পকলা গ্রীক শিল্প ও স্থাপত্যে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে ,গ্রীকরা সনাতন শিল্পকলা হতে সৌন্দর্য ও সৌকর্যমূলক বাইজান্টাইন শিল্পকলার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। খ্রিষ্টীয় ,রোমীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলাতে এর প্রভাবের কারণেই তারা গীর্জার কাঠের ছাদের স্থানে ইট ও পাথরের গম্বুজ সংযোজনের ধারা গ্রহণ করে এবং স্তম্ভযুক্ত দেয়ালের দিকে আকৃষ্ট হয়।
সাসানী স্থাপত্য হতেই ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের মসজিদে দালান কোঠা ও ভবনগুলোতে বড় বড় দরজা ও গম্বুজ তৈরির প্রচলন লাভ করে। কোন কিছুই ইতিহাসে হারিয়ে যায় না ,তবে সময়ের পরিক্রমায় সৃজনশীল সকল চিন্তা ও কর্মই পরিবর্তন লাভ করে এবং এর রং ও উৎকর্ষ মানব সভ্যতায় নিজের স্থান করে নেয়।”
‘
মধ্যপ্রাচ্যবিদগণের দৃষ্টিতে ইরান’
গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে‘
ইসলামী শিল্পকলার উৎস’
অধ্যায়ে মেট্রোপল জাদুঘরের মধ্য ও নিকটপ্রাচ্যের শিল্পকলা বিভাগের প্রধান দিমান্ড রচিত‘
এক নজরে ইসলামী শিল্পকলা’
গ্রন্থ হতে উল্লিখিত হয়েছে ,হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে আরবদের মধ্যে স্থাপত্য ও শিল্পকলার কোন চর্চা ছিল না বা থাকলেও উল্লেখ্য নয় বললেই চলে। কিন্তু সিরিয়া ,টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল (ইরাক) ,মিশর ও ইরান জয়ের পর আরবরা এতদঞ্চলের শিল্প ও স্থাপত্যকলা গ্রহণ করে। চীনা গ্রন্থ হতে জানা যায় উমাইয়্যা শাসকগণ বিজিত সকল অঞ্চল হতে স্থপতি ও বিশেষজ্ঞদের প্রাসাদ ,শহর ও মসজিদসমূহ নির্মাণের জন্য উচ্চ মজুরী দানের মাধ্যমে আকর্ষণ করতেন। দামেস্কের মসজিদগুলোতে কারুকার্য করার জন্য সিরিয়ান ও বাইজান্টাইন কারুশিল্পীদের নিয়োগ করা হয়েছিল। তারা একজন ইরানী শিক্ষকের অধীনে এ কাজ করত।
মক্কাতেও বিভিন্ন দালান নির্মাণের জন্য মিশর ও দামেস্কের কুদ্স হতে স্থপতি ও কারিগর আনা হতো। গৃহ নির্মাণের উপাদান হতে কারিগর পর্যন্ত সব কিছুই এ সকল স্থান হতে সংগৃহীত হতো। আব্বাসীয়দের সময়কাল পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ,বাগদাদের প্রাসাদসমূহ নির্মাণের জন্যও সিরিয়া ,ইরান ,মুসেল ও কুফা হতে সহযোগিতা নেয়া হতো। সুতরাং ইসলামী স্থাপত্য ও শিল্পকলা প্রাচ্যের খ্রিষ্টীয় ও সাসানী এ দু’
শিল্পকলা হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। একই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন ,ইতোপূর্বে কোন কোন বিশেষ ইসলামী স্থাপত্য ও শিল্পকলায় সাসানী স্থাপত্য ও শিল্পের প্রভাবের বিষয়টি উদ্ঘাটন করলেও বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা যায় নি ,কিন্তু সম্প্রতি বাগদাদের নিকটবর্তী তিসফুন (মাদায়েন) ,দজলা-ফোরাতের (টাইগ্রীস ,ইউফ্রেটিস) মধ্যবর্তী কিশ এবং ইরানের দামেগান অঞ্চলে যে সকল খননকার্য সম্পাদিত হয়েছে তাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের প্রত্নতাত্ত্বিক সৌন্দর্যমূলক চূর্ণকর্মের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে যেগুলো ইসলামী স্থাপত্য ও প্রত্নকলার প্রাথমিক ভিত্তি ছিল বলে নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন ,সাসানী স্থাপত্য ও শিল্পকলা ইসলামী শিল্প ও স্থাপত্যকলায় মিশে গিয়েছে। স্থপতি ও কারুশিল্পীরা কখনও কখনও একই নকশা ও কারুকার্য ব্যবহার করতেন। কখনও আবার পরিবর্তন করে বিশেষ কোন নতুন নকশা প্রণয়ন করতেন।
নেহরু তাঁর‘
বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ’
গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে‘
ইরানের প্রাচীন রীতির ধারাবাহিকতা’
নামক একটি পৃথক আলোচনায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন ইরানী শিল্প ও সংস্কৃতি দু’
হাজার বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে।
তিনি বলেন ,
“
ইরানী সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উজ্জ্বল ও দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্য দু’
হাজার বছর ধরে চলে এসেছে যা অশুরীয় সভ্যতার পর থেকে শুরু হয়েছিল। ইরানে রাজকীয় শাসন ব্যবস্থা ও ধর্মে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর ভূখণ্ড কখনও দেশীয় শাসকবর্গ কখনও বিজাতীয়দের দ্বারা শাসিত হয়েছে। ইসলাম এ দেশে প্রবেশ করে অনেক কিছুতেই পরিবর্তন সাধন করেছে। তদুপরি ইরানী শিল্পকলা এখনও পূর্বের ন্যায় অব্যাহত রয়েছে ।”
তিনি আরো বলেছেন ,
“
আরব সেনাদল মধ্য এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় অগ্রাভিযানে শুধু নতুন ধর্ম নয় ;বরং সে সাথে নব বিকাশমান এক সভ্যতাকে বহন করে নিয়ে যায়। সিরিয়া ,দজলা-ফোরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল ,মিশর সকল স্থানই আরবীয় (ইসলামী) সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ফলে আরবী ভাষা তাদের রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত হলো ,এমনকি জাতিগতভাবেও তারা আরবদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সদৃশে পরিণত হলো। দামেস্ক ,কায়রো আরবদের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। নব সভ্যতার শক্তিশালী বিবর্তন ক্রিয়ার প্রভাবে সেখানে আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদসমূহ তৈরি হলো... ইরান আরবদের সদৃশে পরিণত না হলেও ইসলামী আরব সভ্যতা তাদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ভারতবর্ষের ন্যায় ইরানেও ইসলাম শিল্পকলায় নতুন জীবন দান করে। ইসলামী আরব সভ্যতাও ইরানী সভ্যতা ও শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত হয়।”
আমরা জানি উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় আমলে বেশ কিছু ফার্সী গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয় যদিও অন্যান্য ভাষা হতে অনূদিত গ্রন্থের তুলনায় এটি তেমন কিছু নয়। তদুপরি একে ইসলামী সভ্যতায় ইরানী সভ্যতার এক প্রকার সহযোগিতা বলা যায়। আমরা পরবর্তীতে ইরানী অনুবাদসমূহের আলোচনায় এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করব।
মুসলমানগণ রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা পদ্ধতি ইরানীদের নিকট হতে গ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয় কার্যালয় ও অফিস-আদালত প্রাচীন ইরানী পদ্ধতির অনুকরণে সাজানো হয়েছিল। এমনকি সাধারণত সরকারী কার্যালয়ে ফার্সী ভাষাই ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে ইরানী মুসলমানগণ তা আরবীতে রূপান্তরিত করেন।
ইবনুন নাদিম তাঁর‘
আল ফেহেরেস্ত’
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ,
‘
সর্বপ্রথম খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার নির্দেশে অন্য ভাষা হতে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়। তিনি জ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বিশেষত রসায়নবিদ্যার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ ছিল। তিনি মিশরের অধিবাসী কতিপয় গ্রীক দার্শনিককে দামেস্কে আহ্বান জানান। যেহেতু তাঁরা আরবী ভাষাতেও পণ্ডিত ছিলেন তাই তিনি তাঁদের গ্রীক ও কিবতী ভাষার এতদ্সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুবাদ করার নির্দেশ দেন। এটিই আরবীতে অনুবাদের সূচনা।
অতঃপর বলেছেন ,
‘
হাজ্জাজের আমলে সালেহ ইবনে আবদুর রহমান নামের এক ইরানী বংশোদ্ভূত ব্যক্তি সরকারী কার্যালয় ও আদালতসমূহের কাগজপত্র ফার্সী হতে আরবীতে অনুবাদ করেন যা দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুবাদ কার্যক্রম বলে পরিগণিত। সালেহ হাজ্জাজের মন্ত্রী যদানফারাখের অধীনে কাজ করতেন। যেহেতু সালেহ আরবী ও ফার্সী উভয় ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন সেহেতু তাঁর প্রতি হাজ্জাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একদিন সালেহ যদানফারাখকে বলেন: আমার ভয় হয় ভবিষ্যতে হাজ্জাজ তোমার ওপর আমাকে প্রাধান্য দিতে পারে এবং তার নিকট তোমার অবস্থান নীচে নেমে যেতে পারে। যদানফারাখ বলেন: তুমি ভয় কর না। এটি কখনও হবে না। কারণ তোমার চেয়ে আমাকে হাজ্জাজের অধিক প্রয়োজন। হিসাবকার্যে আমার চেয়ে অভিজ্ঞ কেউ নেই। সালেহ বলেন: আল্লাহর শপথ! যদি চাই সরকারী কাগজপত্র সবই আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারি তখন ফার্সীর আর কোন প্রয়োজন পড়বে না। যদানফারাখ পরীক্ষা করে দেখলেন সালেহ সত্য বলেছেন। তাই সালেহকে বললেন: তুমি কয়েকদিন অসুস্থতার অজুহাতে দরবারে এসো না। হাজ্জাজ তার বিশেষ চিকিৎসককে সালেহের নিকট প্রেরণ করলে তিনি ফিরে এসে হাজ্জাজকে জানালেন তাঁর মধ্যে অসুস্থতার কোন লক্ষণ নেই। ইতোমধ্যে মুহাম্মদ ইবনে কায়েসের বিদ্রোহের দাঙ্গায় যদানফারাখ নিহত হলে স্বাভাবিকভাবেই সালেহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। একদিন যদানফারাখের সঙ্গে নিজ কথোপকথনের বিষয়টি সালেহ হাজ্জাজের নিকট উপস্থাপন করলে অনুবাদের এ কর্ম বাস্তব রূপ লাভ করে।
কিন্তু এ বিষয়টি ফার্সী ভাষাভাষীদের ক্ষুব্ধ করে তুলল। বিশেষত যারা ফার্সীভাষী হওয়ার কারণে এরূপ কর্মে নিয়োগ লাভ করেছিল তারা খুবই মনক্ষুন্ন হলো। একদিন যদানফারাখের পুত্র সালেহকে হিসাব সম্পর্কিত কয়েকটি ফার্সী পরিভাষার আরবী রূপ কি হবে তা জানতে চাইলে তিনি সমার্থের আরবী পরিভাষা বর্ণনা করেন। এতে সে রাগান্বিত হয়ে বলে: আল্লাহ্ তোমার শিকড় ধ্বংস করুন। কারণ তুমি ফার্সী ভাষার শিকড় কেটেছ। একদল ফার্সীভাষী সালেহকে এক লক্ষ দিরহাম দিয়ে এ কর্মে অপারগতা প্রকাশ করতে বললে তিনি রাজী হননি।”
ইবনুন নাদিম বলেন ,
“
সিরিয়ার দরবারীরা রাজকীয় নথিপত্র ও হিসাব রোমীয় ভাষায় লিখত (ফার্সী ভাষায় নয়)। হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের সময়ে তা-ও আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়।”
এ বিষয়গুলো তৎকালীন খলীফা ও শাসকবর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। আরবদের কাছ থেকে স্বাধীন হওয়ার পর ইরানী শাসকবর্গ তাঁদের সরকারী নথিপত্র ও হিসাব পুনরায় ফার্সীতে লেখা শুরু করেন। গজনভীদের শাসনামলে এটি আবার আরবীতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ইতিহাসও দীর্ঘ।
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ,এ আলোচনায় আমরা প্রাচীন ইরানী সভ্যতা নবীন ইসলামী সভ্যতায় কি ভূমিকা রেখেছে তার প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করব। তবে এ কর্মের যোগ্যতা আমাদের নেই। তাই প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে দু’
টি বিষয়কে আমরা তুলে ধরেছি: প্রথমত ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও ইরান স্বতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার অধিকারী ছিল এবং এ সভ্যতা ইসলামী সভ্যতার অন্যতম উৎস বলে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়ত ইরানের পতনশীল সভ্যতা ইসলামের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত হয় এবং ইসলাম ইরানকে নতুন জীবন ও রূপ দান করে। এ দু’
টি বিষয় অনস্বীকার্য। অনুসন্ধিৎসুরা এ সম্পর্কিত বিদ্যমান পর্যাপ্ত সূত্রে তা অধ্যয়ন করতে পারেন।
ইসলাম ও আন্তরিকতা
এখন আমরা আমাদের প্রকৃত আলোচনায় প্রবেশ করব। তা হলো ইরানীরা ইসলামে যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তা ঈমান ,ইসলাম ও আন্তরিকতার ভিত্তিতেই করেছে। আমরা প্রথমে ইরানীদের ইসলাম ও আন্তরিকতা নিয়ে আলোচনা করব । তারপর তাদের অবদানের বিষয়টি আলোচনায় আনব।
ইরানীদের অবদানের বিষয়টি নিয়ে অতিরঞ্জিত করার ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা এ দাবিও করছি না যে ,সকল ইরানীই ইসলামের প্রতি নিবেদিত ও আন্তরিক ছিল বা তাদের সকলের অবদানই পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও সম্পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সম্পাদিত হয়েছিল। আমরা যা দাবি করছি তা হলো অধিকাংশ ইরানী ইসলামের প্রতি আন্তরিক ছিল ,তারা ইসলামের খেদমত ব্যতীত অন্য কোন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেনি এবং নিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরব-অনারব কেউই ইরানীদের সমকক্ষ নয়। তারা এ ক্ষেত্রে পৃথিবীতে অনন্য অর্থাৎ কোন জাতিই কোন ধর্মের প্রতি এতটা খেদমত করেনি বা এতটা নিবেদিত সেবা দেয়নি।
একটি জাতিকে শক্তি প্রয়োগে অনুগত করা যায় ,কিন্তু বাহুবলে তাদের মাঝে ঈমানী চেতনা ,প্রেম-ভালবাসা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায় না। শক্তি ও ক্ষমতা এ ক্ষেত্রে পরিসীমিত। মানব জাতির সেরা সৃষ্টি ও অবদানসমূহ ভালবাসা ও ঈমানের ফল।
কেউ কেউ ইসলামী সংস্কৃতিতে ইরানীদের অভূতপূর্ব অবদানের পেছনে কাদেসীয়া ,জালুলা ,হালওয়ান ও নাহাভান্দে আরবদের নিকট পরাজয়ের ক্ষতিপূরণের মনোবৃত্তি কার্যকর ছিল বলে মনে করেন। কারণ ইরানীরা জানত সামরিক পরাজয় সার্বিক পরাজয় নয় ;বরং প্রকৃত পরাজয় হলো সাংস্কৃতিক পরাজয়। ইরানীরা জাতীয় চেতনার অনুভূতিতে অন্য জাতির বিরুদ্ধে বিশেষত আরবদের মুকাবিলায় স্বকীয় সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের প্রয়াসে ইসলামী বৈশিষ্ট্যসমূহের আবরণে নিজ চিন্তা-চেতনা ,রীতি-নীতি ও আচারকে আচ্ছাদিত করে এবং এ লক্ষেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালায়। অন্যভাবে বলা যায় ,ইসলামকে বাস্তবতার কারণে প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে কিভাবে একে ইরানী রূপ দেয়া যায় সে চিন্তায় মগ্ন হয়। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ইসলামী জ্ঞান আহরণ অপেক্ষা উত্তম কোন পথ ছিল না বলে এ পথকে মনোনীত করে।
আমাদের বিশ্বাস এরূপ ব্যাখ্যা সত্য হতে অনেক দূরে। কারণ প্রথমত পূর্বেই আমরা বর্ণনা করেছি ,মুসলমানদের হাতে ইরানের সামরিক পরাজয়ের অনেক পূর্ব হতেই ইরানীরা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল । ইরানীরা সামরিক পরাজয়ের পরে ইসলামের যে খেদমত করেছে তা সামরিক পরাজয়ের পূর্বের মতই। দ্বিতীয়ত যদি এ আন্তরিক উদ্দীপনা না থাকত তবে তা চৌদ্দ শতাব্দী যাবত অব্যাহত থাকতে পারত না। কোন ক্ষণস্থায়ী আন্দোলনকে এরূপ ব্যাখ্যা দেয়া যায় ,কিন্তু শতাব্দীকাল ধরে বহমান কোন আন্দোলনকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।
সময়ের দীর্ঘতার বিষয়টি বাদ দিলেও আন্দোলনের ধরন ও প্রকৃতিও ঐরূপ প্রবণতার উপস্থিতিকে প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানীদের কর্ম পদ্ধতি ও ধরন যে তাদের ঈমান ও নিষ্ঠার প্রমাণ দেয় তা আমরা দেখব।
তদুপরি যদি সামরিক পরাজয়ের ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে ইরানীরা ইসলামের সেবায় রত হয়ে থাকে তবে স্বয়ং তারা কেন ইসলামের প্রচারক সেজে অন্যান্য জাতি হতে নিজেদের সংখ্যার কয়েকগুণ মানুষকে ইসলামের পতাকা তলে নিয়ে আসল ? যখন ইসলাম হুমকির সম্মুখীন হয়েছে ইরানী দৃষ্টিতে তা ক্ষতিকর কিছু না হওয়া সত্ত্বেও কেন তারা নিজেদের জীবন বাজী রেখে ইসলামকে রক্ষার প্রচেষ্টায় আত্মবিসর্জন দিয়েছে ? কেন ইসলামের বিপক্ষে অন্যায় প্রচারণা ও অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে তারা অন্যদের চেয়ে অধিকতর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ?
পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। এখন ইসলামী জাতিসমূহের মধ্যে জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উদ্দীপনার কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা শুরু করছি।
উদ্দীপনাসমূহ
প্রথমেই উদ্দীপনার দৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে ইসলামী বিশ্বকে মূল্যায়নের প্রয়োজন মনে করছি। ইসলামী বিশ্ব জ্ঞান ও সাংস্কৃতির যে আন্দোলন শুরু করে তাতে আরব ,ইরানী ,ভারতীয় ,মিশরীয় ,আলজিরীয় ,তিউনিসীয় ,মরোক্কীয় ,সিরীয় ,এমনকি ইউরোপীয় স্পেনও অংশগ্রহণ করে। এ আন্দোলনে ইসলামী ভূখণ্ডের দূরপ্রাচ্য হতে দূরপাশ্চাত্য পর্যন্ত যেমন সংযুক্ত হয়েছিল তেমনি ইসলামী বিশ্বের উত্তর প্রান্ত হতে দক্ষিণ প্রান্তও সংযুক্ত ছিল। এ আন্দোলনে যেমন ইরানের ইবনে সিনা ,রাযী ও সিবাভেইরা অংশগ্রহণ করেছেন তেমনি স্পেনের (আন্দালুসের) ইবনে মালিক ইবনে রুশদও ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু এ বৃহৎ আন্দোলনের উদ্দীপক কি ছিল ? এ ক্ষেত্রে কয়েকটি মত হতে পারে।
1. এ সকল জাতির মধ্যে আরবীয় জাতীয় চেতনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা সকলেই আরব জাতীয়তাবাদের ছায়ায় এরূপ সমঝোতাপূর্ণ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল।
অবশ্যই এরূপ ধারণা সঠিক নয় ;যদিও কোন কোন সাম্প্রতিক আরব লেখক ইতিহাসকে এভাবে বিকৃত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।
কোন কোন ইউরোপীয় লেখক ইসলামী সভ্যতাকে আরবীয় সভ্যতা হিসেবে দেখাতে চান। এর উদ্দেশ্য হলো একদিকে আরবদের আত্ম-অহংকারী করার মাধ্যমে পূর্ব হতে অধিকতর আরব জাতীয়তাবাদের ওপর নির্ভরশীল করে ইসলামী বিশ্ব হতে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়া ও বিচ্ছিন্ন করা। অন্যদিকে অন্যান্য মুসলিম জাতিকে এরূপ মিথ্যা প্রচারণার কারণে আরবদের ওপর অসন্তুষ্ট করা।
2. ইসলামী জাতিসমূহ প্রত্যেকেই স্ব স্ব জাতি ও গোত্রের চিন্তার আলোকে কার্যক্রম চালাত। তাদের প্রত্যেকের প্রবণতা নিজস্ব জাতীয় অনুভূতি হতে জাগরিত হয়েছিল।
এ মতও যে গ্রহণযোগ্য নয় তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। আমরা এ গ্রন্থের প্রথমাংশে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করেছি। ইসলামী জাতিসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীরে প্রবেশের কারণেই ভারতীয় ,ইরানী ,আফ্রিকীয় বা স্পেনীয় মুসলমান পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছিল।
3. মুসলিম জাতিসমূহ তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র ও জাতিগত বিশেষত্ব সত্ত্বেও জাতি-বর্ণের ঊর্ধ্বে একক চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে জীবন যাপন করত এবং তাদের জ্ঞান ও সংস্কৃতিগত কর্মকাণ্ডের উদ্দীপনা তারা ইসলাম ,ইসলামের বিশ্বজনীন ও মানবিক শিক্ষা হতে লাভ করেছিল। ইতিহাস এ সত্যকেই সমর্থন ও প্রমাণ করেছে।
কোন ব্যক্তি বা জাতির ঐতিহাসিক ভূমিকার পশ্চাতে কোন্ উদ্দীপনা কাজ করেছে তা জানতে হলে তার কর্মপদ্ধতি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করতে হবে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ইরানীদের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করব যা তাদের এ ঐতিহাসিক অবদানের পশ্চাতের উদ্দীপনাসমূহকে আমাদের নিকট তুলে ধরবে।
এখানে আমরা আত্তারাদীর লেখা হতে কিছু অংশ‘
ইরানীদের ইসলামী কর্মকাণ্ড’
শিরোনামে তুলে ধরছি।
 0%
0%
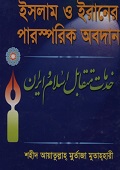 লেখক: শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী
লেখক: শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী