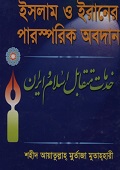চীনে ইসলামের প্রবেশ ও বিস্তার
সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান মতে চীনে বর্তমানে পাঁচ কোটি মুসলমান বাস করেন। চীনে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার একদল মুসলমান-যাঁরা সেখানে হিজরত ও বসতি স্থাপন করেছিলেন ,তাঁদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল। চীনে ইসলামের প্রচারে ইরানী মুসলমানদের ভূমিকা বেশ ব্যাপক ছিল।
‘
সিরাতে মুস্তাকিম’
নামক গ্রন্থে‘
চীনে ইসলামী সংস্কৃতি’
শিরোনামের এক প্রবন্ধে চীনে ইসলামের প্রবেশ ,উন্নয়ন ও ক্রমাবনতির যুগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চীনে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ইরানীদের ভূমিকা এ প্রবন্ধে লক্ষণীয়।
তিনি চীনে ইসলামের প্রবেশের এক নাতিদীর্ঘ ইতিহাস চীনের বিভিন্ন গ্রন্থসূত্র ও উৎস হতে উল্লেখ করেছেন। কোন ইসলামী উৎসে তা উল্লিখিত হয়নি বলে তিনি বলেছেন। তিনি বলেন ,
“
তাং বংশের প্রাচীন ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে সম্রাট ইয়াংভির শাসনামলের দ্বিতীয় বর্ষে (31 হিজরীতে) মদীনা হতে দূত তাঁর দরবারে কিছু উপঢৌকন ও উপহার নিয়ে আসেন। দূত বর্ণনা করেন যে ,একত্রিশ বছর হলো তাঁদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে... সম্রাট দূতকে কিছু প্রশ্ন করার পর ইসলাম সম্পর্কে যা শুনতে পান তাতে একে কনফুসিয়াসের শিক্ষার অনুরূপ বলে বুঝতে পারেন। তিনি ইসলামকে সত্যায়ন করেন ,কিন্তু প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও বছরে এক মাস রোযার বিষয়টি পালন কষ্টকর মনে করেন। তাই তা পালনে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি মদীনা হতে আগত দূত সা’
দ
ও তাঁর সঙ্গীদের চীনে ইসলাম প্রচারের অনুমতি দেন এবং‘
চানগান শহর’
-এ সর্বপ্রথম মসজিদ স্থাপনে নিজ সম্মতি ঘোষণা করেন । এভাবে তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রদর্শন করেন। এই মসজিদটি ইসলামী ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকর্ম যা এখনও পুনঃপুন সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যমান রয়েছে।’
যদি উপরোক্ত ঘটনা সত্য হয় তবে ইসলাম আরব মুসলমানদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম চীনে প্রবেশ করে । এ ঘটনা ছাড়াও চীনে মুসলমান বণিকগণ যাঁদের অনেকেই ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন তাঁরা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
একই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে ,
“
বনি উমাইয়্যা ও আব্বাসীয়দের শাসনামলে মুসলিম বণিক ও ধর্মপ্রচারকদের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বনি উমাইয়্যার শাসনামলে অনেক আরব বণিকই চীনে গিয়েছিলেন যাঁদের‘
আরব শুভ্র পোশাকধারী’
বলা হতো। আব্বাসীয়দের খেলাফতকালে মুসলিম ও চীন সম্রাজ্যের মধ্যে অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক গড়ে উঠলে প্রচুর আরব বণিক সেখানে যান। তাঁরা‘
কৃষ্ণ পোশাকধারী’
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
...একশত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে (31 হতে 184 হিজরী পর্যন্ত) প্রচুর সংখ্যক আরব ও ইরানী বণিক চীনে পৌঁছে এবং চীনের কুয়াংচু বন্দরে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে তারা তীরবর্তী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে যায় ও ধীরে ধীরে উত্তর চীনের হাংচু শহর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে... ইতোমধ্যে দক্ষিণ চীনে মুসলিম বণিকদের সংখ্যা বেশ বেড়ে যায়। তাদের অনেকেই চীনাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। এই মুসলামানদের ভিন্ন সমাজ ছিল। তারা অন্য ধর্মাবলম্বী চীনাদের হতে স্বতন্ত্রভাবে ইসলামের প্রাত্যহিক ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন শুরু করে ,এমনকি বিবাহ ,তালাক ,উত্তরাধিকার ও অন্যান্য ইসলামী বিধিবিধানের ক্ষেত্রে তাদের স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ ছিল। এটি তৎকালীন সময়ে মুসলিম সমাজের প্রভাব ও আধিপত্যের একটি প্রমাণ।”
তিনি আরো বলেন ,
“
ইরানী ও আরব ব্যবসায়ীরা চীন হতে রেশমী বস্ত্র ,চীনামাটির পাত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নিয়ে যেত। আবার ঐ সকল অঞ্চল হতে মশলাদ্রব্য ,উদ্ভিজ্জ চিকিৎসা উপকরণ ,মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর ও সামগ্রী চীনে নিয়ে আসত। এ বণিকরা এই লাভজনক ব্যবসায়ের মাধ্যমে অন্যান্য মুসলিম বণিকদেরও চীনে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করত। ফলে মুসলিম বণিকদের নতুন নতুন দল চীনে প্রবেশ করে উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও ধর্মীয় প্রচারও বৃদ্ধি পায়।”
ঐ গ্রন্থে আরো উল্লিখিত হয়েছে :
“
চীনের উত্তরাঞ্চলে অধিকাংশ ভারবাহী পশু (বাণিজ্য কাফেলার জন্য ব্যবহৃত) ,যেমন উট ,ঘোড়া ও গাধা মুসলমানদের অধিকারেই ছিল। এ ছাড়াও ইয়াংতিসি ও হাওয়াইহু
নদী ও এদের শাখা-প্রশাখার তীরবর্তী অঞ্চলে যে ধান উৎপন্ন হতো তা বেচাকেনা ও বহন ,মেষ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্রয়-বিক্রয় সবই মুসলমানদের দ্বারা সম্পন্ন হতো। এখনও বিভিন্ন প্রাণীর বেচাকেনায় ফার্সী পরিভাষার ব্যবহার তৎকালীন সময়ে এতদঞ্চলে মুসলমানদের প্রভাবের বিষয়টিকে প্রমাণ করে।”
তিনি অন্যত্র বলেছেন ,
“
চীনের মুসলমানগণ দু’
ভাগে বিভক্ত ছিল। একদল হলো সিকিয়াং-এর মুসলমানগণ যাদের পাগড়ীধারী মুসলমান বলা হয় এবং অন্যদল হলো‘
হান’
গণ...‘
হান’
মুসলমানগণ সাধারণত দীনী বিষয়ে আরবী ও ফার্সী পরিভাষা বিশেষত ফার্সী পরিভাষা বিশেষ গঠনরূপে ব্যবহার করে থাকে।”
এ গ্রন্থে আরো উল্লিখিত হয়েছে ,
“
মসজিদের আলেমদের প্রধানকে‘
আখুন্দ’
অথবা‘
অখুনাক’
বলা হতো যার অর্থ ইসলামী বিধান শিক্ষাদাতা। জামায়াতের নামাজের ইমাম প্রধান আলেমের সহযোগী বলে বিবেচিত হতেন... চীনের তৎকালীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইরান ও আরবের অনুকরণে ছিল।”
‘
হেযারেয়ে শেখ তুসী’
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সাইয়্যেদ জাফর শাহিদী‘
বিশ্বে ইসলামের প্রসারে ইরান জাতির অবদান’
শীর্ষক প্রবন্ধে (যা তিনি গত বছরে অনুষ্ঠিত শেখ তুসীর সহস্রতম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পাঠ করেন) চীনে ইসলামের প্রবেশের বিষয়ে আতা মূলক জুয়াইনীর‘
জাহান গুশাই’
গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ,
“
এ বিষয়টি (নবুওয়াতের সত্যতা) বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব এবং কল্পনা হতেও দূরে নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিতে দু’
টি বিষয় রয়েছে: প্রথমত নবুওয়াতের প্রকাশ ,দ্বিতীয়ত নবুওয়াতের বাণী। এটি একটি শক্তিশালী অলৌকিক নিদর্শন যে ,ছয়শ’
বছরের কিছু পর নবী (সা.)-এর বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছিলেন: আমার জন্য পৃথিবী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। সুতরাং আমি দেখতে পাচ্ছি পূর্ব-পশ্চিমের সেই প্রস্তুত হয়ে থাকা দেশগুলোকে যেখানে আমার উম্মতের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।”
এটি বহিঃশত্রুর পতনের মাধ্যমে সম্ভবপর হবে... এবং এর ফলে ইসলামের পতাকা সমুন্নত ,ইসলাম ধর্মের প্রদীপ প্রজ্বলিত এবং মুহাম্মদী দীনের আলো সকল ভূমিকে আলোকিত করবে ,অথচ এমন ভূমিতে ইসলামের আগমন ঘটেছিল যেখানে পূর্বে ইসলামের সুগন্ধ কখনও পৌঁছেনি ,তাদের অধিবাসীরা আজান ও তাকবীরের ধ্বনি শুনেনি ,নাপাক লাত ও উজ্জার উপাসনা ছাড়া সেখানে কিছু ছিল না। আর এই ভূমিতেই কিছু মুমিনের সৃষ্টি হয় যাঁরা নিজ ভূমির সীমা অতিক্রম করে দূরবর্তী স্থানে পৌঁছেন ও সেখানে বসতি স্থাপন করে ইসলামের বাণী প্রচার করেন ।
অনারবদের কেউ কেউ খোরাসান ও উজবেকিস্তান (সামারকান্দ ও বোখারা) হতে মোগলদের মাধ্যমে কারিগর ও পশুপালক হিসেবে তাদের বিজিত ভূমিতে (চীনে) কাজের জন্য গৃহীত হয় এবং কেউ কেউ সিরিয়া ,ইরাক ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চল হতে ব্যবসায় অথবা পর্যটনের উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলে যায়। তারা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই পরিচিতি লাভ করেছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপসনালয়ের পাশাপাশি মসজিদ ,মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আলেমগণ ধর্মীয় শিক্ষা ,জ্ঞান ও নিজ চিন্তা-মতকে সবার মধ্যে প্রচার করেন ও একে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সম্ভবত এ সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসূল (সা.) বলেছিলেন ,“
চীনে গিয়ে হলেও জ্ঞান শিক্ষা কর।”
ছয়শ’
বছর পর ইরানী ও অ-ইরানী ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণ চীনে যাবেন ও তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত করবেন এ সম্পর্কিত নবীর ভবিষ্যদ্বাণীকে আতা মূলক জুয়াইনী তাঁর অন্যতম মুজিযা মনে করেছেন।
ইসলামের পথে আত্মোৎসর্গীকৃত সামরিক সেবা
ইসলামের পথে ইরানীদের সামরিক সেবা ইসলাম ও ইরানের সম্পর্কের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এই সামরিক সেবা তারা আন্তরিকভাবেই দিয়েছিল।
আমরা ইয়েমেনের অধিবাসী ইরানী মুসলমানদের আত্মত্যাগী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছি। উমাইয়্যা শাসকদের বিরুদ্ধে ইরানীদের আন্দোলন আব্বাসীয়দেরকে ক্ষমতায় বসায় তাও এরূপ ভূমিকার সাক্ষ্য। তাদের এই সামরিক অভ্যুত্থান শুধু আরবদের ইসলামের সঠিক ধারায় প্রত্যাবর্তন করানো ও প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ছিল। যদিও এই সামরিক অভ্যুত্থানের বিজয়ে উমাইয়্যাদের পতন ঘটেছিল ,কিন্তু তার পরিবর্তে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের হতে উত্তম ছিল না। ফলে উত্তম কোন ফল হয়নি।
দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে ইরানের অভ্যন্তরেই কিছু আন্দোলন শুরু হয় যা ইসলামবিরোধী ছিল বিধায় দমন করা হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ,এ ইসলামবিরোধী আন্দোলনগুলোকে আরবরা নয় ,ইরানীরাই দমন করে।
তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে আজারবাইজানে ববাক খুররাম দীনের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ হয় যদি ইরানী সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিকরা না থাকত তাহলে আড়াই লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে তা দমন করা সম্ভব হতো না। আল মুকাননাহ্ ,সিনবাদ অথবা উসতাদাসিসের নেতৃত্বে যে আন্দোলনগুলো হয়েছিল তাও অনুরূপ। সুলতান মাহমুদ গজনভী ভারতবর্ষে যে সকল সেনা অভিযান চালান তাতে ইসলামী জিহাদের রং দিয়েছিলেন বলেই ইরানীরা জিহাদের উদ্দীপনা নিয়ে ভারতের বিজয়ে অংশ নিয়েছিল। তেমনিভাবে ইরানের বিভিন্ন সম্রাট পাশ্চাত্যের পক্ষ হতে পরিচালিত ক্রুসেডের যুদ্ধগুলোতে ইরানী মুসলমানদের ইসলামী অনুভূতি ও চেতনাকে ব্যবহার করেছিলেন বলেই ভাল ফল পেয়েছিলেন।
ইরানী সৈন্যরাই এশিয়া মাইনরে ইসলামের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল ,আরবরা নয়। এখানে‘
হাজারেয়ে শেখ তুসী’
গ্রন্থের ডক্টর সাইয়্যেদ জাফর শাহিদীর প্রবন্ধ হতে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেছেন ,
“
মুসলমানগণ পূর্ব রোমকে রোমসাম্রাজ্য এবং ভূমধ্যসাগরকে‘
রোম সাগর’
বলে থাকে। এ কারণেই এশিয়া মাইনরকে (তুরস্ক ,লেবানন ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য দেশও এর অন্তর্ভুক্ত) তারা রোম বলত।... মুসলমানরা যখন সমগ্র সিরিয়া দখল করে তখন এশিয়া মাইনরও হস্তগত করা তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। খলীফা হযরত উমরের শাসনামলে মুয়াবিয়া চেয়েছিলেন ঐ অঞ্চলে আক্রমণ করতে ,কিন্তু খলীফা অনুমতি দেননি। খলীফা হযরত উসমানের শাসনামলে তাঁর অনুমতি নিয়ে তিনি আমুবিয়া পর্যন্ত জয় করেন। কিন্তু তখন হতেই এই ভূমি নিয়ে মুসলমান ও রোমীয়দের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এতদঞ্চলের ভূমি ,শহর ও দুর্গগুলো কখনও উমাইয়্যা বা আব্বাসীয় খলীফাদের আওতায় কখনও রোমীয়দের আওতায় হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক সাক্ষ্য মতে উমাইয়্যা বা আব্বাসীয় খলীফা কারো পক্ষেই সমগ্র অঞ্চলে ইসলামের স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।... দীর্ঘ সময় পর একমাত্র সালজুকীদের শাসনামলে এই অঞ্চলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে এবং সমগ্র এশিয়া মাইনর তাদের অধীনে আসে। এ সময়েই ইসলামের বাণী ও শিক্ষা সেখানে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচারিত হয় এবং এতটা বিকাশ লাভ করে যে ,ইসলামী অধ্যাত্মবাদের প্রবাদ পুরুষ জালালুদ্দীন রুমীর ন্যায় ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় ও এই জ্যোতি সকল ফার্সী ভাষী ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।
এ অংশটি অকসারায়ী প্রণীত‘
মুসামেরাতুল আখবার’
নামক এশিয়া মাইনরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ হতে বর্ণনা করছি। কারণ এ গ্রন্থে এতদঞ্চলের ইরানী শাসক ও মুসলমান জনসাধারণের চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। যদি ইরাক ও পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলোতে মুসলিম খলীফাদের আক্রমণ এ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে যে ,জিযিয়া লাভের মাধ্যমে বায়তুল মালের পরিমাণ বৃদ্ধি ;পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে ইরানী মুসলিম বিজেতাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু ইসলামের প্রচার ও প্রসার। অকসারায়ী বর্ণনা করেছেন ,‘
রোম সম্রাট আরমিয়ানুস এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ইসলামী ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হলেন। প্রথমে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের
সীমান্তবর্তী নাকিসারুসিওয়াম ,তুকাত ,আবলিস্তান ও অন্যান্য অংশে আক্রমণের চিন্তা করেন। এতদঞ্চলের শাসক দানেশমান্দ মুসলিম শাসক কাল্জ আরসালানের নিকট দূত পাঠিয়ে কাফেরদের মোকাবিলায় উৎসাহিত করলেন ও প্রতিশ্রুতি দিলেন যদি মুসলমানরা জয়ী হয় তাহলে তাদের এক লক্ষ দিনার ও আবলিস্তান উপহার দেবেন। কাল্জ আরসালান ইসলামী দৃষ্টিতে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে অন্যান্য মুসলিম শাসকদের সহযোগিতা নিয়ে বড় এক সেনাবাহিনী নিয়ে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁরা বিজয় লাভ করেন এবং আরমিয়ানুস যুদ্ধ হতে পলায়নে বাধ্য হন ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর খুব কমই প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়। সম্রাট দানেশমান্দ কাল্জ আরসালানের নিকট এক লক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে আবলিস্তান হস্তান্তরে সম্মত হলেন। মুসলিম শাসক কাল্জ আরসালান এ কথা শুনে ঐ এক লক্ষ দিরহাম ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন ,“
আমি ইসলামের জন্য এ যুদ্ধ করেছি। দিনার ও দিরহামের আমার কোন প্রয়োজন নেই।”
একই গ্রন্থে ভারতবর্ষে মুসলমানদের সামরিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে :
“
43 হিজরীতে প্রথমবারের মতো আবদুল্লাহ্ ইবনে সাওয়ার আবদী ,আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের ইবনে কুরাইযের পক্ষ হতে সিন্ধু প্রদেশে আক্রমণ চালান ও ব্যর্থ হন। 44 হিজরীতে মুহাল্লাব ইবনে আবি সুফরাহ্ সেখানে আক্রমণ চালান ,কিন্তু সফল হননি। 89 হিজরীতে মুহাম্মদ বিন কাসিম এক যুদ্ধে সিন্ধুর রাজাকে পরাস্ত করেন ও তাঁকে হত্যার মাধ্যমে এ অঞ্চল মুসলমানদের হস্তগত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচারকার্য ইরানীদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল।
এখানেও আমরা ঐতিহাসিক সূত্র লক্ষ্য করলে দেখতে পাই ঐতিহাসিক জারফাদকানী বাদশাহ নাসিরুদ্দীন সাবক্তাকীন সম্পর্কে বলেছেন ,“
তিনি কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ ও ইসলামের শত্রুদের দমনের কাজ শুরু করেন এবং মূর্তিসমূহের উপাসনালয় ও ইসলামের শত্রুদের আবাসস্থলকে ধর্মীয় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেন।”
সুলতান মাহমুদ গজনভীর জীবনী আলোচনায় তিনি লিখেছেন ,“
সুলতান ইয়ামিনুদ্দৌলা ও আমিনুল মিল্লাহ্ যখন ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ দখল করতে শুরু করেন তখন এমন দূরবর্তী স্থানসমূহেও পৌঁছান যেখানে কখনও ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হয়নি ও কোন সময়েই মুহাম্মদী ধর্মের দাওয়াত ,কেরাআনের আয়াত ও মুজিযার কথা পৌঁছেনি। তাঁরা সেখান হতে র্শিক ও কুফরের অন্ধকার দূর করেন ,ইসলামের শরীয়তের মশালকে সেখানকার শহর ও গ্রামগুলোতে নিয়ে যান ,মসজিদসমূহ তৈরি করেন ,কোরআন পাঠ ও শিক্ষাদান শুরু করেন ,ইসলামের আজান ও ঈমানের আহ্বানকে প্রকাশ করেন...।”
সুলতান মাহমুদ গজনভীর প্রাচ্যে বিজয় অভিযান ও শাসন পদ্ধতির সঙ্গে স্পেনে প্রথম মুসলিম শাসক আবদুর রহমানের আচরণের তেমন অমিল না থাকলেও প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলামের বিজয় অভিযানের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। আরব মুসলমানরা পাশ্চাত্যে তাদের বিজয় অভিযান ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত চালাতে সক্ষম হলেও ইতিহাসের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে তা মুসলমানদের আধিপত্যের বাইরে চলে যায় এবং ঐ অঞ্চলের নবীন মুসলমানরাও ইসলাম ত্যাগ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। কিন্তু ইরানী জাতিভুক্তদের মাধ্যমে প্রাচ্যে ইসলামী সভ্যতার যে ভিত্তি স্থাপিত হয় তা এতটা দৃঢ় ও মজবুত ছিল যে শত শত বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও এতদঞ্চলের মানুষ মুসলমান হিসেবে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে ও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো ,যে বছর
আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলের একটি অংশ ইসলামের শত্রুদের দ্বারা অধিকৃত হয়
সে বছরই ইরানের পূর্ব দিকে 9 কোটি মানুষ স্বতন্ত্র ইসলামী ভূমি ও দেশ হিসেবে পাকিস্তান নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে নিজ সম্পৃক্ততার ঘোষণা দেয়।
যদিও যে সকল মুসলিম বিজেতার নাম এখানে এসেছে ,যেমন কাল্জ আরসালান ,নাসিরুদ্দীন সাবক্তাকীন ,সুলতান মাহমুদ গজনভী ও অন্যান্য সকলেই ইরানী তুর্কী বংশোদ্ভূত ছিলেন ,কিন্তু যেমনটি ডক্টর শাহিদী বলেছেন যে ,তাঁরা ছিলেন তৎকালীন ইরানের প্রতিনিধি ও এ ভূখণ্ডের শক্তির প্রতীক ও এতদঞ্চলের মুসলমানদের শাসক এবং তাদের পক্ষে ইসলামের নামে ইরানীরাই জিহাদ করত ;অন্যরা নয়।
জ্ঞান ও সংস্কৃতি
ইরানীদের ইসলামের পেছনে অবদানের ক্ষেত্র হিসেবে সবচেয়ে ব্যাপক ও উদ্দীপনার স্বাক্ষরসম্পন্ন ক্ষেত্রটি হলো জ্ঞান ও সংস্কৃতি।
সভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশ ,সামগ্রিকতা ও সর্বজনীনতা ,সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ,সামষ্টিক ও সুন্দর উদ্যোগসমূহের বিচিত্রতা প্রভৃতি দিকগুলো ইসলামী সভ্যতার তীব্র আকর্ষণীয় বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত।
জর্জি যাইদান বলেছেন ,
“
আরবগণ (মুসলমানগণ) এক শতাব্দীর কিছু বেশি সময়ের মধ্যে অন্য ভাষা হতে বিভিন্ন জ্ঞানের যে বিপুল সংখ্যক অনুবাদ করে রোমীয়গণ কয়েক শতাব্দীতেও তা পারেনি। হ্যাঁ ,মুসলমানগণ সভ্যতা সৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরূপ দ্রুতগতিতেই অগ্রসর হয়েছিল।”
মুসলমানগণ কোরআন ও সুন্নাতকে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানসমূহ ,যেমন কেরাআত ,তাফসীর ,কালামশাস্ত্র ,হাদীস ,ফিকাহ্ ,সারফ ,নাহু (ব্যাকরণশাস্ত্র) ,মায়ানী ,বাদীই ও বায়ান (বর্ণনাভঙ্গী ও অলংকারশাস্ত্র) ,সীরাতুন্নবী (নবীর জীবন ও ইতিহাস) প্রভৃতি নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। এ সকল বিষয়ে যদি কিছু অন্যদের হতে নিয়েও থাকে তা অনুল্লেখ্য। যে সকল জ্ঞান তৎকালীন অন্যান্য জাতির নিকট ছিল ও ভিন্ন জাতির প্রচেষ্টার ফল বলে বিবেচিত হতো ,যেমন অংকশাস্ত্র ,প্রকৃতিবিজ্ঞান ,জ্যোতির্বিজ্ঞান ,চিকিৎসাশাস্ত্র ,দর্শন ও অন্যান্য জ্ঞান তা আরবীতে ভাষান্তরিত ও অনূদিত হয়েছিল। জর্জি যাইদান বলেছেন ,
“
ইসলামী সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব হলো গ্রীক ,পারসিক ,ভারতীয় ও ব্যাবিলনীয় ভাষার গ্রন্থগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করে সেগুলোর পরিবর্ধন সাধনের মাধ্যমে পূর্ণতা দান।”
মুসলমানগণ বিভিন্ন ভাষায় বিদ্যমান দর্শন ,অংকশাস্ত্র ,জ্যামিতি ,জ্যোতির্বিজ্ঞান ,সাহিত্য ,চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহকে আরবীতে অনুবাদ করে। তৎকালীন প্রসিদ্ধ ভাষাসমূহ যথা গ্রীক ,ভারতীয় (হিন্দী) ,ফার্সী ভাষা হতে গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করা হয়। বলা যায় প্রতিটি জাতিরই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানগুলোকে তারা গ্রহণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ গ্রীকদের নিকট থেকে দর্শন ,চিকিৎসাশাস্ত্র ,জ্যামিতিবিজ্ঞান ,যুক্তিশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা ;ইরানীদের নিকট থেকে ইতিহাস ,সাহিত্য ,সংগীত ,উপদেশবাণী ও জ্যোতিষ্কবিদ্যা ;ভারতীয়দের নিকট থেকে ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা ,উদ্ভিদবিজ্ঞান ,তারকাবিজ্ঞান ,হিসাবশাস্ত্র ,গল্পকাহিনী রচনা ও সংগীত শিল্প। ব্যাবিলনীয় ও নাবতীদের নিকট থেকে কৃষিকাজ ,উদ্ভিদের পরিচর্যা ,জ্যোতির্বিদ্যা ,যাদু ও হিপনোটিসম ;মিসরীয়দের নিকট থেকে রসায়ন ও বিশ্লেষণবিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে আরবগণ (মুসলমানগণ) অ্যাসিরীয় ,ব্যাবিলনীয় ,মিশরীয় ,ইরানী ,ভারতীয় ও গ্রীক জ্ঞানসম্ভারকে (সাহিত্য ,স্থাপত্য ও অন্যান্য জ্ঞান) সমন্বিত করে ও উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতার জন্ম দেয়।
প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র
ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতি (সার্বিকভাবে ইসলামী সভ্যতা) ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে বিকাশ লাভ করে গৌরবময় স্থানে পৌঁছায়। যেমনভাবে সজীব প্রাণীসমূহ প্রথমদিকে এককোষী হিসেবে উৎপত্তি লাভ করে ও ধীরে ধীরে তার অভ্যন্তরীণ প্রাণসত্তা ও ক্ষমতার বিকাশের মাধ্যমে শাখা-প্রশাখা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয় ও সবশেষে পূর্ণাঙ্গ সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তেমনিভাবে ইসলামী সভ্যতাও বিকশিত হয়ে পূর্ণতায় পৌঁছায়।
মুসলমানদের জ্ঞান অন্বেষণের ধারা ও উদ্দীপনা একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে শুরু হয়। এখন আমরা দেখব কোন্ স্থানে এ আন্দোলনের ধারাটি শুরু হয় অর্থাৎ মুসলমানদের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্রটি কোথায় চালু হয় ?
মুসলমানদের জ্ঞানার্জন ও বিকাশের ধারা মদীনা হতে শুরু হয়েছিল। প্রথম যে গ্রন্থটি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও মুসলমানগণ তার অন্বেষায় আত্মনিয়োগ করে তা হলো কোরআন। কোরআনের পর তাদের অধ্যয়নের বিষয় ছিল হাদীসসমূহ। হেজাযের আরবরা প্রথমবারের ন্যায় শিক্ষক-ছাত্রের মুখস্থকরণ ,সংকলন প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। মুসলমানগণ আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ কোরআনের আয়াতসমূহ মুখস্থ করত। যে সকল আয়াত তারা সরাসরি রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে না শুনত তা রাসূলের নির্দেশে কোরআন সংকলনের দায়িত্বপ্রাপ্তদের
নিকট থেকে শুনত ও মুখস্থ করত। তদুপরি তারা রাসূলের পুনঃপুন নির্দেশের কারণে তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীসমূহকে পরস্পরের নিকট থেকে শ্রবণ করে মুখস্থ করত অথবা লিখে রাখত।
মদীনার মসজিদে নিয়মিত শিক্ষার আসর বসত এবং সেখানে বিভিন্ন শিক্ষণীয় ইসলামী বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা হতো। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন দু’
দল লোক ভিন্ন দু’
ধরনের কর্মে মশগুল রয়েছে। একদল ইবাদাত ও যিকর-আযকারে মশগুল অপর দল জ্ঞানের আলোচনায়। রাসূল দু’
দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন ,
كلاهما على خير و لكن بالتّعليم أُرسلت
“
দু’
দলই কল্যাণময় কর্মে লিপ্ত রয়েছে ,তবে আমি শিক্ষাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।”
অতঃপর রাসূল জ্ঞানের আলোচনায় লিপ্তদের সঙ্গে গিয়ে বসলেন।
মদীনার পর ইরাক জ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সর্বপ্রথম ইরাকের বসরা ও কুফা এই দু’
শহর জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। পরে বাগদাদ শহর নির্মিত হলে তা জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এখান হতেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে খোরাসান ,রেই ,বুখারা ,সামারকান্দ (বর্তমানের উজবেকিস্তানের দু’
শহর) ,মিশর ,সিরিয়া ,আন্দালুস ও অন্যান্য স্থান জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়। জর্জি যাইদান মুসলিম শাসকদের উদ্যোগকে এ বিষয়ে সবচেয়ে কার্যকর প্রভাবশীল বলে মনে করেন। তিনি বলেন ,
“
ইসলামী ব্যক্তিত্বসমূহ ও উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিবর্গের জ্ঞানের অনুরাগ ও জ্ঞান চর্চার মনোবৃত্তির ফলে ইসলামী দেশসমূহে গ্রন্থ ও গ্রন্থ রচয়িতার পরিমাণ প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে ও গবেষণার পরিধির উত্তরোত্তর বিস্তৃতি ঘটে। সম্রাট ,উজীর ,প্রাদেশিক শাসনকর্তা ,ধনী ,দরিদ্র ,আরব ,ইরানী ,রোমীয় ,ভারতীয় ,তুর্কী ,মিশরীয় ,ইহুদী ,খ্রিষ্টান ,দাইলামী ,সুরিয়ানী সকলেই ইসলামী ভূখণ্ডের সকল স্থানে যথা সিরিয়া ,মিশর ,ইরাক ,ইরান ,খোরাসান ,উজবেকিস্তান ,সিন্ধু ,আফ্রিকা ,স্পেন প্রভৃতিতে দিবা-রাত্র গ্রন্থ রচনা ও সংকলনে মনোনিবেশ করলেন। অর্থাৎ যেখানেই ইসলামী শাসন ছিল সেখানেই জ্ঞানের দ্রুত বিস্তার ঘটতে লাগল। এ সকল মূল্যবান রচনাসমগ্র ও সংকলনে পূর্ববর্তী যুগসমূহের সকল গবেষণার সারসংক্ষেপ সংকলিত হয়েছিল। ফলে প্রকৃতিবিজ্ঞান ,ঐশী জ্ঞান ,ইতিহাস ,অংকশাস্ত্র ,সাহিত্য ,দর্শন ,প্রজ্ঞা প্রভৃতি বিষয় এ গ্রন্থসমূহে সমন্বিতভাবে বিদ্যমান ছিল। মুসলিম মনীষীদের গবেষণার ফল হিসেবে উপরোক্ত জ্ঞানসমূহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত হয়।’
যখন অন্য ভাষার জ্ঞানসমূহ আরবীতে অনূদিত হওয়া শুরু হয় তখন খ্রিষ্টান মনীষীরা বিশেষত সিরীয় খ্রিষ্টানরা এ বিষয়ে অন্যদের হতে অগ্রগামী ছিলেন। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মুসলমানগণ সে স্থান অধিকার করে।
জর্জি যাইদান বলেন ,
“
আব্বাসীয় খলীফাগণ জ্ঞান ও সাহিত্যের বীজ বাগদাদের মাটিতে রোপন করেন এবং এর ফল পর্যায়ক্রমে খোরাসান ,রেই ,আজারবাইজান ,উজবেকিস্তান ,মিশর ,সিরিয়া ,আফ্রিকা ,স্পেন প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদে খেলাফত ও ইসলামী ভূখণ্ডের সম্পদের কেন্দ্র হিসেবে পূর্বের ন্যায় মনীষীদের সম্মিলন কেন্দ্ররূপে এরপরও বিদ্যমান থাকে। আব্বাসীয় খলীফাদের সেবায় নিয়োজিত খ্রিষ্টান চিকিৎসকগণই প্রথমদিকে চিকিৎসা ও অনুবাদের কাজ করতেন। পরবর্তীতে বাগদাদ হতে কিছু মুসলিম পণ্ডিত এ কর্মে নিয়োজিত হন। কিন্তু সার্বিকভাবে বাগদাদের প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চ পর্যায়ের মনীষীদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান ছিলেন যাঁরা খলীফাদের দরবারে কর্মের জন্য ইরাক ও অন্যান্য স্থান হতে নিয়োগ পেয়েছিলেন। মুসলিম মনীষীদের অধিকাংশই বাগদাদের বাইরে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বিশেষত যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় তখন ঐ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের শাসকগণ খলীফাদের অনুসরণে জ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া শুরু করেন ও তাঁদের অধীন বিভিন্ন অঞ্চল ,যেমন কায়রো ,গাজনীন ,দামেস্ক ,নিশাবুর ,ইসতাখর ও অন্যান্য স্থান হতে পণ্ডিত ও গবেষকদের আহ্বান জানান। ফলে রেই হতে জাকারিয়া রাযী ;তুর্কিস্তানের
বোখারা হতে ইবনে সিনা ;সিন্ধের বিরুন হতে আল বিরুনী ,উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইবনে জালিল ,দার্শনিক ইবনে বাজা ,চিকিৎসক ইবনে জাহরা ,দার্শনিক ইবনে রুশদ ;স্পেন হতে উদ্ভিদবিদ ইবনে রুমীয়া ও অন্যান্যদের সৃষ্টি হয়।’
সুতরাং প্রথম জ্ঞান ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল মদীনা এবং সেখানেই জ্ঞানের প্রথম বীজ রোপিত হয়।
জ্ঞানের প্রথম বিষয়বস্তু
প্রথম কোন্ বিষয়টি মুসলমানদের আকর্ষণ করে ও তাদের মধ্যে জ্ঞানের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে ? মুসলমানদের জ্ঞানের শুরু কোরআন দিয়ে। তারা প্রথম কোরআনের আয়াতের অর্থ ও বিষয়বস্তু অনুধাবন ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে। অতঃপর হাদীস গবেষণা শুরু করে। তাই যে শহরটিতে সর্বপ্রথম জ্ঞানের জাগরণ শুরু হয় তা হলো মদীনা। মুসলমানদের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল মসজিদ। তাদের শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল কোরআন ও সুন্নাহ্ এবং তাদের প্রথম শিক্ষক ছিলেন রাসূল (সা.)। ইসলামের প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় ছিল পঠন ,তাফসীর ,কালামশাস্ত্র ,হাদীস ,রিজালশাস্ত্র ,ভাষাজ্ঞান ,অভিধান ,সারফ ও নাহু (ব্যাকরণশাস্ত্র) ,বাচনভঙ্গী ও অলংকারশাস্ত্র ,ইতিহাস ইত্যাদি। এ সকল জ্ঞান কোরআন ও সুন্নাতের স্বার্থে সৃষ্টি হয়েছিল। এডওয়ার্ড ব্রাউন বলেছেন ,
“
বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদ প্রফেসর দাখভিয়া এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকার বাইশতম খণ্ডে তাবারী ও অন্যান্য আরব ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে প্রশংসনীয়ভাবে ইসলামী সমাজে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশকে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত কোরআনের আলোকে ইতিহাসের জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশের বিষয়টি সেখানে আলোচিত হয়েছে। তিনি এ জ্ঞানসমূহ কিরূপে ঐশী প্রজ্ঞার ভিত্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রথমত শব্দ ও ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়। যখন অন্যান্য ভাষাভাষীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ শুরু করে তখন আরবী শব্দ ও বাক্যগঠন এবং ব্যাকরণশাস্ত্রের আশু প্রয়োজন অনুভূত হলো। কারণ পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। কোরআনে বর্ণিত অপ্রচলিত শব্দসমূহের অর্থ বিশ্লেষণের জন্য আরবী প্রাচীন কবিতাসমূহ যথাসম্ভব সংকলনের প্রয়োজন পড়ল... এই কবিতাসমূহের অর্থ অনুধাবনের জন্য আরবদের বংশ পরিচিতিবিদ্যা ও তৎকালীন আরবদের ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা অপরিহার্য হিসেবে দেখা দিল। কোরআনে অবতীর্ণ বিধিবিধানের পূর্ণতার জন্য জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবী ও তাবেয়ীদের নিকট হতে নবীর বাণী ও কর্ম সম্পর্কিত প্রশ্নের ফলশ্রুতিতে হাদীসশাস্ত্রের জন্ম হলো। হাদীসসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের জন্য হাদীসের সনদ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি অপরিহার্য বিষয় বলে পরিগণিত হলো।... গবেষণার স্বার্থে সনদের বাস্তবতা ,ইতিহাসের জ্ঞান ,বর্ণনাকারীদের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক অবস্থা সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো। এর ফলে হাদীসশাস্ত্রবিদগণের জীবনী ,বিভিন্ন সময়ের জ্ঞান ,প্রশিক্ষণ ও ঘটনাসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান উদ্ভূত হলো। এ ক্ষেত্রে আরবের ইতিহাস যথেষ্ট ছিল না। তাই প্রতিবেশী দেশসমূহ বিশেষত ইরানী ,গ্রীক ,হামিরী ,হাবাশী ও অন্যান্য দেশের ইতিহাস জানাও কোরআনে সন্নিবেশিত জ্ঞান ও প্রাচীন কবিতা বোঝার জন্য অপরিহার্য হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ভূগোলবিদ্যাও এ উদ্দেশ্যে উদ্ভূত হয়েছিল। এরূপ অন্যান্য বিদ্যাও ইসলামী সাম্রাজ্যে দ্রুত বিস্তারের সাথে সাথে অপরিহার্য হিসেবে উদ্ভূত হয়।”
জর্জি যাইদানের মত এটিই যে ,অন্যান্য জ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ কোরআনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। মুসলমানগণ কোরআনের প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং এর সঠিক তেলাওয়াত ও উচ্চারণের বিষয়ে গুরুত্ব দিত। কোরআন তাদের দীন ও দুনিয়ার সমস্যার সমাধান দিত এবং তারা কোরআনের বিধান বোঝার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাত। কোরআনের শব্দ ও অর্থ অনুধাবনের প্রচেষ্টা বিভিন্ন জ্ঞানের উদ্ভব ঘটায়। ইসলামী সমাজে যে সজীব কোষটি জন্মের পর বিকাশ ও পূর্ণতার মাধ্যমে বৃহৎ ইসলামী সভ্যতার জন্ম দেয় সে কোষটি হলো কোরআনের প্রতি মুসলমানদের সীমাহীন ভালবাসা ও প্রেম। কোরআনের প্রতি মুসলমানদের অকুণ্ঠ ভালবাসাই যে জ্ঞানের সকল দ্বার উন্মোচনে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই বলে জর্জি যাইদান মনে করেন। তিনি বলেন ,
“
মুসলমানগণ কোরআন লিখন ও সংরক্ষণে যথার্থ দৃষ্টি রাখত ও এ বিষয়কে এতটা গুরুত্ব দিত যে ,ইতোপূর্বে অন্য কারো ক্ষেত্রে তা লক্ষ্য করা যায়নি। তারা এমনকি স্বর্ণ ,রৌপ্য ও হাতির দাঁতের পত্রের ওপরও কোরআন লিখত। কখনও রেশমী কাপড় বা দামী কোন কাপড়ের ওপর স্বর্ণ ও রৌপ্যের কালি দ্বারা কোরআনের আয়াত লিখা হতো। গৃহ ,মসজিদ ,গ্রন্থাগার ,সভাকক্ষের দেয়াল ও দরবারসমূহ এরূপ কাপড় ও কোরআনের আয়াতের দ্বারা অলংকৃত করত। লেখার জন্য সুন্দর হাতের লেখা ব্যবহার করত। বিভিন্ন ধরনের চামড়া ও কাগজ কোরআন লিখনে ব্যবহৃত হতো এবং বিভিন্ন রংয়ের কালির মাধ্যমে লিখে তার চারিপাশের রেখাগুলো স্বর্ণ দিয়ে অলংকৃত করা হতো।... মুসলমানগণ কোরআনের শব্দ ও আয়াত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করত ,এমনকি কোরআনের বর্ণসংখ্যা স্বতন্ত্রভাবে তারা গণনা করেছিল।”
তিনি বলেছেন ,
“
...তাদের সকল বক্তব্য ও লেখনীতে কোরআনের পথকে তাদের কর্মপদ্ধতির আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা তাদের লেখনীতে কোরআনের আয়াতসমূহ হতে উদাহরণ নিয়ে আসত। কোরআনের শিক্ষা ও আদব তাদের দৈনন্দিন জীবনের চরিত্রে ও আচরণে ব্যাপক প্রভাব রাখত। অথচ অধিকাংশ মুসলিম জাতির ভাষা কোরআনের ভাষা ছিল না এবং তারা এমন দেশে বাস করত যেখান হতে কোরআন অনেক দূরে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী মুসলমানগণ শরীয়তের জ্ঞান ছাড়াও আরবী ব্যাকরণের বিষয়েও কোরআনের আয়াত ও অর্থ হতে উদাহরণ উপস্থাপন করত ,যেমন আরবী ভাষা ও ব্যাকরণবিদ সিবাভেই তাঁর গ্রন্থে কোরআন হতে তিনশ’
আয়াত উদাহরণ হিসেবে এনেছেন। যে সকল সাহিত্যিক ও লেখক তাঁদের বক্তব্য ও লেখনীকে সুন্দর ও অলংকৃত করতে চাইতেন অবশ্যই কোরআনের আয়াতের সহযোগিতা নিতেন।”
জর্জি যাইদান আরো উল্লেখ করেছেন ,
‘
সালাউদ্দীন আইউবী মিশর অধিকারের পর দ্বিতীয় ফাতেমী খলীফা আল আযিয বিল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে স্বর্ণ দ্বারা লিখিত ও অলংকৃত তিন হাজার চারশ’
কোরআন পান। আল আযিয বিল্লার মন্ত্রী ইয়াকুব ইবনে কালাস তাঁকে এরূপ কোরআন লিপিবদ্ধ করার কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।”
ইরানের মাশহাদে ইমাম রেযা (আ.)-এর যাদুঘরে যে প্রাচীন কোরআন সংরক্ষিত আছে সেগুলোর আকর্ষণীয় ও আশ্চর্যজনক সুন্দর লিখনপদ্ধতি ও অলংকৃত পৃষ্ঠাসমূহ এ দেশের মানুষের কোরআনের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসার প্রমাণ।
ইসলামের জ্ঞানগত ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বর্ণিত পর্যায়ক্রমিক ধারাতেই বিকশিত হয়েছিল। এখন আমরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আলোচনা করব।
যদিও ইসলামী বিশ্বের বাইরে হতে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বলিত যে সকল গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল তা ইরানী ছিল না ,কিন্তু ইসলামী বিশ্বের ধর্মীয় ও অন্যান্য জ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থ ইরানী মুসলিম মনীষীদের মাধ্যমেই রচিত ও সংকলিত হয়েছিল। এটিই ইসলামী শাসনামলে ইরানীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এডওয়ার্ড ব্রাউন বলেছেন ,
“
তাফসীর ,হাদীস ,কালামশাস্ত্র ,দর্শন ,চিকিৎসাশাস্ত্র ,অভিধান ,জীবনী ,ইতিহাস ,এমনকি আরবী ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রের বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ আরবদের নামে প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভ করেছে তার অধিকাংশই ইরানীদের রচনা এবং ইরানীদের অংশ বাদ দিলে এ সকল জ্ঞানের উল্লেখযোগ্য ও উত্তম অংশ আর অবশিষ্ট থাকবে না।”
আমরা এ বিষয়ে অতিরঞ্জিত মন্তব্য করে অ-ইরানী মুসলমানদের অবদানকে অস্বীকার করতে চাই না। কারণ ইসলামী সভ্যতা বিশেষ কোন জাতির নয় ;বরং সকল মুসলমানের। তাই আরব ,ইরানী বা অন্য কোন জাতি তাঁকে নিজস্ব বলে দাবি করতে পারে না। তবে প্রতি জাতিই তার অবদানের অংশটুকু বর্ণনা ও নির্দিষ্ট করার অধিকার রাখে।
রচনা ও সংকলনের প্রারম্ভ
সাধারণত প্রাচ্যবিদগণ ও তাঁদের অনুসারীরা দাবি করে থাকেন ,ইসলামের প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ রাসূল (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের প্রচলন ছিল না ;বরং তা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁরা এ ক্ষেত্রে রচনা ও সংকলনের বিষয়ে রাসূলের নিষেধাজ্ঞার একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। তাঁদের মতে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ইসলামের প্রসার ঘটলে রচনা ও সংকলন শুরু হয় এবং তখনই মুসলমানগণ রচনা ও সংকলনের সুফল বর্ণনা করে রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীস উপস্থাপন শুরু করে ।
জর্জি যাইদান বলেছেন ,
“
খোলাফায়ে রাশেদীন আরবদের বেদুইন অবস্থা হতে শহুরে জীবনে প্রবেশের বিষয়টিকে ভয় পেতেন। তাঁরা মনে করতেন শহুরে জীবন লাভ করলে তারা সরল সাধারণ জীবন ও উদ্দীপনাপূর্ণ জীবন হতে দূরে সরে যাবে। এ কারণেই আরবদেরকে গ্রন্থ রচনা ও সংকলন হতে তাঁরা বিরত রাখতেন।... কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলামের প্রসার ঘটলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত হয়। ফলে সাহাবীরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং চিন্তা-বিশ্বাসের মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত ও সে সবের উত্তর আহ্বান করা হলো। মুসলমানগণ বাধ্য হয়ে হাদীস ,ফিকাহ্ ও কোরআন সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও সংকলন শুরু করল। তারা দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন ও ইজতিহাদ শুরু করল।... ফলে তখন থেকে রচনা ও সংকলনকে মাকরুহ বা অপছন্দনীয় কর্ম মনে না করে মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় কর্ম বলা শুরু করল এবং এ বিষয়ে নবী (সা.)-এর নিকট হতে আনাস ইবনে মালেক বর্ণিত হাদীসটি উপস্থাপন করল।”
জর্জি যাইদান খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি যে বিষয়টি আরোপ করেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। জর্জি যাইদান শহুরে জীবনের প্রতি অনীহা এবং রচনা ও সংকলন নিষিদ্ধ থাকার বিষয়টি নিয়ে যা বলেছেন তার কোনটিই ঠিক নয়। নবী (সা.)-এর সাহাবীদের মদীনা হতে বহির্গত হওয়া ও অন্য স্থানে বসতি স্থাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধকরণে নিষেধ ও বাধা প্রদানের বিষয়টি খোলাফায়ে রাশেদীনের সকল খলীফার প্রতি আরোপ করা কখনই সঠিক নয়। কারণ এ বিষয়টি শুধু দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পূর্বে আমরা হাদীস সংকলনের বিষয়ে একদিকে হযরত আলী ও একদল সাহাবীর অবস্থান গ্রহণ ও অন্যদিকে হযরত উমর ও আরেকদল সাহাবীর তার বিপরীতে অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছি। আমরা পরে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। মদীনা হতে অন্যত্র হিজরত ও বসতি স্থাপনের বিষয়েও হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। এ কারণেই রাজধানী কুফায় স্থানান্তরের পর হযরত আলী তাঁর বিপরীত নির্দেশ দেন। তাই জর্জি যাইদানের বক্তব্য ভিত্তিহীন।
এডওয়ার্ড ব্রাউনের মতেও প্রথম হিজরী শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা থাকলেও কোন গ্রন্থ সংকলিত হয়নি। তাই জ্ঞান ও তথ্যসমূহ মুখস্থের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং বলতে গেলে একমাত্র কোরআনই লিখিতরূপে গ্রন্থ হিসেবে বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেছেন ,
“
প্রথম হিজরী শতাব্দীতে জ্ঞান অর্জন একমাত্র ভ্রমণ ও হিজরতের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল। তারা জ্ঞানান্বেষণে দীর্ঘ সফর করত। প্রথমদিকে পরিস্থিতির কারণেই সফরের বিষয়টি অপরিহার্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সফর নিয়মে পরিণত হয় ও এক রকম উন্মাদনা সৃষ্টি করে। নিম্নোক্ত হাদীসের ন্যায় জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে সফরের মর্যাদা ও গুরুত্ব বর্ণনাকারী হাদীসসমূহ এর সমর্থনে উপস্থাপিত হলো। যেমন নবী (সা.) বলেছেন:“
যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করে আল্লাহ্ তাকে বেহেশতের পথে পরিচালিত করেন।”
মিশরের অধিবাসী মাকহুল নামের একজন দাস তার মনিব কর্তৃক মুক্ত ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ততক্ষণ মিশর ত্যাগ করেনি যতক্ষণ মিশরের প্রচলিত জ্ঞানসমূহ অর্জন সমাপ্ত হয়নি। অতঃপর যখন তার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল তখন সে হেজায ,সিরিয়া ও ইরাকে যায় ও গনীমতের মাল বণ্টন সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ সংকলন করে।”
কিন্তু এ মতটি ভিত্তিহীন। ইসলামের প্রাথমিক যুগের নিদর্শনসমূহ হতে বোঝা যায় নবী (সা.)-এর সময় হতেই লিখন ও সংকলন শুরু হয় ও অব্যাহত থাকে। এর সপক্ষে অনেক প্রমাণ উপস্থিত। ব্রাউনের‘
হিস্ট্রি অব লিটারেচার’
গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদের প্রথম খণ্ডের টীকা অংশে ব্রাউনের মতো ব্যক্তিদের মতকে খণ্ডন করে আল্লামা শাইখুল ইসলাম যানজানীর‘
মুসন্নাফাতুশ শিয়াতিল ইমামিয়া ফিল উলুমিল ইসলামিয়া’
গ্রন্থ হতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি এর বিপরীত মতকেই প্রমাণ করেছেন।
মরহুম আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ হাসান সাদর (আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করুন) তাঁর‘
তাসিসুশ শিয়া লি উলুমিল ইসলাম’
নামক মূল্যবান গ্রন্থেও এ মতটির ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেছেন। আমরা পরবর্তী আলোচনায় সেখান হতে কিছু অংশ উপস্থাপন করব। আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে এখানে তা উল্লেখ হতে বিরত থাকছি।
দ্রুততার ভিত্তি ও কারণ
জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের দ্রুত উন্নয়নের অন্যতম কারণ হলো তারা জ্ঞান ,শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন গোঁড়ামি পোষণ করত না। তারা যেখানেই বা যার কাছেই জ্ঞানের সন্ধান পেত তা আহরণ করত। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তারা উদার মনোভাব পোষণ করত।
আমরা জানি যে ,নবী (সা.)-এর হাদীসেও জ্ঞান যেখানেই ও যার কাছেই পাওয়া যাক না কেন তা লাভ করতে বলা হয়েছে। যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন ,
كلمة الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو أحقّ بها
“
সঠিক প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ। তাই যেখানেই তা পায় তা অর্জনে তার অধিকার সর্বাধিক।”
নাহজুল বালাগায় এসেছে :
الحكمة ضالّة المؤمن فخذ الحكمة و لو من أهل النّفاق
“
সঠিক জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ। তাই তা গ্রহণ কর যদিও মুনাফিকের নিকট হতে হয়।”
হযরত আলী (আ.) অন্যত্র বলেছেন ,
خذوا الحكمة و لو من المشركين
“
জ্ঞান শিক্ষা কর যদিও মুশরিকদের নিকট হতে হয়।”
পবিত্র ইমামগণের নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে ,হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন ,
خذوا الحقّ من أهل الباطل و لا تأخذوا الباطل من أهل الحقّ و كونوا نقّاد الكلام
“
সত্য জ্ঞানকে ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের নিকট হতে হলেও গ্রহণ কর ,কিন্তু ভ্রান্ত ধারণাকে সত্যপন্থীর নিকট হতে হলেও গ্রহণ কর না এবং যে কোন কথা পর্যালোচনা কর।”
সমুন্নত চিন্তা ,গোঁড়ামিমুক্ত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির এ সকল হাদীস অমুসলমানদের হতেও জ্ঞান অর্জনে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেছে। এ হাদীসসমূহ জ্ঞানার্জনে মুসলমানদের মধ্যে সংস্কারহীন ও মুক্ত মনের সৃষ্টি করেছে।
এ কারণেই মুসলমানরা এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিত না যে ,কার নিকট হতে জ্ঞান লাভ করছে বা কার মাধ্যমে গ্রন্থসমূহ অনূদিত হয়ে তাদের নিকট পৌঁছেছে ;বরং তাদের ইমামদের শিক্ষানুযায়ী মুমিন ও জ্ঞানের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেদের মনে করত এবং অন্যদের নিকট তা গচ্ছিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করত। মাওলানা রুমীর ভাষায় :
“
জ্ঞান অন্যের নিকট তোমার ঋণ যেন
দাস বিক্রেতার নিকট ক্রীতদাসী সম।”
মুসলমানরা বিশ্বাস করত ইলম ও ঈমান পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে না এবং ঈমানহীন পরিবেশে জ্ঞান অপরিচিত হিসেবে মূল্যহীন হয়ে রয়েছে। তাই তার প্রকৃত ও পরিচিত ভূমি মুমিনের অন্তরে ফিরে আসা প্রয়োজন।
তাই রাসূলেরكلمة الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو أحقّ بها
এ কথা উপরোক্ত সকল কিছুকেই ধারণ করে। আর এজন্যই মুসলমানদের সকল প্রচেষ্টা এ চিন্তাকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো যে ,কিরূপে বিশ্বের সকল জ্ঞানভাণ্ডার হস্তগত করা যায়।
জর্জি যাইদান ইসলামী সভ্যতার দ্রুত প্রসার ও বিস্তারের কারণ সম্পর্কে বলেন ,
“
ইসলামী সভ্যতার দ্রুত প্রসার এবং জ্ঞান ও সাহিত্যের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কারণ আব্বাসীয় খলীফাগণ অন্য ভাষার জ্ঞান অনুবাদের বিষয়ে ব্যয় করতে কোন দ্বিধা করতেন না এবং জাতি ,ধর্ম ও বংশের বিষয়টি লক্ষ্য করা ব্যতীতই সকল অনুবাদক ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি অভূতপূর্ব সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাঁদের সকল ধরনের সহযোগিতা দিতেন। এ কারণেই ইহুদী ,খ্রিষ্টান ,যারথুষ্ট্র ,সাবেয়ী ও সামেরী সকল ধর্মের পণ্ডিত ব্যক্তিই খলীফাদের নিকট আসত। এ ক্ষেত্রে আব্বাসীয় খলীফাদের আচরণ সকল জাতি ও ধর্মের সেই সকল নেতা যাঁরা স্বাধীন ও ন্যায়পরায়ণ চিন্তা করেন তাঁদের আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত।”
জর্জি যাইদান সাইয়্যেদ শরীফ রাযী কর্তৃক সাবেয়ী ধর্মানুসারী আবু ইসহাক নামের এক ব্যক্তির প্রতি মর্সিয়া পাঠের প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন ,চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও মনীষীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি এতটা প্রচলিত যে ,একজন আলেম সম্পূর্ণ মুক্ত মনে একজন সাবেয়ী মনীষীর প্রশংসায় মর্সিয়া পাঠ করেছেন ।
জর্জি যাইদানের মতে খলীফা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের উদারতা ও তাঁদের সংস্কারমুক্ত হওয়ার কারণেই সাধারণ মানুষও তাঁদের অনুসরণে এরূপ করত। যদি নির্দেশদাতা ও সম্ভ্রান্তগণ স্বাধীন নীতি গ্রহণ করেন তাহলে অন্যরাও তাঁদের অনুসরণে তা-ই করে। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। কারণ সাইয়্যেদ শরীফ রাযীর ন্যায় ব্যক্তিবর্গ খলীফাদের অনুসরণ করতেন না এবং এ উদারতা ও সমুন্নত চিন্তা তাঁরা খলীফাদের নিকট হতে শিক্ষাগ্রহণ করেননি। তাঁরা এটি পবিত্র ইসলাম ধর্মের নীতি হতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন যা মনে করে যে ,জ্ঞান সকল অবস্থায়ই সম্মানিত। তাই যখন মর্সিয়া পাঠের কারণে সাইয়্যেদের সমালোচনা করা হয় তখন তিনি উত্তরে বলেন ,“
আমি জ্ঞানের প্রশংসায় মর্সিয়া পাঠ করেছি ;ব্যক্তির প্রশংসায় নয়।”
ডক্টর যেররিন কুবও তাঁর‘
করনামেহ ইসলাম’
গ্রন্থে মুসলমানদের দ্রুত অগ্রগতির পেছনে গোঁড়ামিমুক্ত উদার নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলে উল্লেখ করেছেন।
মুসলমানদের জ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়ার অন্যতম কারণ হলো জ্ঞানার্জনের জন্য ইসলামের পুনঃপুন অনুপ্রেরণা দান ও তাকিদ। জর্জি যাইদান খ্রিষ্টধর্মের প্রতি গোঁড়ামি পোষণ সত্ত্বেও (যা তাঁর কোন কোন লেখায় স্পষ্ট ,যেমন তিনি বলেছেন ,‘
প্রথম যুগের মুসলমানগণ কোরআন ব্যতীত অন্য সকল গ্রন্থের বিরোধী ছিল’
) এটি স্বীকার করেছেন ,জ্ঞানের প্রতি ইসলামের অনুপ্রেরণা দানের বিষয়টি মুসলমানদের অগ্রগতিতে বিশেষ প্রভাব রেখেছিল। তিনি বলেন ,
“
যখন ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটল এবং মুসলমানগণ ইসলামী শিক্ষার প্রসার সম্পন্ন করল তখন ধীরে ধীরে শিল্প ও অন্যান্য জ্ঞান অন্বেষণে লিপ্ত হলো। তারা নিজ সভ্যতার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ শুরু করল। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই শিল্প ও অন্যান্য জ্ঞান অর্জনের পথে পা বাড়াল। যেহেতু তারা খ্রিষ্টান পাদ্রীদের হতে দর্শন সম্পর্কে শুনেছিল সেহেতু অন্যান্য জ্ঞান অপেক্ষা দর্শনের প্রতি অধিকতর ঝুঁকে পড়ল। বিশেষত রাসূলের নিকট হতে জ্ঞান অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছিল ,যেমন‘
জ্ঞান অর্জন কর যদিও তা চীনে গিয়ে অর্জন করতে হয়’
,‘
প্রজ্ঞা মুমিনের হারান সম্পদ ,যার কাছেই পাও তা গ্রহণ কর যদিও সে ব্যক্তি মুশরিকও হয়’
,‘
প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর ওপর জ্ঞান অর্জন ফরয’
এবং‘
দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর’
তা তাদের এ পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।”
ডক্টর যেররিন কুব বলেছেন ,
“
ইসলাম ইলম (জ্ঞান) ও আলেমের (জ্ঞানীর) প্রতি গুরুত্ব ও মনোযোগ দানের বিষয়ে এতটা উদ্বুদ্ধ করেছিল যে ,তা মানবিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি শিক্ষায় মুসলমানদের অগ্রগতির কারণ হয়েছিল। কোরআন মানব জাতিকে পুনঃপুন বিশ্বজগৎ ও কোরআনের আয়াতের রহস্য অনুসন্ধানে চিন্তা করতে বলেছে ,অনেক স্থানেই অন্যান্যদের ওপর জ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেছে ,একস্থানে আল্লাহ্ ও ফেরেশতামণ্ডলীর সাক্ষ্যের সমপর্যায়ে জ্ঞানীর সাক্ষ্যের মূল্য দিয়েছে ,এ বিষয়গুলো জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে যথেষ্ট বলে ইমাম গাজ্জালী মনে করেন। তদুপরি বিভিন্ন সূত্রে রাসূল (সা.)-এর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসসমূহও ইলম ও আলেমের মর্যাদার সাক্ষ্য। হাদীসসমূহ ও তাতে নির্দেশিত জ্ঞানের বিষয়ে মতানৈক্যও জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি মুসলমানদের আসক্তির কারণ হয়েছিল। এ বিষয়টি বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনে ও এ সম্পর্কে চিন্তা ও পর্যালোচনায় তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। রাসূল স্বয়ং জ্ঞানার্জনে অনুপ্রেরণা দিতেন। বদরের যুদ্ধে যে সকল বন্দী মুক্তিপণ হিসেবে অর্থ প্রদানে সক্ষম ছিল না তারা যদি মদীনার দশটি শিশুকে অক্ষরজ্ঞান দান করত তবে মুক্তি পেত। রাসূলের অনুপ্রেরণাতেই যাইদ ইবনে সাবেত সুরিয়ানী ও হিব্র“
ভাষা শিক্ষা লাভ করেন এবং অন্য সাহাবীরাও জ্ঞানের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। যেমন প্রসিদ্ধ সূত্রমতে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) তাওরাত ও ইঞ্জিলে পণ্ডিত ছিলেন ,আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আসও তাওরাতের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি সুরিয়ানী ভাষা জানতেন বলেও কথিত আছে। নবীর তাকিদ ও অনুপ্রেরণা যেমন মুসলমানদের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিল তেমনি জ্ঞানী ও আলেমের সম্মানকে বর্ধিত করেছিল।”
এখন আমরা ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতিতে ইরানীদের প্রভাব ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্যও এটিই ,ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইরানীদের কার্যকর ভূমিকাসমূহ নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ। ইতোপূর্বে যা বলেছি তা এ আলোচনারই ভূমিকাস্বরূপ এনেছি।
ইতোপূর্বে কয়েকবার বলেছি এবং এখানেও বলছি ইসলামী সভ্যতা বিশেষ কোন জাতির নয় ;বরং ইসলাম ও সকল মুসলমানের। তাই কোন জাতিরই অধিকার নেই তা নিজস্ব বলে দাবি করার। হোক সে আরব বা ইরানী অথবা অন্য কোন জাতির। তবে প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব অবদান নিয়ে কথা বলার অধিকার রয়েছে।
 0%
0%
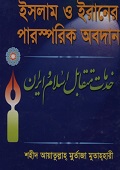 লেখক: শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী
লেখক: শহীদ অধ্যাপক মুর্তাজা মুতাহ্হারী