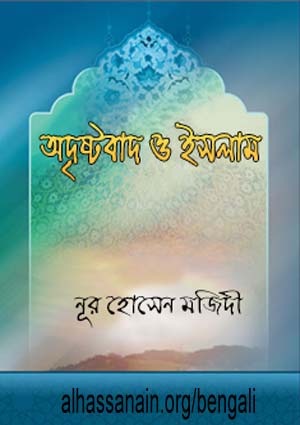আল্লাহ্ ও মানুষের কাজের মধ্যে মিল-অমিল
জাবর্ ও নিরঙ্কুশ এখতিয়ারের পরস্পর বিরোধী ধারণা থেকে সৃষ্ট জটিলতার সমাধানের জন্য আল্লাহ্ তা‘
আলা ও মানুষের কাজের মধ্যে মিল ও অমিলের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। কারণ , আল্লাহ্ তা‘
আলা মানুষকে স্বীয় গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা‘
আলা এরশাদ করেন:
(
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ)
“
(এ হলো) আল্লাহর প্রকৃতি ; আল্লাহ্ এর ওপরেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ; আল্লাহর সৃষ্টিতে (সৃষ্টির মূল পরিকল্পনা ও কাঠামোতে) কোনোরূপ পরিবর্তনের স্থান নেই।”
(সূরাহ্ আর্-রূম্: ৩০)
এ থেকে সুস্পষ্ট যে , আল্লাহ্ তা‘
আলার মধ্যে যে সব গুণ রয়েছে মানুষের মধ্যে তার সবই রয়েছে। জীবন , ইচ্ছাশক্তি , জ্ঞান , প্রকাশ ক্ষমতা , সৃজনশীলতা , দয়া , ভালোবাসা ইত্যাদি আল্লাহ্ তা‘
আলার সব গুণই মানুষকে দেয়া হয়েছে। মানুষকে আল্লাহ্ তা‘
আলার কোনো গুণ না দেয়া হলে তিনি এ কথা বলতেন না যে , তিনি মানুষকে তাঁর প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ মানুষ আল্লাহ্ তা‘
আলার খলীফাহ্ , আর খলীফাহ্ বা প্রতিনিধি হওয়ার দাবী হচ্ছে এই যে , আল্লাহ্ তা‘
আলা সমগ্র সৃষ্টিলোকের ক্ষেত্রে যত কাজ সম্পাদন করেন মানুষও ধরণীর বুকে তা সম্পাদন করবে। এজন্য তাকে অবশ্যই ঐসব কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর ও তা কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় এখতিয়ারের অধিকারী থাকতে হবে। অন্যথায় তাকে আল্লাহ্ তা‘
আলার খলীফাহ্ নামে অভিহিত করা সঙ্গত হতো না।
অবশ্য জন্মের সময় মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তা‘
আলার গুণাবলী সুপ্ত সম্ভাবনা আকারে বিদ্যমান থাকে , তাই তা কাজে লাগানোর জন্য প্রথমে তার যথাযথ বিকাশের প্রয়োজন। এই বিকাশ যতটা না মানুষের পারিপার্শ্বিকতার ওপরে নির্ভরশীল , তার চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল।
মোদ্দা কথা , মানুষকে আল্লাহর প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করায় এবং সে আল্লাহ্ তা‘
আলার খলীফাহ্ বিধায় তার গুণাবলী আল্লাহর গুণাবলীর অনুরূপ। অতএব , সে ইচ্ছাশক্তি , এখতিয়ার ও স্বাধীন কর্মক্ষমতার অধিকারী এবং এ কারণে তার কাজকর্ম আল্লাহ্ তা‘
আলার কাজকর্মের অনুরূপ। অতএব , এ থেকে শুধু মানুষের এখতিয়ারই প্রমাণিত হয় না , বরং মানুষের কাজকর্মের ধরন পর্যালোচনা করে আল্লাহ্ তা‘
আলার কার্যাবলীর ধরন উদ্ঘাটন করা যেতে পারে। কারণ , আল্লাহ্ তা‘
আলা মানুষের সত্তায় স্বীয় কার্যাবলীর ধরন নিহিত রেখেছেন এবং সে তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই কাজ করে থাকে।
এ হলো গুণাবলী ও কাজকর্মের দিক থেকে আল্লাহ্ তা‘
আলা ও মানুষের মধ্যকার মিল। তবে উভয়ের মধ্যে বিরাট অমিলও রয়েছে। এ অমিল হলো: আল্লাহ্ তা‘
আলা হচ্ছেন মানুষের স্রষ্টা , আর মানুষ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টি ; আল্লাহ্ অনাদি , অনন্ত ও অসীম সত্তা , আর মানুষ স্থান ও কালের গর্ভে আবির্ভূত সসীম সত্তা। আল্লাহ্ তা‘
আলার গুণাবলী ও সত্তা অভিন্ন , কিন্তু মানুষের সত্তা ও গুণাবলী বিভিন্ন। আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তার সাথে অভিন্ন বিধায় চিরন্তন ও চির পরিপূর্ণ , কিন্তু মানুষের যে কোনো গুণ তার সত্তায় সম্ভাবনা আকারে বিদ্যমান ও ক্রমবিকাশমান বা ক্রম-অর্জনীয়। সসীমতার কারণে মানুষ বস্তুদেহের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও যৌন প্রেরণার অধিকারী , কিন্তু অসীমতার কারণে তিনি এসবের প্রয়োজনীয়তা থেকে পরম প্রমুক্ত। জ্ঞান , যোগ্যতা ও ক্ষমতার পূর্ণতা ও অসীমতার কারণে আল্লাহ্ তা‘
আলার একক ও প্রত্যক্ষ কর্মে কোনোরূপ ত্রুটি অকল্পনীয় , কিন্তু অপূর্ণতা ও সসীমতার কারণে মানুষের যে কোনো কাজে দুর্বলতা ও ত্রুটির সম্ভাবনা থেকেই যায়। আল্লাহ্ তা‘
আলা তাঁর কাজের ক্ষেত্রে কারো বা কোনো কিছুর দ্বারা প্রভাবিত বা বাধাগ্রস্ত হন না ; তিনি যা-ই চান তা যেভাবে ও যে প্রক্রিয়ায় চান সেভাবে ও সে প্রক্রিয়ায় হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি , এখতিয়ার ও কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অ-প্রাকৃতিক কারণের দ্বারা বাধাগ্রস্ত বা প্রভাবিত হয় এবং সে যেভাবে চায় প্রায়শঃই হুবহু সেভাবে সংঘটিত হয় না। এর ফলে এটা সন্দেহাতীত যে , সে এখতিয়ারের অধিকারী বটে , তবে নিরঙ্কুশ এখতিয়ারের অধিকারী নয়।
বস্তুতঃ আমরা কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিদেরকে যেভাবে তার কার্যাবলী সম্পাদন করতে দেখি তা তার সত্তায় আল্লাহ্ তা‘
আলার কার্যাবলীর অনুসরণ ও অনুকরণের যে সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ , যদিও তার গুণাবলীর সীমাবদ্ধতার কারণে সে হুবহু তা অনুকরণ ও অনুসরণ করতে সক্ষম হয় না , বরং তার কাজে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কাজ পর্যালোচনা করে আল্লাহ্ তা‘
আলার কাজের ধরন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।
আমরা দেখতে পাই যে , কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক বা সর্বময় কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি যে সব কাজ নিজেই সম্পাদনে সক্ষম তার মধ্য থেকে অনেক কিছুই অন্যের দ্বারা সম্পাদন করিয়ে নেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তি বা প্রতিনিধিকে যেমন কাজের এখতিয়ার প্রদান করেন তেমনি কাজ সম্পাদনের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং তার কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। মালিক বা সর্বময় কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি সাধারণতঃ নীচের দিকের কর্মকর্তা , কর্মচারী , শ্রমিক ও চাকর-চাকরানীদেরকে স্বয়ং নিয়োগ দেন না , বরং এ দায়িত্ব প্রতিনিধি বা উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের হাতে ছেড়ে দেন , তবে প্রয়োজন বোধে কখনো কখনো কতককে নিজেই নিয়োগ দেন বা বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়োগদানের জন্য প্রতিনিধি বা উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের পথনির্দেশ দেন বা বাধ্য করেন। অনেক ক্ষেত্রে একজন মালিক বা কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি এমন ব্যক্তিকে কোনো গুরুদায়িত্ব প্রদান করতে পারেন যে ব্যক্তি যোগ্য কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বস্ত নয়। এর কারণ হয়তো পুরোপুরি বিশ্বস্ত সুযোগ্য লোকের অভাব। আবার বিশ্বস্ত লোককে গুরুদায়িত্ব প্রদান থেকে বিরত থাকেন ; কারণ , সে বিশ্বস্ত হলেও সুযোগ্য নয়। ক্ষেত্রবিশেষে এমন লোককেও দায়িত্ব দেয়া হতে পারে যে ব্যক্তি বিশ্বস্তও নয় , সুযোগ্যও নয় ; কারণ উভয় ধরনের লোকের অভাব। এটা আল্লাহ্ তা‘
আলার সৃষ্টিব্যবস্থাপনারই প্রতিফলন। মানুষ যে , এ ধরনের ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করতে পেরেছে এবং তা কার্যকর করতে সক্ষম হচ্ছে তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘
আলার সৃষ্টিব্যবস্থাপনারই অংশবিশেষ মাত্র। তবে আল্লাহ্ তা‘
আলা তাঁর প্রত্যক্ষ কর্মে , যেমন: নবী-রাসূলগণকে (আঃ) স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে কখনোই ভুল ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন নি , কিন্তু মানুষ মালিক বা কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি যথোপযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি সত্ত্বেও সঠিক মনে করেই ভুল ব্যক্তিকে স্বীয় প্রতিনিধি তথা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করতে পারেন ।
মানবিক জগতে কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর নিয়োজিত প্রতিনিধি , কর্মকর্তা , কর্মচারী , শ্রমিক ও চাকর-চাকরানীদের কাজে কাজটি সম্পাদনকালে পদে পদে হস্তক্ষেপ করেন না , বরং কাজের শেষে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদনকারীকে পুরস্কৃত করেন এবং কাজে ইচ্ছাকৃত ত্রুটি সৃষ্টিকারী , ক্ষমতা ও দায়িত্বের অপব্যবহারকারী ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করলে কাজ সম্পাদনকালেও তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে , স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘
আলাও তাঁর প্রাণশীল সৃষ্টিকুলকে , বিশেষ করে মানুষকে কাজ করার ক্ষমতা ও এখতিয়ার দিয়েছেন এবং তাদের কাজের ওপর নযর রাখেন , আর প্রয়োজন হলে যে কোনো সময় হস্তক্ষেপ করেন। তবে সীমাবদ্ধতার অধিকারী হওয়ার কারণে কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন , প্রতিনিধি ও কর্তাব্যক্তিদের নিয়োগদান , কাজের দিকনির্দেশ প্রদান , তাদের কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা , কাজে হস্তক্ষেপ এবং তাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ভুল করতে পারেন , কিন্তু যে কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা থেকে প্রমুক্ত সত্তা আল্লাহ্ তা‘
আলা কোনো ব্যাপারেই বিন্দুমাত্র ভুল করেন না।
আল্লাহ্ তা‘
আলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়টিও মানুষের আচরণ থেকে সহজেই বুঝা যেতে পারে। কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক বা সর্বময় কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি তার অধীনস্থ লোকদেরকে স্বীয় অঙ্গীকার বা তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকেন না। অনেক সময় তিনি এর বাইরেও অনেককে অনেক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। এ অনুগ্রহ প্রদর্শনের মানদণ্ডও সব সময় এক নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন অধীনস্থ ব্যক্তি কেবল তার চুক্তিভিত্তিক বা নিয়োগপত্রে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত থাকে না , বরং সে এর বাইরে অতিরিক্ত খেদমতও আঞ্জাম দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিক বা কর্তা তার কাছ থেকে অতিরিক্ত খেদমত চায় এবং তা সম্পাদন করায় তার জন্যে নির্ধারিত বিনিময় প্রদান করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিক বা কর্তা না চাইলেও সে স্ব-উদ্যোগে অতিরিক্ত কাজ করতে পারে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে তার কাজের উদ্দেশ্য দুই ধরনের হতে পারে: হয় সে মালিক বা কর্তাকে খুশী করার জন্য এ কাজ করে , কারণ সে জানে যে , মালিক বা কর্তা খুশী হলে কখনো না কখনো এবং কোনো না কোনোভাবে সে লাভবান হবেই , অথবা কোনো না কোনো কারণে সে মালিক বা কর্তাকে ভালোবাসে এবং তাঁকে ভালোবাসে বলেই কোনোরূপ বস্তুগত লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ ছাড়াই নির্ধারিত দায়িত্বের অতিরিক্ত খেদমত আঞ্জাম দেয়। অন্য কথায় , সে অতিরিক্ত খেদমত আঞ্জাম দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে এবং মালিক বা কর্তার স্নেহ-ভালোবাসা প্রাপ্তি ছাড়া কোনোকিছুর প্রতিই তার দৃষ্টি থাকে না। এমনকি এমনও হতে পারে যে , মালিক বা কর্তার ভালোবাসা প্রাপ্তির দিকেও তার দৃষ্টি নেই , বরং মালিক বা কর্তাকে ভালোবাসতে পেরে ও তদনুযায়ী কাজ করতে পেরেই সে নিজেকে ধন্য মনে করে। এ ধরনের কর্মী মালিক বা কর্তার বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী হয় এবং সে অনুগ্রহ বস্তুগত বা অবস্তুগত বা একই সাথে উভয় ধরনের হতে পারে।
আরো কতক ক্ষেত্রেও অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি মালিক বা কর্তার অনুগ্রহ বর্ষিত হতে পারে। কোনো কর্মী যে কাজ সম্পাদন করে তার বিনিময়ে যে বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তা কাজের বিচারে যথেষ্ট হলেও তার প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট না-ও হতে পারে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি মালিক বা কর্তার নিকট বিশেষ অনুগ্রহের জন্য আবেদন জানাতে পারে। তখন মালিক বা কর্তা তাকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করতে পারেন বা কোনো কারণে না-ও করতে পারেন ; তবে এ ক্ষেত্রে অনুগ্রহ প্রদানের সম্ভাবনার পাল্লাই ভারী থাকে। আবার এমনও হতে পারে যে , সে ব্যক্তি তার অসুবিধা সত্ত্বেও মালিক বা কর্তার নিকট অনুগ্রহের জন্য আবেদন না-ও জানাতে পারে। এমতাবস্থায় মালিক বা কর্তা তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করতে পারেন বা না-ও করতে পারেন ; তবে এ ক্ষেত্রে সাহায্য না করার সম্ভাবনাই প্রবল। শুধু তা-ই নয় , অধীনস্থ ব্যক্তি যে বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তা তার জন্যে যথেষ্ট হলেও এবং তার কোনো বিশেষ অভাব বা অসুবিধা বা সমস্যা না থাকলেও সে আরো বেশী আরাম-আয়েশের জন্য মালিক বা কর্তার কাছে অনুগ্রহের জন্য আবেদন জানাতে পারে। এ ক্ষেত্রেও মালিক বা কর্তা তার প্রতি অনুগ্রহ করতেও পারেন বা না-ও করতে পারেন। অবশ্য মালিক বা কর্তার এসব আচরণের (অনুগহ করা বা না করা) পিছনে বিভিন্ন ধরনের কারণ থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কোনো কর্মচারী মালিককে পসন্দ বা অপসন্দ করতে পারে , কাজে ফাঁকি দিয়ে থাকতে পারে বা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে থাকতে পারে , তার কোনো উত্তম গুণ বা কোনো খারাপ অভ্যাস থাকতে পারে , কোনো উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তির সাথে সম্পর্কের কারণে তার অনুকূলে সুপারিশ করা হয়ে থাকতে পারে , সে মালিক বা কর্তার কোনো বন্ধু বা প্রিয়জনের প্রিয়ভাজন বা অপ্রিয়ভাজন হয়ে থাকতে পারে। এভাবে জ্ঞাত-অজ্ঞাত আরো অনেক কারণ থাকতে পারে ; এমনকি এমন কারণও থাকতে পারে যে সম্পর্কে স্বয়ং ব্যক্তি নিজেও সচেতন নয় , বরং কেবল মালিক বা কর্তা অবগত আছেন বলেই তিনি তদনুযায়ী আচরণ করেন। এর মধ্যে কেবল স্বীয় বদান্যতা-গুণের কারণে অনুগ্রহকরণও অন্যতম।
বলা বাহুল্য যে , মানুষের এ সব আচরণ আল্লাহ্ তা‘
আলার আচরণের উদ্ঘাটনকারী। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘
আলাও এভাবেই আচরণ করেন এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সত্তাগতভাবে মানুষের মধ্যে এ প্রবণতা বিদ্যমান বিধায়ই তারা এরূপ আচরণ করে থাকে। তবে পার্থক্য এখানে যে একজন মানুষ মালিক বা কর্তার মধ্যে আল্লাহ্ তা‘
আলার সকল গুণই সসীম ও অপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার মধ্যে কোনো কোনো গুণ খুবই কম বা প্রায় শূন্য মাত্রায় থাকতে পারে। ফলে মানুষের আচরণে অন্যায় , সীমালঙ্ঘন , ভ্রান্তি , ভারসাম্যহীনতা ও অযৌক্তিকতা থাকতে পারে-আল্লাহ্ তা‘
আলার আচরণ যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত।
এ থেকে প্রমাণিত হয় যে , আল্লাহ্ তা‘
আলা তাঁর সৃষ্টিলোকে প্রাণশীল সৃষ্টিনিচয়ের জন্য , বিশেষ করে মানুষের কাজকর্ম সম্বন্ধে যে প্রক্রিয়া জারী রেখেছেন তা জাবর্-ও নয় , নিরঙ্কুশ এখতিয়ারও নয় , বরং জাবর্ ও এখতিয়ারের সমন্বিত রূপ। অর্থাৎ মানুষের ভাগ্য তার আওতা বহির্ভূত অসংখ্য কারণ দ্বারা ও আল্লাহ্ তা‘
আলার হস্তক্ষেপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত , কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ সব নিয়ন্ত্রণের অধীনে তার সীমিত পরিমাণ স্বাধীনতা ও এখতিয়ার রয়েছে। একজন মানুষ মালিক বা কর্তা যেভাবে তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিকে তার আওতা বহির্ভূত সীমাবদ্ধতা ও কাজে তজ্জনিত ত্রুটির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করেন না , কিন্তু তার আওতাভুক্ত ও এখতিয়ারাধীন বিষয়ে জবাবদিহি করতে বাধ্য করেন ও তার ভিত্তিতে শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করেন , তাতে এ সত্যেরই প্রতিফলন ঘটে যে , আল্লাহ্ তা‘
আলা মানুষকে তার আওতা বহির্ভূত সীমাবদ্ধতা ও আমলের ত্রুটির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করবেন না , কিন্তু তার যতটুকু স্বাধীনতা রয়েছে ততটুকুর জন্য তথা তার আওতাভুক্ত ও এখতিয়ারাধীন কার্যাবলীর ভালোমন্দের জন্য তার নিকট জবাবদিহি আদায় করবেন এবং তাকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। এ থেকে এ-ও জানা যায় যে , একজন কর্মীর আওতা বহির্ভূত সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটির ওপরে তার প্রতি মালিক বা সর্বময় কর্তার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি নির্ভর করে না , বরং তার নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ওপরে নির্ভর করে , তেমনি আওতা বহির্ভূত কারণে মানুষের পার্থিব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ধারিত হতে পারে বটে , কিন্তু তার পরকালীন সাফল্য ও ব্যর্থতা তথা আল্লাহ্ তা‘
আলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি কেবল এর ওপরই নির্ভর করে যে , সে কি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ তা‘
আলার সন্তুষ্টি অর্জনমূলক কাজ করেছে , নাকি তাঁর নির্দেশ অমান্য করার ও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছে।
 0%
0%
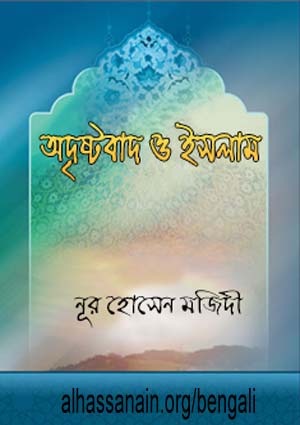 লেখক: নূর হোসেন মজিদী
লেখক: নূর হোসেন মজিদী