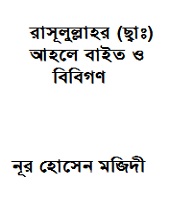পরিশিষ্ট-৩
কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে ছ্বাহাবী ও রাসূলুল্লাহর (ছ্বাঃ) যুগের মুনাফিক্ব্
বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ছ্বাহাবী ছিলেন তাঁরা যারা তাঁকে খুব সামান্য সময়ের জন্য হলেও ঈমানের ঘোষণার পরে তাঁকে চাক্ষুষভাবে দেখেছেন এবং মৃত্যুর আগে এ ঘোষণা পরিত্যাগ করেন নি। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর উক্তি হিসেবে দাবী করে একটি খব্ রে ওয়াহেদ্ হাদীছে বলা হয়েছে যে , তিনি এরশাদ করেছেন :
اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم
.-“
আমার ছ্বাহাবীরা হচ্ছে নক্ষত্রতুল্য ; তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে অনুসরণ করলেই তোমরা হেদায়াত পাবে। ” আরেকটি খব্ রে ওয়াহেদ্ হাদীছে বলা হয়েছে যে , রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) দশজন ছ্বাহাবীকে নামোল্লেখ করে তাঁদের জীবদ্দশায় বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এ দু’
টি খব্ রে ওয়াহেদ্ হাদীছের ভিত্তিতে , প্রচলিত সংজ্ঞার ছ্বাহাবীগণকে সমালোচনার উর্ধে গণ্য করা হয় ; এমনকি তাঁদের কারো সমালোচনা করলে সমালোচনাকারীকে কাফের বলেও ঘোষণা করা হয় , যদিও উক্ত সংজ্ঞা ও কুফরীর ফত্ওয়া ইসলামের কোনো অকাট্য জ্ঞানসূত্র (আক্ব্ল্ , কোরআন , মুতাওয়াতির্ হাদীছ ও প্রথম যুগ থেকে চলে আসা উম্মাহর মতৈক্য ভিত্তিক বিষয়াদি) থেকে গৃহীত হয় নি।
অন্যদিকে মুনাফিক্বের সংজ্ঞা কোরআন মজীদের একাধিক আয়াত্ থেকে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। মুনাফিক্ব্ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে মুখে ঈমানের দাবী করলেও অন্তরে ঈমানদার নয়। সুতরাং হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর যুগের মুনাফিক্ব্ ছিলো সেই সব লোক যারা মুখে ঈমানের ঘোষণা দিলেও এবং বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের ন্যায় আমল করলেও অন্তরে ঈমান পোষণ করতো না ; এরা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) , ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অকল্যাণ কামনা করতো , গোপনে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রাখতো এবং সুযোগ পেলেই রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ) , ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করতো ; নিঃসন্দেহে তাদের ও রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ওফাতের পরে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যকার মুনাফিক্বদের এ চরিত্র ও অপচেষ্টা রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ওফাত-পরবর্তী যুগ সমূহেও অব্যাহত থাকে।
এবার আমরা দেখবো যে , কোরআন মজীদের দৃষ্টিতে ছ্বাহাবী সংক্রান্ত বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞাটি সঠিক কিনা এবং বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞাটি সঠিক হলে ছ্বাহাবীদের নক্ষত্রতুল্য বলে অভিহিতকারী হাদীছটি ও দশজন ছ্বাহাবীকে জীবদ্দশায় বেহেশতের সুসংবাদ প্রদানকারী হাদীছটি-যে দু’
টি হাদীছের ভিত্তিতে বহুলপ্রচলিত সংজ্ঞার ছ্বাহাবীদের কারো সমালোচনাকারীকে কাফের বলে ফত্ওয়া দেয়া হয়-ছ্বহীহ্ কিনা।
যারা উপরোক্ত প্রচলিত সংজ্ঞার ছ্বাহাবীদের মর্যাদা ও জীবদ্দশায় দশজন ছ্বাহাবীর বেহেশতের সুসংবাদ লাভের ধারণায় বিশ্বাসী তাঁরা সাধারণতঃ তাঁদের মতের সপক্ষে কোরআন মজীদের দু’
টি আয়াত্ উদ্ধৃত করে থাকেন ; একটি হচ্ছে সূরাহ্ আত্-তাওবাহর ১০০ নং আয়াত্ এবং আরেকটি হচ্ছে সূরাহ্ আল্-ফাত্ হ্-এর ২৯ নং আয়াত্।
সূরাহ্ আত্-তাওবাহর ১০০ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে :
)
وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(
“ আর মুহাজিরদের মধ্যকার প্রথম অগ্রবর্তীগণ ও তাদেরকে সাহায্যকারীগণ (আন্ ছ্বার্ গণ) এবং যারা (এ ব্যাপারে) তাদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণ করেছে , আল্লাহ্ তাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর (আল্লাহর) ওপর সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদেরকে সেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে ; তারা সেখানে চিরদিন থাকবে ; বস্তুতঃ এ এক বিরাট সাফল্য। ”
আর সূরাহ্ আল্-ফাত্ হ্-এর ২৯ নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে :
)
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا(
“ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ও যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের ওপর অত্যন্ত কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি দয়াশীল তাদের মধ্যকার যারা ঈমান এনেছে ও যথাযথ আমল করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও বিরাট পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ”
এখানে আলোচনার শুরুতেই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে , কোরআন মজীদে বিশেষভাবে বা সুনির্দিষ্টভাবে নামোল্লেখ করে কোনো মানুষকেই জীবদ্দশায় বেহেশতের আগাম সুসংবাদ দেয়া হয় নি ; সুসংবাদ দেয়া হয়েছে ঈমান ও আমলের শর্তে সাধারণভাবে। যদিও আমরা জানি যে , নবী-রাসূলগণ (‘
আঃ) সহ আল্লাহর খাছ্ব বান্দাহ্ গণ-যারা আল্লাহ্ তা’
আলার পরিপূর্ণ আনুগত্যের ওপর ইন্তেকাল করেছেন-অবশ্যই বেহেশতে যাবেন , কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁদের কাউকেই , এমনকি হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)কে-যাকে আল্লাহ্ তা’
আলা জগতসমগ্রের জন্য তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত্ বলে উল্লেখ করেছেন , তাঁকেও বেহেশতের আগাম সুসংবাদ দেয়া হয় নি। আল্লাহ্ তা’
আলা নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর উদ্দেশে এরশাদ করেন :
)
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ(
“ (হে রাসূল!) বলুন , আমি রাসূলদের মধ্যে কোনো অভিনব রাসূল নই এবং আমি জানি না আমার কাছে যা ওয়াহী করা হয়েছে তা ব্যতীত আমি যদি অন্য কিছুর অনুসরণ করি তাহলে আমার ও তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে। আর আমি তো সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী বৈ নই। ” (সূরাহ্ আল্-আহ্ ক্বাফ্ : ৯)
এমতাবস্থায় এটা কী করে সম্ভব যে , আল্লাহ্ তা’
আলা নামোল্লেখ করে দশজন ছ্বাহাবীকে বেহেশতের আগাম সুসংবাদ দিয়ে থাকবেন ? সুতরাং সংশ্লিষ্ট হাদীছটি রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর নামে রচিত একটি মিথ্যা হাদীছ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।
এখানে বিস্তারিত আলোচনার মতো অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও সংক্ষেপে এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট বলে মনে হয় যে , যেহেতু মানুষকে আল্লাহর গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা’
আলা নিরঙ্কুশ স্বাধীন সেহেতু যে কোনো মানুষের পক্ষেই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করতে চাওয়া অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে বসা অসম্ভব নয় , এমনকি নবী-রাসূলগণের (‘
আঃ) পক্ষেও নয়। উপরোদ্ধৃত আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)কে যে বলতে বলা হয়েছে“
আমার কাছে যা ওয়াহী করা হয়েছে তা ব্যতীত আমি যদি অন্য কিছুর অনুসরণ করি ” -এতেই এ সত্য নিহিত রয়েছে যে , তাঁর নাফরমানী করার ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয় নি।
এর সাথে অবশ্য ইছ্বমাত্ (নিষ্পাপত্ব)-এর কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই। কারণ , নবী-রাসূলগণ (‘
আঃ) ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামগণের (‘
আঃ) নিষ্পাপত্বের মানে এই নয় যে , তাঁদের মধ্য থেকে গুনাহ্ করার ক্ষমতা বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। তাহলে তো তাঁরা ফেরেশতা সমতুল্য হয়ে যেতেন এবং সে ক্ষেত্রে তাঁদের মাধ্যমে আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা’
আলার হুজ্জাত্ পূর্ণ হতো না। কারণ , সে ক্ষেত্রে তাঁদেরকে আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য হিসেবে নির্ধারণ করা আল্লাহ্ তা’
আলার সুবিচারের ছ্বিফাতের বরখেলাফ হতো। তাই তাঁদের ইছ্বমাতের স্বরূপ হচ্ছে এই যে , তাঁদের মধ্য থেকে নাফরমানীর ক্ষমতা বিলুপ্ত না করা সত্ত্বেও রক্তধারার পবিত্রতা , জন্মের পর থেকেই পূতপবিত্র জীবনের অভ্যস্ততা ও খোদায়ী ওয়াহীর জ্ঞানের কারণে , বিশেষতঃ ইল্ মে হুযূরীর কারণে , তাঁরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকেন।
এখানে বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। তা হচ্ছে ,“
মা’
ছূম্ ” একটি পরিভাষা ; ওপরে যে অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে সে অর্থেই নবী-রাসূলগণ (‘
আঃ) ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামগণ (‘
আঃ) মা’
ছূম্ ছিলেন , নচেৎ শব্দটি যদি অক্ষরিকভাবে‘
নিষ্পাপ ’ অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে গুনাহ্ করার ক্ষমতা আছে এমন কোনো ব্যক্তিকেই জীবদ্দশায় মা’
ছূম্ বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। যদিও নবী-রাসূলগণ (‘
আঃ) ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমামগণ (‘
আঃ) গুনাহ্ করার ক্ষমতা ও এখতিয়ারের অধিকারী থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অবস্থার আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে , বাস্তবে তাঁদের পক্ষে গুনাহ্ করার সম্ভাবনা ছিলো এতোই ক্ষীণ যে , তা শতাংশের ভগ্নাংশেও প্রকাশ করা সম্ভব নয় , তথাপি যেহেতু তাঁরা এ ব্যাপারে অক্ষম ছিলেন না সেহেতু প্রচলিত পারিভাষিক অর্থে তাঁরা অবশ্যই মা’
ছূম্ ছিলেন এবং তাঁরা যে বেহেশতে যাবেন এ ব্যাপারে মানুষের পক্ষে সন্দেহ করার বিন্দুমাত্র কারণ ছিলো না , বরং নির্দ্বিধায় বলা সম্ভব ছিলো যে , তাঁরা অবশ্যই বেহেশতে যাবেন এবং বেহেশতবাসীদের মধ্যে অগ্রবর্তী হবেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বয়ং আল্লাহ্ তা’
আলার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে বেহেশতী হিসেবে অগ্রিম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া সম্ভবপর ছিলো না।
বিষয়টি মানুষের আচরণ থেকে দৃষ্টান্তের মাধ্যমেও অনুধাবন করা যেতে পারে। তাঁদের ইছ্বমাতের (নিষ্পাপত্বের) দৃষ্টান্ত হচ্ছে অত্যন্ত উন্নত রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় যিনি চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও ফুটপাতে খোলা অবস্থায় বিক্রি করা হয় এমন খাবার খান না। এহেন ব্যক্তি যদি এমন অবস্থার মুখোমুখি হন যে , ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন এবং সেখানে খাবার মতো কিছুই নেই এমতাবস্থায় তিনি যদি কোথাও মানুষের মল পেয়ে যান এবং জানেন যে , তাতে পুষ্টি আছে বলেই কুকুর তা খায় , সুতরাং তা খেয়ে জীবন বাঁচানো সম্ভব , তথাপি তিনি তা খেয়ে জীবন বাঁচাবেন এমন সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও আছে বলে আমরা মনে করি না। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে ও আক্ষরিকভাবে তাঁর পক্ষে তা খাওয়া অসম্ভব বলা যাবে না। সুতরাং এ বিষয়টির ওপরে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ বাযী (ধরুন বিলিয়ন ডলারের) ধরবেন না।
আর মানুষের পক্ষ থেকে মা’
ছূমগণকে (‘
আঃ) জীবদ্দশায় বেহেশতী বলে অভিহিত করা ও আল্লাহ্ তা’
আলার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদেরকে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি না দেয়ার উপমা হচ্ছে একজন ব্যতিক্রমী প্রতিভাবান ছাত্রের ন্যায় যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক ও আশেপাশের লোকদের সকলেই নিশ্চয়তার সাথে জানে যে , বরাবরের মতো আগামী পরীক্ষায়ও সে প্রথম হবে এবং নতুন ক্লাসে তার ক্রমিক নম্বর হবে‘
এক ’ , তাই তারা নিশ্চয়তার সাথে বলে যে , আগামী বছরের ক্লাসে সে-ই‘
প্রথম ছাত্র ’ , তথাপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত হবার আগে পরবর্তী বছরের ছাত্রহাযিরা খাতায় তার নাম প্রথম ক্রমিকে তুলে রাখবেন না। কারণ , তা করলে ঐ ছাত্রের পক্ষে আলসেমি বা দুষ্টামি করে হলেও পরীক্ষা দেয়া হতে বিরত থাকা অসম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের উক্ত কাজ হবে তাঁর পদমর্যাদার অনুপযোগী একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ।
একইভাবে নবী-রাসূলগণ সহ মা’
ছূমগণকে (‘
আঃ) যদি জীবদ্দশায় বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হতো তাহলে তাঁদের পক্ষে মানুষের মধ্যে নিহিত নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার ঐশী গুণের ব্যবহার করে আল্লাহর নাফরমানী করে বসা অসম্ভব হতো না। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা’
আলা ওয়াদা বরখেলাফ করেন না সেহেতু নাফরমানী করলেও তাঁদেরকে বেহেশতে নিতে হতো। কিন্তু কোনো নবী গুনাহর কাজ করলে বান্দাহ্ দের জন্য খোদায়ী হুজ্জাত পূর্ণ হতো না , কারণ , মুখ্ লিছ্ব লোকদের পক্ষেও এ ধরনের নবীর নবুওয়াতের ব্যাপারে ইয়াক্বীনের অধিকারী হওয়া সম্ভব হতো না। তাই , এ কালের পরিভাষায় বলা যেতে পারে যে , আল্লাহ্ তা’
আলা কোনো নবীকে ব্লাঙ্ক চেক্ দেন নি। তাহলে তা দশজন ছ্বাহাবীকে কী করে দেয়া হতে পারে ?
এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছে যে , ইসলামের সকল ধারার হাদীছগ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ্ অনুযায়ী নবী করীম (ছ্বাঃ) যে হযরত ফাত্বেমাহ্ (সালামুল্লাহ্‘
আলাইহা)কে‘
বেহেশতে নারীদের নেত্রী ’ এবং হযরত ইমাম হাসান্ ও হযরত ইমাম হোসেন (‘
আঃ)কে‘
বেহেশতে যুবকদের নেতা ’ বলে উল্লেখ করেছেন তার ব্যাখ্যা কী ?
এর ব্যাখ্যাও ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট। এটা স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক ও আশেপাশের লোকদের পক্ষ থেকে পরীক্ষার আগেই কোনো ছাত্রকে পরবর্তী ক্লাসের‘
প্রথম ছাত্র ’ হিসেবে উল্লেখ করার ন্যায় আক্ষরিকভাবে ও সন্দেহাতীতভাবে সত্য , তবে তাতে‘
ঠিকভাবে পরীক্ষা দেয়া সাপেক্ষে ’ শর্তটি উহ্য থাকে এবং এর মানে এ নয় যে , প্রধান শিক্ষক তার নাম পরীক্ষা সমাপ্ত হবার আগেই পরবর্তী বছরের ছাত্রহাযিরা খাতায় তুলে রেখেছেন।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে , আমি হাদীছের বিরোধী নই ; যারা নিঃশর্তভাবে সমস্ত হাদীছই প্রত্যাখ্যান করে তাদের বিরুদ্ধে আমি লিখেছি এবং তা পত্রপত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে , প্রচলিত হাদীছগ্রন্থ সমূহ হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওফাতের দুই শতাধিক বছর পরে সংকলন করা হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে মুখে মুখে বহু স্তরে একেকটি হাদীছ বর্ণিত হয়ে এরপর সংকলক পর্যন্ত পৌঁছেছে। সংকলকগণ নিজেরাও মিথ্যা হাদীছের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং তাঁরা যে সব হাদীছ সংগ্রহ করেছেন সেগুলোর মধ্য থেকে লক্ষ লক্ষ হাদীছকে মিথ্যা , বিকৃত , পরিবর্তিত ও দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁদের হাদীছসংকলন সমূহে স্থান দেয়া থেকে বিরত থাকেন। এমতাবস্থায় তাঁরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে সব হাদীছকে ছ্বহীহ্ মনে করে তাঁদের সংকলনে স্থান দিয়েছেন সে সবের মধ্যেও বহু জাল ও বিকৃত হাদীছ থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ , তাঁরা নবী-রাসূল ও খোদায়ী ওয়াহীপ্রাপ্ত ছিলেন না এবং তাঁরা নবী-রাসূলগণের (‘
আঃ) ন্যায় মা’
ছূম্ ছিলেন না। সুতরাং তাঁরা আমাদের মতোই গুনাহ্ ও ভুলের উর্ধে ছিলেন না যে , তাঁদের কাজ অবশ্যই নির্ভুল হবে।
অন্যদিকে মুসলমান হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ওপর ঈমান আনা শর্ত , এ ব্যক্তিদের ওপর ঈমান আনা শর্ত নয়। তেমনি যদিও রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর দ্বীন ও শরী’
আত্ সংশ্লিষ্ট এবং আদর্শিক , শিক্ষামূলক ও তথ্যমূলক যে কোনো কথাই ওয়াহী (মাত্ লূ বা গ্বায়রে মাত্ লূ) হিসেবে মেনে নেয়া যরূরী , কিন্তু তাঁর কথা হিসেবে দাবী করে বলা হয়েছে অন্য লোকদের এ ধরনের যে কোনো কথাকেই তাঁর কথা বলে মেনে নেয়া একটি ভ্রান্ত ও অসতর্ক কর্মনীতি এবং তা দ্বীন ও ঈমানের জন্য খুবই ঝুঁকির ব্যাপার। তাই খব্ রে ওয়াহেদ অর্থাৎ কোনো না কোনো স্তরে , বিশেষ করে প্রথম দিককার কোনো স্তরে কম সূত্রে বর্ণিত হাদীছ অবশ্যই কেবল চার অকাট্য দলীল (আক্বল্ , কোরআন , মুতাওয়াতির্ হাদীছ ও প্রথম যুগ থেকে সমগ্র উম্মাহর মতৈক্যভিত্তিক বিষয়াদি)-এর সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে কেবল গৌণ (মুস্তাহাব্ ও মাক্ রূহ্) ও প্রায়োগিক বিষয়াদিতে গ্রহণযোগ্য।
এবার আমরা ছ্বাহাবীদের সংজ্ঞা ও মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দেবো।
কেউ ঈমানের ঘোষণা সহকারে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)কে চাক্ষুষভাবে এক নযর দেখে থাকলে তিনিই ছ্বাহাবী-বহুলপ্রচলনকৃত এ সংজ্ঞাকে সঠিক বলে গ্রহণ করা হলে বলতে হবে“
ছ্বাহাবী ” স্রেফ একটি জনগোষ্ঠীর কালিক পরিচয় মাত্র ; ছ্বাহাবী হওয়ার মধ্যে কোনো বিশেষ ফযীলত্ নিহিত নেই। কারণ , রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)কে চাক্ষুষভাবে এক নযর দেখা এমন কোনো কাজ নয় যা কাউকে আল্লাহ্ তা’
আলার আদেশ-নিষেধের অনুবর্তিতার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। কারণ , ছ্বাহাবীর এ সংজ্ঞা কোরআন মজীদে বা মুতাওয়াতির হাদীছে আসে নি এবং এ ব্যাপারে সমগ্র উম্মাহর মধ্যে মতৈক্য (ইজমা’
)ও নেই। আর আক্বল্ ও এটা গ্রহণ করে না। এ সংজ্ঞা আপনার-আমার মতো মানুষের দেয়া যারা ভুল ও স্বার্থের উর্ধে ছিলেন না।
অন্যদিকে ছ্বাহাবী হওয়াকে যদি ফযীলতের ব্যাপার বলে গণ্য করতে হয় তাহলে এ সংজ্ঞা প্রত্যাখ্যাত এবং ছ্বাহাবীর সংজ্ঞা নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে। সংক্ষেপে তা হচ্ছে , যারা অন্তরে ও মুখে ঈমান এনেছিলেন এবং তদনুযায়ী আমল করতেন ও ইখলাছ্বের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)কে ভালোবাসতেন তাঁকে চাক্ষুষভাবে দর্শনকারী এমন ব্যক্তিগণই ছ্বাহাবী। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর সাথে কারো বাহ্যিক সাহচর্য (মা’
য়িয়াতে জিস্ মানী)ই কাউকে তাঁর ছ্বাহাবীতে পরিণত করে নি , বরং কেবল তাঁকে চাক্ষুষভাবে দর্শনকারী কোনো ব্যক্তির তাঁর সাথে আত্মিক সাহচর্য (মা’
য়িয়াতে রূহানী)ই তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর ছ্বাহাবীতে পরিণত করে।
সূরাহ্ আল্-ফাত্ হ্-এর ২৯ নম্বর আয়াতে“
ওয়াল্লাযীনা মা’
আহু ” বলতে দৃশ্যতঃ মা’
য়িয়াতে জিস্ মানী বুঝানো হয়েছে বলে তাৎপর্য গ্রহণের সুযোগ আছে বটে , তবে আল্লাহ্ তা’
আলা‘
ক্ষমা ও বিরাট পুরষ্কারের ’ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেবল তাঁদেরকে যারা তাঁর সাথে মা’
য়িয়াতে জিস্ মানী ও মা’
য়িয়াতে রূহানী এ উভয় ধরনের সাহচর্য রক্ষা করতেন। কারণ , আয়াতের শেষাংশে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে :“
তাদের মধ্যকার যারা ঈমান এনেছে ও যথাযথ আমল করেছে তাদেরকে ক্ষমা ও বিরাট পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ”
এ থেকে এটাও সুস্পষ্ট যে , নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর বাহ্যিক সহচরদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিলো দৃশ্যতঃ যারা বর্ণিত সকল গুণের আধার হলেও তাদের অন্তরে ঈমান ছিলো না , বরং তারা কোনো বিশেষ কারণে বা বিশেষ উদ্দেশ্য হাছ্বিলের লক্ষ্যে ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলো এবং বাহ্যিকভাবে প্রকৃত ছ্বাহাবীদের ন্যায়-যারা আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছিলেন-আমল করতো ।
এছাড়াও আয়াতের শুরুর দিকে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর সহচরদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ,“
তারা কাফেরদের ওপর অত্যন্ত কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি দয়াশীল ” । কিন্তু পরবর্তীকালে যখন একাধিক বার এরূপ ঘটেছে যে , তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন ও পরস্পরকে হত্যা করেছেন , তখন নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যকার একদল“
প্রকৃত ঈমান পোষণকারী ও যথাযথ আমল সম্পাদনকারী ” ছিলো না অর্থাৎ মুনাফিক্ব্ ছিলো যা-দেরীতে প্রকাশ পায়।
সূরাহ্ আত্-তাওবাহর ১০০ নং আয়াতের দলীল উপস্থাপন প্রসঙ্গে বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে , কোরআন মজীদ এবং তাঁর সূরাহ্ সমূহ ও আয়াত সমূহ থেকে সঠিক অর্থ গ্রহণের জন্য কিছু পূর্বপ্রস্তুতির (মুক্বাদ্দামাত্) শর্ত আছে ; কেবল তরযমার ওপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয় , এমনকি কেবল আরবী ভাষা জানা থাকাও কোরআন থেকে অর্থ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। যেহেতু কোরআন মজীদ একটি একক পূর্ণাঙ্গ সত্তা তাই এর অংশগুলো পরস্পর সম্পৃক্ত এবং এর একেকটি অংশ অপর এক বা একাধিক অংশকে ব্যাখ্যা করে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সমস্ত পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। এখানে শুধু একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই , তা হচ্ছে , কোরআন মজীদে অনেক আয়াতে“
সাধারণ ” (‘
আম্) বক্তব্য পেশ করা হয়েছে এবং অন্য আয়াতে হয়তো তার তাৎপর্যকে সীমিত করা (তাখ্ ছ্বীছ্ব) করা হয়েছে। সূরাহ্ আত্-তাওবাহর ১০০ নম্বর আয়াত্ টি এ ধরনের একটি সাধারণ তথ্য সম্বলিত আয়াত্। এতে সাধারণভাবে মুহাজেরিন ও আন্ ছ্বারদের মধ্যকার অগ্রবর্তীদের কথা বলা হয়েছে যাদের মধ্যে ব্যতিক্রম থাকা অসম্ভব নয়। কারণ , যে কোনো উত্তম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই অনুপ্রবেশকারী থাকতে পারে। তাছাড়াالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ
কতোজন ও কারা ছিলেন সে সম্পর্কে অকাট্য দলীলে , বিশেষতঃ কোরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত নেই। তাছাড়া হিজরত ও সাহায্যকরণের ব্যাপারে তাঁদের অনুসরণকারীদের বেলায়بِإِحْسَانٍ
শর্ত যোগ করা হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রেও তাঁরা ক’
জন ও কে কে তা কোনো অকাট্য দলীল থেকে জানা যায় না।
অন্যদিকে কোরআন মজীদে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর যুগের যে মুনাফিক্ব্ দের কথা বলা হয়েছে তাদের সকলেই ছিলো ঈমানের ঘোষণা সহ তাঁকে দর্শনকারী তথা প্রচলিত সংজ্ঞার ছ্বাহাবী। কারণ , আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন :
)
إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ(
“ (হে রাসূল!) মুনাফিক্ব্ রা যখন আপনার কাছে আসবে তখন বলবে , আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে , অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল। ” (সূরাহ্ আল্-মুনাফিক্বুন্ : ১) অতএব , তাদের ঈমানের ঘোষণা সহ রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)কে চাক্ষুষভাবে দেখার ব্যাপারে সন্দেহ নেই।
প্রশ্ন হচ্ছে , মুনাফিক্বরা সংখ্যায় ক’
জন ছিলো ?
প্রণিধানযোগ্য যে , সূরাহ্ আত্-তাওবাহর উক্ত ১০০ নম্বর আয়াতের পরেই অর্থাৎ ১০১ নম্বর আয়াতেই এদের বিরাট সংখ্যার ব্যাপারে আভাস দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে :
)
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ(
“ আর তোমাদের আশেপাশে যারা আছে তাদের মধ্যকার আরবদের মধ্যে মুনাফিক্বরা আছে এবং মদীনাহ্ বাসীদের মধ্যেও (মুনাফিক্বরা আছে)-যারা নেফাক্বের ওপরে খুবই কঠোর। (হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে (মুনাফিক্ব হিসেবে) চিনেন না , কিন্তু আমি তাদেরকে চিনি। ”
অনেকে অবশ্যأعْرَابِ
-এর মানে করেন (বেদুঈন বা যাযাবর আরব) যদিওأعْرَابِ
হচ্ছেعرب
শব্দের বহুবচন এবংأعْرَبِ
মানে বিশুদ্ধ আরব বা বেদুঈন যাযাবর আরব। এমনকি যদি‘
বেদুঈন বা যাযাবর আরব ’ অর্থকেই সঠিক বলে ধরা হয় তাতেও পার্থক্য হচ্ছে না। কারণ , তারা ঈমানের ঘোষণা প্রদানকারী ছিলো এবং এ কারণে ছ্বাহাবী হিসেবে পরিচিত ছিলো। অর্থাৎ মুহাজির ও আন্ ছ্বার নির্বিশেষে তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মুনাফিক্ব লুকিয়ে ছিলো। আর এই বিপুল সংখ্যক মুনাফিক্বের মধ্যে কেবল আব্ দুল্লাহ্ ইব্ নে উবাই সহ দু’
চার জন ছাড়া অকাট্যভাবে আর কাউকেই মুনাফিক্ব্ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় নি এবং এদের সকলেই ছ্বাহাবী হিসেবে পরিচিত।
এছাড়া মক্কাহ্ বিজয়ের দিনে যারা পরিস্থিতির চাপে পড়ে ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলো তাদের ঈমান আল্লাহ্ তা’
আলা কবূল করেন নি (সূরাহ্ আস্-সাজদাহ্ : ২৮-২৯) । কিন্তু তারাও ছ্বাহাবী হিসেবে পরিচিত হয়েছে।
সুতরাং ছ্বাহাবীর প্রচলিত সংজ্ঞাকে মানলে ছ্বাহাবী হওয়াকে কোনো ফযীলতের ব্যাপার বলে গণ্য করা চলে না। অতএব , তাঁদের কাজকর্ম বিচার করে তাঁদের প্রত্যেকের অবস্থা সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ভাবে ধারণা নিতে হবে। আর ছ্বাহাবী হওয়াকে ফযীলতের ব্যাপার বলে গণ্য করতে হলে ছ্বাহাবীর সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে হবে এবং তৎকালীন লোকদের আমল বিচার করে কে ছ্বাহাবী ও কে নয় তা নির্ধারণ করতে হবে।
মক্কাহ্ বিজয়ের দিনে ঈমান
সূরাহ্ আস্-সাজদাহর ২৮ ও ২৯ নং আয়াতের ভিত্তিতে‘
মক্কাহ্ বিজয়ের দিনে যারা পরিস্থিতির চাপে পড়ে ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলো তাদের ঈমান আল্লাহ্ তা’
আলা কবূল করেন নি ’ -এ অভিমতের সাথে অনেকের দ্বিমত আছে , বিশেষ করে এ কারণে যে , কোনো কোনো তাফসীরে ও রেওয়াইয়াতে ২৯ নং আয়াতেরيَوْمَ الْفَتْحِ
কথাটির অর্থ করা হয়েছে‘
ফয়ছ্বালার দিন ’ অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন। তাই এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়।
উক্ত আয়াতদ্বয়ে এরশাদ হয়েছে :
)
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ(
“ আর তারা বলে: এ বিজয় কখন (আসবে) যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো ? (হে রাসূল!) বলুন , বিজয়ের দিনে কাফেরদের ঈমান তাদেরকে কোনো কল্যাণ দেবে না। ”
কোরআন মজীদ প্রধানতঃ তার সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফাছ্বাহাত্-বালাগ্বাতের কারণে মু ’ জিযাহ্। আর ফাছ্বীহ্ ও বালীগ্ব বক্তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে , যে কথা ও শব্দ তাঁর উদ্দেশ্য বুঝাবার জন্য সর্বাধিক উপযোগী তা-ই তিনি ব্যবহার করবেন। অন্যদিকে বহু অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ অর্থ বুঝাবার নিদর্শন না থাকলে বহুল প্রচলিত অর্থটিই গ্রহণ করতে হবে।
“ ফয়ছ্বালা ” শব্দটিও আরবী এবং কোরআন মজীদে শেষ বিচারের দিন বুঝাতে বেশ কয়েক জায়গায়يوم الفصل
ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে (সূরাহ্ আস্-সাজদাহ্: ২৮-২৯) আল্লাহ্ তা’
আলা“
ফয়ছ্বালার দিন ” বুঝাতে চাইলে ফাছ্বাহাত্-বালাগ্বাতের দাবী অনুযায়ীيوم الفصل
ব্যবহার করতেন।
অন্যদিকে“
ঈমান আনয়ন ” কথাটি শেষ বিচারের দিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যে , মনে করতে হবে , তারা সেখানে ঈমান আনবে , কিন্তু তা কাজে লাগবে না। আর যদি দুনিয়ার বুকে ঈমান আনে এবং আল্লাহর কাছে তাদের ঈমান আনয়ন কবূল হয় তো শেষ বিচারের দিনে“
কাফেরদের ঈমান কল্যাণ দেবে না ” উল্লেখ করার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং এর মানে একটাই যে , যে সব কাফের (মক্কাহ্-)বিজয়ের দিনে নিরুপায় হয়ে জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে ঈমানের ঘোষণা দিয়েছিলো তাদের ঈমান প্রকৃত ঈমান নয় এবং এ কারণে তা আল্লাহ্ তা’
আলার কাছে কবূল হয় নি। আর ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে , এ ধরনের লোকেরা ইসলামী উম্মাহর জন্য বিরাট বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিলো এবং তা যে তাদের নেফাক্বের কারণে হয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই।
মা’
ছূমগণের (‘
আঃ) প্রশ্নে ইত্ মামে হজ্জাত্ বনাম নেফাক্ব্
এখানে বিভ্রান্তি এড়ানোর লক্ষ্যে একটি বিষয়ে আলোকপাত করা যরূরী মনে করছি। এটা অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য যে , হযরত রাসূলের আকরাম (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় ঈমানের ঘোষণা প্রদানকারী কোনো কোনো লোক তাঁর কোনো কোনো কথা বা সিদ্ধান্তকে‘
সঠিক নয় ’ বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর আদেশ বা সিদ্ধান্ত অমান্য করেছেন। অন্যদিকে এ-ও অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য যে , নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তৎকালীন মুসলমানদের বেশীর ভাগই প্রথমেই আহ্ লে বাইতের (‘
আঃ) অন্যতম মা’
ছূম ব্যক্তিত্ব হযরত‘
আলী (আঃ)-এর নেতৃত্ব মেনে নেন নি এবং কেউ কেউ তাঁদের সাথে শত্রুতা-বিদ্বেষের পরিচয় দেয় , এমনকি আরো পরে কতক লোক তাঁদের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালায় ও তাঁদের অনেককে হত্যা করে। প্রশ্ন হচ্ছে , এরা কি মুসলমান ছিলো , নাকি মুনাফিক্ব ছিলো ?
এ ব্যাপারে সংক্ষেপে বলতে হয় যে , বিষয়টি ইত্ মামে হুজ্জাত্ ও সতর্কতার নীতির দৃষ্টিতে দেখতে হবে। (ইত্ মামে হুজ্জাত্ ও সতর্কতার নীতি সম্পর্কে আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।) তা হচ্ছে , যে ব্যক্তি ইখ্ লাছ্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নবী বা ইমামের (‘
আঃ) পরিচয় ইয়াক্বীন্ সৃষ্টিকারী পর্যায়ে অকাট্যভাবে লাভ না করার কারণে তাঁকে নবী বা ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে নি এ জন্য তাকে পাকড়াও হতে হবে না , বরং তাওহীদ ও আখেরাতে ঈমান এবং আমলে ছ্বালেহর কারণে এমন ব্যক্তি নাজাত্ লাভ করবেন , তবে এরূপ ব্যক্তি ইখ্ লাছ্বের অধিকারী হলে অন্ততঃ পূতচরিত্র ব্যক্তি হিসেবে নবী বা ইমামের (‘
আঃ) সরাসরি বিরোধিতা করা হতে বিরত থাকবেন। অন্যথায় অবশ্যই তাকে পাকড়াও হতে হবে।
হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওফাতের পর মুসলমানদের আচরণকে এর আলোকেই বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ মা’
ছূম্ ইমামের (‘
আঃ) মা’
ছূম্ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম হবার ব্যাপারে যাদের জন্য ইত্ মামে হুজ্জাত্ না হওয়ার কারণে তাঁকে গ্রহণ করেন নি কিন্তু তাঁর সহ আহ্ লে বাইত ও আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর সাথে প্রকাশ্য বিরোধিতা ও শত্রুতা-বিদ্বেষের আশ্রয় নেন নি তাঁদেরকে কিছুতেই মুনাফিক্ব্ বলা যাবে না। আর যদি বিষয়টি এমন হয় যে , তাঁদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি এ ব্যাপারে ইত্ মামে হুজ্জাত্ হওয়া সত্ত্বেও কোনো পার্থিব স্বার্থে সুবিধাবাদী নীতির কারণে তাঁদেরকে স্বীকার করা হতে বিরত থেকে থাকে , কিন্তু প্রকাশ্য বিরোধিতা ও শত্রুতা-বিদ্বেষের আশ্রয় না নিয়ে থাকে তো এ ধরনের লোকদের বিষয়টি আল্লাহ্ তা’
আলার ওপরে সোপর্দ ; কারণ , অন্তরের খবর কেবল তিনিই রাখেন।
সুতরাং কেবল আহ্ লে বাইত ও আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)কে গ্রহণ করা হতে বিরত থাকার জন্যই কাউকে মুনাফিক্ব বলে গণ্য করা যাবে না , যদি না সরাসরি তাঁদের সাথে বিরোধিতা ও শত্রুতা-বিদ্বেষের আশ্রয় না নিয়ে থাকেন।
এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে , হযরত রাসূলে আকরাম (ছ্বাঃ)-এর যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন , অনেক লোকের অন্ধ বিশ্বাসের বিপরীতে , তাঁদের মধ্যে এমন একটি বিরাট সংখ্যক লোক ছিলেন যাদের কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ছিলো খুবই সীমিত কারণ , তখন লেখাপড়ার প্রচলন ছিলো খুবই অল্প এবং নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় যাদের হাতে পুরো কোরআন মজীদের কপি ছিলো বা যারা পুরো কোরআন মজীদ মুখস্ত করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা তৎকালীন মোট মুসলমান-সংখ্যার তুলনায় শতকরা হারের দৃষ্টিতে দেখলে এক শতাংশেরও ভগ্নাংশ ছিলো। শুধু তা-ই নয় , অনেকের ঈমান ছিলো খুবই দুর্বল ও ভাসাভাসা। আল্লাহ্ তা’
আলা এরশাদ করেন :
)
قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا(
“ আরবগণ বলে : আমরা ঈমান এনেছি। (হে রাসূল! আপনি তাদেরকে) বলুন , তোমরা এখনো ঈমান আনয়ন করো নি , বরং তোমরা বলো যে. আমরা আত্মসমর্পণ করেছি (মুসলমান হয়েছি) , কিন্তু এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নি। তবে তোমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে তোমাদের আমল সমূহ থেকে কিছুই নিষ্ফল হবে না। ” (সূরাহ্ আল্-হুজুরাত্ : ১৪)
অনেকে অবশ্য উপরোক্ত আয়াতেরالأعْرَابُ
শব্দের অর্থ করেছেন‘
মরুবাসীগণ ’ বা‘
বেদুঈন আরবগণ ’ । যদিও এরূপ অর্থ করা ঠিক নয় , কারণ , ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি ,اعْرَابُ
হচ্ছেعرب
শব্দের বহুবচন , সুতরাং এতে মদীনাহর বাইরের শহর ও মরু নির্বিশেষে সকল এলাকার আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের সকলেই নবী করীম (ছ্বাঃ)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং তারা সংখ্যায় ছিলো অনেক। এমতাবস্থায় এ ধরনের যে সব লোকের ব্যাপারে আহ্ লে বাইত ও আলে মুহাম্মাদ (ছ্বাঃ)-এর সাথে সরাসরি বিরোধিতা বা শত্রুতা-বিদ্বেষের অকাট্য প্রমাণ নেই তাদেরকে মুনাফিক্ব্ হিসেবে গণ্য করা যাবে না , যদিও সূরাহ্ আত্-তাওবাহর ১০১ নং আয়াত্ অনুযায়ী এদের মধ্যেও বহু মুনাফিক্ব্ ছিলো।
 0%
0%
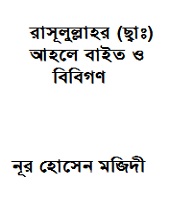 লেখক: নূর হোসেন মজিদী
লেখক: নূর হোসেন মজিদী