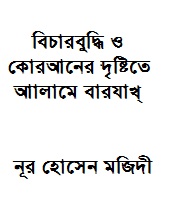দেহবিহীন আত্মার অনুভূতিশক্তি
এরপরও প্রশ্ন উঠতে পারে যে , মৃত্যুর পরে দেহবিহীন আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার অনুভূতিশক্তি থাকবে কিনা ? এ প্রশ্নের ভিত্তি হচ্ছে এই যে , দুনিয়ায় আমরা দেহের মাধ্যমে তথা দৈহিক ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধ্যমে বাইরের জগত সম্পর্কে তথ্যাদি আহরণ করি এবং সুখ-দুঃখের অনুভূতি অর্জন করি। দুনিয়ার বুকে আনন্দভোগ ও শাস্তিভোগ উভয়ই দেহের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অন্যদিকে শেষ বিচারের জন্য দেহসহ পুনরুত্থান সংঘটিত হবে এবং দেহসহই ব্যক্তিকে পুরষ্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। ধর্মীয় সূত্রও এটাই বলে এবং বিচারবুদ্ধিও এটাই দাবী করে। এমতাবস্থায় দেহবিহীন আত্মার সুখ-দুঃখের অনুভূতির সম্ভাবনা কতোখানি ?
এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে , পার্থিব জীবনেও মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই আনন্দ ও বেদনার অনেক অনুভূতি অর্জন করে থাকে। আর ক্ষেত্রবিশেষে তা দৈহিক ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধ্যমে অর্জিত অনুভূতির তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে। একজন মানুষকে প্রকাশ্য রাস্তায় অসম্মানজনক কথা বললে বা গালি দিলে ক্ষেত্রবিশেষে তা বেত্রাঘাত বা ছুরিকাঘাতের চেয়েও অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে।
অবশ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়ে থাকে তা-ও গুরুত্বহীন নয়। এ কারণেই পুনরুত্থান সংঘটিত হবে পার্থিব জীবনের ন্যায় দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে এবং বিচারবুদ্ধির দাবী অনুযায়ী এমনটিই হওয়া উচিত। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা অত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তুর জন্য অপরিহার্য নয়।) তবে পার্থিব জীবনে দেহ কেবল ব্যক্তিসত্তাকে অনুভূতি অর্জনে সহায়তাই করে না , বরং অনুভূতিঅর্জনক্ষমতার ওপর সীমাবদ্ধতাও আরোপ করে। কারণ , পার্থিব জীবনে ব্যক্তিসত্তার মনোযোগের একটি বিরাট অংশ , বরং সিংহভাগই তার দেহের প্রতি নিবদ্ধ থাকে - যাতে দেহ কোনো ভুল কাজ না করে , ভুলবশতঃ নিজের ক্ষতি না করে এবং বিপদে না পড়ে। ফলে জাগ্রত অবস্থায় অন্যান্য ক্ষেত্রে আত্মার বিচরণ ও অনুভূতি তার মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার তুলনায় খুবই সীমাবদ্ধ থাকে।
এছাড়া দেহের দুর্বলতা ও ক্লান্তি-শ্রান্তির কারণে ব্যক্তির জন্য ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা অবস্তুগত বিধায় তার ক্ষয় , দুর্বলতা ও ক্লান্তি-শ্রান্তি থাকতে পারে না , ফলে তার ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজন থাকতে পারে না। তেমনি জীবিত ও জাগ্রত অবস্থায় দেহের প্রতি আত্মার যে সিংহভাগ মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে মৃত্যুর পরে তার আর প্রয়োজন না থাকায় আত্মার অনুভূতি পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর থাকে এবং তার তৎপরতার ক্ষেত্র হয় ব্যাপকবিস্তৃত। এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য মৃত্যুর পর ব্যক্তির আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা আাল্লাহ্ তা‘
আলা কর্তৃক ফেরেশেতাদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত একটি জগতে সীমাবদ্ধতার আওতায় আসে। তবে এটা একটি স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়।
মোদ্দা কথা , মৃত্যুর ফলে দেহযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার ভালো-মন্দের অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে বা তার সকল প্রকার কর্মতৎপরতা অসম্ভব হয়ে পড়বে - বিচারবুদ্ধি এটা মানতে পারে না।
অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে , দেহযন্ত্র অচল হয়ে পড়ায় আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার কর্মতৎপরতার আওতা সীমিত হয়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু তার অনুভূতি না থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ , জীবদ্দশায় শরীরের যে অনুভূতি তা আসলে শরীরযন্ত্রের মাধ্যমে আত্মার অর্জিত অনুভূতি বৈ নয়। এমতাবস্থায় মৃত্যুর পরেও যদি আত্মা টিকে থাকে (এবং আসলেই টিকে থাকে) তাহলে তার সুখ-দুঃখের উর্ধে ওঠার ধারণার পিছনে কোনোই যৌক্তিকতা নেই।
দুনিয়ার জীবনে মানুষের আত্মা অতীতের ভালো ও সুখকর স্মৃতির কথা স্মরণ করে আনন্দিত হয় , ভবিষ্যতের শুভ সম্ভাবনার কথা ভেবে আশান্বিত হয়ে ওঠে , অতীতের তিক্ত স্মৃতি বা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য খারাপ পরিণতি আনয়নকারী অতীত ভুলভ্রান্তি এবং ভবিষ্যতের অনিবার্য দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করে হতাশ , ব্যথিত ও যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়ে। ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের আনন্দের অনুভূতি এমন চরমে উপনীত হতে পারে যে , এর আতিশয্যে তার মৃত্যু ঘটতে পারে। তেমনি ভবিষ্যত বিপদাশঙ্কাও এমন হতে পারে যে , তা তার মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। অন্যদিকে ভবিষ্যত দুঃখকষ্টের দুঃসহতার কথা চিন্তা করে তার হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক সময় আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে দেখা যায়। যুদ্ধে শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে নির্যাতিত হবার ভয়ে আহত সৈনিকের আত্মহত্যার ঘটনার কথাও অনেক শোনা যায়।
এ থেকে সুস্পষ্ট যে , আত্মা কেবল অতীত ও ভবিষ্যতের ভালো-মন্দের কারণেও বর্তমানে সুখ বা দুঃখ অনুভব করতে পারে। আর বলা বাহুল্য যে , এ ধরনের সুখ ও দুঃখ বস্তুগত বা দৈহিক নয় , বরং পুরোপুরি আত্মিক ব্যাপার। এমতাবস্থায় মৃত্যুর তথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর ব্যক্তির আত্মা অতীতের ভালো-মন্দ আমল এবং ভবিষ্যতের পুরষ্কার ও শাস্তির কথা চিন্তা করে আনন্দিত বা যন্ত্রণাকাতর ও অনুতপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক।
অবশ্য ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার আত্মা বস্তুগত দেহের অধিকারী না থাকায় শারীরিক তৎপরতা চালাতে সক্ষম হয় না। তেমনি সুচিন্তা ও অনুতাপ সহ যে সব আত্মিক কর্ম দুনিয়ার বুকে আঞ্জাম দিলে তা থেকে শেষ বিচারে ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতো মৃত্যুর পরে সে সব কাজ আঞ্জাম দিলে শেষ বিচারে লাভবান হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু তাই বলে মৃত্যুপরবর্তী জগতে ব্যক্তির আত্মিক তৎপরতা ও আত্মিক অনুভূতি বন্ধ হয়ে যাবে - তার কোনোই কারণ নেই। তবে আত্মা দুনিয়ার বুকে যে সব আত্মিক তৎপরতা চালায় মৃত্যুর পরে তার কতোখানি চালাতে পারে বা কতোখানি চালাবার স্বাধীনতা লাভ করে এবং কোন্ ধরনের ব্যক্তিদের আত্মা স্বাধীনতা লাভ করে এবং যারা তা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে কে কতোখানি স্বাধীনতা লাভ করেন তা এক ভিন্ন বিষয়। এ সম্পর্কে বিচারবুদ্ধি কিছুটা ধারণায় উপনীত হতে পারলেও বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভে সক্ষম নয়। কিন্তু ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার আত্মার সুখ-দুঃখের অনুভূতি এবং অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে এক অনস্বীকার্য ব্যাপার।
বিষয়টি একটি পার্থিব দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝার জন্য চেষ্টা করলে বুঝতে পারা সহজ হতে পারে। যেমন : ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দেয়ার পর যখন ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তখন যারা খারাপ পরীক্ষা দিয়েছে তারা তাদের অতীতের ভুলের জন্য মনস্তাপে ভুগতে থাকে এবং ফলাফল ঘোষণার পরে সম্ভাব্য অকৃতকার্যতা তার জন্য যে নিন্দা ও ধিক্কার ডেকে আনবে এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তা তার মধ্যে চরম যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে থাকে। অন্যদিকে যে ছাত্র ভালো পরীক্ষা দিয়েছে সে তার এ পরীক্ষার কারণে মানসিক প্রশান্তির অধিকারী থাকে এবং ভবিষ্যত শুভ ফলাফলের চিন্তা তার মধ্যে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে। শুধু তা-ই নয় , ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত না হওয়া সত্ত্বেও যারা এ দু’
জন ছাত্রের পড়াশুনা ও পরীক্ষার অবস্থা সম্পর্কে অবগত তারা খারাপ ছাত্রটির প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায় এবং আত্মীয়-স্বজন তাকে সমাদর করে না , অন্যদিকে সকলেই ভালো ছাত্রটির প্রতি স্নেহ-মমতার দৃষ্টিতে তাকায় ও তাকে খাতির করে , সমাদর করে। এ দুই বিপরীত আচরণও দুই ছাত্রের মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনুভূতির সৃষ্টি করে থাকে। মৃত্যুর পরমুহূর্ত থেকে শুরু করে পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে আত্মার অবস্থা এ অবস্থার সাথে তুলনীয়।
মোদ্দা কথা , বিচারবুদ্ধি মৃত্যুর পরবর্তী ও পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী সময়ে আত্মার অনুভূতি , সুখ-দুঃখ এবং তার ওপরে অতীত-ভবিষ্যতের প্রতিক্রিয়াকে একটি অপরিহার্য বিষয় বলে গণ্য করে।
আালামে বারযাখ্ কোথায় ?
বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে‘
আালামে বারযাখ্ বা মৃত্যুর পরবর্তী ও পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী জগত সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে : এ জগত কোথায় অবস্থিত ?
নিঃসন্দেহে এ জগতের বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে অকাট্যভাবে জানা বিচারবুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। তেমনি এর অবস্থান সম্পর্কে যেমন বিচারবুদ্ধির দাবী থাকতে পারে , তেমনি বিচারবুদ্ধি এ সংক্রান্ত কোনো কোনো সমস্যা উপস্থাপন করতে ও তার সম্ভাব্য জবাব প্রদান করতে পারে।
আমরা ইতিপূর্বে যেমন আলোচনা করেছি , বিচারবুদ্ধি মৃত প্রিয়জনদের আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা ও জীবিত প্রিয়জনদের মধ্যে নৈকট্য কামনা করে এবং এ কারণেই মৃতদের ব্যক্তিসত্তার ঘুমন্ত অবস্থা পসন্দ করে না , বরং জাগ্রত অবস্থা পসন্দ করে। অতএব , এ নৈকট্যের দাবী অনুযায়ী মৃতদের ব্যক্তিসত্তার জীবিতদের কাছাকাছি অবস্থানই কাম্য। অবশ্য কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মা বা ব্যক্তিসত্তা‘
আালামে বারযাখে কতোখানি স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ও জীবিত প্রিয়জনদের কাছাকাছি আসতে পারবে অথবা আদৌ সে সুযোগ পাবে কিনা তা স্বতন্ত্র বিষয় ; বিচারবুদ্ধি এ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে ও নিশ্চিতভাবে মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে , বিচারবুদ্ধি মৃতদের ব্যক্তিসত্তার জীবিতদের কাছাকাছি অবস্থান কামনা করে। অতএব , বিচারবুদ্ধির দাবী অনুযায়ী ,‘
আালামে বারযাখ্ এই পৃথিবীর বুকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর পরিবর্তে দূরবর্তী কোনো নক্ষত্রলোকে বা অন্য কোনো গ্যালাক্সিতে‘
আালামে বারযাখের অবস্থান হলে মানবমন প্রিয়জনদের ব্যক্তিসত্তার সুদূর লোকে অবস্থানজনিত বিষাদ অনুভব করতে বাধ্য। তাই এটা কাম্য নয়। বিশেষ করে‘
আালামে বারযাখের অবস্থান এ পৃথিবীর বুকে হতে যখন কোনো বাধা নেই এমতাবস্থায় তা দূরবর্তী কোনো নক্ষত্রলোকে বা গ্যালাক্সিতে তা হওয়ার কোনো কারণ নেই।
তবে বিচারবুদ্ধি‘
আালামে বারযাখের অনিবার্যভাবে মাটির নীচে হওয়াকেও মানতে পারে না। কারণ , এমন অনেক মানুষ আছে যাদের মৃতদেহকে মাটির নীচে ক্ববর দেয়া হয় না , বরং পুড়িয়ে ফেলা হয় , বা শীতল গৃহে সংরক্ষণ করা হয়। তাছাড়া অনেক লোক বন্যজন্তুর বা সামুদ্রিক প্রাণীর পেটে গিয়েছে এবং অনেকের শরীর পচেগলে পানিতে মিশে গিয়েছে ; তাদের জন্য মাটির ক্ববরের প্রশ্ন আসে না। তাই শরীরবিহীন ব্যক্তিসত্তার জন্য‘
আালামে বারযাখ্ কোথায় হবে তার সাথে তার মৃতদেহ কোথায় আছে তার সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য নয়। সুতরাং‘
আালামে বারযাখ্ যেমন এ পৃথিবীর বুকে হওয়া কাম্য তেমনি তা মাটির নীচে না হয়ে মাটির ওপরে হওয়াও কাম্য। আর আল্লাহ্ তা‘
আলার পক্ষে তা খুবই সহজসাধ্য। অবশ্য অধিকতর সঠিকভাবে বললে বলতে হয় , যেহেতু‘
আালামে বারযাখ্ একটি ভিন্ন মাত্রার অবস্তুগত জগত সেহেতু তার জন্য মাটির ওপর-নীচ ও এতদুভয়ের কোনো কিছুই বাধা নয় , বরং তার ক্ষেত্রে মাটির ওপর-নীচ কথাটা আদৌ প্রযোজ্য নয়।
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ,‘
আালামে বারযাখ্ যদি এ পৃথিবীর বুকেই থেকে থাকে তাহলে আমরা কেন মৃত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তাকে ও সে জগতের নিদর্শনাদি দেখতে পাই না ? তাছাড়া যে সব জনাকীর্ণ জনপদে মানুষ ব্যাপকভাবে বিচরণশীল ও কর্মতৎপর সে সব জায়গায় আরেকটি জগতের অস্তিত্ব কীভাবে সম্ভব ?
এ প্রশ্নের জবাবে আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে ,‘
আালামে বারযাখ্ হচ্ছে আত্মা বা ব্যক্তিসত্তার জগত। তাই তা এক ভিন্ন মাত্রার (Dimension
) জগত। এ কারণে একদিকে যেমন সে জগত আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয়ের ধারণক্ষমতার বাইরে অন্যদিকে একই কারণে বস্তুজগতের সাথে সে জগতের সাংঘর্ষিকতার প্রশ্ন আসে না।
এমনকি আমাদের পার্থিব জগতেও অভিন্ন স্থান-কালে কোনোরূপ সাংঘর্ষিকতা ব্যতীতই একাধিক অস্তিত্বের অবস্থানের দৃষ্টান্ত আছে। উদাহরণস্বরূপ , কাঁচ , বায়ু ও পানির মধ্য দিয়ে আলো অবাধে যাতায়াত করে এবং যাতায়াতকালে খুবই অল্প সময়ের জন্য হলেও (সেকেণ্ডের ক্ষুদ্রাংশের জন্য হলেও) এ সবের মধ্যে অবস্থান করে (যদিও স্থির অবস্থান নয় , বরং গতিশীল অবস্থায় অবস্থান , তবে অবস্থান করে অবশ্যই) । কিন্তু ঐ সব বস্তুর ভিতরে আলোর অবস্থান বা ওগুলোর ভিতর দিয়ে অতিক্রম করার জন্য ওগুলোকে অপসারণ করার প্রয়োজন হয় না।
একইভাবে , বিদ্যুত ধাতব পদার্থ , মাটি ও পানির মধ্য দিয়ে চলাচল করে এবং বিদ্যুততরঙ্গ এতদসহ সব কিছুর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ; এ জন্য কোনো কিছুকে অপসারণ করতে হয় না। চৌম্বক ক্ষেত্রও কোনো কিছু অপসারণ না করে অবস্থান করে। সর্বোপরি আমাদের দেহ জুড়ে যে আত্মার অবস্থান তা-ও বস্তুদেহের কোনো অংশকে অপসারণ না করেই অবস্থান করে। অতএব , এতে সন্দেহের কোনোই কারণ নেই যে ,‘
আালামে বারযাখ্ ভিন্ন মাত্রার জগত হবার কারণে এ বস্তুজগতের কোনো কিছুর অবস্থানকে বাধাগ্রস্ত না করেই এখানে অবস্থিত হতে পারে। আর ভিন্ন মাত্রার জগত হবার কারণেই আমরা আমাদের বস্তুদেহের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা‘
আালামে বারযাখের অস্তিত্ব ও সে জগতের ঘটনাবলী অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছি না।
আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার জগতেও অনেক কিছু বস্তুদেহের পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে ব্যর্থ হই। বায়ু পুরোপুরি অদৃশ্য এবং পূর্ণ স্বচ্ছ কাঁচ ও পানি প্রায় অদৃশ্য। অবশ্য এগুলোকে আমরা আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারি। কিন্তু আমরা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনোটি দ্বারাই আলো-কে সরাসরি অনুভব করতে পারি না ; কেবল কোনো বস্তুতে আলো পতিত হলে তা দেখা যাওয়ার কারণে আমরা আলোর অস্তিত্ব বুঝতে পারি। বিদ্যুত ও চৌম্বক ক্ষেত্রের ব্যাপারটিও অনুরূপ ; আমরা এতদুভয়ের অস্তিত্ব কেবল উভয়ের প্রতিক্রিয়া থেকেই বুঝতে পারি। অন্যদিকে রঞ্জন রশ্মি ও অতি লাল রশ্মি সহ এমন কতক রশ্মি আছে যা বায়ু , কাঁচ ও পানি ছাড়াও অন্যান্য স্থূল বস্তুকে - আমাদের প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার সাধারণ অলোকরশ্মি যেগুলোকে ভেদ করতে পারে না - ভেদ করে চলে যায় বিধায় সাধারণ আলোকরশ্মির মতো তা বস্তুতে পতিত হবার পর প্রতিফলিত হয় না , ফলে সাধাণভাবে আমরা ঐ সব রশ্মির অস্তিত্ব সরাসরি ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা পরোক্ষভাবেও অনুভব করি না ; কেবল বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যেই এ ধরনের আলোর প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ে। অথচ সংশ্লিষ্ট যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার আগেও এ ধরনের রশ্মির অস্তিত্ব ছিলো এবং তা বস্তুর ওপরে পতিত হয়ে তা ভেদ করে চলে যেতো , কিন্তু আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা না এ সব রশ্মির অস্তিত্ব বুঝতে পারতাম , না এ সবের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারতাম।
অতএব ,‘
আালামে বারযাখের অস্তিত্ব এ পৃথিবীর বুকে হওয়ার বিষয়টিকে অসম্ভব মনে করার কারণ নেই। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ,‘
আালামে বারযাখ্ আমাদের এ পৃথিবীতে হওয়ার মানে এ নয় যে , এ জগতের অস্তিত্ব এবং মৃত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তার অবস্থান ও বিচরণ কেবল মাটির ওপরে মানুষের স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে। বরং আসমান-যমীনের সর্বত্রই এ জগতের আওতাভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ , বস্তুদেহের যে সীমাবদ্ধতা আছে আত্মার জন্য সে ধরনের বস্তুগত সীমাবদ্ধতা থাকার প্রশ্ন আসে না যদি না সে জগতের পরিচালনাব্যবস্থার আওতায় বিশেষভাবে কারো ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়। অন্যদিকে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে যেমন রঞ্জন রশ্মি ও অতি লাল রশ্মির প্রতিক্রিয়া ধরা সম্ভব হচ্ছে তেমনি শক্তিশালী ব্যক্তিসত্তার অধিকারী জীবিত মানুষের পক্ষে‘
আালামে বারযাখের অবস্থা অবহিত হওয়া সম্ভব হতে পারে। এটাই বিচারবুদ্ধির রায়।
 0%
0%
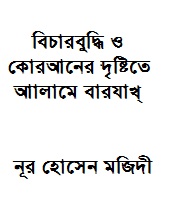 লেখক: নূর হোসেন মজিদী
লেখক: নূর হোসেন মজিদী